বিজ্ঞান এখন কিভাবে বাংলাভাষী কিশোরদের কাছে উপস্থাপিত হচ্ছে তার স্বরূপটা জানা প্রয়োজন। বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনার জনপ্রিয়তা তাদের মাঝে অনেকদিনের। ভালো বেতন, অসাধারণ বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া, বিখ্যাত বিজ্ঞানী হবার স্বপ্ন, এগুলি কিশোরদেরকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দেয়। কিন্তু তাদের কাছে বিজ্ঞানের অর্থ কি? তাদের যদি জানতে চাওয়া হয়, বিজ্ঞান মানে কি? তারা কী ভাবে? এটা জানা দরকার। আমাদের দেশে যারা বিজ্ঞানের প্রসারে কাজ করে যাচ্ছেন, তারা বিজ্ঞান নিয়ে লেখায় বিজ্ঞানকে কিভাবে উপস্থাপন করছেন জানাটা জরুরি।
লেখকের নিজের বিজ্ঞান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে বিজ্ঞানের ব্যাপারে উত্সাহিত করে যা কিছুই লিখুন না কেন তাতে নিজের খামখেয়ালিপনা, অবিজ্ঞানসুলভ ব্যাপারগুলো নিয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ থেকেই যাবে।
বিজ্ঞান নিয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠার পরে যখন একজন মানুষ বিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য বিষয়গুলোর সংঘাতপূর্ণ ব্যাপারগুলো নিয়ে প্রশ্ন শুরু করে, সেগুলোর উত্তর করতে আমাদের (অন্তত মুক্তমনাদের) অনেকের যথেষ্ট সময় ব্যয় হয়। অবৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করে সন্ধান দেবার চেষ্টা করা হয় বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তাদের স্বরূপ কি।
এই সংঘাতময় বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্নের নিরসন একান্ত জরুরী। কারণ আমাদের বিশ্বাস, প্রগতির পথে এই সংঘাত একটি অপচয়। এগিয়ে চলার পথে বাঁধা। তাই আমাদের প্রয়োজন পড়ে সেই বাঁধাগুলোকে অপসারণ করার।
বিজ্ঞানের বাইরের সংঘাতময় বিষয়গুলো নিয়ে বিজ্ঞানের সবচেয়ে শক্তিশালী দর্শনটির কিন্তু অনেক শক্তিশালী একটি অবস্থান আছে। আমাদের প্রয়োজন প্রশ্নগুলো নিরসনে এই দর্শনটির দিকে মনোনিবেশ করা। আর কেবল নিরসনের নিমিত্তেই নয়, বিজ্ঞানের সবচেয়ে শক্তিশালী দর্শন হিসেবে প্রয়োজন বিজ্ঞানের প্রসারে এই দর্শনের প্রসারকে অন্তর্ভুক্ত করা। কেননা বিজ্ঞানের উত্থানের পেছনের দর্শন ছিল এটি। আধুনিক বিজ্ঞানেও এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি।
আর এই দর্শনটি হলো প্রত্যক্ষবাদ (positivism)। যা মানুষের জল্পনা-কল্পনাপ্রসূত নয় বরং কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং যাচাইযোগ্য পর্যবেক্ষণকেই যথার্থ জ্ঞান মনে করে। এটি একটি সহজ সংজ্ঞা, তবে এর নিহিতার্থ কিন্তু ব্যাপক। যে তত্ত্ব পর্যবেক্ষণ-অসাধ্য তার আলোচনা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অর্থহীন। কেননা তা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়, যাচাই করা সম্ভব নয়। যাচাই-অযোগ্য কোনো কথার উপর ভরসার মানে কি?
প্রত্যক্ষবাদ যে পুরোপুরি বিজ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করে ফেলেছে তা নয়। তবে এর হাত ধরে অর্থপূর্ণভাবে এগোনো গেছে। খুব সহজ একটি সংজ্ঞায় আসা গেছে – “বিজ্ঞান হল পর্যবেক্ষণসংক্রান্ত পূর্বাভাসের প্রণালীবদ্ধ চর্চা।” ঠিক তাই। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে পূর্বাভাস করতে পারতে হবে। কারণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে হতে হবে যাচাইযোগ্য, যথার্থতা-নির্ধারণযোগ্য (falsifiable)। তত্ত্ব যখন পর্যবেক্ষণের উপর কোনো পূর্বাভাস দেবে, কেবল তখনই সুযোগ থাকবে পূর্বাভাসের নির্ভুলতার উপর ভিত্তি করে তার যথার্ততা নির্ধারণের।
প্রত্যক্ষবাদের সমালোচক আছে, বিশেষ করে সমাজ বিজ্ঞানে। আমার আগ্রহ, এ বিষয়ে প্রথমে বিজ্ঞানানুরাগীদের মাঝেই আলোচনার শুরু করা। লক্ষ্য, বাংলাভাষীদের মাঝে বিজ্ঞানের প্রসারে প্রত্যক্ষবাদী দর্শনকে সামনে নিয়ে আসা।
আমি বিজ্ঞানের বেশকিছু দেশী-বিদেশী ছাত্র, গবেষকের সাথে আলোচনা করে দেখতে পেয়েছি বিজ্ঞান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব। যেমন একজন আমাকে প্রস্তাব করেছেন – “বিজ্ঞানের লক্ষ্য যেহেতু পর্যবেক্ষণের সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যা, সেখানে একজন অধিকর্তার অনুমান বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেই কাঙ্ক্ষিত।” আমি তার প্রস্তাব নিয়ে কুতর্কে যাই নি, আমি কেবল ব্যাখ্যা করেছি যে বিজ্ঞানের লক্ষ্য পর্যবেক্ষণের সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যা নয়, বরং পর্যবেক্ষণের সবচেয়ে নিঁখুত পূর্বাভাস। ফলে ঘটে যাওয়া কোনো পর্যবেক্ষণকে একটি তত্ত্ব বা প্রস্তাব দ্বারা ব্যাখ্যা করা গেলেই কেবল চলবে না, সেই পর্যবেক্ষণের উপর তার পূর্বাভাস করার ক্ষমতা থাকতে হবে, যাতে প্রস্তাবটির যথার্থতা/সত্য-মিথ্যা যাচাই করা যায়। একজন যুক্তিপূর্ণ মানুষ এই ব্যাখ্যার পর আর অযৌক্তিক প্রস্তাব করেন না। কাব্যগ্রন্থে গ্রহ-নক্ষত্রের উল্লেখের পেছনে বিজ্ঞানকে খোঁজেন না।
আমার আকাঙ্ক্ষা, আগামী প্রজন্মে একদল বিজ্ঞানানুরাগী আসবে, যারা বিজ্ঞানের লক্ষ্য, দর্শন নিয়ে নিশ্চিত থাকবে। সংঘাতের প্রশ্নে যাদের নিরসন আছে সদা প্রস্তুত। যারা তাই সংঘাতের তর্কে কালাতিকাল ব্যয় করবে না, সহজে অন্যকে বুঝিয়ে দিবে ও এগিয়ে যাবে।
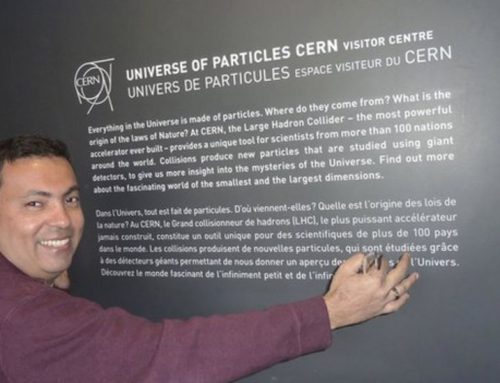
বিজ্ঞানের দর্শনের কতটা প্রভাব থাকতে পারে তা বোঝার জন্য Daubert Standard এর কথা বলা যেতে পারে যা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট জারি করে বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যকে সনাক্ত করার জন্য। এর প্রথম শর্তটিই হচ্ছে, সাক্ষ্যকে falsifiable হতে হবে।
যুক্তরাষ্ট্রের আরকানসাসের এক জজ creationism কে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে বাতিল করে আরকানসাসের পাবলিক স্কুলে না পড়ানোর রায় দেন এই falsifiability কে বিবেচনা করে।
ধ্রুবের সাথে উপরে আলোচনা করতে গিয়ে ‘দৃষ্টি বিভ্রমের’ (visual illusion) উদাহরণ হাজির করেছি যেখানে বক্ররেখাগুলোকে সর্পিলাকার কুন্ডলীর টানেল বলে বিভ্রম হচ্ছে ( যদিও বাস্তবতা ছিল, বক্ররেখাগুলো একেকটি বৃত্ত)। আরেকটা মজার ইল্যুশনের উদাহরণ দেই। নীচের ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হবে বৃত্তগুলো ঘূরছে । এটা কিন্তু আসলে কোন এনিমেটেড জিফ ফাইল নয়। আঁকার কারণে এমন বিভ্রম হচ্ছে। আপনি পরীক্ষা করতে চাইলে ছবিটির যে কোন এক জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন, দেখবেন অন্ততঃ সে জায়গার ঘোরাঘুরি থেমে গেছে –
[img]http://www.mukto-mona.com/illusion/optical-illusion-wheels-circles-rotating.png[/img]
ইন্দ্রিয়-প্রতারণার আরেকটি উদাহরণ!
@অভিজিৎ,
ওপটিকেল ইল্যুশন বা সাক্ষাৎ মে’রাজ –
নীচের ছবিটির নাকের উপর চারটি ছোট্ট ছোট্ট ডট আছে। ত্রিশ সেকেন্ড ডটের উপর চোখ রাখুন। এবার দেয়ালে বা ছাদে চেয়ে দেখুন, দেখবেন প্রভু ঈসা আপনার সামনে বসে আছেন। এভাবে আল্লাহকেও দেখা সম্ভব।
http://www.coolopticalillusions.com/illusions/jesus.gif
ধ্রুব,
একটা কথা প্রথমেই জানিয়ে রাখি – আপনার ব্যতিক্রমী লেখাগুলো সব সময়ই আমি মন দিয়ে পড়ার চেষ্টা করি। নিঃসন্দেহে আপনি মুক্তমনায় একজন উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আপনার লেখায় মন্তব্য কখনো কম দেখলেও হতাশ হবেন না। আপনার লেখা সব সময়ই একটা আলাদ মনোযোগ দাবী করে। তবে একটি সাজেশন দেয়া যায় যে, প্রবন্ধগুলো খুব স্ট্রার্চার্ড ভাবে না লিখে আরেকটু সাবলীলতা আনতে পারেন। অবশ্য এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত। আমি দেখেছি – কিছু মজার উদাহরণ, সমাজের কিছু প্যাটার্ন, কিছু পরিচিত উদাহরণ যোগ করলে বেশি করে পাঠকদের কাছে পৌঁছয়। কারণ অনেকেই আছে নিরস তত্ত্বকথায় বেশি পাত্তা দিতে চান না, মনোযোগ দেন তখনই যখন পরিচিত কিছু উদাহরণ খুঁজে পান। তবে আমার এই সাজেশন আপনার না শুনলেও চলবে। আপনার লেখা এমনিতেই ভাল, আগেই বলে দিচ্ছি।
এবারে ডেভিলস এডভোকেট হিসেবে আলোচনা শুরু করি। আপনার প্রত্যক্ষবাদের সাথে একমত পোষণ করেও আলোচনা করতে চাইছি কারণ আপনি নিজেই বলেছেন –
ঠিক আছে। ডেভিলস এডভোকেট হিসেবে তর্ক শুরু করি। শুরু করি আপনার বলা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা দিয়েই। আপনি প্রত্যক্ষবাদের সংজ্ঞায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু ইন্দ্রিয় কি মানুষকে প্রতারিত করে না? ধরুন, মানুষ একটা সময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার উপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী পৃথিবীর গোলত্বকে অস্বীকার করে ভেবে নিয়েছিল সমতল। কিংবা ভেবেছিল সূর্যই বুঝি পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে। কারণ মানুষের ইন্দ্রিয় এভাবেই মানুষকে প্রতারিত করেছে। আরো এগুই। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে পাওয়া উপসংহার গুলো যেমন কালের প্রসারণ (টাইম ডায়েলেশন) কিংবা দৈর্ঘ্যের সংকোচন (লেন্থ কন্ট্রাকশন) প্রভৃতি বিষয়গুলো কিন্তু মানবিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার সাথে খাপ খায় না। কিন্তু কেউ নিশ্চয় সেগুলো বিজ্ঞান বিরোধি বলবেন না।
এমনকি আপনার যাচাইযোগ্য পর্যবেক্ষণ নিয়েও কিছু সমস্যা আছে। আধুনিক স্ট্রিং তত্ত্বের যে আমাদের বস্তু জগতের জন্য এগারো মাত্রার ধারণা দিয়েছে কিংবা আঁদ্রে লিন্ডে সহ অন্যান্য বিজ্ঞানীদের দেওয়া ‘মাল্টিভার্স’ তত্তের ব্যাপারেই বা কি বলবেন? ওগুলো গাণিতিকভাবে প্রমাণিত, কিন্তু এখনো যাচাইযোগ্য পর্যবেক্ষণের আওতায় বোধ হয় নয়। তারপরেও বিজ্ঞানীরা কিন্তু ওগুলোকে বিজ্ঞানের কিংবা বৈজ্ঞানিক গবেষণার অংশ বলেই মেনে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আপনার কি অভিমত?
@অভিজিৎদা, আমার লেখায় কেন এই কাঠামোভাবটা চলে আসছে সেটা নিয়ে গতকালই অনেক চিন্তা করছিলাম। বেশ কিছু কারণ সনাক্ত করেছি, সেগুলো নিয়ে কাজ করব।
তর্ক করেছেন দেখে আমি প্রীত 🙂
আপনি প্রত্যক্ষবাদের আলোচনায় আসতে পারে এমন মৌলিক দুইটি প্রশ্নই করে ফেলেছেন। এগুলো প্রত্যক্ষবাদের প্রায়শ: জিজ্ঞাস্যতে থাকা উচিত।
এই যে বহুকাল আমরা পৃথিবীকে সমতল মনে করেছি এবং সূর্যকে পৃথিবীর চারদিকে ঘূর্ণায়মান কল্পনা করেছি, এটা কি করা হয়েছে সত্যকে অস্বীকার করে? অর্থাৎ এমনটা কি যে আমরা তখনই বুঝতাম যে পৃথিবী গোল আর সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, কিন্তু মানতে চাইছি না। বাইবেলের প্রভাবের বাইরের কথা বলছি। বাইবেলে যদি এসব কিছু না লেখা থাকত, তাহলেও কি মানুষ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ ছাড়াই আসল সত্যটা অনুধাবন করে ফেলতে পারত?
মানুষ আগে পৃথিবীর প্রকৃতি সম্পর্কে যা ভেবেছে, তার পেছনে কিন্তু তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যবেক্ষণই দায়ী। এটাকে আমি ধোঁকা বলব না। এটা বরং সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত। আমরা যতটুকু দেখতে পাই, তার ভিত্তিতেই আমরা সিদ্ধান্ত নেই। যেটা দেখতে পাচ্ছি না, সেটা কিভাবে নিশ্চিত করব? এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাই মানুষকে চিন্তায় স্বাবলম্বী করছে, কোনো গল্পগ্রন্থের বর্ণনার উপর নির্ভরশীল করছে না, যেখানে অজস্র কাল্পনিক বর্ণনা আছে যার অধিকাংশই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না।
এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার উপর নির্ভরশীলতার কারণেই কিন্তু সম্ভব হলো পৃথিবী যে সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান বা পৃথিবী যে গোল এই ধারণাগুলো পাওয়া। কেননা আমি যখন আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করছি এবং এমন ঘটনা পর্যবেক্ষণ করছি যা আমার পূর্ব-প্রপঞ্চের সাথে যাচ্ছে না, যেমন সমুদ্রে জাহাজের নিম্নাংশ দেখা না যাওয়া, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থেকে দৃষ্ট তারামন্ডলীর অবস্থানের পার্থক্য সমতল পৃথিবীর বিরোধপূর্ণ হওয়া, চন্দ্রগ্রহণে চাঁদের উপর পৃথিবীর ছায়াকৃতি, অথবা টেলিস্কোপ দিয়ে যখন বিভিন্ন গ্রহ বা তার উপগ্রহের গতি পর্যবেক্ষণ করছি, তখন তা পৃথিবীকেন্দ্রিক মডেলের সাথে বিরোধপূর্ণ হওয়া, এই সবই তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যবেক্ষণ তাই না? এগুলোই তো আমাদের সাহায্য করেছে পূর্বের মডেলকে নাকচ করে আরো মানানসই মডেল গ্রহণের।
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা শব্দটিতে সম্ভবত একটি অতিরিক্ত দ্যোতনা আছে, যেটা দ্বারা মনে হতে পারে, কোনো যন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে সরাসরি বা মানবিক পর্যবেক্ষণ। প্রত্যক্ষবাদ কিন্তু আসলে তা বোঝায় না। অবশ্যই পর্যবেক্ষণের জন্য আপনার প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতি আপনি ব্যবহার করবেন। তবে সবশেষে সেই যন্ত্রের যে আউটপুট আসবে তা আপনার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতেই হবে। কোনো একটি গ্রাফ, একটি মিটার, একটি ছায়া, একটি শব্দ, যন্ত্রকে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য একটি ফলাফল দিতে পারতে হবে। প্রত্যক্ষবাদের সংজ্ঞানুসারে আপেক্ষিকতত্ত্ব অবশ্যই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।
স্ট্রিংতত্ত্ব আর মাল্টিভার্স তত্ত্বের ক্ষেত্রে যে আপনি বললেন
এটা কিন্তু একেবারেই ঠিক না। 🙂
মনে হতে পারে প্রত্যক্ষবাদকে টিকিয়ে রাখার খাতিরে এই তর্ক করছি। আমি এই দুটি তত্ত্ব সম্পর্কে যা বুঝি, তাতে এটাই ছিল আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া কোনো সন্দেহ নেই। তবে এরপর বিজ্ঞানে এদের অবস্থান যাচাই করতে গিয়ে নিশ্চিত হয়েছি, প্রথমত এরা অবশ্যই অদ্যাবধি পরীক্ষিত নয়, ফলে প্রতিষ্ঠিত নয়, প্রপঞ্চ। তদুপরি অনেক বিজ্ঞানী এদের falsifiability নিয়ে সন্দিহান। সেই অর্থে অনেক বিজ্ঞানী এগুলোকে বৈজ্ঞানিক প্রপঞ্চ মানতেও নারাজ।
কারণটা কিন্তু খুবই যৌক্তিক। ধরুন আমি দাবী করলাম এক চির-অদৃশ্য ঘোড়াই হলো জগতের আসল ব্যাখ্যা। কিন্তু আপনাকে কোনভাবেই আমি দেখাতে পারলাম না সেই ঘোড়া, কারণ সেতো চির-অদৃশ্য। এখন সেরকম কোনো প্রপঞ্চ যদি গাণিতিক ভিত্তিপূর্ণও হয়, তাতেই কি আপনার আস্থা তৈরী হয়ে যাবে ব্যাখ্যাটির প্রতি? এরকম আরো হাজারটা গাণিতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্বও কি বের করা সম্ভব না, যার প্রতিটিই জগতকে ব্যাখ্যা করে? তখন আপনি অবশ্যই জানতে চাইবেন এই সকল গাণিতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের মধ্যে কোনটি সত্য; সবগুলো হতে পারে না।
এর জন্যই আপনি চাইবেন তত্ত্বগুলো যাতে যাচাইযোগ্য হয়, যাতে আপনি সত্যতা যাচাই করে নিতে পারেন। অনেকটা এমন যে আপনার সামনে দশটা পীর কেরামতি দেখাচ্ছে, আপনি যৌক্তিক মানুষ, যাচাইয়ের সুযোগ না থাকলে আপনি কারো কেরামতিই বিশ্বাস করবেন না। এখন যে পীর বলল, আমাকে যাচাই করা সম্ভব না, তার দিকে আপনার কতটা সুনজর যাবে?
একারণেই বৈজ্ঞানিক প্রপঞ্চের যাচাইযোগ্যতা থাকতে হয়। আর যাচাইযোগ্য হবার শর্ত হলো পর্যবেক্ষণের উপর এর পূর্বানুমানের ক্ষমতা থাকতে হবে। ঘটে যাওয়া ঘটনা কেবল ব্যাখ্যা করতে পারলে হবে না। বার বার ঝড়ে বক পড়লেই বলা হয় হুজুরের কেরামতি, কিন্তু তার যদি আসলেই কেরামতি থাকে তাহলে বকটা পড়ার আগে তাকে বলতে হবে। নাহলে কেরামতি যাচাই হবে কিভাবে?
এমনিভাবে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বও যদি কোনো পূর্বানুমান করতে না পারত, তবে তা আজ প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে পরিণত হত না। তার তত্ত্ব পূর্বানুমান করেছিল আলো সূর্যের কাছ দিয়ে যাবার সময় বেঁকে যাবে এবং কতটা বাঁকবে। তত্ত্বটি পূর্বানুমান করতে পারছে, তাই এটি যাচাইযোগ্য। এর যথার্থতা-নির্ধারণযোগ্য। ১৯১৯ সালের সূর্যগ্রহণের সময় তার এই পূর্বানুমান নির্ভুল প্রমাণিত হলো। প্রপঞ্চটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো।
অপরদিকে, স্ট্রিংতত্ত্বের যাচাইযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ। এমনকি গাণিতিক পদার্থবিদ Peter Woit স্ট্রিংতত্ত্বকে বলেছেন “not even wrong”, তুলনা করেছেন ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের সাথে, এর কেবল ব্যাখ্যা হয়ে ওঠা কিন্তু (তাঁর মতে) যাচাইযোগ্য না হবার কারণে। দ্রষ্টব্য, বিবর্তনতত্ত্ব কিন্তু কেবল ব্যাখ্যা নয়, এটি পূর্বানুমানক্ষম ও যাচাইযোগ্য।
তথাপি, স্ট্রিংতত্ত্বের যাচাইযোগ্যতা একটি মীমাংসিত বিষয় নয়। তবে মনে রাখতে হবে, একে গাণিতিক থেকে বৈজ্ঞানিক প্রপঞ্চ হয়ে উঠতে হলে পর্যবেক্ষণের উপর একটি পূর্বানুমান করতে পারতে হবে যা কেবল এই তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় এবং একটি সম্ভাব্য পরীক্ষা (হতে পারে বর্তমানের প্রযুক্তিতে সম্ভব নয়) বর্ণনা করতে পারতে হবে, যার দ্বারা এই পূর্বানুমানকে যাচাই করা যায়। তখন বিজ্ঞানে এর একটি বৈধ স্থান অবশ্যই থাকবে। হোক সে তত্ত্ব ভুল, অন্তত falsifiable বৈজ্ঞানিক প্রপঞ্চতো!
কথাগুলো মাল্টিভার্সের ক্ষেত্রে প্রায় পুরোপুরিই প্রযোজ্য।
যেকোনো খটকা থাকলে আপনি বা যেকেউ নির্দ্বিধায় বলুন।
@ধ্রুব,
খুব চমৎকার করেই ব্যাখ্যা করেছেন, ধ্রুব। :yes:
আগেই বলেছিলাম ডেভিলস এডভোকেট হিসেবে তর্ক করছি, এবং তর্ক করছি আপনার প্রত্যক্ষবাদকে সমর্থন করেই (তাহলে তর্ক যে করছি কেন কে জানে? 🙂 ), কাজেই আমি প্রশ্ন করেই বুঝতে পেরেছিলাম কি ধরণের উত্তর আসবে। আসলে বিশেষতঃ দেখার ইচ্ছে ছিল আপনি পুরো বিষয়টাকে কিভাবে ট্যাকেল করেন। ভালই করেছেন বলা যায়। 😀
আবারো ডেভিলস এডভোকেট সাজি না হয়।
আমার আসলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাকে (আক্ষরিক অর্থে বলছি) খুব বেশি প্রাধান্য দিতে সায় দেয় না। কারণ আপনিই বলেছেন –
কিন্তু তার চেয়েও বড় আপত্তি আমার ইন্দ্রিয়ের প্রতারণা নিয়ে। ইন্দ্রিয় আসলে প্রতারণা করে। আসলে মানুষ জন্মেই দেখে এই পৃথিবীটা সমতল আর উপরে চোখ তুললেই দেখে সূর্যকে পূব থেকে পশ্চিমে যাত্রা করতে। কিন্তু এই দেখা যে ভুল – তা নিজের মস্তিস্ককে বোঝাতে সময় লেগেছে। আসলে দেখাটাই তো সব নয়। যেমন নীচের ছবিটা দেখুন – ছবিটি দেখুন । বক্ররেখাগুলোকে সর্পিলাকার কুন্ডলী বলে বিভ্রম হবে। যদিও বাস্তবতা হল, বক্ররেখাগুলো একেকটি বৃত্ত।
[img]http://www.mukto-mona.com/illusion/SpiralIllusion.jpg[/img]
এরকম উদাহরণ দেয়া যায় বহু। এগুলোকে কি বলবেন? ইন্দ্রিয় কি আপনাকে প্রতারিত করছে না? 🙂
যাচাইযোগ্য পর্যবেক্ষণ নিয়ে আরেকটু প্যাচাই এবারে। স্ট্রিং থিওরী, মাল্টিভার্স বাতিল করেছেন – এগুলো পর্যবেক্ষণের আওতায় পড়ে না বলে। যদিও, আমি বলব, নোবেল বিজয়ী বহু বিজ্ঞানীই কিন্তু স্ট্রিং এবং মাল্টিভার্স নিয়ে গবেষণা করেছেন। যেমন, ওয়েইনবার্গের মত বিজ্ঞানীও বলেছেন এটা বিজ্ঞানেরই অংশ –
মাল্টিভার্স সম্বন্ধেও তার একই মত।
এবারে বলুন ডার্ক ম্যাটার, ডার্ক এনার্জি কিংবা হিগস ফিল্ড নিয়ে কি বলবেন? এগুলো কি পর্যবেক্ষণের আওতায়, নাকি এগুলোকেও বাতিল করবেন? আপনার বাতিলের তালিকা কিন্তু ক্রমশঃ বড় হয়ে যাচ্ছে 🙂
তবে ইন্দ্রিয়ের প্রতারণা নিয়ে আমার আপত্তি থাকলেও কার্ল পপার প্রদত্ত ‘ফলসিফায়েবিলিটি’ নিয়ে নেই। আমি আমার মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে বইটি লিখতে গিয়ে আমি পপারকে উদ্ধৃত করে বলেছিলাম –
আপনি কি বলেন?
@অভিজিৎদা, আপনার ডেভিল’স এডভোকেটগিরিতে আমি চমত্কৃত!
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা নিয়ে আমার বক্তব্যের সাথে আপনার যে বিরোধ নেই বুঝতে পারছি, কেননা আমি ব্যাখ্যা করেছি, প্রত্যক্ষবাদে এর অর্থ কেবল সরাসরি বা unassisted পর্যবেক্ষণ নয়। তারপরেও পাঠকের কাছে যাতে ভুল বার্তা না পৌঁছায়, তাই লিখছি:
এই যে দৃষ্টিভ্রমের উদাহরণ দিলেন, ইন্দ্রিয় আমাদের প্রতারণা করছে দেখাতে, আবার বললেন “বক্ররেখাগুলো একেকটি বৃত্ত”, এখন কি করে নিশ্চিত হব যে আসলে তারা সর্পিল না, বরং বৃত্ত?
সেটা বোঝানোর নিশ্চয়ই উপায় আছে, ধীরে ধীরে একটি রেখাকে অনুসরণ করতে বলবেন, আঙ্গুল ব্যবহার করতে বলবেন, বা আরেকটি চিহ্নিতকারী রেখাই এঁকে দিবেন ছবির উপরে অথবা ছবিটি যে প্রোগ্রাম লিখে তৈরী সেটা দেখিয়ে (নিচের ছবির জন্যও একই কথা প্রযোজ্য)। আর তা আমাকে আবার চক্ষু দিয়েই পর্যবেক্ষণ করে নিতে হবে। অর্থাৎ, সবশেষে সকল জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতেই হবে। প্রত্যক্ষবাদে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার জোরটা পর্যবেক্ষণবিহীন ধারণাগুলোর সাথে প্রতিতুলনা করার জন্য দেয়া হয়। অর্থাৎ গাঁজাখুরি গল্প যার পর্যবেক্ষণ নাই, সেগুলো যে কোনো প্রকার অর্থপূর্ণ জ্ঞান না তার উপর জোর দেবার জন্য।
তা আপনার এই ইন্দ্রিয় নিয়ে প্রতারিত বোধ করার পেছনের বার্তাটা আরেকটু স্পষ্ট করবেন? 😉
এগুলো নিয়ে ঘেঁটে দেখলাম এদের প্রত্যেকেরই অন্তত পরোক্ষ পর্যবেক্ষণ-সম্ভাব্যতার ইঙ্গিত আছে। আমি তো আগেই বলেছি, বর্তমান প্রযুক্তিতে পরীক্ষাটি করা সম্ভব নাও হতে পারে, কিন্তু প্রস্তাবিত একটি পূর্বানুমান ও পরীক্ষা থাকতে হবে।
এখন স্ট্রিংতত্ত্ব আর মাল্টিভার্সের সেরকম পরীক্ষা এখনো নেই বলে আমি যে বাতিল করে দিয়েছি তা তো নয়। বিজ্ঞানের সংজ্ঞা তো পাল্টায় না। এর প্রেক্ষিতে তত্ত্বগুলোর বর্তমান অবস্থান কোথায় তা আমি গত মন্তব্যের শেষ প্যারাতে ব্যাখ্যা দিয়েছি।
ওয়েইনবার্গ ঠিক সে কথাটিই কিন্তু একজন আশাবাদীর ভাষ্যে বলে দিয়েছেন-
তা এখন প্রত্যক্ষবাদ নিয়েও আপনি একমত, ফলসিফায়েবিলিটি নিয়েও, তাহলে আপনার খটকাগুলো কি কেবলই ডেভিলের উকিলীয়? 😉
এবার আমি আপনাকে উকিলীয় প্রশ্ন করি। আমার লেখায় বর্ণিত বিজ্ঞানের সংজ্ঞার ব্যাপারে আপনার মতামত কি অথবা আপনার মতে বিজ্ঞানের সংজ্ঞাটি কি? সেই সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে আপনার কাছে স্ট্রিংতত্ত্বের অবস্থানটা কোথায়?
ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন কেন বিজ্ঞান নয় আর বিবর্তনতত্ত্ব কেন বিজ্ঞান? এখানে আমার উত্তর, বিবর্তনের পর্যবেক্ষণসংক্রান্ত পূর্বানুমান আছে এবং তা পরীক্ষা দ্বারা যাচাইযোগ্য। আইডিতে তার কোনটাই নেই, থাকার সম্ভাবনাও নিশ্চিতভাবেই নেই (যেটা আবার স্ট্রিংতত্ত্বের ক্ষেত্রে সত্য না)। এটা প্রত্যক্ষবাদী উত্তর। আপনার আলাদা উত্তর দিন এবং আমার উত্তরের উপর মন্তব্য করুন।
@অভিজিৎ ভাই,
মোক্ষম বলেছেন। বিজ্ঞানের দর্শন নিয়ে কথা আপনার লেখায় থাকবে সেটা আমি আগেই অনুমান করেছিলাম।
প্রত্যক্ষবাদী চোখে জগতটা অনেক ক্লিয়ার লাগে 🙂
প্রত্যক্ষবাদ কে পুঁজি বিজ্ঞানের এগিয়ে যাওয়াটাকে জনবোধ্য করে তোলার জন্য তিনটা বিষয় আছে:
– বিজ্ঞানের দর্শন
– বিজ্ঞান (ফরমাল এবং এম্পিরিক্যাল)
– বিজ্ঞানসাহিত্য
এর মধ্যে শেষোক্তটি অর্থাৎ বিজ্ঞানসাহিত্যের কাজ হচ্ছে উপরের দুটিকে সর্বসাধারণের কাছে নিয়ে যাওয়া, নিজে আলাদা কোন স্পেকুলেশন করা নয়, এই নীতিটি যখন মানা হবে তখন বিজ্ঞানসাহিত্য নিয়ে আর কোন সংশয় থাকতে পারে না। বরং বিজ্ঞানসাহিত্যই হতে পারে দর্শন এবং বিজ্ঞান এ মানুষকে আগ্রহী করে সেটা চর্চার ধারা বজায় রাখা, বা সমাজকে বিজ্ঞান-দর্শন দ্বারা প্রভাবিত করার চাবিকাঠি।
লক্ষ্যনীয় আমি এখানে “জনপ্রিয় বিজ্ঞান” শব্দটি ব্যবহার করি নি। কারণ, মিশেল ফুকো এবং অন্যান্যদের জ্ঞান-ক্ষমতা নিয়ে এতো কাজ হয়ে যাওয়ার পর পপুলার সায়েন্স শব্দটি কেমন যেন হিউমিলিয়েটিং লাগে। জনপ্রিয় জ্ঞান মানে তারা বলতেন- যে জ্ঞান জনপ্রিয়, বা যে জ্ঞান অর্জনই করা হয়েছে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে। এটা খুবই বিভ্রান্তিমূলক। মূলত ইংরেজি পপুলার সায়েন্স শব্দের বাংলা হিসেবেও আমি বিজ্ঞানসাহিত্য ব্যবহার করি। কারণ জনপ্রিয় জ্ঞান ও এক ধরণের জ্ঞান এবং তার অধিকাংশটাই ভুল বা বিভ্রান্তিমূলক। কিন্তু বিজ্ঞানসাহিত্য আদতে কোন জ্ঞান নয়, বরং জ্ঞানের সহজবোধ্য ধারা বর্ণনা। আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে বিজ্ঞানসাহিত্যে নতুন কোন হাইপোথেসিস বা থিওরি দাঁড় করানোর চেষ্টা না করা হয়, কিংবা বিজ্ঞানের সব থিওরি বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট একটা থিওরির পক্ষে প্রোপাগান্ডা চালানো না হয়। সেটা হলে সাহিত্য গ্রন্থটির মান এমনিতেই কমে যাবে।
বাংলায় বিজ্ঞানসাহিত্যের ভাণ্ডার এখনও ভালভাবে দাঁড়ায়নি, তবে অবস্থা একেবারে খারাপও না। আসলে প্রতিটা বিজ্ঞানসাহিত্য গ্রন্থ রচনার আগে সংশ্লিষ্ট দর্শনের সাথে পরিচিত হয়ে নেয়া উচিত, প্রত্যক্ষবাদ সম্পর্কে খুব সচেতন থাকা উচিত এবং প্রতিটা লাইন এমনভাবে লেখা উচিত যাতে কোনভাবেই বিজ্ঞানের দর্শন বা মূল বিজ্ঞানের কোন নীতি লংঘিত না হয়। গতকাল পথিক এর লেখা পড়ে মনে হল দেশের অনেক স্বীকৃত লেখকেরাও এটা মেনে চলছেন না।
@শিক্ষানবিস,
আপনার বিশ্লেষণ চমত্কার লাগলো। আমি অনেকদিন ধরেই এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছি। বিজ্ঞানসংশ্লিষ্টদের দার্শনিক দীনতা নিয়ে। পথিকের লেখায় আমার ধারণাটা পাকাপোক্ত হলো। দেশের এত বড় মাপের লেখকের লেখায় যদি এসব কাল্পনিক ঝোঁক উঠে আসে, তাহলে তার কিশোর পাঠকরা এসব পড়ে কি বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকবে নাকি যেই কাল্পনিক মহাশক্তির কারণে এই পৃথিবী টিকে আছে বলে তিনি ইঙ্গিত দিচ্ছেন, তার দিকে?
ধ্রুব, আমার প্রায়ই মনে হয়, আমাদের দেশে বিজ্ঞান চর্চার একটা মৌলিক সমস্যা আছে। আমাদের দেশে তেমন বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয় না, ফলে সেগুলো নিয়ে কোন বাংলা জারনালে রিসার্চ পেপার প্রকাশ হয় না (অল্প সল্প যা হয় সেটা আবার ইংলিশ জারনালে প্রকাশ হয়)। বেসিক বিজ্ঞান চর্চা না হওয়ার ফলে, তেমনভাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন কাটিং এজ বিষয় নিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য জনপ্রিয় ধারার বিজ্ঞান নিয়ে তেমন লেখালেখিও তেমনভাবে বিকশিত হয় না। এটা না হলে বিজ্ঞানমনষ্কতা তৈরি করা তো বেশ কঠিন হওয়ার কথা।
@বন্যা আহমেদ, বটেই! তাতো আছেই। তবে উচ্চশিক্ষার সুবাদে বাংলা-ভাষাভাষীরা বিদেশে হলেও বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ করে নিচ্ছে। তার প্রভাব দেশ পর্যন্তও নিশ্চিয়ই ফেরত যাবে। তাদের মানসপটেও কিন্তু তাদের কিশোরকালীন, বিজ্ঞানের-প্রসারমূলক লেখালেখি পড়ার একটা প্রভাব থাকে। ফলে বিজ্ঞান নিয়ে যারা উত্সাহ দিয়ে বিশেষভাবে কিশোরদের জন্য লেখা লিখছেন, তাদের বিজ্ঞান-দর্শনে দীক্ষিত হওয়া একদম জরুরি।
তার সাথে যারা গবেষণা করছেন, তাদেরও প্রয়োজন এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা। বিজ্ঞান-দর্শনে দীক্ষিত না হয়েও কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক-গবেষণা সম্ভব হয় অনেক গবেষণার কিছু গৎ-বাঁধা ধরনের কারণে। তথাপি, কাটিং এজ গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুতর অবদানে এই দীক্ষার শক্তিশালী প্রভাব আছে। সেটা অন্যভাষী বা বিদেশী গবেষকদের জন্যও প্রযোজ্য। পৃথিবীতে গবেষক আজ ভুরিভুরি। অনুপাতের বিচারে তাই প্রকৃত-অর্থে দীক্ষিত গবেষক এমনকি পশ্চিমেও কম। অজস্র পশ্চিমা গবেষকদের দেখবেন এবসার্ড কথা বার্তা বলতে।
কিন্তু যে অংশটি প্রকৃত-অর্থে দীক্ষিত, বিজ্ঞানের সঠিক দর্শনটি বহন করে, সংখ্যায় কম হলেও তাদের চিন্তা চেতনা কিন্তু গবেষণায় অনেক বৃহৎ পদক্ষেপ ফেলতে পারে। তাদের মাঝে আমি কয়েকজন বাংলা-ভাষীকেও দেখতে চাই।
আর এই চিন্তা চেতনার প্রভাব সামাজিক পটেও প্রয়োজন। হয়ত অধিকাংশ মানুষ এর ধার ধরবে না, কিন্তু এই দর্শনে অনুরাগী গোষ্ঠীর কিন্তু মূল্য অনেক। আবোল-তাবোল, ভুলভাল, হাবিজাবি চিন্তা করে সময় নষ্ট করা মানুষের সংখ্যা কমবে। পৃথিবীতে হাবিজাবি চিন্তা করা মানুষের সংখ্যা অনেক। বাংলা-ভাষীদের মধ্যে হয়ত তা পশ্চিমের তুলনায় আরো বেশি। তাই বিজ্ঞান প্রসারের ক্ষেত্রে বর্তমান জনপ্রিয় লেখকদের দর্শনগত ঝোঁকটার স্বরূপটা জানার আগ্রহ।
সাথে সঠিক দর্শনকে সনাক্ত করবার প্রয়াস। যা শুধু আগামীদিনের বিজ্ঞানানুরাগীদেরকেই তৈরী করবে না, আমাদের বিজ্ঞান সংক্রান্ত চিন্তাভাবনাকে পুনরায় সনাক্ত করবার সুযোগ দিবে, বিশ্বাস আর দর্শনে সংঘাতের প্রশ্নে নিরসনের উপযুক্ত হাতিয়ার সরবরাহ করবে।
@ধ্রুব,
আমি আসলে জনপ্রিয় ধারার বিজ্ঞান বলতে শুধুমাত্র ‘জনপ্রিয় করার জন্য হাবিজাবি বিজ্ঞান’ বোঝাতে চাইনি। ঐশী প্রেরণাকে তুলে ধরা লেখা আমার কাছে বিজ্ঞানের লেখা বলেই বিবেচিত হবে না। মুহাম্মদের মন্তব্যটা পড়ে বুঝলাম কোথায় সমস্যাটা হচ্ছে। আমি আসলে জনপ্রিয় বিজ্ঞান বলতে বিজ্ঞান সাহিত্যই বোঝাতে চেয়েছি।
গত কয়েক বছর ধরে বিজ্ঞানের উপর লেখালিখি ও অন্যান্য বেশ কিছু কাজের সাথে সংযুক্ত হয়ে এবং বাংলাদেশে যারা এ নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছেন তাদের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ থেকে যা বুঝেছি, খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে তা হল,
১) আমাদের দেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখকেরা বিজ্ঞানের দর্শন নিয়ে লিখতে ভয় পান, তারা এক ধরণের মধ্যবর্তী অবস্থান নেন, যা তে বিপদে না পড়েন, জনপ্রিয়তা না হারান। এদের কাছ থেকে খুব বেশী কিছু পাওয়ার আশা না করাই ভালো। আর যারা এটা করেন না, তাদের ওনেকের জন্য প্রকাশক খুঁজে পাওয়া কঠিন।
২) দেশে সারাসরি বিজ্ঞানের গবেষনা না হওয়ার ফলে, এবং কোন বিজ্ঞান পত্রিকা না থাকার ফলে সঠিক বিজ্ঞান সম্পর্কে খুব কম মানুষেরই কোন সুষ্পষ্ট ধারণা আছে। শুধু দর্শনই নয়, এমনকি বিজ্ঞানের সাহিত্য লেখার জন্য যে ভাষগত বিবর্তনের দরকার সেটাও ঘটে না আমাদের দেশে। যে কেউ বিজ্ঞান নিয়ে লিখতে গেলেই এই সমস্যায় পড়েন।
৩) দেশে এখন সিউডো বিজ্ঞানের ছড়াছড়ি ধর্মীয় টিভি চ্যানেলগুলো এখন তথাকথিত বিজ্ঞানের প্রবক্তা। সেদিন দিগন্ত না কি নামের ইসলামিক টিভি চ্যানেল হাতের গঠন নিয়ে একটা চমৎকার অনুষ্ঠান করলো, এর পিছনে কি ধরণের বিজ্ঞান কাজ করে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। বেশ ভালোই চলছিল, শেষে এসে বলা হল এসবই সৃষ্টিকর্তারই তৈরি!!!! এখন কথা হচ্ছে, আমরা এদেরকে থামাতে পারবো না, কিন্তু এর উলটো পিঠটা আমরা যদি তুলে ধরতে না পারি তাহলে আমাদের দেশে বিজ্ঞান প্রসারের কোন আশাই থাকবে না আর।
৪) এত সব নেগেটিভ কথা বলেও এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে দেশে এখনও বিশাল একটা বিজ্ঞামনষ্ক পাঠক গোষ্ঠী আছে, কিন্তু লেখক নেই। আমার ‘বিবর্তনের পথ ধরে’ বইটা বা অভিজিতের লেখা সবগুলো বিজ্ঞানের বই যেভাবে চলেছে তা কিছুটা হলেও বিষ্ময়কর। আমরা দেশের এমন সব প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে পাঠকদের কাছ থেকে ইমেইল পাই যে অবাক হয়ে যাই। আমাদের বইগুলো এক্কেবারে ‘Core’ বিজ্ঞানের বই, বিজ্ঞান সাহিত্য বলা যেতে পারে এবং বিজ্ঞানের বেসিক দর্শনকে তুলে ধরে কোনরকম আপোষ ছাড়াই। এই মূহুর্তে যার অভাব তা হচ্ছে, বিজ্ঞান লেখকের এবং বিজ্ঞান বই এর। আমার ধারণা একটা বেশ বড় বিজ্ঞানমনষ্ক পাঠকগোষ্ঠী তৈরি করা সম্ভব যদি তাদের জন্য প্রয়োজনীয় বই, নিউজ, অনুষ্ঠান তৈরি করা যায়। বিজ্ঞান বক্তা এবং সমকালের কালস্রোতের সম্পাদক আসিফ একটা কথা বলে, আমরা এতদিন এই ঘুণে ধরা সিষ্টেমটা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতাম, ভাবতাম কিছু হবে না এ দিয়ে। কিন্তু আসলেই যদি কিছু করতেই হয় তাহলে এই সিষ্টেমের ভিতর থেকেই শুরু করতে হবে এবং সেখান থেকে যাতে ভেঙ্গে বেড়িয়ে আসা যায় সেই লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে। আসিফ দেশে বিজ্ঞান বক্তৃতা দেন, এবং শ’য়ে শ’য়ে মানুষ প্যাসা দিয়ে টিকিট কেটে তা দেখতে আসে, এটা যে বাংলাদেশে সম্ভব তা আসিফকে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না।
৫) প্রসংগটা যখন উঠলোই আরেকটা বিষয় উল্লেখ করি… বিপ্লব পাল, অনন্ত, আসিফ, অভিজিত এবং আমি গত কয়েক সপ্তাহ ধরে দেশে ( এবং কোলকাতায়) কিভাবে টিভি চ্যানেলগুলোর জন্য বিজ্ঞানের মিডিয়া প্যাকেজ, নিউজ প্যাকেজ তৈরি করা শুরু করা যায়, এবং সেখান থেকে ধীরে ধীরে একটা মাসিক বিজ্ঞানের পত্রিকা বের করা যায় তা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছি। আমাদের না আছে লোকবল না আছে টাকা পয়সার শক্তি। মুক্তমনার সদস্যরা সদি আমাদের সাথে যোগ দিতে চান তাহলে আওয়াজ দিয়েন।
@বন্যা আহমেদ,
:yes:
আপনি দেশের বিজ্ঞানের প্রসার নিয়ে একটা চমত্কার চিত্র তুলে ধরলে।
যে কার্যক্রমের পরিকল্পনার কথা বলছেন, তার প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন। এভাবেই সম্ভব। আমার দু-পয়সার বক্তব্যটা ছিল, এই অভিযাত্রায় বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষবাদী দর্শনকে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করার। নাহলে, টিভি চ্যানেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনার পরিশেষে কেউ যখন আবার ঐশী প্রেরণার ইঙ্গিত দেবেন, তখন উত্তর কিভাবে করব আমরা? প্রত্যক্ষবাদে এর সরাসরি উত্তর, যাচাই-অযোগ্য, “unfalsifiable” তত্ত্ব বিজ্ঞান না, কোনো অর্থপূর্ণ জ্ঞানও না। অর্থাৎ আমাদের অবস্থান যে ধর্মবিরোধিতা থেকে নয়, বরং বিজ্ঞানানুগামিতা থেকে উত্সারিত, সেটা পরিষ্কার করা অত্যন্ত সহজ হবে।
জনপ্রিয় লেখকরা যে গা বাঁচিয়ে চলছেন, এটা খুবই আশঙ্কাজনক। প্রতিক্রিয়াশীলতার ভয় বুকের ভিতরে রেখে কারো বিজ্ঞান নিয়ে না লেখাই উচিত। তাদের উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের প্রসার না, নিজের জনপ্রিয়তা।
@বন্যা আহমেদ,
কথাটা একদম ঠিক বলেছেন। একটা গুরুতর সমস্যা সনাক্ত করেছেন। গোড়ায় না ঢেলে আগায় পানি ঢেলে আর কতটা হবে? প্রবাসী উচ্চশিক্ষারত বা গবেষকদের দ্বারা হয়ত তারপরেও কিছু অবদান সম্ভব।
তবে কথাটি আপনার পরের বাক্যের সাথে মিলিয়ে পড়ে আমার আরেকটি কথা হলো – জনপ্রিয় ধারার বিজ্ঞান লেখালেখির সাথে কিন্তু বিজ্ঞানমনষ্কতার অত ভালো সম্পর্ক নেই। জনপ্রিয় ধারার বিজ্ঞান নিয়ে অনেক লেখাজোকা এমনকি সেসবে অবদান রেখেও তো পরিশেষে বলা সম্ভব, এই যে এক অদ্ভূত অনুপাতের উপর পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে, তার পেছনে কিন্তু আমাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার এক ঐশী প্রেরণা আছে।
বিজ্ঞানমনষ্ক বলা গেল না। কারণ এই বাড়তি জ্ঞানটি জল্পনা-কল্পনাপ্রসূত, প্রত্যক্ষবাদের চোখে নিরর্থক বা অর্থহীন জ্ঞান।
@ধ্রুব,
বন্যা আপার মন্তব্যের ব্যাপারে আমিও একমত। বাংলাদেশের ভেতরে যতোদিন না সিরিয়াস বিজ্ঞান গবেষণা ও গবেষণাগার শুরু হচ্ছে ততোদিন বিজ্ঞানমনস্কতা প্রচারে বাঁধা থেকেই যাবে। বাংলায় গবেষণাপত্র প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাও আছে বলে মনে করি। এমনকি বিশ্বখ্যাত পেপার গুলোও বঙ্গানুবাদ করা উচিত মনে হয়।
আর জনপ্রিয় বিজ্ঞান না বলে নিচে বিজ্ঞানসাহিত্যের দিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। আমার মনে হয় বিজ্ঞানসাহিত্য কে স্পেকুলেটিভ না হয়ে ন্যারেটিভ হতে হবে, বিজ্ঞান এবং দর্শনের ন্যারেটিভই হবে বিজ্ঞানসাহিত্য- অন্যকিছু না।
প্রত্যক্ষবাদ নিয়ে তর্ক থাকাটা আমি স্বাভাবিক মনে করছি। সেই তর্ককে আমি স্বাগত জানাচ্ছি।