তৃতীয় সূত্র: চেতনকে কেবল পর্বতের চূড়া বলা যায়, আমাদের মনের মধ্যে যা কিছু ঘটে তার অধিকাংশই গোপন থাকে। সুতরাং চেতন আমাদের এই বলে বিভ্রান্ত করতে পারে যে, মস্তিষ্কের বর্তনী খুব সরল। আমরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হই সেগুলো সমাধান করা আপাতদৃষ্টিতে সহজ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তার জন্য অনেক জটিল স্নায়বিক বর্তনীর জটিল যোগসাজোশের প্রয়োজন পড়ে।
আমাদের চেতন মনকে তুলনা করা যায় দেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে। দেশের কোন কোণায় কোন আইন লঙ্ঘিত হচ্ছে সেটা প্রধানমন্ত্রী কিভাবে জানেন? ধরা যাক সন্দ্বীপে একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটল। ঘটার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী তা জানবেন কিভাবে?- দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পুলিশ, গোয়েন্দা, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি এবং সংবাদপত্রের সংবাদদাতাদের মাধ্যমেই খবরটি সরাসরি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চলে আসবে। এই সকল তথ্যের ভিত্তিতে স্বরাষ্ট্র সচিব প্রতিবেদন তৈরী করবেন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সেটা প্রধানমন্ত্রীকে দেবেন। প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এই ঘটনার খুটিনাটি বের করার বিস্তারিত প্রক্রিয়ার কিছুই জানেন না। তিনি কেবল জানেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে তার কাছে এই খবর নিয়ে এসেছেন। তিনি কেবল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কিভাবে কাজটি করেছেন তা জানেন। একইভাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কেবল সচিবের দায়িত্বের কথাটুকু জানেন। প্রত্যেকে তার এক ধাপ অধস্তন সম্পর্কে জানে, এর বেশি না। আমাদের চেতন মন হল প্রধানমন্ত্রী। সবাই তাকে রেডিমেড তথ্য সরবরাহ করে এবং তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের উপায়ও তাকে জানানো হয় না। এজন্যই আমরা মস্তিষ্কের তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জটিলতা একটুও বুঝতে পারি না। একজন মনোবিজ্ঞানীর এটা সবসময় মনে রাখা উচিত। কারণ চেতনার মাধ্যমে অনেক কিছু জানতে পারলেও মাঝেমাঝে সেই চেতনাই আমাদের পথভ্রষ্ট করে।
স্বজ্ঞা আমাদেরকে কিভাবে বোকা বানায় একমাত্র দৃষ্টি শক্তি দিয়েই তা ব্যাখ্যা করা যায়। আমাদের দেখার কৌশল যে কত জটিল তার ছিটেফোটাও আমরা বুঝতে পারি না। মনে করি, আলো আসে, রেটিনায় আঘাত করে আর সাথে সাথেই চোখের সামনের সবকিছু দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এমনকি রেটিনায় আঘাত লাগাটাও আমাদের পক্ষে অনুভব করা সম্ভব না। অথচ এ কৌশলের জটিলতা অভাবনীয়। প্রথম কথা হচ্ছে রেটিনা একটি দ্বিমাত্রিক সমতল যা বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তু দিয়ে গঠিত, এর অবস্থান অক্ষিগোলকের পেছনের দিকে। এই দ্বিমাত্রিক তলে নানান ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মাধ্যমে কিভাবে ত্রিমাত্রিক জগতের এত নিখুঁত ধারণা পাওয়া সম্ভব এটা আমরা ভেবেও দেখি না। আসলে দেখার কাজ শুধু চোখ দিয়ে নয় বরং চোখ ও মস্তিষ্কের যৌথ প্রচেষ্টায় ঘটে। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক একটি শিশু তার মাকে হাটতে দেখছে এবং চিনতে পারছে যে এটাই তার মা। এই অতি জটিল দর্শন ও চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়ার জন্য অনেক বিশেষায়িত স্নায়বিক বর্তনী আছে। অন্তত সাতটি বর্তনীর কথা বলা যায়। এই বর্তনীগুলোর কাজ অনেকটা এরকম: (১) বস্তুর আকার বিশ্লেষণ (২) গতির উপস্থিতি সনাক্তকরণ (৩) গতির দিক সনাক্তকরণ (৪) দূরত্ব বিচার (৫) রং বিশ্লেষণ (৬) বস্তুটিকে মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা এবং (৭) চোখে দেখা মুখটি যে মায়ের তা বোঝা। বোঝাই যাচ্ছে প্রক্রিয়াটি কত জটিল। প্রকৃতপক্ষে রেটিনার দ্বিমাত্রিক উল্টো ছবিকে ত্রিমাত্রিক সরল বাস্তবতায় রূপ দেয়ার কাজটি মস্তিষ্কেই ঘটে।
বিভিন্ন কাজ করার জন্য বিশেষায়িত বর্তনীগুলো আলাদা হলেও তারা একসাথে কাজ করতে জানে। আসলে তাদের কাজকে একত্রিত করার উপায়ও মস্তিষ্কে আছে। এই বিশ্লেষণ থেকে আমরা বুঝতে পারি, অতি সরল মানবিক কাজকর্মগুলোর রাসায়নিক প্রক্রিয়া কত জটিল। কাউকে দেখামাত্র ভালো লেগে যেতে পারে, মনে হতে পারে এজন্য আমাকে কোন কষ্টই করতে হয়নি। হ্যাঁ, এক অর্থে প্রেমিকার স্পর্শ অনুভব করতে কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু যেই অমানবিক যন্ত্রগুলো এ ধরণের অনুভূতিকে সম্ভব করে তোলে তাদের কষ্ট বোঝার সাধ্য বোধকরি মানুষেরও নেই। কারণ এর পুরোটাই আমাদের চেতনার বাইরে থাকে। এমনকি হয়ত অবচেতনেরও বাইরে থাকে।
চতুর্থ সূত্র: প্রতিটি অভিযোজনগত সমস্যা সমাধানের জন্য পৃথক পৃথক স্নায়বিক বর্তনী আছে। প্রতিটি বর্তনী কেবল নিজ কাজ করার জন্যই বিশেষায়িত।
প্রযুক্তির একটি মৌলিক নীতি হচ্ছে, একেক কাজের জন্য একেকটি বিশেষায়িত যন্ত্র থাকতে হবে। এক যন্ত্র দিয়ে অনেক কাজ করা মোটেই লাভজনক নয়। যেমন স্ক্রু ড্রাইভার যে কাজ করে করাত দিয়ে সে কাজ করা সম্ভব না। তাদের পৃথক পৃথক কাজ আছে। মানব দেহও এই নিয়ম মেনে চলে। হৃৎপিণ্ডের কাজ রক্ত পাম্প করা আর যকৃতের কাজ বিষ ছাড়ানো। একে অন্যের কাজে কখনও হস্তক্ষেপ করে না। স্নায়বিক বর্তনীর ক্ষেত্রেও এটা সত্য। একের পক্ষে অন্যের কাজ করা সম্ভব না এবং একই বর্তনী দিয়ে অনেক ধরণের কাজ করাও সম্ভব না। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করা যায়: ধরা যাক একটি মেয়ে যে স্নায়বিক বর্তনী দিয়ে বিভিন্ন বস্তুর গন্ধ শুঁকে সেই বর্তনী দিয়েই প্রেমিক খুঁজতে শুরু করল। ফলাফল দাঁড়াবে ভয়ানক, আস্ত মানুষ নির্বাচনের পরিবর্তে সে হয়ত প্রেমিক হিসেবে বেছে নেবে বিশালকায় কোন মিষ্টি চকোলেটকে।
অসংখ্য বর্তনীর সমন্বয়ে মস্তিষ্ক গঠিত। এটাকে কম্পিউটারের ডিস্ট্রিবিউটিং অপারেটিং সিস্টেমের সাথে তুলনা করা যায়। এ ধরণের তন্ত্রে অনেকগুলো মিনি-কম্পিউটার থাকে যাদের প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে। সবার কাজ মূল কম্পিউটারে গিয়ে একত্রিত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থ তৈরী করে। মানুষের বিশেষায়িত স্নায়বিক বর্তনীগুলো এসব মিনি কম্পিউটারের সমতুল্য। এরা সবাই একসাথে মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ স্বভাব তৈরী করতে পারে। মনোবিজ্ঞানীরা অনেক আগেই আবিষ্কার করেছেন, বিভিন্ন ধরণের ইন্দ্রিয়ানুভূতির- যেমন দর্শন বা শ্রবণ- জন্য মস্তিষ্কে পৃথক পৃথক বিশেষায়িত বর্তনী আছে। কিন্তু এই কিছুকাল আগেও তাদের একটি বদ্ধমূল ধারণা ছিল, ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং খুব সম্ভবত ভাষা ছাড়া আর কোন বৌদ্ধিক প্রক্রিয়াই বিশেষায়িত বর্তনী দ্বারা চালিত হয় না। মনে করা হতো, অন্যান্য বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া যেমন, শিক্ষা গ্রহণ, কারণ দর্শানো, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদির জন্য কোন বিশেষায়িত বর্তনী নেই, একই বর্তনী তথা একই প্রোগ্রাম দিয়ে এই কাজগুলো করা সম্ভব। রেশনাল এলগরিদমকগুলোকেই এর জন্য দায়ী করা হতো। বায়েস সূত্র বা প্রোপোজিশনাল ক্যালকুলাসের মাধ্যমে মানুষ একই বর্তনী ব্যবহার করে সকল যুক্তিগত সমস্যার সমাধান করতে পারে বলে ধারণা করা হতো। এভাবে হয়ত একই ধরণের আরোহী বা অবরোহী যুক্তি ব্যবহার করে সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব। এটা ভাবারও যথেষ্ট কারণ ছিল- মানুষ এত বহুরুপী যুক্তিগত সমস্যার সমাধান করতে পারে যে এর প্রত্যেকটির জন্য বিশেষায়িত বর্তনী নিয়োগ করলে সবগুলোর হিসাব রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে।
কিন্তু বিবর্তনীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এক্ষেত্রেও আমাদের কঠিন পথে হাটতে হচ্ছে। টুবি এবং কসমাইডস তাদের ১৯৯২ সালের বইয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষের বিবর্তন পরিবেশের উপর এত বেশি নির্ভর করে যে প্রতিটি স্বভাবের পেছনে বিবর্তনের বিশেষায়িত ভূমিকাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। সাধারণ বর্তনী থাকলে যেমনটি হওয়ার কথা অনেক ক্ষেত্রেই তার ব্যতিক্রম দেখা গেছে। যেমন মানুষের “রঙের নিত্যতা”- ভর দুপুর এবং সূর্যাস্ত দুই সময়েই মানুষ ঘাসকে পুরোপুরি সবুজ দেখে। কিন্তু ঘাস এই দুই সময়ে বর্ণালির যে অংশ প্রতিফলিত করে সে অনুসারে এমনটা হওয়ার কথা না, একেক সময়ে ঘাসকে একেক রঙের দেখার কথা। মানুষের চোখ এমনভাবে বিবর্তিত হয়েছে যে সে ভিন্ন রঙের ব্যাপারটি সংশোধন করে রঙের নিত্যতা বজায় রাখে। বায়েস নীতি বা প্রোপোজিশনাল ক্যালকুলাসের নিয়মে এমনটা হওয়ার কথা না। কারণ এগুলো content-independent, অর্থাৎ যে বিষয়ের উপরই কাজ করুক তার নীতিতে কোন পরিবর্তন হবে না। প্রোপোজিশনাল ক্যালকুলাসের দুটি বহুল ব্যবহৃত যুক্তির উদাহরণ দেয়া যাক:
মোডাস পনেন্স:
যদি “ক” হয় তবে “খ” হবে। “ক” হয়েছে, অতএব “খ” হয়েছে।
তুমি “ঘুমালে” “স্বপ্ন” দেখবে। তুমি ঘুমিয়েছো, অতএব তুমি স্বপ্ন দেখেছো।
মোডাস টলেন্স:
যদি “ক” হয় তবে “খ” হবে। “খ” হয়নি, অতএব “ক” হয়নি।
তুমি “ঘুমালে” “স্বপ্ন” দেখবে। তুমি স্বপ্ন দেখনি, অতএব তুমি ঘুমাওনি।
বিবর্তিত মানুষের মনের উপর এহেন যুক্তি প্রয়োগ সবসময় সঠিক ফল দেবে না। কারণ অভিযোজনগত সমস্যা সমাধানের জন্য নিয়োজিত বর্তনীগুলো কাজ শুরু করার আগেই অগ্রিম কিছু তথ্য পায়। এই অগ্রিম তথ্যগুলোকে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের ভাষায় “ক্রিব শিট” বলা হয়। এককথায়, সমাধান শুরু করার আগেই তারা সমস্যা সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে আসে। শিশুর মস্তিষ্কে এমন কিছু বর্তনী থাকে যার কারণে সে জন্মের পরই মানুষের মুখ দেখার প্রত্যাশা করে। মাত্র ১০ মিনিট বয়সী বাচ্চার উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে তারা মানুষের মুখ দেখলে সাড়া দেয়, কিন্তু সেই মুখমণ্ডলই একটু বিকৃত করে উপস্থাপন করলে সেরকম সাড়া দেয় না। স্পষ্ট মুখমণ্ডল দেখলেই তারা চোখ বা মাথা নাড়িয়ে সেদিকে নির্দেশ করে। এমনকি মুখমণ্ডলটি যত সুশ্রী হয় তারা ততই তীব্রভাবে সাড়া দেয়। মাত্র আড়াই মাস বয়সেই বাচ্চারা পৃথিবী কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক ধারণা পোষণ করতে শুরু করে। তারা এ সময়ই বুঝে ফেলে যে পৃথিবীতে এমন সব অনঢ় বস্তু থাকে যারা স্থান-কালে অবিচ্ছিন্ন, এমনকি এই জগৎ বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত সেটাও বুঝতে শুরু করে। এমনকি অল্প বয়সেই বাচ্চারা মানুষের মন বোঝার ক্ষমতা অর্জন করে, তারা চোখের নড়াচড়া এবং চাহনির দিক অনুসরণের মাধ্যমে অন্যদের মানসিক অবস্থা বুঝতে পারে। এই ক্ষমতা যাদের থাকে না তারা অন্যরা কি ভাবছে তা একেবারে বুঝতে পারে না, অন্যদের মানসিক অবস্থা আন্দাজ করতে পারে না। এটা অটিজম রোগের অন্যতম কারণ।
মুখমণ্ডল, অনঢ় বস্তু এবং অন্যের মন বোঝার এই ক্ষমতাগুলো না থাকলে শিশুরা পরিবেশ থেকে তেমন কিছুই শিতে পারত না। যেমন অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের বুদ্ধিমত্তা সাধারণ বা সাধারণের চেয়ে বেশি থাকা সত্ত্বেও আরা অন্যের মানসিক অবস্থা আন্দাজ করতে পারে না। আবার উইলিয়ামস সিনড্রোমে আক্রান্তরা অন্যের মন বুঝতে পারলেও স্থান-কাল সংক্রান্ত অতি সাধারণ সমস্যার সমাধান করতে পারে না। জন্মের আগেই তাদের মস্তিষ্কে যে বিবর্তনীয় ভিত্তিগুলো তৈরী হয় তার মাধ্যমেই শিশুরা পরিবেশ থেকে শেখা শুরু করে। এগুলোকেই বলা যায় ক্রিব শিট। একেক সমস্যার জন্য একেক ধরণের ক্রিব শিট প্রয়োজন। আগের সূত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশেষায়িত বর্তনী সম্পর্কে যা বলেছি সেটা আসলে পৃথক পৃথক ক্রিব শিটের কারণে ঘটে। এক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে যদি কেউ অন্য সমস্যার জন্য সংরক্ষিত তথ্য কাজে লাগানো শুরু করে তবে কখনই সমাধানে পৌঁছুতে পারবে না। এজন্যই বিশেষায়িত ক্রিব শিট এবং যথারীতি বিশেষায়িত স্নায়বিক বর্তনী আবশ্যক।
একটি তন্ত্রে যত বেশি ক্রিব শিট থাকবে সে তত সূক্ষ্ণ স্বভাব তৈরি করতে পারবে। বায়েসের সূত্র বা প্রোপোজিশনাল ক্যালকুলাস অনুসরণকারী content-independent যন্ত্রের তুলনায় উপরে উল্লেখিত ক্রিব শিট সমৃদ্ধ content-dependent যন্ত্র অনেক বেশি কার্যকরি। সাধারণ যুক্তিতেও এর সত্যতা বোঝা যায়। যে যুক্তি যেকোন বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তার কোন ক্রিব শিট তথা হেড স্টার্ট থাকবে না, কোন সমস্যা সমাধান করছে সে সম্পর্কে তার কোন ধারণাই থাকবে না। কিন্তু কি নিয়ে কাজ করছে তার উপর নির্ভর করে সে উক্ত বিষয়ে আগে থেকেই কিছু জেনে আসতে পারে। ব্যাপারটা উপস্থিত বক্তৃতা এবং নির্ধারিত বক্তৃতার পার্থক্যের সাথে তুল্য। নিঃসন্দেহে যে বক্তৃতার বিষয় আগে থেকে নির্ধারিত তা বেশি তথ্যসমৃদ্ধ ও কার্যকরি হবে। পেশাদার আর নবিশের উদাহরণও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একই প্রক্রিয়ায় কাজ করলেও নবিশের তুলনায় পেশাদারের তা শেষ করতে কম সময় লাগবে এবং তারটাই বেশি নিখুঁত হবে। কারণ সে আগে থেকেই সমস্যা সম্পর্কে অনেক কিছু জানে।
এই পরিপ্রেক্ষিতে উইলিয়াম জেমসের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে যদিও বিংশ শতকের অনেকটা সময় তা অবহেলিত ছিল। বর্তমানে মানুষের যৌক্তিক স্বভাব নির্ধারণকারী অনেকগুলো বিশেষায়িত বর্তনীর সন্ধানও পাওয়া গেছে। স্পষ্টতই, সব যুক্তিগত সমস্যা এক প্রক্রিয়ায় সমাধান করা হয় না। বস্তু, ভৌত হেতুবাদ, সংখ্যা, জৈবিক বিশ্ব, বিশ্বাস, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ইত্যাদি যুক্তিগত বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক বর্তনী আবিষ্কৃত হয়েছে। নোম চমস্কিদের “ল্যাংগুয়েজ একুইজিশন ডিভাইস” (LAD) তো সর্বজনবিদিত। চমস্কি এবং অন্যান্য ভাষাবিজ্ঞানীরা বলছেন শিশুর মস্তিষ্কে এই বর্তনী আগে থেকেই থাকে। এটাকে ভাষা শেখার প্লাটফর্ম বলা যায়। এটা থাকার কারণেই বাচ্চারা এত দ্রুত ভাষা শিখে ফেলতে পারে। তারা বড়দের কাছ থেকে নানান শব্দ ও বাক্য শুনে কিন্তু সেগুলো কিভাবে একটার পর আরেকটা জোড়া লেগে অর্থবোধক হয়ে ওঠে সে সম্পর্কে তাদেরকে কোন শিক্ষা দেয়া হয় না। তারপরও তারা পেরে ওঠে। LAD থাকার কারণেই এটা সম্ভব হয়। এটিও এক ধরণের ক্রিব শিট।
এই আলোচনার সুবাদে মানুষের স্বজ্ঞা বিষয়ক সিদ্ধান্ত আরও জোড়ালো হয়েছে। লোকে বলে, জন্তুরা স্বজ্ঞা দ্বারা চালিত হলেও মানুষ চালিত হয় যুক্তি দ্বারা। কিন্তু আমরা দেখছি যুক্তিও অসংখ্য স্বজ্ঞার সার্থক সমন্বয় বৈ অন্য কিছু নয়। উপরে যে বর্তনীগুলোর কথা বলা হল তাদের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যনীয়:
(১) সুনির্দিষ্ট অভিযোজনগত সমস্যা সমাধানের জন্য জটিলভাবে বিশেষায়িত
(২) সব সাধারণ মানুষের মাঝেই এটা বিকশিত হয়
(৩) এগুলোর বিকাশ সম্পর্কে মানুষ সচেতন নয় এবং এগুলোর জন্য কোন শিক্ষাও লাগে না
(৪) এদের যুক্তি সম্পর্কে কোন সচেতন ধারণা না থাকার পরও সবাই তা প্রয়োগ করতে পারে
(৫) উন্নত তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বা বুদ্ধিমত্তা থেকে তারা অনেকটাই আলাদা। এই সবগুলো বৈশিষ্ট্যই কিন্তু চিৎকার করে স্বজ্ঞাকে নির্দেশ করছে।
তাই বলা যায় যুক্তিও এক ধরণের স্বজ্ঞা। যুক্তি বা শিক্ষা শব্দগুলোর বদলে তাই আমরা “যুক্তিগত স্বজ্ঞা” এবং “শিক্ষাগত স্বজ্ঞা” ব্যবহার করতে পারি।
পঞ্চম সূত্র: আমাদের আধুনিক খুলির ভেতর একটি প্রস্তর যুগীয় মন বাস করে।
বিবর্তন অনেক দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় কোন একটি পরিবর্তন আসতে হাজার হাজার বা ক্ষেত্র বিশেষে লক্ষ লক্ষ বছর লেগে যায়। এজন্যই মানব সভ্যতার কোনকিছুই বিবর্তনকে খুব বেশি প্রভাবিত করতে পারেনি। কারণ আধুনিক মানুষের বিবর্তনীয় ইতিহাসের শতকরা ৯৯ ভাগ সময়ই মানুষ ছিল শিকারী-সংগ্রাহক। অর্থাৎ তারা শিকারের মাধ্যমে এক দিনের খাবার সংগ্রহ করতো এবং উদরপূর্তির পর পরদিন আবার শিকারে বের হতো। তাদের জীবন মানেই ছিল চিরন্তন শিকার অভিযান। তারা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে শিকার করতো, তাই এই ছোট্ট দলে বসবাস এবং শিকার করতে গিয়ে তারা যেসব অভিযোজনগত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সেগুলোই বিবর্তনের গতিপথ ঠিক করেছে। মানুষ কৃষিকাজ আবিষ্কার করেছে ১০,০০০ বছর আগে, অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজ শুরু করে স্থায়ি বসতি নির্মাণ শুরু করেছে মাত্র ৫,০০০ বছর আগে। অন্য যে কোনকিছুর তুলনায় মানুষ শিকারী-সংগ্রাহক হিসেবে ১,০০০ গুণ বেশি সময় অতিবাহিত করেছে। সুতরাং আমাদের প্রায় পুরো বিবর্তনই যে এই যুগে ঘটেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একেই সূত্রের আদলে বলা হচ্ছে, আমাদের আধুনিক খুলির ভেতর একটি প্রস্তর যুগীয় মন বাস করে।
মন নিয়ে গবেষণা করতে গেলে তাই আমাদেরকে এমন সব অভিযোজনগত সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে আমাদের শিকারী-সংগ্রাহক পূর্বপুরুষেরা যেগুলোর সম্মুখীন হয়েছিল। আমেরিকার মানুষ রাস্তায় চলতে ফিরতে যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তার কোনই বিবর্তনীয় গুরুত্ব নেই। বরং আমরা এ ধরণের সমস্যা নিয়ে ভাবতে পারি: সঙ্গী নির্বাচন, শিকার, খাদ্য সংগ্রহ, বন্ধুদের প্রতি ব্যবহার, নিজেদেরকে সহিংসতা থেকে রক্ষা করা, সন্তান লালন-পালন, সুন্দর বাসস্থান নির্বাচন ইত্যাদি। প্রস্তর যুগীয় মনের কিছু প্রমাণ কিন্তু আমাদের সামনেই আছে। সাপের চেয়ে বৈদ্যুতিক সকেটে মৃত্যুর সম্ভাবনা বেশি থাকা সত্ত্বেও আমরা সাপ বেশি ভয় পাই কারণ আমাদের শিকারী-সংগ্রাহক পূর্বপুরুষেরা এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল এবং তাদের কাছ থেকে জন্মসূত্রেই আমরা এটা পেয়েছি। একটি শিকারী-সংগ্রাহক দলে যত মানুষ থাকে সে সংখ্যক মানুষের সামনে আমরা স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা বলতে পারি, কিন্তু বিশাল জনসমাবেশে কথা বলতে আমাদের ভয় করে। এজন্যই বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান গবেষণার জন্য আমাদের ফিরে যেতে হবে আফ্রিকান সাভানাতে বসবাসকারী শিকারী-সংগ্রাহক হোমো স্যাপিয়েন্সদের কাছে, ভাবতে হবে তারা প্রতিদিন কি কি সমস্যা মোকাবেলা করত।
এজন্যই বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান খুব বেশি অতীতাশ্রয়ী। বৌদ্ধিক মনোবিজ্ঞানের গতানুগতিক গবেষণা পদ্ধতি এখানে অকেজো। সকল স্বভাব-প্রকৃতি ব্যাখ্যার জন্য অবশ্যই শিকারী-সংগ্রাহকদের একটি সমস্যা উল্লেখ করতে হবে। এমনকি বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, কোন স্বভাবকেই আধুনিক সমস্যার প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা যাবে না, ব্যাখ্যা করলেও সেটা পুরোপুরি সঠিক হবে না। এ নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে অনেক বিতর্ক আছে। সায়মন্স এবং টুবি ও কসমাইডস এর লেখায় সেগুলো বারবার প্রকাশিত হয়েছে।
তবে প্রস্তর যুগীয় মন বলে যে আমাদেরকে শুধুই আফ্রিকান সাভানাহ নিয়ে গবেষণা করতে হবে এমন কোন কথা নেই। কারণ বিবর্তনের জন্য স্থান-কালের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে “বিবর্তনীয় অভিযোজনের পরিবেশ” (Environment of Evolutionary Adaptedness – EEA)। এটা কোন স্থান বা সময় নয়। এটা হল কোন একটি অভিযোজনের নকশা করতে গিয়ে যে নির্বাচন চাপের (selection pressure) সম্মুখীন হতে হয়েছে তার পরিসাংখ্যিক সমষ্টি। সুতরাং একেক অভিযোজনের ইইএ একেক রকম। রঙের অনন্যতার কথাই ধরা যাক। মেরুদণ্ডী প্রাণীর চোখের জন্য ইইএ লক্ষ-কোটি বছর ধরে অপরিবর্তনীয় আছে, কারণ পরিবেশে আলোর খুব একটা তারতম্য ঘটেনি। কিন্তু মানুষের সন্তান ভরণপোষণের ইইএ অনেক কম, মাত্র ২০ লক্ষ বছর। কারণ ঠিক অত বছর আগেই অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের থেকে তার ভিন্ন রকম অভিযোজন ঘটেছে।
[চলবে…]

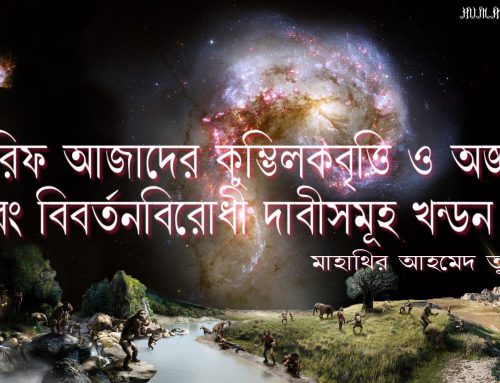
এই কথাটার সাথে আমার লেখায় “জ্ঞানের বিমূর্ত স্তরীভবন” ধারণাটার ব্যাপক মিল অনুভব করছি। সত্যি, আমরা সর্বদাই ভাবি, আমাদের চেতনাটাই আমি, কিন্তু তার পেছনে যে কত অজস্র বিশেষায়িত ফাংশন কাজ করছে। সর্বোচ্চস্তরের জ্ঞান ধারণকারী এই চেতনার মূল উত্স কিন্তু শেষে গিয়ে একেবারে ইন্দ্রিয়-পর্যায়ের ফাংশনগুলোই। ইন্দ্রিয় দিয়ে ইনপুট নিচ্ছি, আর সেগুলোই বিভিন্ন বিশেষায়িত ফাংশন দ্বারা প্রক্রিয়াজাত হয়ে আমাদের চেতনায় উচ্চতর জ্ঞানের সৃষ্টি করছে।
এই চেতনা নিয়ে কিছু লিখলে মন্দ হত না।
বরাবরের মতই দারুণ হয়েছে। :rose:
ধন্যবাদ সৈকত দা…
আমি কিন্তু আমার এই ‘মহামূল্যবান মনকে’ (বা তোমাদের কথা অনুযায়ী ‘ভৌত যন্ত্র মস্তিষ্ককে’) হাসিনা, খালেদার ( আয় হায়, এরশাদ, জিয়াও এই লিষ্টের মধ্যে চলে আসবে মনে হচ্ছে) সাথে তুলনা করাতে খুব অপমানিত বোধ করছি এবং এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।
কোন দুঃখে যে এই উদাহরণটা দিছিলাম। পুরা দুর্বল পয়েন্ট হয়ে গেছে। এইটার জন্য টিজ খাইতে হবে সামনে আরও বুঝতেছি। ব্লগটা দেয়ার আগেও অন্তত টেম্পারিং করে কিছু পরিবর্তন করে দেয়া যেতো। বিশাল ভুল করছি…
হাসিনা-খালেদা-এরশাদ-জিয়া টার্ম অনুপ্রবেশ করানোর মাধ্যমে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানকে উপহাস করার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।
হেঃ হেঃ !! এক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধাণমন্ত্রী হলে চেতন মনের জন্য দুর্ভাগ্যই অপেক্ষা করেছে। হয়তো তলার দিকের সচিবেরা ঘুষ খেয়ে কিছু জানালোই না। কিংবা হয়তো সাহারা খাতুনের মত বলল – মামুলি ব্যাপার ঘটতেই পারে। কোন আইন লঙ্ঘিতই হয় নি… 🙂
সিরিয়াস লেখায় ফাইজলামি করে বসলাম। লেখাটা ভাল হচ্ছে… চলুক! বোঝা যাচ্ছে, বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান খুব বেশি অতীতাশ্রয়ী। এ নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে যে অনেক বিতর্ক আছে সেগুলো নিয়েও আলোচনা দাবী করছি। হয়তো পরবর্তী কোন পর্বে আসবে এগুলো।
পুরো বিষয়টা নিয়ে বই লেখার কথা মাথায় রেখো।
কি ভাবতে গিয়া যে মহান বাংলার প্রধানমন্ত্রী নিয়ে আসছিলাম কে জানে। ঐ সময় শিউর মাথা আউলায়া ছিল। 😀
এই লেখার মধ্যেই বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান নিয়ে বিতর্কগুলা যোগ করতে চাইছিলাম। কিন্তু শেষে ধৈর্য্যহারা হয়ে আর করা হয় নাই। শেষের দিকে এক দুই প্যারায় আছে মনে হয়।
আমার বই লেখার কথা নাকি? বই তো লিখবেন আপনি, তাও আবার অনুমতি পাওয়া পরে। দ্রুত আপনার অনুমতি মিলুক এই কামনা করতেছি 😀
@শিক্ষানবিস,
নীচে কমেন্ট দেখেই নিশ্চয় বুঝতেছ যে, নারীবাদীরা বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানরে খুব একটা পছন্দ করে না। কাজেই আমার আশায় বসে থাকলে সাতমন ঘিও কোনদিন পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।
কাজেই দুর্দিনে তুমিই ভরসা। তুমিই বই লিখা ফেলো।
আমার দ্বারা কিছু হবে এটা যদি ভেবে থাকেন তাইলে অতি সত্বর বন্যা আপার সাথে যোগাযোগ করেন। লিখব লিখব করে আগের কাজটাই এখনও ঠিকমতো শুরু করতে পারে নাই। আমার বিচার হওয়া দরকার।