“শ্রমজীবীভাষা” কলকাতার একটি স্বল্প পরিচিত ক্ষুদ্র বাংলা প্রগতিশীল মাসিক পত্রিকা। তার সাম্প্রতিক এক সংখ্যায় পড়ছিলাম কলকাতার প্রখ্যাত ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ও সমাজ গবেষক ডাঃ স্থবির দাশগুপ্তর লেখা একটি প্রবন্ধ: “সরকারি স্বাস্থ্য-পরিষেবার বিকল্প কি করপোরেট?” ভারি চমৎকার লেখা। জনস্বাস্থ্য সমস্যার উত্থাপন, উদ্বেগের প্রকাশ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থার পরিচিতি, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের নব্য-উদারনীতির ভয়াল প্রকোপে দরিদ্র মানুষের চিকিৎসার সামান্য সুযোগের কর্পোরেট ছিনতাই―সব মিলিয়েই ডাঃ দাশগুপ্তর প্রবন্ধটি আমাদের চিন্তাভাবনাকে যথেষ্ট আলোড়িত করে দিয়েছিল। পড়তে পড়তে ভাবছিলাম, এত নামী একজন চিকিৎসক, নিশ্চয়ই সারা দিন কত ব্যস্ত থাকেন নিজের পেশায়; তারপরও এত চিন্তাশীল মনমোহনী লেখার সময় কীভাবে বের করে নেন? কীভাবে নিজেকে এতটা সামাজিক দায়ের মধ্যেও নিমগ্ন করতে পারেন? সমাজের সুবিধাভোগী স্তরটায় বসবাস করেও তার সম্পর্কেই এতটা বৈচারিক হয়ে উঠতে পারেন কোন ইন্দ্রজালে? অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে উঠেছিলাম পংক্তির পর পংক্তি অক্ষি-লেহনে।
চমকে গেলাম প্রবন্ধের একেবারে শেষ অংশে এসে। ঠিক দেখেছি তো? হ্যাঁ, আর একবার ভালো করে মিলিয়ে নিলাম, লেখক বলেছেন: “করপোরেট সংস্কৃতি শেখায় যে স্বাস্থ্যের অধিকার কেবল তাদেরই যারা যোগ্যতম। যোগ্যতম শব্দটা আমরা ডারউইন-এর কাছ থেকে ধার করলাম, তিনি আবার সেটা ধার করেছিলেন হার্বার্ট স্পেন্সার-এর কাছ থেকে। স্পেন্সার ছিলেন একজন সৃজনশীল জীববিদ্যাবিশারদ। যোগ্যতম শব্দটা তিনি ডারউইন-এর মতো যান্ত্রিক অর্থে ব্যবহার করেননি। করেছিলেন একটি শব্দালঙ্কার হিসেবে। আমরাও সেভাবেই ব্যবহার করে বলতে পারি, দেশের জনমানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় করপোরেট সংস্কৃতি এক কথায় অযোগ্যতম।” [দাশগুপ্ত ২০১৫]
আগাগোড়া এই সুন্দর প্রবন্ধের কোথাও ডারউইনের নাম বা বিবর্তনবাদের কোনো প্রসঙ্গ আসেনি, কথা ওঠেনি। স্পেন্সারের কথাও আসেনি। সেই সব বিষয় ওখানে ওঠার কথাও নয়। আলোচ্য বিষয়ের সাথে তাঁদের বা বিষয়গুলির কোনো সুদূরতম সংযোগও নেই। হঠাৎ করে শেষ পরিচ্ছেদে এমন একটি মন্তব্য উঠে এল কীভাবে? কেনই বা হার্বার্ট স্পেন্সার একজন সৃজনশীল জীববিদ্যাবিশারদ হয়ে উঠলেন এই প্রাজ্ঞ মানুষটির কাছে? “যোগ্যতম” শব্দটা ডারউইনের লেখার ক্ষেত্রে যান্ত্রিক আর স্পেন্সারের ব্যবহারে আলঙ্কারিক―এই পার্থক্যেরই বা চাবিকাঠি কী? শব্দটির প্রথম ব্যবহার কর্তা হিসাবে তিনি যখন স্পেন্সারের নাম জানেন, তখন শুধু শুধু ডারউইনকে আর টেনেই বা আনলেন কেন?
সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন গোলমেলে মনে হল।
এক অচেনা ডারউইন
স্মৃতির সরণি ধরে আর একটু এগোতেই (বা আসলে একটু পিছিয়ে যেতেই) মনে পড়ে গেল, অনেক দিন আগে চার্লস্ ডারউইনের জন্মের দ্বিশতবর্ষ এবং তাঁর “প্রজাতির উদ্ভব” গ্রন্থ প্রকাশের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে (২০০৯) ডাঃ দাশগুপ্তের একটা বেশ বড় প্রবন্ধ পড়েছিলাম। “ডারউইন, আধুনিক জীববিদ্যা ও ক্যানসার”। বেরিয়েছিল সত্যজিত চৌধুরী ও বিজলী সরকার সম্পাদিত, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার নৈহাটির বঙ্কিম ভবন গবেষণা কেন্দ্রের মুখপত্র “বঙ্গদর্শন” পত্রিকায়। [দাশগুপ্ত ২০০৯] সেই প্রবন্ধে লেখক ডারউইনের বিবর্তনবাদকে কাটাছেঁড়া করে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ব্যর্থ একটি অবৈজ্ঞানিক মতবাদ হিসাবে প্রমাণ করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। প্রবন্ধটির বক্তব্য তখনই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তাকে সেই সময় খুব একটা গুরুত্ব দিইনি। এবারের ছোট মন্তব্যটি বুঝিয়ে দিল, সেই অবহেলা করাটা বিরাট একটা ভুল হয়েছিল। বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিজ্ঞানের দর্শনের তরফে আমাদের আরও সজাগ থাকা আবশ্যক। ডারউইনীয় চিন্তাধারার উপর আক্রমণ এই প্রথম নয়। কিন্তু সেটা যখন সমাজের খুব উঁচু সম্মাননীয় জায়গা থেকে দেশের আনাচে-কানাচে বিনা বাধায় জায়গা করে নিতে থাকে তার ক্ষতি করার ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। ফলে, আমাদের দিক থেকে দেখলে, এসম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন না করাটা এক অমার্জনীয় ত্রুটি তো বটেই।
তাছাড়া, এও আমরা জানি, সমাজে এরকম ধারণা পোষণকারী মানুষের সংখ্যা খুব কম নয়। অতএব দেরিতে হলেও ডাঃ স্থবির দাশগুপ্তর সেই প্রবন্ধকে সামনে রেখে আমি এখানে আমার সীমিত সাধ্য নিয়ে ডারউইন এবং বিজ্ঞানের সপক্ষে কিছু কথা বলার চেষ্টা করব। চিকিৎসক দাশগুপ্তের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা বজায় রেখেই তাঁর বিজ্ঞান ভাষ্য সম্পর্কে আমার মতামত খোলাখুলি রাখতে চাই। আশা করি সকল পাঠকবৃন্দ বিবেচনা করে দেখবেন।
প্রথমেই একটা বিস্ময়কর ঘটনার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, সেই প্রবন্ধের শুরুতেই লেখক আক্ষেপ করেন, বিবর্তন তত্ত্বের স্রষ্টা হিসাবে আলফ্রেড ওয়ালেসের যে ডারউইনের সমান ভূমিকা ছিল তার স্বীকৃতি থেকে যেন ইতিহাস তাঁকে বঞ্চিত করেছে। [দাশগুপ্ত ২০০৯, ৩৯-৪০] কিন্তু পরে তিনি যখন সেই তত্ত্বের বিরুদ্ধেই একের পর এক ড্রোন চালনা করতে থাকেন, তখন একবারের জন্যও আর সেই ওয়ালেসের নাম উচ্চারণ করেন না। যাবতীয় আক্রমণ শুধু একজনেরই প্রাপ্য হয়। এর কারণ আমাদের কাছে কখনই পরিষ্কার হয় না। শুধু মনে হয় যেন, জীব বিবর্তনের তত্ত্ব আবিষ্কারের কৃতিত্ব দুজনেরই। কিন্তু এর মধ্যে ভুলভ্রান্তি যা কিছু, তার দায় একা ডারউইনেরই।
হ্যাঁ, ইতিহাসের দিক থেকে একথা সত্য যে এই তত্ত্ব দুজনেই স্বতন্ত্রভাবে আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু শুধু তো এইটুকুই ঘটনার সব নয়। আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও তো পাশাপাশি বিদ্যমান। সেইগুলো একই সঙ্গে বলে না দিলে ডারউইন সম্পর্কে ভুল বোঝার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। মনে হবে, দুজনের কৃতিত্ব তিনি বুঝি কায়দা করে একাই নিজের নামে বাগিয়ে নিয়ে খ্যাতি ভোগ করে গেছেন! যথা: (এক) ডারউইন জীববৈচিত্র্য ও ভূ-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ‘বিগ্ল’ জাহাজে চেপে সমুদ্রভ্রমণে বেরিয়েছিলেন ১৮৩১ সালে আর ফিরে আসেন পাঁচ বছর বাদে। পৃথিবীর সমুদ্রতটভূমির প্রায় অর্ধেক তিনি ঘুরে দেখে আসেন। ওয়ালেস সমুদ্র ভ্রমণে বেরলেন একবার ১৮৪৮ সালে দক্ষিণ আমেরিকায় আর ফিরে এলেন ১৮৫২ সালে। তারপর আবার বেরলেন ১৮৫৪ সালে এবং ১৮৬২ সাল পর্যন্ত ঘুরে বেড়ালেন পূর্ব গোলার্ধের মালয় দ্বীপপুঞ্জে। (দুই) ডারউইনের নোটবইগুলি এবং কিছু ব্যক্তিগত চিঠিপত্র থেকে নিশ্চিতভাবেই জানা যায়, তিনি ১৮৪০ সালের মধ্যেই বিবর্তনের মূল তাত্ত্বিক কাঠামোটি এক রকম নির্মাণ করে ফেলেছিলেন। তাঁর বিজ্ঞানী বন্ধুরা বারবার করে তাঁকে অনুরোধ করছিলেন, সেই তত্ত্ব বই আকারে লিখে তাড়াতাড়ি প্রকাশ করার জন্য।
হ্যাঁ, ওয়ালেসও তাঁর মতো করে একই তত্ত্ব রচনা করে ফেলেন মোটামুটি ১৮৫৫ সাল নাগাদ। ডারউইনের অন্তত পনের বছর পরে। সেও তাঁর নিজের লেখাপত্র পড়েই জানা গেছে। বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, তাঁদের মধ্যে এই তথ্যগুলি নিয়ে আজ আর সম্ভবত কোনো দ্বৈমত্য নেই। (তিন) ওয়ালেস যে সুদূর মালয়ভূমি থেকে তাঁর লেখা বিশাল পাণ্ডুলিপিটি ১৮৫৮ সালে বেছে বেছে অখ্যাত অজ্ঞাত ডিগ্রিহীন অ-পেশাদার নিরীহ প্রকৃতিবিদ ডারউইনের কাছেই ডাকযোগে পাঠাতে গেলেন―তারও নিশ্চয়ই কিছু বিশেষ কারণ ছিল। এবং সেগুলো ডাঃ দাশগুপ্ত জানেন বলেই মনে হয়। অতএব প্রশ্ন হচ্ছে, এই সমস্ত তথ্যাদি তিনি চেপে রাখতে চাইলেন কেন?
আসলে ডারউইনের বিজ্ঞানী বন্ধুরা তাঁর আবিষ্কারের প্রাথমিকতা অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েই, ওয়ালেসের সাথে কথা বলেই, ডারউইনের বইটি, “প্রজাতির উদ্ভব”, অবিলম্বে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ওয়ালেসও ডারউইনের দীর্ঘদিনের কাজের সমস্ত ইতিবৃত্ত জানবার পর সানন্দে এই প্রস্তাবে মত দেন। মানুষ হিসাবে তিনিও মহৎ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। আবার ডারউইন ওয়ালেসের এই উদারতার ঋণ চিরদিন মনে রেখেছেন শুধু নয়, তাঁকে সাধ্যমতো বহুভাবে সাহায্য করে গেছেন। এমনকি, ওয়ালেস যখন প্রেততত্ত্ব ও প্ল্যাঞ্চেট নিয়ে এক বিশাল কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েন এবং সমকালীন সমস্ত বিজ্ঞানীরা তাঁকে বিজ্ঞানের সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে কার্যত বয়কট করে বসেন, তখনও ডারউইন অন্য সমস্ত বিশিষ্ট বন্ধুদের সঙ্গে বিচ্ছেদের ঝুঁকি নিয়েও দারিদ্র্য পীড়িত ওয়ালেসের পাশে দাঁড়িয়ে থেকেছেন। সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে এই বয়ঃকনিষ্ঠ বন্ধুটির জন্য মাসিক একটা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে দিয়েছেন।
ডাঃ দাশগুপ্ত যে ওয়ালেস প্রসঙ্গ উত্থাপন করেও এই সমস্ত তথ্য অনুচ্চারিত রেখে দিলেন, তার কারণও আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। এমনটা নয় তো, ওয়ালেসের প্রতি পাঠকের সহানুভূতি জাগিয়ে দিয়ে . . .?
তারপর লামার্ক। লামার্কের তত্ত্ব নিয়ে কোনো বৈজ্ঞানিক বিচার তাঁর এই রচনায় নেই। অথচ তিনি জানালেন দুটো খুব আকর্ষণীয় তথ্য, যদি অবশ্য এরকম মন্তব্যকে তথ্য বলা যায়। (এক) “তাঁর বক্তব্যের অতি-সরলীকরণ করে তাঁকে যথেষ্ট বিদ্রূপ করা হয়েছে”; এবং (দুই) “পরবর্তীকালে ডারউইন নিজেই তাঁর ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে লামার্ক থেকে অবলীলায় আহরণ করে গেছেন।” [দাশগুপ্ত ২০০৯, ৪১] যদি ধরেও নিই, কেউ কেউ লামার্কের ব্যবহার-অব্যবহার তত্ত্ব নিয়ে বিদ্রূপ করেছে, ডারউইন তো কোথাও তা করেননি, বরং লামার্কের ঋণ তাঁর “প্রজাতির উদ্ভব” গ্রন্থের ভূমিকায় শতমুখে স্বীকার করে গেছেন। আর, অতি-সরলীকরণ না করেও জীববিজ্ঞানীদের অনেকেই তো লামার্কীয় তত্ত্বকে সঠিকভাবে উপস্থাপন ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করেছেন। সেই কথাগুলো ডাক্তারবাবুর মনে পড়ল না দেখে অবাকই হতে হয়। অথবা যদি তিনি মনেই করেন যে লামার্কীয় তত্ত্বটা ডারউইনের চেয়ে বেশি কার্যকরী সেটা মুখ ফুটে বললে এবং আমাদের বুঝিয়ে দিলেই তো আরও ভালো হত। সেটা না করে . . .।
এবং স্পেন্সার। এই ভদ্রলোক তাঁর জীবদ্দশায় বহু বিষয়ে পাণ্ডিত্যের জন্য দেশে বিদেশে বেশ খ্যাতিমান ছিলেন, অনেক বিষয়েই মোটা মোটা বইও লিখে গেছেন। অথচ মৃত্যুর পর দশ বছরের মধ্যে তাঁর নিজের দেশেই তিনি প্রায় হারিয়ে গেলেন। কেন না, তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে সেই বৃহদায়তন রচনাবলির কোনোটার থেকেই পরবর্তীকালে জ্ঞানের রাজ্যে এগোনোর মতো কিছু মাত্র কাজের মালমশলা পাওয়া যায়নি। বরং বিশ শতকের প্রথমার্ধে যে সৌজাত্যবাদ (eugenics) এবং সামাজিক-ডারউইনবাদ (social Darwinism) সারা পৃথিবীতেই প্রচুর সমালোচনার সামনে পড়েছিল, তিনি ছিলেন সেই সব মতেরই একজন সোচ্চার আদি সমর্থক। পক্ষান্তরে, বিবর্তন বিষয়ে ডারউইনের নিজস্ব অনেক বক্তব্য বিজ্ঞানের পরবর্তী অগ্রগতির ধারায় বাতিল হয়ে গেলেও তাঁর মূল তত্ত্ব এবং সিদ্ধান্তটি কিন্তু আজ অবধি টিকে গেছে।
কোথাও কি তাঁর মনে পূর্ব ধারণার স্থির মেঘ জমে ছিল? তিনি কি ডারউইন সম্পর্কে প্রথম থেকেই পাঠককে কিঞ্চিত বিরূপ করে দিতে চেয়েছিলেন? সেই জন্যই কি কখনও ওয়ালেস, কখনও স্পেন্সার, আর কখনও লামার্ক তাঁর লেখায় ডারউইনকে ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠেন? হয়ত এই জন্যই তাঁকে বলতে শুনি: “এখান থেকেই ডারউইনকে দেখা দরকার; তাতে অন্তত চতুর্দিকে যা গদগদ ভাব দেখি তা থেকে রেহাই পাওয়া যায়।” [দাশগুপ্ত ২০০৯, ৪১] ডারউইনের প্রতি কার বা কাদের এই গদগদভাব তা আর তিনি খুলে বলেননি। আমাদের মনে একটা খটকা থেকেই যায়।
শুধু পড়তে নয়, মনের গভীর অন্তস্থল থেকে যে বুদ্বুদটা উঠে আসতে চায়, ভাবতেও কষ্ট হয় সেই কথা।
ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব: বাঁকা চোখে
ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সুপরিচিত বিষয়। এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য তত্ত্বের মতোই এরও বিকাশের একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ডারউইনবাদ নামে পরিচিত হলেও নিছক ডারউইনের কথার মধ্যে তা আর অনেক দিনই সীমাবদ্ধ নেই। ইতিহাসের প্রতি সুবিচারকল্পে হয়ত আমরা অনেকেই ডারউইনের নিজের বক্তব্য থেকেই আলাপন শুরু করি। কিন্তু এটা জেনেই যে ডারউইন এই বিষয়ে যতদূর বলেছিলেন বা বলতে পেরেছিলেন, আজ বিজ্ঞান তার অনেক কিছুই আর সঠিক মনে করে না, তাকে ছাড়িয়ে বিজ্ঞান এই প্রশ্নেও বহু দূরে এগিয়ে গেছে।
শুধু ডারউইন কেন, সমস্ত বড় বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রে এই একই কথা। নিউটনের বলবিদ্যার তত্ত্বও আজকাল কেউ নিউটনের নিজের বয়ানে শেখে না। শেখে আধুনিক অগ্রসর জ্ঞানের আলোকে। তার মধ্যে তাঁর প্রদত্ত অনেক সিদ্ধান্তই বাতিল হয়ে অন্যদের কাজ ঢুকে যায়। তবু নিউটন অমর হয়ে থাকেন বিজ্ঞানের ইতিহাসে, ডারউইনও। তাঁদের যাঁর যতটুকু গুরুত্ব ও স্বীকৃতি প্রাপ্য তা দেওয়াকে কেউ “গদগদভাব” বলে না। যেমন, তাঁদের ভুল বা সীমাবদ্ধতা দেখানোকেও কেউ অশ্রদ্ধা বলে মনে করে না। বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মশাস্ত্রের এই জায়গাতেই তো পার্থক্য।
স্থবিরবাবু তাহলে এই সতর্কবাণী দিতে গেলেন কেন?
কারণ তাঁর ধারণা অনুযায়ী, ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব অনেক দিন আগেই বিজ্ঞানে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়ে গেছে, কিন্তু বিজ্ঞানীরা বা বিজ্ঞান অনুরাগীরা এখনও সেই তত্ত্বকে ছাড়তে পারছেন না এর নিরীশ্বরবাদিতার কারণে। আর তিনি চেয়েছেন, সেই ভুলগুলিকে ধরিয়ে দিতে। স্পষ্টভাষায়, জোরের সাথে, কোনো দুর্বলতার নামগন্ধ না রেখে। ফলে, ডারউইন তত্ত্বের মূল কথাগুলি কী কী, তার মধ্যে কোন কোনটা ভুল সাব্যস্ত হয়েছে, কোন বিষয়টা এখনও গ্রাহ্য―এই রকম স্বাভাবিক প্রচলিত বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রতর্কের রাস্তায় না হেঁটে তিনি কিছু মিঠে-কড়া মন্তব্য বিক্ষিপ্তভাবে ছুঁড়ে দিয়েছেন।
যেমন, বিবর্তনের ধারণা লাভ করে “জীববিজ্ঞান কতটা মহত্তর হয়েছে বা মানবমন কতটা পরিশীলিত হয়েছে তা নিয়ে সংশয় আছে।” আর, “জীববিজ্ঞানে ডারউইনীয় বিপ্লব যে কতটা মৌলিক তা নিয়েও সংশয় ঘনীভূত হয়।” [দাশগুপ্ত ২০০৯, ৪০] অর্থাৎ, জীব-বিজ্ঞানে বা সাধারণভাবে বিজ্ঞানচিন্তার জগতে যে কথাগুলো এখন নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত, সেগুলো সম্বন্ধেই তিনি সন্দিহান, এবং পাঠককেও সেই সন্দেহের অংশীদার করে তুলতে চান। জ্ঞানের জগত যে কোনো নতুন সত্যোপলব্ধির দ্বারা উপকৃত ও সমৃদ্ধ হয় এবং মানব মনও তার ফলে পরিশীলিত হয়ে ওঠে―এটা একটা সাধারণ সত্য। বিবর্তনের ধারণা সত্য হলে তার দ্বারাও এই উপকারগুলি হবে, না হলে হবে না। ফলে ধারণাটা সত্য কিনা এই প্রশ্নটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মহত্ত্ব-টহত্ত্বের কথা এখানে কেন উঠবে? (এই বিষয়ে আমি পরে আরও কিছু কথা বলব।)
অতঃপর ম্যালথাস। বিগ্ল জাহাজে বিশ্ব ভ্রমণ করে এসে ডারউইন “ম্যালথাসে অনুরক্ত” [দাশগুপ্ত ২০০৯, ৪১] হন। ওয়ালেসও যে একইভাবে পূর্ব গোলার্ধ পাড়ি দিতে দিতে ম্যালথাসে অনুরক্ত হয়েছিলেন, এবং হুবহু একই কারণে, সেই কথাটা ডাঃ দাশগুপ্ত পাঠককে বলে তাঁদের আর কেন জানি না পাঠ-ক্লান্ত করেন না। ম্যালথাস থেকে ডারউইন কী নিলেন? “অযোগ্য মানুষ ক্রমাগত জাহান্নমে যাবে, এমনই এক বর্বর সমাজের ছবি এঁকেছিলেন ম্যালথাস। আর জীবজগতের কথা রূপ ভাবতে গিয়ে সেই ছবিই ডারউইনের মনোগত ধারণার সাথে খাপে খাপে মিলে গিয়েছিল।” [দাশগুপ্ত ২০০৯, ৪৩] কেন না, লেখকের মতে, “বিবর্তনের ডারউইনীয় ধারণাটির মূল সুর হল প্রতিযোগিতা, তীব্র থেকে তীব্র প্রতিযোগিতা, আর জীবনসংগ্রাম, প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতর। . . . সে যেন এক নৃশংস গৃহযুদ্ধ, . . . সে যেন এক মাৎস্যন্যায়।” [দাশগুপ্ত ২০০৯, ৪২] পাঠক যদি এখনও বিরূপ না হয়ে থাকেন তো জেনে রাখুন: “ম্যালথাস বা হাক্সলি বা ডারউইনের কাছ থেকে আমরা পেলাম একটি আদ্যোপান্ত প্রতিযোগী, মুনাফালোভী, যৌনাকাঙ্ক্ষায় কাতর আর ভোগী সমাজের ছবি।” [দাশুগুপ্ত ২০০৯, ৪৩] কী সাংঘাতিক বিপজ্জনক লোক ছিলেন ডারউইন এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবরা, বুঝতে পারছেন তো?
যাঁরা ডারউইনের বিবর্তন সংক্রান্ত বক্তব্য জানেন, তাঁদের নিশ্চয়ই এও জানা আছে যে এই তত্ত্বকাঠামোয় একটা মূল স্তম্ভ হল প্রাকৃতিক নির্বাচন। এই তত্ত্বের অন্য সব কিছু ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে এই “নির্বাচন”-এর ধারণা। আধুনিক জীববিজ্ঞানে এটা একটা অত্যন্ত শক্তিশালী কার্যকরী ধারণা হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। অথচ লেখক তার কোনো রকম ব্যাখ্যায় যান না। তাঁর কাছে এটা নিতান্তই একটা ছক। “পরিবেশের সাথে জীবের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ফলে জীব এলোপাতারিভাবে নানান বৈচিত্র্য অর্জন করে। প্রকৃতি সেই বৈচিত্র্য থেকে যা যা লাভজনক আর সুবিধাজনক তা নির্বাচন করে দেয়। আপাতভাবে এই তত্ত্ব বেশ গ্রহণযোগ্য মনে হলেও এ নিয়ে বারবার নানান দিক থেকে নানান প্রশ্ন উঠেছে। সদুত্তর মেলেনি।” [দাশগুপ্ত ২০০৯, ৪১]
খুব স্বাভাবিক ব্যাপার, তাই না?
সত্যিই যদি প্রাকৃতিক নির্বাচন বলতে এই রকম কিছু বোঝায়, একটা মানব সদৃশ সচেতন কারকের মতো, তাহলে তো উপরোক্ত প্রশ্নগুলো উঠবেই, আর সদুত্তরও পাওয়া যাবে না। প্রাচীন কাল থেকেই মতবাদিক বিতর্কের এ একটা অনন্য কৌশল, যা বুদ্ধিমান লোকেরা ব্যবহার করে এসেছে: যে তত্ত্বকে খণ্ডন করতে চাও, তাকে প্রথমে এমনভাবে উপস্থাপন কর যাতে তা সহজেই খণ্ডনযোগ্য হয়ে পড়ে। সন্তান পাগল মা-কালীর কাছে বলি যদি দিতেই হয় অজগর নয়, অজকে বলি দাও। তাহলে, মা খাক না খাক, পুজো মিটিয়ে পরে নিজেরাও মাংস খেতে পাবে। এই কায়দা অবলম্বনের ফলে কত সহজ হয়ে যায় বিজ্ঞান বিষয়ক তার্কিক আলোচনা। এই রকম উপস্থাপনার জোরেই এটা দেখানো অতি সহজ হয়ে ওঠে যে প্রাকৃতিক নির্বাচন কিছুই করতে পারে না, নতুন কোনো প্রজাতি সৃষ্টি করতে বা বিদ্যমান প্রজাতিতে নতুন কোনো গুণ বা অঙ্গ তৈরি করতে পারে না, সে শুধু ঋণাত্মক ভূমিকা পালন করতে পারে, প্রজাতি বিলুপ্তির ব্যাখ্যাই করতে পারে। ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও উদাহরণ উঠে আসে তাঁর লেখায়। তাতে শেষ পর্যন্ত “প্রাকৃতিক নির্বাচনের সূত্রটি যে আদতে কেবল কথার মারপ্যাঁচ” এটা প্রমাণিত হয়ে যায়। বোঝা যায় যে “ডারউইনীয় যুক্তিগুলোর অধিকাংশই আসলে বৃত্তাকার যুক্তি, যেখান থেকে শুরু হয় সেখানেই এসে শেষ হয়।” [দাশগুপ্ত ২০০৯, ৪৭]
জিনতত্ত্ব এবং তার পরিব্যক্তির তত্ত্ব সম্পর্কে স্থবিরবাবুর উপস্থাপনাও মোটামুটি একই রকম। যেভাবে বললে আধুনিক জিনতত্ত্বকে সম্পূর্ণ নস্যাত করে দেওয়া যায়, সেভাবেই রাখ। সত্য মিথ্যার তোয়াক্কা না করেই। যেমন, “মিউটেশন দিয়ে তো নতুন প্রজাতিও সৃষ্টি হচ্ছে না কারণ মিউটেশনের ফলে কোনো নতুন কাঁচা মাল তৈরি হচ্ছে না। তাহলে বিবর্তনলব্ধ পরিবর্তনের কারণ তো মিউটেশন নয়।” [দাশগুপ্ত ২০০৯, ৪৬] এর পর তিনি জিনপুলগত বৈচিত্র্য আর প্রজাতিগত বৈচিত্র্যকে মিলিয়ে ফেলেন এবং ঘোষণা করেন, “জিনগত বৈচিত্র্যের ফলে কোনো সরীসৃপ কখনও পাখি হয়ে যায় না।” [দাশগুপ্ত ২০০৯, ৪৭] “শিম্পাঞ্জির সাথে মানুষের জিনগত পার্থক্য তো মাত্র ২%; তাতে কী এমন ঘটে গেল যে প্রজাতি হিসেবেই আমরা আলাদা হয়ে গেলাম? ডারউইনের কাছে এসবের কোনো ব্যাখ্যা আমরা পাইনি।” [দাশগুপ্ত ২০০৯, ৫১] শুধু কি তাই? “মানব জিনোম প্রকল্পের কল্যাণে আমরা জানতে পেরেছি, আমাদের ডি এন এ-তে যে জিনসঙ্কেত থাকে তার ৯০% উদ্দেশ্যহীন, আর বাকি ১০% দিয়ে এমন সুন্দর [হাত, চোখ, ইত্যাদির] অবয়ব গঠনের ব্যাখ্যা অসম্ভব।” এবং “অনেক আশা সত্ত্বেও মানব জিনোম প্রকল্প পশু থেকে মানুষে উত্তরণের কারণ খুঁজে পায়নি। জিন দিয়ে তার ব্যাখ্যা সম্ভব হয়নি।” [দাশগুপ্ত ২০০৯, ৫৮] কে বা কারা যে জিন-বৈচিত্র্য দিয়ে সরীসৃপ থেকে পাখির উদ্ভবের কথা বলেছে, কিংবা জিনের সাহায্যে মানুষের মানবিক গুণে উত্তরণের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে, তাও জানতে পারি না। শুধু অভিযোগটাই শুনি। হা করে, অবাক বিস্ময়ে!
খণ্ডতাবাদ: আর এক আসামী
কেন এই ব্যর্থতা? তারও জবাব তৈরি আছে স্থবিরবাবুর কাছে। খণ্ডতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি (reductionist approach)। পূর্ণ বাস্তবকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে তার বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলিকে “জোড়া লাগিয়ে পূর্ণ বাস্তবের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা” হল “খণ্ডতাবাদের সার্বিক লক্ষণ।” তার ফলে কী হয়? বিজ্ঞানে এক সরলরৈখিক ব্যাখ্যার প্রবণতা বাড়তে থাকে। কিন্তু “গবেষণা যত এগোচ্ছে তত স্পষ্ট হচ্ছে যে কোষের মধ্যে, কোষের বাইরে, জিনের মধ্যে, জিনের বাইরে এবং জিনের অভিব্যক্তির মধ্যে বহু বহু জটিলতা ও গতিময়তা (‘ডায়নামিজম’) অনবরত কাজ করে যায়। খণ্ডতাবাদী বিশ্ববীক্ষা দিয়ে সেই গতিময়তাকে ধরা যায় না।” [দাশগুপ্ত ২০০৯, ৫০-৫১]
কিছু কি বুঝলেন পাঠক? তাহলে তো খণ্ডতাবাদী গবেষণার অগ্রগতি থেকেই বোঝা গেল খণ্ডতাবাদ দিয়ে কাজ হয় না। একটু খচখচ করছে না? যাঁরা জীবের কোষে এবং কোষের জিনে জটিলতা ও গতিময়তা খুঁজে পেলেন, কী করে পেলেন? তাঁরা তো খণ্ডতাবাদী বিশ্ববীক্ষা নিয়ে চলছেন। তাঁদের এসব দেখার বা দেখতে পাওয়ার কথা নয়। তাঁরা তো স্কুল পাঠ্য জ্যামিতিতে সরল রেখা ছাড়া আর বিশেষ কিছু শেখেননি!
খণ্ডতাবাদীর আরও অপরাধ ধরা পড়েছে। তাঁরা বলেন যে “জীব আবশ্যিকভাবে সহজ থেকে জটিল বা জটিলতর হয়ে ওঠে, যাকে বলে সারল্য থেকে জটিলতায় উত্তরণ”, যা “একটি নিপাট সরলরৈখিক ধারণা।” স্থবির দাশগুপ্ত সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন: “খণ্ডতাবাদী ধ্যানধারণাগুলো আমাদের আজন্ম-লালিত বলে এককোষী জীব কীসে সরল তা আমরা ভেবে দেখতে চাই না।” [দাশগুপ্ত ২০০৯, ৫১] সুতরাং তিনিই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে একটা মাত্র কোষের মধ্যে কী বিশাল জটিল ধুন্ধুমার কাণ্ডকারখানা চলতে থাকে তার বিবরণ দেন! তারপর বলেন, “সারল্য কোথায়, সবটাই তো অভাবনীয় জটিল! একেই অনেকে বলেছেন অহ্রস্বনীয় জটিলতা (irreducible complexity)। আমরা খণ্ডতাবাদ দিয়ে এই অখণ্ডনীয় বাস্তবকে ব্যাখ্যা করার বাতুল চেষ্টা চালাই।” [ঐ]
আবারও দুটো খটকা জেগে ওঠে। হয়ত ডারউইনপন্থী খণ্ডতাবাদের চাপেই। এক নম্বর, একটা কোষের ভেতরের এই সব জটিল কাণ্ডকারখানার হদিশ কারা খুঁজে বের করল―সেই খণ্ডতাবাদী বিজ্ঞানীরা, না, নতুন একদল অখণ্ডতাবাদী জীববিজ্ঞানী আসরে নেমে পড়েছেন? স্থবিরবাবু এটা আমাদের জানিয়ে দিলে এখন থেকে আমরা সেই অখণ্ডতাবাদী বিজ্ঞানীদের রচনাই পড়ব। কিন্তু নিশ্চিতভাবে জানাতে হবে যে খণ্ডতাবাদীরা এই সবের হদিশ পাননি। দু নম্বর কথা, একটা কোষ যে খুব জটিল ব্যাপার সে তো না হয় বোঝা গেল (কে বা কারা এটা অস্বীকার করেছিল তা অবশ্য আমার জানা নেই)। কিন্তু বহুকোষী জীবগুলির দেহ গঠন বা ক্রিয়া কি এককোষীদের চাইতে সরল নাকি? শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদের তুলনায় আম গাছের গঠন বোধ হয় সরলতর? ব্যাক্টিরিয়ার তুলনায় আরশোলার শারীরস্থান ও শারীরবৃত্ত সরলতর বুঝি? ছত্রাকের সঙ্গে তুলনা করলে মানুষকে তাহলে এখন থেকে অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখে সরলতর বলতে হবে? বলা যায় না, কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হয়ত জটিলতা কমে যেতেও পারে! বিপুলা এ অখণ্ড বিশ্বের আমরা খণ্ডতাবাদীরা আর কতটুকু জানি!
বিবর্তনের কোনো সালানুক্রম আছে কি? জীবাশ্ম-খাতা থেকে সম্ভবত বলা যায়, কোন সময়ে কী ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছে। তার মধ্যে বোধ হয় সারল্য থেকে জটিলতায় উত্তরণের একটা সাধারণ ছবিও দেখতে পাওয়া যায়। প্রিক্যাম্ব্রিয়ান যুগে তো নয়ই, এমনকি আজ থেকে ২০ কোটি বছরের আগে স্তন্যপায়ীদের জীবাশ্মের দেখা যে মেলে না―তার কারণ দৃষ্টিটা খণ্ডিত বলে নয়। জীবাশ্ম তৈরি হওয়ার মতো সেরকম প্রাণীরা কেউ আসেনি বলেই। [Wikipedia 2015] ইঁদুরের জীবাশ্ম যে-অতীত কাল থেকে পাওয়া যায়, সে সময়ে বানরের বা গরিলার জীবাশ্ম দেখা যায়নি। শিম্পাঞ্জির অনেক পরেই যে মানুষের বিবর্তন ঘটেছে জীবাশ্ম-সাক্ষ্য থেকে এটাও নিশ্চিতভাবেই জানা আছে, এবং ডাক্তার দাশগুপ্তও নিশ্চয়ই তা জানেন। আর মানুষের সেই সব পূর্বপুরুষদের তুলনায় মানুষের হাতদুটির যে অতুলনীয় “সৌকর্ষ” বিকশিত হল, তাও যে শিম্পাঞ্জির উদ্ভবের বেশ অনেক কাল পরেই হয়েছে এটাও তিনি জানেন। তাহলে সরল থেকে জটিল হওয়াটা কি আটকানো গেল? শুধু খণ্ডতাবাদীরা নয়, অখণ্ডতাবাদীদেরকেও একই সত্য স্বীকার করতে হচ্ছে। তথ্যেন নান্য পন্থাঃ বিদ্যতে। আরও দুঃখের কথা হল, সেই খণ্ডতাবাদীদের থেকেই তথ্য সংগ্রহ করে তাঁদের এগুলো বলতে হচ্ছে।
বিবর্তন যদি হয়ে থাকে এবং জীবাশ্ম সাক্ষ্য অনুযায়ী যদি দেখি যত প্রাচীনতর জীব তত তার সরলতর গঠন ও ক্রিয়াকলাপ, এবং যত আধুনিক ততই জটিল সংগঠন ও কার্যকলাপ, তাহলে খণ্ডতাবাদীই হোন বা অখণ্ডতাবাদী, এই সোজা কথাটা তো স্বীকার করতেই হবে। আর এর মধ্যে সরলরৈখিক কী আছে? এমন তো নয় যে জীববিজ্ঞানীদের মতে বিবর্তনের ধারায় সময়ের একই সরল রেখায় একের পর এক বিভিন্ন প্রাণী এবং উদ্ভিদ বা অন্যান্য জীবগুলি এসেছে। ডারউইনের ধারণায়ও কোনো সরল রৈখিক বিকাশের ছবি ছিল না। ডারউইনের বইতে একটি মাত্র ছবি আছে—যা এই ধারণার সম্ভাবনাকে পুরোপুরিই নাকচ করে দেয়। এটা বিবর্তনবাদ বিরোধীরা বিবর্তনের ধারণাকে বিরোধিতা করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যের দিক থেকে সুবিধা করতে না পেরে নিজেদের মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভাবন করে একটা মিথ্যা দাবি তার উপরে চাপিয়ে দিয়েছেন। হাতের সামনে এর একটা জলজ্যান্ত উদাহরণ রয়েছে। স্বয়ং ডাঃ দাশগুপ্ত যখন ভুল করে বা অসাবধানতা বশত লিখে ফেলেন, “নিতান্ত বানর থেকে মানুষের বিবর্তনের ব্যাখ্যাটি কত সরলরৈখিক”, তখন হয়ত ভুল খুঁজে পাওয়ার জন্যই একটা ভ্রান্ত অতিসরলীকৃত বিবৃতি বিবর্তনবাদীদের মুখে বসিয়ে দেন। “বানর থেকে মানুষের বিবর্তন” সংক্রান্ত একরেখ এই ধারণাটি ডারউইন থেকে শুরু করে আজ অবধি কোনো জীববিজ্ঞানীর মুখেই আমরা শুনতে পাইনি। এটা ছিল বিবর্তন তত্ত্বের প্রথম যুগের একদল লোকপ্রিয় ভাষ্যকারদের অবুঝ উপস্থাপনা। আর এটাকেই সেই তত্ত্বের সার কথা ধরে নিয়ে খ্রিস্টীয় ধর্মতাত্ত্বিকরা ডারউইনের বিরুদ্ধে তাঁদের (কু)-যুক্তিতে শান দিয়েছিলেন। স্থবিরবাবু কীভাবে সেটাকেই জীববিজ্ঞানীদের ধারণা বলে ধরে নিলেন―এটা আমার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর ঠেকেছে। জীববিজ্ঞানীদের এ সম্পর্কে বক্তব্য হল, বর্তমানে বিদ্যমান বানর, নরবানর ও মানুষের প্রজাতিগুলির কোনো এক প্রাচীনতর প্রাইমেট পূর্বপুরুষ রয়েছে, যেখান থেকে তাদের ভিন্ন ভিন্ন বিবর্তন পথগুলি শুরু হয়েছিল।
আরও দু একটা সন্দেহ জেগে ওঠে। (এক) অহ্রস্বনীয় জটিলতা মানে হল জটিলতার সবচাইতে কম মাত্রা। যার থেকে আর জটিলতা কমানো যাবে না। বাড়ানোও কি যাবে না? বাস্তবে বাড়ে না কি? নাকি আমারই বুঝতে ভুল হয়ে গেল? (দুই) সরীসৃপ থেকে পাখির বিবর্তনের প্রশ্নে বলি: কোনো একটি সরীসৃপের জিনপুলগত বৈচিত্র্য থেকে নিশ্চয়ই পাখির উদ্ভব হয় না। কিন্তু যখন কোনো এক সরীসৃপ প্রজাতির ধারা থেকে পাখির ধারাটির শুরুয়াত হয়, তখনও কি তারা জিনগতভাবে আলাদা হয়ে যায় না? তাদের মধ্যেকার পার্থক্যের বিষয়গুলিতে বাইরের আকার আকৃতি আচরণগত উপাদানগুলির পাশাপাশি আভ্যন্তরীন পর্যায়ে জিনগত উপাদানকেও কি ধরা যায় না? ধরলে নিশ্চয়ই ভুল হয় না, বরং বিবর্তনের ধারণা আরও শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধশালী হয়।
আসলে এ যেন পণ করে বসে থাকা যে আমি বিবর্তনের তত্ত্বকে ভুল সাব্যস্ত করবই। না হলে, বিবর্তন সম্পর্কে সঠিক বিবরণ যুক্ত প্রামাণ্য বইপত্রের সংখ্যা আজকের দিনে খুব একটা কম নয়।
আর শেষে খণ্ডতাবাদ প্রসঙ্গেও কয়েকটা জরুরি কথা বলে রাখি। ইদানিং কালে বিজ্ঞানের দর্শন চর্চায় খণ্ড-অখণ্ড নিয়ে আক্ষেপের যেন ধুম পড়েছে। অনেকেই দেখি খুব চিন্তিত আধুনিক বিজ্ঞানের খণ্ডচিত্র নিয়ে। তাঁরা যেন আপ্রাণ চেষ্টায় চান বিজ্ঞানকে এক অখণ্ডবাদী বীক্ষায় দীক্ষিত করতে। অথচ তাঁরা খেয়াল করেন না, বুঝতেও চেষ্টা করেন না, বিজ্ঞানের কোনো অখণ্ড দৃকপাত (holistic approach) হয় না। বিজ্ঞান মানেই তা অংশের জ্ঞান, খণ্ডের বিশ্লেষণ, যাকে বুঝতে চাই টুকরো টুকরো করে দেখা। যতদিন মানুষ এক সাথে সব কিছুকে জানবার চেষ্টা করেছে, সে কিছুই সঠিকভাবে জানতে পারেনি। সতের শতকের শুরুতে ফরাসি যুক্তিবাদী দার্শনিক রন দকার্ত প্রথম আমাদের জানালেন, জানতে হবে একটু একটু করে। ছোট ছোট প্রশ্ন করে এবং সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে। অল্প অল্প করে জানতে জানতে এগোতে হবে। এইভাবেই জানার পরিমাণ বাড়বে। আর বাস্তবেও ঠিক তাই ঘটেছে। এইভাবেই মানুষ জ্ঞানের রাজ্যে অগ্রসর হয়েছে।
আবার এইভাবে জানতে হয় বলেই মানুষ একটা সময় থেকে বিজ্ঞানের পরিধিকে বিভিন্ন শাখায় ভেঙে নিয়েছে। প্রকৃতি সমাজ ও মানুষের এক একটা ক্ষেত্রের নিপুণ জ্ঞানের প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ নৈপুণ্যায়ন (specialization)-এর আয়োজন করে নিয়েছে। বিজ্ঞান যদি অণু পরমাণু থেকে ইলেকট্রন প্রোটন হয়ে কোয়ার্ক গ্লুওন ইত্যাদির দিকে না এগোয়, বস্তুজগতকে সে বিস্তারিতভাবে জানবে কীভাবে? বিজ্ঞান যদি কোষের ভেতরে ঢুকে প্রোটোপ্লাজম নিউক্লিয়াস ক্রোমোসোম জিন ডিএনএ আরএনএ না খুঁজত, না জানত, আজ আমরা সেই ঊনবিংশ শতাব্দের জীববিজ্ঞানের এলাকাতেই পড়ে থাকতাম। ডারউইনের তত্ত্ব ডারউইনের বইতেই সীমিত হয়ে থাকত। টুকরো টুকরো করে জানবার প্রচেষ্টাতেই আমাদের জ্ঞানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই নৈপুণ্যায়ন মানে অবশ্যই খণ্ডিত জ্ঞান; আংশিক জ্ঞান। তাই বলে তা কিন্তু আবশ্যিকভাবে খণ্ডতাবাদের জন্ম দেয় না। সতর্ক থাকলে দেয় না; অসতর্ক থাকলে দিতেও পারে। অনেক সময় দিয়েও থাকে। কীভাবে, সে কথায় একটু পরেই আসছি।
হ্যাঁ, বিজ্ঞানেও জুড়বার কাজ করতে হয়। বেশ অনেক টুকরো জ্ঞান সঞ্চয়ের পর সেগুলোকে জুড়ে জুড়ে একটা বড় সমগ্রের ধারণা পেতে হয়। গ্যালিলেও আর কেপলারের কাজগুলিকে যেমন নিউটন জুড়ে দিয়ে তাঁর বলবিদ্যার কাঠামোটি গড়ে তুলেছিলেন। তা দিয়ে অনেক কিছু বোঝা গিয়েছিল, অনেক প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়েছিল। তার সাহায্যে অনেক নতুন জিনিস আবিষ্কার হয়েছে। যথা, আকাশে টেলিস্কোপের সাহায্যে ইউরেনাস নেপচুন আর প্লুটোকে খুঁজে পাওয়া গেছে। ধূমকেতুর আগমনের হিসাব করা সম্ভব হয়েছে। আবার, তা সত্ত্বেও নিউটনের বলবিদ্যা এক খণ্ড বিদ্যা। বস্তু ও শক্তির এক অত্যন্ত সীমিত অংশেরই জ্ঞান। শুধুমাত্র যান্ত্রিক শক্তির এবং রৈখিক স্থান পরিবর্তনের অধিপাঠ। ম্যাক্সওয়েলের হাত ধরে তড়িচ্চুম্বক তরঙ্গ গতিতত্ত্ব, তারপর তাপগতিবিদ্যা, আপেক্ষিকতাবাদ, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা, ইত্যাদি এসে একে একে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল―বস্তুজগতের আরও কত দেশ মহাদেশ অনাবিষ্কৃত হয়ে এতকাল পড়েছিল। তারও সবই তো শেষ বিচারে খণ্ডবিদ্যাই। অংশেরই তো জ্ঞান। কিন্তু বর্ধিত জ্ঞান। কেউ যদি পণ করে বসতেন, আমরা অংশকে আর জানব না, জানতে হলে একবারে সবটুকুর জ্ঞান পাকড়ে নেব―তাঁর আর কিছুই জানা হত না। আগের অংশেই পড়ে থাকতে হত।
বিজ্ঞানেও জুড়বার প্রয়াস অব্যাহত বলেই তো পদার্থবিজ্ঞানীরা মাঝে মাঝেই এক একটা মহাতত্ত্বের সন্ধান করে ফেরেন। এই যেমন আইনস্টাইন―জীবনের একটা বড় অংশ ব্যয় করে গেলেন কোনো এক সন্নিবিষ্ট ক্ষেত্রের তত্ত্ব তালাশে―unified field theory-র নির্মাণে। সেই প্রচেষ্টা সফল না হলেও অন্যেরাও খণ্ডে খুশি নন, কোয়ান্টাম তত্ত্ব আর আপেক্ষিকতাবাদের যূথবদ্ধ তত্ত্ব নির্মাণের মধ্য দিয়ে “খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশপাথর”―যার পোশাকি নাম “Theory of everything”। কিন্তু হায়! কী যে কপাল তাঁদের! কিছু দিনের মধ্যেই সেই পরশপাথর আর একা রইল না, বহুবচনে আত্মপরিচয়ের আভাস দিতে লাগল: “Theories of everything”!
রসায়নশাস্ত্রের জন্য এই রকম একটি মহাতত্ত্বের খোঁজেই ঊনবিংশ শতাব্দে রাশিয়ান বিজ্ঞানী দ্মিত্রি মেন্ডেলিয়েভ মৌলিক পদার্থগুলিকে এক পর্যায়সারণিভুক্ত করে তাদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের মধ্যে এক সাধারণ ক্রমোত্তরণের প্রবণতা খুঁজে পাওয়ার পরিকাঠামো নির্মাণ করে ফেলেন (১৮৬৯)। তিনি সেদিন মৌলগুলির পারমাণবিক ভর ধরে সারণিটি সাজিয়েছিলেন, তাঁর সময়ে বহু মৌল তখন অবধি আবিষ্কৃত হয়নি বলে সারণির অনেক জায়গা ফাঁকা রাখতে হয়েছিল। আধুনিক কালে সেই সারণি তৈরি হয়েছে পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক দিয়ে, তাছাড়া সমস্ত পার্থিব মৌল আবিষ্কার হয়ে তো গেছেই, উপরন্তু বেশ কিছু (দুই ডজনেরও বেশি) কৃত্রিম মৌলও গবেষণাগারে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে আজকের পর্যায়সারণি মেন্ডেলিয়েভের সেদিনকার থেকে অনেকটাই আলাদা হয়ে গেছে। কিন্তু মূল ধারণাটা রয়ে গেছে। মৌলিক পদার্থগুলো যে আলাদা হয়েও সংসারে পৃথকান্ন হয়ে নেই সেই কথাটা বারে বারে মনে করিয়ে দেবার জন্য।
ঠিক সেই ভাবেই জীববিজ্ঞানের এলাকাতেও কার্ল লিনিয়াসের প্রস্তাবিত প্রাণের দুটি সাম্রাজ্য এখন পাঁচটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। স্থবিরবাবু “তিরিশটি” সাম্রাজ্যের খবর কোত্থেকে পেয়েছেন [দাশগুপ্ত ২০০৯, ৫৩], আমার জানা নেই। গুগ্লি জেলায় ক্লিকবাজি করেও তেমন কোনো খবর পেলাম না। তবে বাস্তবে কেউ কেউ ইদানিং জীব জগতের ছয়টি সাম্রাজ্যের কথা বলেন [Cavalier-Smith 2004], আবার অনেকেই অন্যভাবে আরও বড় গ্রুপে আদিম জীবদের সাজিয়ে দিয়ে বলছেন, তিনটি মহাসাম্রাজ্য (domain)-ই যথেষ্ট। [Woese et al 1990] আগামী দিনে এই বিতর্ক চলতেই থাকবে। যদি সত্যিই কখনও তিরিশটি (বা আরও বেশি) হয়েও যায়, তখন তাদেরকেও আরও বৃহত্তর দু-তিনটি অধিসাম্রাজ্যে ভাগ করে ফেলার চেষ্টা শুরু হবে। ওই খণ্ডতাবাদী বিজ্ঞানীরাই করবেন। যাঁরা ভেঙে ভেঙে জানবার চেষ্টা করছেন, জানার পর তাঁরাই জুড়ে দেবেন। আর তাঁদের কাছে খবর পেয়েই স্থবিরবাবু আর একবার (মানে মাত্র একবার এটা আমি বলছি না) দাবি জানাবেন, দেখেছ, বলেছিলাম না, খণ্ডতাবাদীরা কিছুই জানে না? শুধু জানার ভাণ করে? এই যদি ওরা অখণ্ড এবং অখণ্ড্য ব্রহ্ম থেকে শুরুটা ধরে নিতে সাহস পেত, তাহলে একটাতেই কাজ চলে যেত। বারবার ভাঙাগড়া করতে বা পাল্টাতে হত না। আমরাও একমত, অখণ্ডতার কাজ অবশ্যই হত। তা নিয়ে আমাদের মনেও কোনো ধন্দ নেই। তবে একটা ছোট্ট অসুবিধা হত―জীবজগত সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যেত না।
ফলে স্থবিরবাবু যাকে জ্ঞানরাজ্যের আসামী হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন, সেই খণ্ডতাবাদী বিজ্ঞানীদের কাছেই তাঁর যাবতীয় ঋণ। অখণ্ডতাবাদের জন্যও। পথ সেই খণ্ডতাবাদীদের কাছেই জানতে হচ্ছে!
ডারউইনের তত্ত্ব: বিজ্ঞানের ঝুলিতে
জীবজগতের বিবর্তন সম্পর্কে ডারউইনীয় তত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপটিও আমাদের এবার মনে রাখা দরকার। এই তত্ত্বের প্রধান স্তম্ভ হল চারটি: অশৃঙ্খল প্রভেদন (random variation), অস্তিত্বের সংগ্রাম (struggle for existence), অভিযোজন (adaptation) ও প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural selection)।
অশৃঙ্খল প্রভেদন বলতে বোঝায় জীবজগতের নিরন্তর নানা রকম বৈচিত্র্যের প্রকাশ। এই বৈচিত্র্য বলতে দুরকম জিনিস বোঝানো হয়। একটা হল একই জিনপুল-এর মধ্যেই নানা প্রভেদ। ব্যক্তিক প্রভেদ (ontogenetic variation)। যেমন, সাদা বেড়াল আর কালো বেড়াল। আর একটা হল জিনের পরিব্যক্তির ফলে প্রভেদ। আন্তঃপ্রজাতিক প্রভেদ (phyllogenetic variation)। সমগ্র জিনপুলেরই পরিবর্তন। নতুন প্রজাতি গঠনের দিকে, বা প্রজাতি রূপান্তরের দিকে পদক্ষেপ। বেড়াল আর ভাম; সোরেল আর বনবেড়াল; বাঘ আর চিতা; নেকড়ে শেয়াল আর কুকুর; ইত্যাদি। ডারউইন তাঁর সময়ে এই দুটি বৈচিত্র্যায়নের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই তফাত করতে পারেননি। কিন্তু বর্তমানে জিনবিদ্যার আলোকে এই দুই পরিঘটনার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা সম্ভব। বিবর্তনের তত্ত্বটা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের আকারে দাঁড়িয়েছিল বলেই এই সংশোধন সম্ভব হয়েছে। অতএব, ডাঃ দাশগুপ্ত যখন প্রশ্ন তোলেন, ডারউইন কেন শিম্পাঞ্জি ও মানুষের দুই শতাংশ জিন-পার্থক্যকে ব্যাখ্যা করতে পারেননি, আমরা কিঞ্চিত অবাকই হই―ঠিক পড়লাম তো? ১৮৭১ সালে যখন ডারউইন তাঁর মানুষের বিবর্তন সম্পর্কিত “মানুষের অবতরণ” বইটি বের করছেন, তখন কি এসব জানা ছিল? জিনতত্ত্বের তখন তো জন্মই হয়নি। নাকি, সাল তারিখ মিলিয়েই যদি চর্চা করব, বুঝব, তাহলে আর ডারউইনকে ভুল প্রমাণ করা যাবে কী করে―এই রকম একটা কট্টর মনোভাব থেকেই ডাঃ দাশগুপ্ত তাঁর যাবতীয় সমালোচনার ঘুঁটি সাজিয়ে ফেলেছেন?
দ্বিতীয়ত, অস্তিত্বের সংগ্রাম। এখানেই ডারউইন আর ওয়ালেসকে ম্যালথাসের কাছে হাত পাততে হয়েছিল। একটা ক্লু পাওয়ার জন্য। নিম্নস্তরের এক একটা জীব এক একবারে যে বিপুল পরিমাণ শাবকের জন্ম দেয় তা সত্ত্বেও সেই প্রজাতির জীবদের মোট সংখ্যা একটা নির্দিষ্ট এলাকায় কম বেশি স্থির থেকে যায় কী করে? এর উত্তর তাঁদের সমকালের জীববিজ্ঞানের বিদ্যার সীমানায় জানা ছিল না। সেই অবস্থায় তাঁদের চোখে পড়ে ম্যালথাসের কাজ। ম্যালথাস মানব সমাজের ক্ষেত্রেই তাঁর জনসংখ্যা সংক্রান্ত তত্ত্বটি প্রস্তাব করেছিলেন। তাতে তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন, খাদ্য সম্ভার যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার দ্বারা আরও বেশি দ্রুত হারে ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টিকে পুষ্টি যোগানো সম্ভব হবে না। ফলে পৃথিবীর খাদ্য সম্ভারের সীমাবদ্ধতাই জনসংখ্যাকে একটা সীমার মধ্যে বেঁধে রাখবে যদি রাষ্ট্রের তরফে কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা না হয়। ১৭৯৮ সালে প্রথম প্রস্তাবিত তাঁর এই তত্ত্বটি যে গাণিতিকভাবে ভুল ছিল, ১৮৩৮ সালের একটি বিজ্ঞান পত্রে বেলজিয়ান গণিতবিদ পিয়র ফ্রাঁসোয়া ফেরহালস্ট সেটি প্রমাণ করে একটি বিকল্প গাণিতিক মডেল তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু সেই পত্রটিও মেন্ডেলের বংশগতি সূত্রের পত্রের মতোই সমকালীন বিজ্ঞানীদের, এবং সেই সুবাদে ডারউইনেরও, চোখের আড়ালে থেকে যায়। ১৯২০ সালের আগে সেটি বৃহত্তর দুনিয়া জানতেই পারেনি। [Verhulst 1838; ফেরহালস্টের পত্র এবং তার উদ্ধার সংক্রান্ত বিশদ তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য: Mukhopadhyay 2003]
না, ভুল বললাম, এখনও বেশির ভাগ আম জনতাই শুধু নয়, বিশিষ্ট লেখক গবেষকরাও অনেকে জানেন না যে ম্যালথুসীয় জনসংখ্যা তত্ত্ব বহু দিন আগেই অচল সাব্যস্ত হয়ে গেছে। না হলে, ‘আমেরিকান সায়েন্টিস্ট’-এর মতো একটা বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকায় কীভাবে লেখা হয়―“The fact remains that Malthus, for all his shortcomings as a social theorist, formulated a principle of population growth that no one has been able to falsify and that forms a foundation stone of the theory of evolution by natural selection” [Thomson 1998]―এর ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে না।
সে যাক গে। আমাদের আপাতত দ্রষ্টব্য ম্যালথাসের সূত্র থেকে দুজনেই কীভাবে লাভবান হয়েছিলেন সে সম্পর্কে এই দুজন প্রকৃতিবিদের স্বতন্ত্রভাবে লেখার মধ্যেও কী আশ্চর্য মিল! ডারউইন তাঁর আত্মজীবনীতে লেখেন, তিনি নিছকই কৌতুহলের বশে ম্যালথাসের জনসংখ্যা বিষয়ক প্রবন্ধটি পড়তে শুরু করেছিলেন; কিন্তু পড়তে পড়তে একটা কথা হঠাৎ তাঁর মনে হয়, মানব সমাজের ক্ষেত্রে জীবন সংগ্রাম হিসাবে যে চিত্র ম্যালথাস তুলে ধরেছেন সেটা আসলে হয়ত সমগ্র জীব জগতেরই এক সাধারণ সমস্যা। সীমিত খাদ্যদ্রব্যের জন্য প্রতিযোগিতায় নামতে হয় বলেই যাদের কোনো না কোনো দিক থেকে সামর্থ্য বেশি তারাই অধিকতর খাদ্য সংগ্রহ করে এবং ভালোভাবে আত্মরক্ষা করে বহু দিন বেঁচে থাকে ও বেশি বেশি করে বংশ বিস্তার করতে পারে। “In October 1838, that is, fifteen months after I had begun my systematic inquiry, I happened to read for amusement Malthus on Population, and being well prepared to appreciate the struggle for existence which everywhere goes on from long-continued observation of the habits of animals and plants, it at once struck me that under these circumstances favourable variations would tend to be preserved, and unfavourable ones to be destroyed. The results of this would be the formation of a new species. Here, then I had at last got a theory by which to work; . . . .” [Barlow (ed.) 1993, 120]
আর ওয়ালেসও তাঁর আত্মজীবনীমূলক বইতে মন্তব্য করেন, মালয় দ্বীপপুঞ্জে থাকা কালীন একবার যখন তাঁর জ্বর হয় এবং তিনি কয়েক দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে বাধ্য হন, সেই অবস্থায় ম্যালথাসের রচনাটি এক দিন হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। “It occurred to me to ask the question, Why do some live and some die? And the answer was clearly that on the whole the best fitted lived. From the effects of disease the most healthy escaped; from enemies the strongest, the swiftest, or the most cunning; from famine the best hunters or those with the best digestion; and so on. . . . There suddenly flashed upon me the idea of the survival of the fittest.” [Cited, Bronowsky 1989, 192]
সুতরাং ডারউইন এবং ওয়ালেস ম্যালথাসের সূত্র থেকেই সমাধান খোঁজেন এবং ভুল জায়গা থেকে হলেও তাঁরা তাঁদের সংগৃহীত তথ্যগুলিকে সামলানোর মতো একটা চটজলদি সমাধান সূত্র পেয়েও যান। (মানব সমাজের ক্ষেত্রে ম্যালথাসের বক্তব্য সাধারণ অর্থে ভ্রান্ত সাব্যস্ত হলেও জীবজগতের ক্ষেত্রে উপরে আহৃত সমাধান সূত্রটি কিন্তু ভুল নয়।) সেটি এই: প্রতিটি প্রজাতি যতই শাবক প্রজনন করুক, তার জন্য একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ এলাকায় নির্দিষ্ট সুরক্ষার আয়োজনের মধ্যেই তাদের বাঁচার জন্য চেষ্টা করতে হয়। ফলে খাদ্য সংগ্রহ এবং আত্মরক্ষার জন্য তাদের মধ্যে এক প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। এই প্রতিযোগিতায় এক একটা প্রজাতির কিছু বৈচিত্র্য তাদেরকে সুবিধা দেয়, আবার অন্য কিছু বৈচিত্র্য তাদের পক্ষে অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। স্বভাবতই, যারা সুবিধাজনক বৈচিত্র্য নিয়ে জন্মেছে তারা সেই সীমিত ক্ষেত্রে কিছু বাড়তি সুবিধা পাওয়ার কারণে বেশি দিন বাঁচবে, বেশি করে বংশ বৃদ্ধি করবে, এবং ক্রমে ক্রমে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এইবার তারা যদি (১) একটা স্থায়ী জীবগোষ্ঠী হিসাবে গড়ে উঠতে পারে, (২) নিজেদের মধ্যে বংশ বিস্তার এবং অন্য কাছাকাছি গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রজননগতভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তারা একটা নতুন প্রজাতি হিসাবে উদ্ভূত হবে। (৩) যদি এদের খাদ্য ও আত্মরক্ষার প্রশ্নে কাছাকাছি কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে সাঙ্ঘর্ষিক সম্পর্ক দেখা দেয়, তাহলে সেই দুটো গোষ্ঠীর মধ্যে কে টিকবে কে বিলুপ্ত হবে―এরকম একটা সমস্যা দেখা দিতে থাকে। তা না হলে তারা পাশাপাশিই বিকাশ লাভ করতে থাকে। এই শেষোক্ত প্রক্রিয়াতেই পৃথিবীতে জীববৈচিত্র্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।
একটা নতুন জীবগোষ্ঠী এইভাবে যখন তার পরিবেশে একটা সুস্থিত প্রজাতি-বৈচিত্র্য হিসাবে কোনো একটা অঙ্গস্থানের বা আচরণের কম বা বেশি পরিবর্তিত রূপ অর্জন করে তার দ্বারা অন্যদের তুলনায় কিছুটা বাড়তি সুবিধা পেয়ে কিছু কালের জন্য অন্তত টিকে যায় এবং জীবজগতে তার জায়গা করে নেয়, এই পরিঘটনাকেই বলা হয় অভিযোজন। উপরে বর্ণিত অস্তিত্বের সংগ্রামের এটা একটা আবশ্যিক পরিণাম বলা যেতে পারে।
সব শেষে প্রাকৃতিক নির্বাচন। এই শব্দ-যুগ্ম নিয়ে সেই ১৮৫৯ সাল থেকেই জল ঘোলা হচ্ছে। কেন না, শব্দটার পারিভাষিক অর্থ বোঝার চাইতে নিজেদের (ভুল) বোঝার বোঝা চাপিয়ে দিতেই বেশিরভাগ ভাষ্যকার বেশি আগ্রহী। যেন প্রকৃতি খুব সচেতনভাবে বেছে বেছে একে তুলে নিচ্ছে আর ওকে ফেলে দিচ্ছে, ইত্যাদি। যেন ঈশ্বরেরই আর একটা নতুন প্রতিশব্দ। এই সমস্ত ভুল ব্যাখ্যাগুলিকেই ডারউইনীয় ব্যাখ্যা ধরে নিয়ে শব্দ-জোড়াকে যতটা পারা যায় কাটাছেঁড়া করে নেওয়া তাদের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুঃখের কথা হল, ডাঃ স্থবির দাশগুপ্তও এই দলে ভিড়ে গিয়েছেন। তার ফলেই তিনি কখনও ছক, কখনও সরল রেখা, কখনও ঋণাত্মক ভূমিকা, ইত্যাকার সব অভিযোগ উজাড় করে দিয়েছেন।
প্রথমেই বলি, প্রকৃতি কোনো পছন্দসই নির্বাচন, কাউকে তুলে নেওয়া কাউকে বসিয়ে দেওয়া ইত্যাদি করে না। করা সম্ভব নয়। প্রকৃতি একটা অচেতন সত্তা। বিবর্তন একটা প্রাকৃতিক পরিঘটনা, ঝড় বৃষ্টি ভূমিকম্প বন্যা খরা তুষারপাত নদীস্রোত আদি প্রকৃতির আর পাঁচটা খেয়ালের মতোই এটাও প্রকৃতিতে বিদ্যমান অজস্র পদার্থের যোগসাজশে আপনাআপনিই ঘটে চলেছে। অশৃঙ্খলভাবে। কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই।
দ্বিতীয়ত, সেই কারণেই এর মধ্যে কোনো রকম ছক সাজানো নেই। সরল রেখায় বিকাশ বা বিনাশও নেই। কিন্তু একটা বৃহৎ প্রেক্ষায় নিয়মবদ্ধ স্পষ্ট ছবি আছে। জীবজগতের অনেক কিছু ঘটনাকে বুঝিয়ে দেয়। বুঝতে সুবিধা হয়। অন্য কোনোভাবে যা একটা সাধারণ ব্যাখ্যার আওতায় আসে না। এই কারণেই এই তত্ত্বের এত জনপ্রিয়তা। আর ডারউইনের তত্ত্বে যোগ্যতমের উদ্বর্তন আদৌ তার মূল তত্ত্বের অঙ্গ নয়। প্রজাতির উদ্ভব বইয়ের প্রথম পাঁচটা সংস্করণে এটা ছিল না। ১৮৬০-এর দশকে স্পেন্সার প্রদত্ত সেই লব্জটা ক্রমাগত জনপ্রিয়তা অর্জন করায় ডারউইন যেমন তাঁর বিখ্যাত বইতে, মার্ক্সও তেমনি তাঁর যুগান্তকারী (‘পুঁজি’ শীর্ষক) বইতে এটিকে ঢুকিয়ে দেন। কেন না, এই শব্দগুচ্ছ এখন যে বদনাম কুড়িয়েছে সামাজিক-ডারউইনবাদের কেচ্ছার ফলে, তখন তা ছিল না।
তৃতীয়ত, তাছাড়া ডারউইনের তত্ত্বে সব সময় যোগ্যতমই জয়লাভ করে না। স্থলভূমিতে যেখানে শক্তপোক্ত ডানাওয়ালা পতঙ্গ বা পাখি জয়লাভ করে, সমুদ্রের ধারে সেখানে তারা ধীরে ধীরে পরাস্ত হয়, দুর্বল ডানাওয়ালারাই নির্বাচিত হয়ে বসে। ফলে তাঁর তত্ত্বে ইংরেজি fit শব্দটা যোগ্য অর্থে (manage করার অর্থে) নয়, মিলে যাওয়ার (match করার) অর্থে ব্যবহৃত হয়। যার বা যাদের বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত পরিবেশের সঙ্গে মিলে যায় সে বা তারাই টিকে যেতে পারে। এই বিষয়টা বলে দেবার পরে যতটা সরল বলে মনে হয়, বলে দেবার আগে তা ছিল না। যে কথাটা হাক্সলি একবার একটা সভায় মুখ ফুটে বলেই ফেলেছিলেন। ততখানি সরল হলে লামার্কেরও এটা বলতে পারার কথা ছিল। বা আরও অনেকের।
এইভাবে ডারউইনের তত্ত্বকে বুঝতে পারলে দেখা যাবে, এর মধ্যে অবৈজ্ঞানিক বা অযৌক্তিক কোনো কথা নেই। যদিও তাতে অনেক ফাঁক ফোকর আছে। শুধু পুরনো উপস্থাপনাতেই নয়, আধুনিক ব্যাখ্যার মধ্যেও অনেক জায়গায়ই সব কিছু পরিষ্কার নয়। আবার দুটো জিনিস পরিষ্কার হচ্ছে তো তিনটে নতুন প্রশ্ন তৈরি হয়ে যাচ্ছে। তবে, তাতে দুশ্চিন্তার কিছু নেই, এমনটা সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। আজ পর্যন্ত নিশ্ছিদ্র নিখাদ কোনো তত্ত্ব বিজ্ঞানে এসেছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। ডারউইন নিজেও এসম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁর সময়েই এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে যে সমস্ত আপত্তি উঠেছিল তিনি তার মধ্যে অনেকগুলোর উত্তর দিয়ে যেতে পারলেও অন্তত দুটো প্রশ্নের ক্ষেত্রে কিছুই বলতে পারেননি। প্রশ্ন দুটোকে তিনি তাই বলে এড়িয়ে যাননি। নিজে থেকে নিজের লেখায় এদের উল্লেখ করেই বলেছিলেন: এই আপত্তি দুটির জবাব আমি জানি না। অন্য সমস্ত তথ্যের সমর্থনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা সিদ্ধান্তকে এদের জন্য বাতিলও করতে পারছি না, আবার সিদ্ধান্তটিকে চূড়ান্তভাবে সিদ্ধ বলেও মনে করতে পারছি না। ভাবীকালের হাতে আমি এই তত্ত্বের ভবিষ্যত ছেড়ে দিচ্ছি। যদি আপত্তিদুটির নিষ্পত্তি হয়, তত্ত্বটি টিকবে; আর যদি না হয়, টিকবে না। কতটা বিজ্ঞানমনস্কতার অধিকারী হতে পারলে তবে এভাবে বলা যায় এটা আজকের পাঠকদেরও ভেবে দেখা দরকার। আর সকলের জ্ঞাতার্থে বলে রাখি: দুটি আপত্তিই বিজ্ঞানের পরবর্তী বিকাশের ধারায় তাঁর মৃত্যুর পঁচিশ বছরের মধ্যেই খারিজ হয়ে যায়। [এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Mukhopadhyay 2012, 46-48] এই সব তথ্য জানা না থাকলে মনে হতে পারে, ডারউইনের তত্ত্বকে বুঝি কোনো অস্তিত্বের সংগ্রাম করতে হয়নি। স্রেফ ভাগ্যের জোরে বিনা বাধায় সরল রেখায় এক ছকে বাঁধা পথেই এগিয়ে গেছে। একেবারেই তা নয়। একটার পর একটা বৈজ্ঞানিক আপত্তির উত্তর দিয়ে তবেই তাকে বিজ্ঞানের দরবারে পাকাপাকিভাবে জায়গা করে নিতে হয়েছে।
প্রসঙ্গত, এখানে আর একটা কথা বলে রাখা দরকার। এই জাতীয় সমস্যা মোকাবিলার কাজ ওয়ালেসকে সম্ভবত কখনও করতে হয়নি, বা, তিনি করেননি। অন্তত করেছেন বলে আমাদের কাছে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। আর তিনি মানুষের ক্ষেত্রে নিজের প্রস্তাবিত বিবর্তন তত্ত্ব প্রয়োগ করার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।
তবে সে আর এক গল্প। তার সাতকাহন ফেঁদে আমরা স্বনামধন্য ডাক্তারবাবুকে আর বিব্রত করতে চাই না।
ডারউইনের তত্ত্ব ও জ্ঞানের বিশ্ব
এবার আমাদের অন্য একটা প্রশ্নে ঢুকতে হবে। ডারউইনের বিবর্তনবাদের প্রস্তাবনা ও বিকাশের ফলে মানব চিন্তার দুনিয়ায় কোনো ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে কিনা। ডাঃ দাশগুপ্তের এই অভিযোগ কি সত্য, এর ফলে মানুষের মননশীলতার কোনো সমৃদ্ধি হয়নি?
না, সত্য নয়। প্রথমত, একটা জিনিস লক্ষ করলেই ধরা পড়বে, ডারউইনের দুটো প্রধান গ্রন্থ বেরনোর পর মানুষের জ্ঞানজগতের সমস্ত—হ্যাঁ, একেবারে আক্ষরিক অর্থে সমস্ত―জায়গায় এই বিবর্তনবাদী দৃক্পাতের একটা স্থায়ী ছাপ পড়ে গেল। সাহিত্য সংস্কৃতি ধর্ম দর্শন সঙ্গীত স্থাপত্য চিত্রশিল্প মূর্তিবিদ্যা আইন সমাজতত্ত্ব বিবাহ পরিবার রাষ্ট্র ইত্যাদি মানব সংস্কৃতির সমস্ত কানাচেই বিবর্তনের, ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের একটা বিশ্লেষণমুখী প্রয়াস শুরু হল। ফরাসি নৃতত্ত্ববিদ মার্ক ব্লশ ১৯৮৩ সালে প্রথম এই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। [Bloch 2004, 5] আমি নিজেও এক সময় ডারউইনের “প্রজাতির উদ্ভব” গ্রন্থ প্রকাশের পরবর্তী ১৮৬০-১৯১০ এই পঞ্চাশ বছর সময়কালের একটা নির্বাচিত গ্রন্থতালিকা তৈরি করেছিলাম, যার মধ্যে ডারউইন-প্রভাবের শীলমোহর অতি স্পষ্ট। [Mukhopadhyay 2012, 102-03] এ সম্পর্কে বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানীই খুব সুন্দর ভাবে আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রেখে গেছেন। তাঁদের মধ্য থেকে স্বল্প কয়েকজনের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে বোধ করছি।
প্রথম ল্যুড্হ্বিগ বোলৎস্মান। ১৮৮৬ সালে ঊনবিংশ শতকের এই মহান পদার্থবিজ্ঞানী এক লোকপ্রিয় ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন, “আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আগামী প্রজন্ম আমাদের এই শতাব্দকে ডারউইন শতাব্দ বলেই চিহ্নিত করবে।” আর পরের শতকে জীববিজ্ঞানী জুলিয়ান হাক্সলি লেখেন, “ডারউইন জীব জগতের জন্য যে জানালা খুলে দিয়েছিলেন, তা অন্য বিষয়গুলোকেও এক নতুন বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবার সুযোগ করে দিয়েছে।” কীভাবে? “Men began studying the evolution of nebulae and stars, of languages and tools, of chemical elements, of social organizations. Eventually they were driven to view the universe at large sub specie evolutionis, and so to generalize the evolutionary concept in fullest measure. This extension of Darwin’s central idea—of evolution by natural means―is giving us a new vision of the cosmos and of our human destiny.” [Huxley 1960, 18] প্রায় পঞ্চাশ বছর বাদে একেবারে হুবহু এই কথাগুলোরই যেন পুনরুক্তি করে অতি সাম্প্রতিক কালের দুই লেখক দেখেছেন যে “মহাবিশ্বতত্ত্ব থেকে শুরু করে জীববিজ্ঞান, এমনকি সমাজ বিজ্ঞানের কিছু কিছু অংশও এখন বিবর্তনবাদী চিন্তাধারার উপর নির্ভর করছে” এবং “বিবর্তন তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটা বেশ সমৃদ্ধশালী নির্দেশতন্ত্র হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে।” [Lurquin and Stone 2007, preface] অর্থাৎ, প্রথম প্রকাশের একশ বছর বাদেও যেমন ডারউইনের চিন্তাধারা জীবন্ত ছিল, দেড়শ বছর পরেও তাই।
সবার শেষে স্মরণ করব আর এক বড় মাপের পদার্থবিজ্ঞানী, লুই দ্য ব্রয়ের যোগ্য কৃতী ছাত্র জাঁ পল ভিজিয়র কথা, যিনি লক্ষ করেছেন যে, “জীববিজ্ঞান ও মানববিদ্যা থেকে শুরু করে বিবর্তনের ধারণা ধাপে ধাপে বিজ্ঞান জগতের প্রায় সমস্তটাই দখল করে নিয়েছে; জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে শুরু করে এখন সে রসায়নশাস্ত্র ও পদার্থবিজ্ঞানের রাজ্যেও ঢুকে পড়েছে।” তাঁর মতে: “This idea of history, of evolution, of analysis in terms of development is for us precisely the profound logical root of the dialectics of nature. It can even be said that in a sense all scientific progress is being achieved along the line of abandoning static descriptions for the sake of dynamic analyses combining the intrinsic properties of the analyzed phenomena. For us, science progresses from Cuvier to Darwin, from the static to the dynamic, from formal logic to dialectical logic.” [Cited by Novack 1964]
আশা করব, তিন শতাব্দের বিশেষজ্ঞদের এই মতামতগুলি স্থবিরবাবুর সংশয় কিয়দংশে হলেও দূর করতে সক্ষম হবে। এটা দেখাতে সক্ষম হবে যে জীববিজ্ঞানের নিতান্তই একটা খণ্ডিত জ্ঞানের ঠিকানা থেকে ডারউইনের চিন্তাধারা কীভাবে এক সমগ্রতাবাদী দার্শনিক দৃকপাতের জন্ম দিতে পেরেছিল।
এবার উলটো দিক থেকে আর একটা কথাও বিচার করতে হবে। আমাদের কাছে ডারউইন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? শুধুই কি নিরীশ্বরবাদিতার জন্য?
না। বিজ্ঞান মানেই তা নিরীশ্বরবাদী। বিজ্ঞানের কোনো জায়গাতেই ভগবান বেচারার জন্য একটুও শূন্যস্থান নেই। অনেক বিজ্ঞানীর মনেই হয়ত ধর্মচিন্তা ঈশ্বর বিশ্বাস আছে। তাঁদের অনেকেই লোকপ্রিয় লেখায় বা বক্তৃতায় বিজ্ঞানের সঙ্গে ভগবানের মিলনের কথা বলে থাকেন। বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে। আবেগের সাথে। তাতে কী হল? যখন বিজ্ঞানের নিজস্ব অধিপাঠ তৈরি করতে হয় তাঁদের, সংশ্লিষ্ট সূত্র নিয়ম সমীকরণ উপপাদ্য ইত্যাদি লিখতে হয়, কোনো জায়গাই খুঁজে পান না তাঁরা ভদ্রলোককে বসানোর মতো। অন্তত আজ অবধি কেউ পাননি। সুতরাং ডারউইনের এখানে বিরাট কোনো বিশেষত্ব নেই। হ্যাঁ, তিনি একজন ঘোষিত সংশয়বাদী। নিজের আত্মজীবনীতে এই ব্যাপারে একটা অধ্যায় যোগ করে খুব স্পষ্ট বক্তব্য রেখে গেছেন। এটা আমাদের যুক্তিবাদী বিজ্ঞান অনুরাগী মানুষদের খুবই কাজে লাগে। সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে সুবিধা হয়।
এর চেয়েও আমাদের কাছে অনেক বড় কথা হল, ডারউইন নিজে কীভাবে এই নিরীশ্বরবাদে পৌঁছলেন। বিগ্ল জাহাজে চড়বার সময় তিনি ছিলেন একজন স্থিরচিত্ত নিষ্ঠাবান খ্রিস্টান। ঘোরতর ঈশ্বরবিশ্বাসী। জগত সংসারে শ্রীযুত ভগবানের পরিকল্পিত মঙ্গলময়তায় আস্থাবান। আর সেই তিনি কিনা পাঁচ বছর বাদে যখন ফিরে এলেন টেম্স নদীর পারে, ঈশ্বরকে তিনি কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে যে সমস্ত প্রশ্ন করছেন, তাতে সেই বেচারির পালাই-পালাই অবস্থা! বিজ্ঞানের আর কোনো তত্ত্বই তাঁকে এতটা দুর্দশায় ফেলতে পারেনি। বিবর্তন তত্ত্বের চাইতেও ডারউইনের এই মানস-বিবর্তন বিশ্বের বিজ্ঞান অনুরাগী মানুষজনের কাছে একটা বড় আকর্ষণ।
ঈশ্বরতত্ত্বের সপক্ষে একটা খুব বড় যুক্তি ছিল দৈবী নকশার উপস্থাপন। এক ঐশী স্থপতি হিসাবে ভগবানের চিত্রণ। মাছের পাখনা, পাখির ডানা, স্থলচরের পা—যার যা দরকার সে তাই পেয়েছে। কেউ পরিকল্পনা করে নকশা করে এসব বানিয়ে দেবার ব্যবস্থা না করলে এরা পেল কীভাবে? নিজে নিজে তো আর নিশ্চয়ই যোগাড় করতে পারেনি। ডারউইন ঠিক এই যুক্তির গায়েই একটা মোক্ষম আঘাত দিলেন। অশৃঙ্খল প্রভেদনের কথা বলে তিনি দেখালেন, ঈশ্বরকে দুনিয়ার স্রষ্টা বলে মানতে হলে বলতেই হবে, স্রষ্টা হিসাবে তিনি কিছুই কখনও দরকার মাফিক বানাতে পারেন না। তিনি বানান যেমন তেমন করে। তার অনেকগুলিতেই বহু ত্রুটি থাকে। এতে তাঁর অক্ষমতারই প্রকাশ ঘটে। তার চাইতে বিষয়টাকে প্রকৃতির হাতেই ছেড়ে দেওয়া ভালো। আসলে প্রাকৃতিক নিয়মেই জীবের মধ্যে নানা রকম প্রভেদ দেখা যায়। তার মধ্যে অনেক নকশাই সচরাচর পরিবেশের সাথে খাপ খায় না। কিন্তু সব সময়েই কিছু না কিছু খাপে খাপে মেলে। সেগুলোই টেকে এবং কিছু কালের জন্য স্থায়ী হয়। তাই শেষ পর্যন্ত যারা টিকে যায় তাদের জন্য ঈশ্বরকে কৃতিত্ব দিতে হলে তার চেয়ে অনেক বেশি যেগুলো টেকে না, তার দায় কে নেবে?
আর হ্যাঁ। এই অশৃঙ্খলার ধারণাটিকে বিজ্ঞানের ক্যানভাসে নিয়ে আসার প্রথম কৃতিত্বও ডারউইনের। প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে প্রকৃতির নিজস্ব খেয়ালে, নিজস্ব ধারায়; কারোর ইচ্ছা অনিচ্ছায় নয়, কারোর নির্দেশে বা পরিকল্পনায় নয়; কোনো পূর্ব স্থিরীকৃত নিয়মেও নয়। এই ধারণাটা বিজ্ঞানের দরবারে আসার ফলেই সম্ভাব্যতার নিয়ম বৈজ্ঞানিক নিয়মের জাতে ওঠার ছাড়পত্র পেল। গ্রেগর মেন্ডেল বংশগতির নিয়মে সেই তত্ত্বকেই প্রয়োগ করলেন গাণিতিক ছাঁদে। কিছুদিনের মধ্যেই পদার্থবিজ্ঞানেও সে ঢুকে পড়ল প্রথমে ম্যাক্সওয়েল পরে বোলৎস্মানের হাত ধরে। আর পাঁচ দশক বাদে সেই সম্ভাব্যতার তত্ত্বই হয়ে উঠল কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের মৌল গাণিতিক স্তম্ভস্বরূপ।
সব শেষে একটা সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক মানসের দৃষ্টান্ত হিসাবেও ডারউইন আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ডারউইন যখন দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সংগৃহীত উদ্ভিদ ও প্রাণীর নমুনাগুলি বাক্সবন্দি করে লন্ডনে পাঠাচ্ছিলেন, তখনই তাঁর বৈজ্ঞানিক বন্ধুমহলে সাড়া পড়ে যায়। দেশে ফিরে আসার পর তিনি ভ্রমণ প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ বিষয়ে যে দু একটি প্রবন্ধ লেখেন তাতে তাঁর খ্যাতি আরও বাড়তে থাকে। তাঁর সাথে মাঝে মধ্যে ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনা করেও তাঁরা বুঝতে পারেন, একটা দারুণ বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক মতবাদের অঙ্কুরোদ্গম হতে চলেছে। অথচ, আশ্চর্যের কথা, ডারউইন তাঁর বক্তব্য বাইরে প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক। তিনি নিশ্চিত হতে চান, আরও গভীরভাবে নিশ্চিত হতে চান। সেই জন্য আরও অপেক্ষা করে আরও তথ্য সংগ্রহ করে দেখতে চান, কোথাও তাঁর ভুল হয়ে যাচ্ছে কিনা! ভাবা যায়, যে বৃহৎ তত্ত্বের জন্য তিনি পরবর্তী দুই শতক ধরে টানা প্রশস্তি পেতে থাকবেন (কিছু ব্যতিক্রম সহ), তা তৈরি হয়েও তাঁর টেবিলে পড়েছিল অন্তত কুড়ি বছর। ১৮৫৮ সালে ওয়ালেসের সেই চিঠিটা না এলে সেটা আরও কত বছর পরে প্রেসের দিকে যাত্রা করত, বলা মুশকিল। সত্যের প্রতি এই কঠোর দায়বদ্ধতাই বিজ্ঞানীদের মধ্যে তাঁকে অনন্য করে তুলেছে!
এই বিজ্ঞানমানস তাঁর মধ্যে আর একদিক থেকেও প্রায় ব্যতিক্রমী চরিত্র নিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছিল। সাধারণত অধিকাংশ মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হল, তাঁর মতের সপক্ষে যে তথ্য বা যুক্তি উঠে আসে তার প্রতি একটু বেশি মনোযোগ দেওয়া, আর বিরুদ্ধ তথ্য ও যুক্তির সম্পর্কে সচেতনভাবে না হলেও খানিকটা অগ্রাহ্য করার মনোভাব নিয়ে চলা। ডারউইন কখনই তাঁর তত্ত্বের বিপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি উত্থাপিত হয়েছে তাকে জ্ঞানত উপেক্ষা করেননি। নিজেই তিনি আত্মজীবনীতে বলেছেন, এরকম যুক্তি বা তথ্য পেলে ভুলে যাওয়ার আগেই আমি তাদের নথিভুক্ত করে রাখতাম। তারপর যেসব আপত্তির উত্তর দিতে পেরেছেন, দিয়েছেন; যার উত্তর খুঁজে পাননি, তাকেও উল্লেখ করেই বলে গেছেন, আমার এর সমাধান জানা নেই। এ একটা অত্যন্ত দুর্লভ মানসিকতা। এইগুলো বিজ্ঞান-সংস্কৃতিতে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।
এই বিস্তৃত আলোচনা থেকে আশা করা যায় এটা বোঝানো সম্ভব হয়েছে যে চার্লস্ ডারউইন শুধুমাত্র জীব বিবর্তনের তত্ত্বের জন্যই আমাদের কাছে বরণীয় নন। সেটা তো আছেই। তার সাথে বিজ্ঞানের দেশকাল-উত্তীর্ণ সংস্কৃতিতে তাঁর এই সব দুর্লভ গুণগুলিকে ধরে রাখা ও চর্চা করার প্রয়োজনেই তাঁকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে চাই। ডারউইনের চিন্তাধারার উপরে আঘাতের অর্থ বিজ্ঞানের মহান সৌধের একটা বড় জায়গায় ক্ষতি সাধনের অপচেষ্টা। সেই আক্রমণ কখনও মেনে নেওয়া যায় না।
বিজ্ঞানের কাজের পদ্ধতি
আজকের বিজ্ঞান সম্পর্কে স্থবিরবাবুর অনেক অভিযোগ। চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে অভিযোগ আরও বেশি। যে প্রবন্ধটির কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম এই আলাপন, তারও প্রধান উপজীব্যই ছিল বিজ্ঞানের অগ্রগতির সুযোগ নিয়ে কর্পোরেট চিকিৎসা ব্যবসার হালহকিকত। এই পর্যন্ত তাঁর সাথে আমাদের সম্পূর্ণ সাহমত্য। আমরা বস্তুত খুশি যে নিজে ব্যক্তিগত জীবনে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং সফল চিকিৎসক হয়েও আজকের দিনে তিনি এই নোংরা ব্যবসার বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে মুখ খুলছেন এবং সাধ্যমতো প্রতিবাদ করে যাচ্ছেন। সাধারণ মানুষ বেশিরভাগ সময়ই নিরুপায় হয়ে এই হীনবাণিজ্যসংস্থাগুলির বিরুদ্ধে কিছু করতে না পেরে মুখ বুজে সব কিছু মেনে নেয়। কিন্তু, আমাদের সাথে তাঁর বিরোধ হচ্ছে এই নরমেধ চিকিৎসা-বাণিজ্যের কারক এবং কারণ ঘটিত বিশ্লেষণের জায়গায় এসে।
ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি।
তিনি যখন সমাজের বাস্তব অবস্থার দিকে চোখ মেলে তাকান তখন পুঁজির কর্পোরেট সাম্রাজ্য তাঁর চোখে পড়ে যায়। সেই চক্র কীভাবে স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে বের করে নিজের মুঠোয় পুরে ফেলে তাও তিনি লক্ষ না করে পারেন না। অথচ, তারপরই তিনি এই সমস্ত ছিনিমিনি খেলার জন্য বিজ্ঞানকে দায়ী করেন, বিজ্ঞানের তথাকথিত খণ্ডতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে দায়ী করে বসেন, বিজ্ঞানীদের মধ্যে “ক্ষমতাবান” “শক্তিধর” [দাশগুপ্ত ২০০৯, ৪৭, ৫২] অংশ খুঁজে বেড়ান, ইত্যাদি। এই কর্পোরেট চক্র এবং ক্ষমতাবানদের চাপেই নাকি “বিবর্তনবাদকে মানতেই হয়” [দাশগুপ্ত ২০০৯, ৫২; “ই”-বর্ণটিকে আমি একটু এধার-ওধার করেছি]। অথচ যে জীবাশ্ম ভাণ্ডার আমাদের এই তত্ত্বের বড় উৎস তা হল “পাথরের গায়ে বিলুপ্ত প্রজাতির ছাপ, কিন্তু তা থেকে সেই প্রজাতির প্রাণের স্পন্দনের বা অন্তর্গত কর্মকাণ্ডের সন্ধান পাওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার।” [দাশগুপ্ত ২০০৯, ৫৩] মানুষের দুটি হাত কীভাবে শিম্পাঞ্জির তুলনায় এত শিল্প-কুশল হয়ে উঠল, “তা ডারউইনীয় বিবর্তনচর্চা আমাদের বুঝতে দেয় না।” [ঐ] “সে কেবল বিবর্তনবাদী নিয়ন্ত্রণবাদ দিয়ে একটি মৃত হাতের বর্ণনা দিতে পারে, তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে না। সে মানবকে গঠনগতভাবে বর্ণনা করতে পারে, কিন্তু মানবিকতার হদিশ দিতে পারে না।” [দাশগুপ্ত ২০০৯, ৫৪] জিনতত্ত্ব এবং জিনোম প্রকল্প দিয়ে “মানবমনের রহস্য সন্ধান” করা বা “পশু থেকে মানুষে উত্তরণের কারণ খুঁজে” পাওয়া যায় না, কেন না এই সবই সরলরৈখিক তত্ত্ব! [ঐ]
আর এই সব কোনো কিছুই যখন করা যাচ্ছে না, “এই তর্ক থেকে আমরা বোধ হয় এই ধারণায় উপনীত হতে পারি যে খণ্ডতাবাদী ধারণা নিয়ে জীব-বিবর্তনচর্চার সপক্ষে বিশেষ যুক্তি সাজানো মুশকিল।” [ঐ]
কোথা থেকে কোথায় এসে পৌঁছলাম! পড়ছিলাম জীববিজ্ঞান। জানতে চাইছিলাম, পৃথিবীতে এত জীবের উদ্ভব হল কী করে। জীববিজ্ঞানের কাছে মনোবিজ্ঞান শিখতে হবে, সাহিত্য সংস্কৃতির পাঠ নিতে হবে, শিল্প বা নৃত্যকলার কায়দাকানুন শিখতে হবে বলে তো কখনও ভাবিইনি। এও ভাবিনি যে এই সমস্ত ব্যাপারে সাহায্য করতে না পারলে জীববিজ্ঞান বা বিবর্তন তত্ত্ব পুরোপুরি ব্যর্থ। কিন্তু আমরা না ভাবলে কী হবে, এরকম ভাবার লোক সংসারে আছেই। তাঁরা আমাদেরও ভাবিয়ে ছাড়বেন বলে পণ করেছেন। জ্ঞানের রাজ্যে এরকম মানুষরাই বোধ হয় অখণ্ড জ্ঞানচর্চার নামে কবিতায় বিজ্ঞান, গোয়েন্দা কাহিনিতে রসায়ন শাস্ত্র, পঞ্জিকায় ভূগোল আর জীববিজ্ঞানের পাঠ্যবইতে ভরতনাট্যম নাচের পাঠ খুঁজে বেড়ান। আর সেই সব খুঁজে না পেলেই খণ্ডবাদী বলে গাল পেড়ে সব বাদ দিয়ে দেন।
হেনরি গ্রে ইংল্যান্ডে বসে ১৮৫৮ সালে একটা মানব শারীরসংস্থা বিষয়ক বই লিখেছিলেন, যার ২০০৮ সালে ৪০-তম সংস্করণটি বেরিয়েছে বলে শুনেছি। একাধিক প্রকাশক বইটির কপিরাইট কিনে নিয়ে বিভিন্ন সময় ছাপিয়েছে। বেশ কিছু ইউরোপীয় ভাষায় এর অনুবাদও হয়েছে বলে শোনা যায়। মেডিক্যাল ছাত্ররা এখনও নাকি বইটা পড়ে। অন্তত হাতের সামনে টেবিলে গুছিয়ে রাখে। স্থবিরবাবুও নিশ্চয়ই পড়েছিলেন ছাত্রজীবনে। Gray’s Anatomy নামে খুবই বিখ্যাত একখানা বই। পৃথিবীতে খুব কম পাঠ্যবইয়ের কপালেই এর মতো এতটা দীর্ঘ বিবর্তন ও স্থায়িত্ব লাভের সৌভাগ্য জুটেছে! অথচ কী বিচ্ছিরি একটা খণ্ডতাবাদী বই, একবার ভাবুন। একটা গোটা মানুষের প্রাণস্পন্দন মনোবেদনা শিল্পরুচি খাদ্যপান কাব্যস্পৃহা ক্রীড়ামোদ―এই সব মানবীয় কোনো কিছুর নামগন্ধ পর্যন্ত তাতে নেই। অত মোটা একখানা বইয়ের পাতার পর পাতা জুড়ে আছে কিনা স্রেফ মরা মানুষের শুকনো মাংসপেশী স্নায়ু-শিরা-ধমনী আর হাড়গোড়ের কথা! এরকম একখানা বই দিয়ে ডাক্তারিবিদ্যার পাঠ শুরু করে কী করে মেডিক্যালের ছাত্ররা মানুষের মতো মানুষ হবে?
বুঝতে পারছেন না কথাটা? অস্পষ্ট ঘোলাটে বলে মনে হচ্ছে কথাগুলো?
ঠিক আছে, ভাবনাচিন্তার সাবেকি ধরনটা পালটে ফেলুন; দেখবেন, সহজ সমাধান হাতের সামনেই তো রয়েছে। সেটা হল: সব বইতে সব কিছুই থাকতে হবে। না হলেই খণ্ড। আলাদা করে কোনো বিষয় নিয়ে কোথাও কিছু লেখা বা বলা চলবে না। এই রকম হচ্ছে স্থবির দাশগুপ্ত এবং তাঁর মতো চিন্তাধারার মানুষদের কার্যকরী বক্তব্য। দুনিয়াটা যেহেতু এরকম নয়, কবিরা কবিতাই লেখেন, অভিনেতারা নাটকে বা চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন, চিকিৎসকরা চিকিৎসা করেন, শিক্ষকরা ছাত্রদের পড়ান, চাষিরা চাষবাস করেন, শ্রমিকরা কলকারখানা চালান―তাই এই পৃথিবীতে এত সমস্যা। শিক্ষালাভের উপকরণগুলোতেও গণ্ডগোল। শারীরসংস্থার বইতে হাড়গোড় মাংসপেশীর কথা থাকে, শারীরবৃত্তের বইতে থাকে বিভিন্ন অঙ্গসংস্থানের কার্যকলাপ, পদার্থবিদ্যার বইতে কাব্যসাহিত্য থাকে না, রসায়নশাস্ত্রের খুব ভালো গ্রন্থেও মানুষের মনের খবর দেয় না, আর কবিতার বইতে সজীব কোষ সম্পর্কে কিছুই যে লেখা থাকে না―কর্পোরেটরা এর সুযোগ তো নেবেই! তাই কর্পোরেট সংস্থাগুলি মানুষের প্রয়োজনীয় সব জিনিস দখল করে নিতে পারছে। সবাই যদি সব কিছু জানতেন এবং জানাতেন, সকলেই যদি সব কাজ করতে পারতেন, তাহলে এটা সম্ভব হতই না। এই যেমন আদিম সমাজে, যেখানে সকলকে সব কাজ করতে হত, সেখানে কোনো কর্পোরেট সংস্থা ছিল না!
আক্ষেপের কথাই বটে!
অথচ বিজ্ঞানের এক একটা শাখায় আমরা আলাদা আলাদা জ্ঞানেরই খবর পেয়ে থাকি। পদার্থবিজ্ঞানের সাহায্যে পদার্থের সাধারণ ধর্ম শিখে থাকি, রসায়নশাস্ত্রে এক একটা বস্তুর ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম সম্বন্ধে পড়ে থাকি, গণিতশাত্রে পাঠ করি বস্তুর পরিমাণগত ও আকারগত বৈশিষ্ট্য, ইত্যাদি। ঠিক একইভাবে সাহিত্য পাঠে জানতে পারি বড় বড় লেখকরা গল্প কবিতা উপন্যাসে কী লিখেছেন, কীভাবে লিখেছেন। শিল্প-সংস্কৃতির বিষয় তার নিজস্ব এলাকার থেকেই শিখতে ও বুঝতে হয়। একই রকম ভাবে জীব বিজ্ঞানের পাঠ থেকে আমরা জীব জগতের নানা বৈশিষ্ট্যের খবর পাই। জীবাশ্মবিদ্যার সাহায্যে সময়ের সরণিতে অবলুপ্ত প্রাণী উদ্ভিদ ইত্যাদির সাক্ষ্য প্রমাণ পাই এবং তার সাহায্যে তাদের আকার আকৃতি সংক্রান্ত কিছু কিছু তথ্য পুনরুদ্ধার করতে পারি। যাদের চেনা যায়, তারা জীবিত থাকা কালীন কী খেত, কীভাবে খেত, ইত্যাদি জানা না গেলে জীবাশ্মবিদ্যা মিথ্যা বা অকার্যকর হয়ে যায় না। হৃদ্রোগ বিশেষজ্ঞ যখন একজন অসুস্থ মানুষের হৃৎপিণ্ডের অসুখের চিকিৎসা করেন, হৃদয়বৃত্তি নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে তা সম্ভব হবে না। যদিও তার মানে এই নয় যে সেই চিকিৎসকের হৃদয়বৃত্তি নেই বা তা নিয়ে তাঁর মাথা ব্যথা নেই। আর যদি তা না থেকে থাকে, তার কারণ নিশ্চয়ই এই নয় যে তিনি একজন খণ্ডতাবাদী হৃদ্রোগ বিশেষজ্ঞ। তার পেছনে তাঁর ছাত্র জীবন থেকে নৈতিক চারিত্রিক গঠনের সমস্যা রয়েছে।
খণ্ডতাবাদের স্বরূপ
এত দূর এসে কি ডাঃ দাশগুপ্তর বক্তব্য এখন খুব উদ্ভট মনে হচ্ছে? বেশ, তাহলে আসুন, এবার আমরা আরও একটু গভীরে গিয়ে এই সব জিনিস নিয়ে চিন্তাভাবনার অভ্যাস করি। জ্ঞানরাজ্যের কাজ কারবারগুলি আর একটু ভালো করে বুঝে নেবার চেষ্টা করি। তখন সত্যিই এক আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করে বসব হয়ত।
আসলে খণ্ডতাবাদের কবলে পড়েছেন ডাঃ স্থবিরবাবুই। অবশ্য না জেনেই। কেন না, দর্শনে খণ্ডতাবাদ কোত্থেকে আসে, কীভাবে আসে, কেন আসে―সে সম্পর্কে তাঁর খুব একটা স্পষ্ট ধারণা নেই বলেই আমার বিশ্বাস। তাই খুব আন্তরিকভাবে খণ্ডতাবাদের বিরোধিতা করতে চেয়েও তিনি বুঝতে পারেননি কখন তিনি নিজেই সেই খণ্ডতাবাদের করাল গ্রাসে আটকে পড়েছেন। সেই কথাটা এবার একটু খুলে বলে ফেলি।
খণ্ডতাবাদ কাকে বলে? বিজ্ঞান যে প্রকৃতি ও সমাজকে বাস্তব জগতকে খণ্ড খণ্ড করে বিচার বিশ্লেষণ করে, এবং তারপর সেই খণ্ড বিচারগুলিকে সমন্বিত করে এক একটা জিনিস সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তার থেকে আপনাআপনি কোনো খণ্ডতাবাদ জন্ম নেয় না। বিজ্ঞানের এটাই কাজ এবং কাজের ধরন। এইভাবে কাজ করে বলেই বিজ্ঞান যা কিছু জানতে পারে তা সঠিকভাবে জানতে পারে। পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জানতে চেষ্টা করে। কিন্তু যখন সেই সব খণ্ডের যে কোনো একটা জায়গার খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন জ্ঞানকে ভিত্তি করে সমস্ত দুনিয়াদারি সম্পর্কে কেউ ধারণা পাওয়ার বা দেবার চেষ্টা করে সেটাই তখন খণ্ডতাবাদের জন্ম দিয়ে ফেলে। যেমন ধরুন, প্রাণীজগতের কথা ভালো করে জানতে হলে তাকে তার জায়গায় গিয়ে বিশ্লেষণাত্মক কায়দাতেই জানতে হবে। কিন্তু তারপর যদি কেউ ভাবেন, মানুষও তো শেষ বিচারে একটা প্রাণীই―অতএব মানুষের আচরণ মনন ইত্যাদিকেও পশুর আচরণ দিয়েই বুঝতে হবে, তিনি খণ্ডতাবাদের শিকার হয়ে গেলেন। কিংবা কেউ যদি ডারউইনের জীব বিবর্তন তত্ত্ব পড়বার পর মনে করেন, এই ভাবেই মানব সমাজের বিবর্তনকেও বুঝতে হবে, সঙ্গীতের ক্রমবিকাশকেও একই নিয়মেই ধরতে হবে, ইত্যাদি, তাহলে তিনি খণ্ডতাবাদের চর্চায় ফেঁসে যাবেন। জীবজগতের ক্রম বিবর্তন বোঝার জন্য ডারউইনের তত্ত্ব চর্চা করলে সেটা কোনোভাবেই খণ্ডতাবাদ নয়। এইভাবেই একদল জিন নির্ধারণবাদের খপ্পরে পড়ে বলতে থাকেন, মানুষের প্রেম ভালোবাসা হিংসা বিদ্বেষ রাগ আগ্রাসন ইত্যাদি সবই কোনো না কোনো জিনের দ্বারা নির্ধারিত। আরও এগিয়ে কিছু লোক কবিতার জিন, বিজ্ঞানের জিনও খোঁজেন। খণ্ডতাবাদী কম্পিউটার বিজ্ঞানী দুনিয়ার সমস্ত কিছুর পেছনে পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম খুঁজে পান বা পেতে চেষ্টা করেন। আবার কেউ কেউ স্বয়ং ঈশ্বরকেও একজন নিখুঁত গণিতবিদ করে তোলেন। এইভাবে যাঁরা ভাবনা চিন্তা করেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিটা হচ্ছে অনেকটা মাছের (বা জলচর জীবের) চোখে জলতলের উপরের দুনিয়ার মতো। একটা ত্রিমাত্রিক উলটো-শঙ্কুর মতো। কিংবা ধার্মিক লোকেদের ভাষায়, বিন্দুতে সিন্ধুজ্ঞান!
স্থবিরবাবুর শঙ্কু হচ্ছে বর্তমান স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্থাগুলির তরফে আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যাপক অপপ্রয়োগ, আর তার পেছনে ডারউইনের তত্ত্বের কল্পিত প্রভাব, ইত্যাদি। তাই ম্যালথাস থেকে ডারউইন ঠিক কী এবং কতটুকু নিয়েছেন বিচার না করে তিনি অক্লেশে ম্যালথাসের যাবতীয় মানব-বিদ্বেষী কুমতের ভাগ ডারউইনের উপরও নিশ্চিন্তে চাপিয়ে দেন! তিনি ধরেই নেন, ডারউইন ম্যালথাসের জনসংখ্যা বিষয়ক ফরমুলা নিয়েছেন মানে তাঁর থেকে সবই তুলে নিয়েছেন! খণ্ডতাবাদ ছাড়া এ আর কী? ডারউইন যে তাঁর বইতে মানুষ প্রসঙ্গে ম্যালথাসের মৃদু সমালোচনাও করেছিলেন, তা তাঁর সেই খণ্ডতাবাদী দৃষ্টিতে কখনই ধরা পড়ে না। ডারউইন যে ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ কঠোর ভাষায় ইংরেজ শাসকদের নিন্দা করেছেন, এও তাঁর নজর এড়িয়ে যায়! সমগ্রভাবে দেখতে না পারার ফলেই এই বিপত্তি ঘটে যায়।
মানুষকে বিচারের সময় আমরা অনেকেই এরকম ভুল করে থাকি। ভালো ছাত্র হলেই তিনি ভালো শিক্ষক হন না। সুতরাং একজন শিক্ষক ছাত্রদের ভালো করে পড়াতে পারছেন না দেখেই যদি আমরা ভাবি, ইনি ছাত্র হিসাবে মেধাবী নন, তাতে ভুল করার সম্ভাবনা যথেষ্ট প্রবল। কিংবা, আমরা যদি ডাঃ দাশগুপ্তের এই নিরঙ্কুশ ডারউইন বিরোধিতা লক্ষ করে এবং তা অপছন্দ করে তাঁকে চিকিৎসক হিসাবেও অযোগ্য বলে ধরে নিই, তাও এক রকম খণ্ডতাবাদী সিদ্ধান্তই হবে। কেন না, প্রথমটা থেকে দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটা আপনাআপনি বেরিয়ে আসে না। চিকিৎসক হিসাবে তিনি কতটা যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছেন সেটা তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি অনুশীলনের ক্ষেত্র থেকে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করেই বুঝতে এবং বলতে হবে। এক জায়গার পর্যবেক্ষণ অন্য জায়গায় নির্বিচারে বসিয়ে দিলে ভুল হবে।
বিজ্ঞানের জগতেও এরকম ভুলের সম্ভাবনা থাকে বলেই সমস্ত বড় বিজ্ঞানী এই সংকীর্ণ শঙ্কুর বাইরে বেরিয়ে এসে জগতকে দেখতে চান। কেন না, কাজের সুবিধার জন্য আমরা জ্ঞানের জগতকে ভাগ ভাগ করে নিলেও বাস্তব জগত, প্রকৃতি, পরিবেশ, জীবজগত, সমাজ, মানুষ, মানবিক মনন-ফসল―ইত্যাদির কোনোটাই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন পরিঘটনা নয়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে মিলেমিশে আছে। তাদের মধ্যে নানা ভাবে ও নানা মাত্রায় মিথষ্ক্রিয়া আছে। তাই শেষ বিচারে জগত ও জীবন সম্পর্কে একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার সময় এই পারস্পরিক সংযুক্তি ও নির্ভরশীলতার কথাটাও মাথায় রাখতে হয়।
আলোচ্য প্রসঙ্গে এটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে যে এমনকি ডারউইন যখন শুধুমাত্র জীবের বিবর্তন নিয়ে চর্চা করেছেন, তখনও তিনি বারবার বলেছেন, প্রতিটি জীবের প্রতিটি ছোটখাটো পরিবর্তন এক সঙ্গে অসংখ্য প্রাণী এবং উদ্ভিদের মধ্যেও বহু ধরনের পরিবর্তনের কারণ হয়ে ওঠে। যেমন, পোকামাকড়ের বিবর্তনের সঙ্গে সপুষ্পক উদ্ভিদের পরাগ সংযোগ প্রক্রিয়ার বিকাশের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আবার পতঙ্গের শারীরসংস্থা ও শারীরবৃত্তের বিকাশের সঙ্গে এই সমস্ত উদ্ভিদের ফুল ও ফলের গঠনের বিকাশের ওতপ্রোত নৈকট্য। আজ আমরা এও বলতে পারি, ভূত্বকের স্থলভূমির বিকাশের সাথেও একদিকে স্থলচর উদ্ভিদ অন্য দিকে স্থলচর প্রাণীর উদ্ভবের ঘটনা যুক্ত হয়ে আছে। এইভাবে না বুঝলে জিনিসগুলিকে ধরাই যাবে না। ফলে বিজ্ঞানেও বিচ্ছিন্ন করে বোঝার কোনো উপায় নেই।
অবশ্য, শেষ বিচারে খণ্ডিত জ্ঞানের অংশগুলোকে জুড়বার কাজটি আসলে দর্শনের। দর্শনের কাছেই আমরা জগত ও জীবন সম্পর্কে একটা পূর্ণাঙ্গ দৃকপাত পেতে পারি। কিন্তু অংশকে এইভাবে সমগ্রতে জুড়ে ফেলা মানে বীজগাণিতিক সমষ্টি নির্ণয় করা বোঝায় না। বিজ্ঞান বিশেষ বিশেষ নিপুণ ক্ষেত্রে যা কিছু আবিষ্কার করল, উদ্ঘাটন করল, তার মধ্য থেকে সার সত্যগুলি মন্থন করে সামগ্রিক তাৎপর্যটি তুলে ধরার দায়িত্ব দর্শনের। তবে বিজ্ঞানে যে অর্থে একটা প্রামাণ্য বা সর্বমান্য জ্ঞানের দিশা তৈরি হয়েছে, দর্শনের জগতে সেটা এখনও হয়নি। দর্শন এখনও অনেকটাই ব্যক্তির মতামত নির্ভর হয়ে রয়েছে। বস্তুজগত বা সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে নানা রকম পূর্ব ধারণা ভিত্তিক উপলব্ধির উপর দাঁড়িয়ে আছে। তাই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমার মত আপনার বক্তব্য বলে কিছু না থাকলেও দর্শনের ক্ষেত্রে আছে। সেখানে ভাববাদ প্রত্যক্ষবাদ বস্তুবাদ আছে; তাদের মধ্যেও আবার নানা রকমফের আছে। তার চূড়ান্ত মীমাংসা এখনও হয়নি বলেই দর্শনের দিক থেকে বিজ্ঞানকে বোঝার ক্ষেত্রে আজও বহু বিচিত্র সমস্যা দেখা দেয়। আমাদের দার্শনিক উপলব্ধি অনুযায়ী আমরা বিজ্ঞানকে বুঝতে চাই। আর যখন যার যার নিজস্ব প্রিয় উপলব্ধির সাথে তাকে সর্বাংশে মেলাতে পারা যায় না, তখন অধিকাংশ মানুষই নিজের মতের জায়গায় কোনো আপস করতে চায় না, এতটুকু ছাড় দিতে চায় না; বিজ্ঞানের জ্ঞানকেই বরং কেটে ছেঁটে অন্যভাবে লিখে নিজস্ব বিচারের খাপে বসিয়ে নিতে চেষ্টা করতে থাকে। সমস্যাগুলি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন না থাকলে এই স্খলন এড়ানো খুব কঠিন!
প্রশ্ন হল, আজ অবধি বিজ্ঞানের এত সমস্ত সমুন্নত বিকাশের পরেও দর্শন চিন্তার জগতে খণ্ডতাবাদের জন্ম হল কী করে? আর তা চলছেই বা কীভাবে?
এই প্রশ্নটাকে শুধু মাত্র দর্শনের হিসাবে গণ্য করলে ভুল হবে। দর্শন তো বটেই। কিন্তু সেই সঙ্গে এর পেছনে যে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট কাজ করে চলেছে, তাকে খেয়াল না করলে একটা বিরাট ভুল হয়ে যাবে। সেই খণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিরই শিকার বনে যেতে হবে। বর্তমান দুনিয়ার সমাজ বাস্তবতা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক অসভ্যতার ক্রম বর্ধমান সঙ্কট আর তার জোয়াল থেকে আপামর জনসাধারণের মুক্তি লাভের আকূতি। স্বভাবতই এই সমাজ ব্যবস্থার রক্ষাকর্তারা চায় না যে সাধারণ মানুষ পুঁজিবাদের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য, তার বিকাশ ও পতনের ধারা বুঝে ফেলুক। তার উদ্দেশ্য প্রথমত মানুষকে বিভ্রান্ত করা, তার ক্ষয়িষ্ণু ও মুমূর্ষু অবস্থাকে চিনতে না দেওয়া; দ্বিতীয়ত, তা সত্ত্বেও যদি মানুষ সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদি সঙ্কট সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবার মতো অবস্থায় এসে যায়, তখন তাদের সেই সমস্ত সমস্যার কোনো একটা বিশেষ দিকের প্রতি মনোযোগ সন্নিবদ্ধ করিয়ে দেওয়া। সমস্তটা তারা যেন এক সঙ্গে দেখতে না পায়। কেউ দেখুক শিক্ষার সমস্যা, কেউ দেখুক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অধঃপতন, কারোর কাছে পরিবেশ দুষণের সমস্যা বেশি করে আলোড়ন তুলুক, কাউকে ভাবিয়ে তুলুক বিশ্ব উষ্ণায়নের ঘটনা, কেউ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ুক শক্তির ভবিষ্যত নিয়ে, কিছু মানুষ ব্যস্ত থাকুক কৃষি খাদ্য সুরক্ষার প্রশ্নকে ঘিরে, অন্য একদলকে উদ্বিগ্ন করে রাখুক গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের সমস্যা, জনসাধারণের আর একটা অংশ ব্যস্ত থাকুক ধর্মীয় মৌলবাদ ও সন্ত্রাস নিয়ে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আর যাঁরা যে অংশটায় কাজ করছেন, ভাবছেন, এটাই আসল বা একমাত্র সমস্যা। বাকিগুলোর গুরুত্ব কম।
লক্ষ করে দেখুন, বাস্তবে এই প্রতিটি সমস্যার উৎসমুখ কিন্তু একই―বর্তমান অসভ্য ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। অথচ, যারা এর এক একটা দিক নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন, তারা আসলে একটা গোটা দানবিক ব্যবস্থাকে খণ্ড খণ্ড করে নিয়ে এক একটা খণ্ড সম্পর্কে কাজ করতে যাচ্ছেন। এটা খারাপ হচ্ছে তা নিশ্চয়ই বলা যায় না। যে যেভাবে যেখানে কাজ করছেন, যে সমস্যার সমালোচনা করছেন, তাঁরা সেখানেই পুঁজিবাদকে মৃদুভাবে হলেও আঘাত করছেন। আবার এটাও সত্য যে এর ফলে মূল ব্যবস্থাটা অধিকাংশ মানুষের নজরের বাইরে থেকে যাচ্ছে এবং এক একটা বিচ্ছিন্ন আঘাত কখনই খুব বড় হয়ে তার গায়ে পড়ছে না। সে বেঁচে যাচ্ছে। জ্ঞানের খণ্ডতা নয়, চেতনার খণ্ডতাই এইভাবে খণ্ডতাবাদের জন্ম দিয়ে চলেছে। এটা পরিষ্কারভাবে ধরতে পারলে তবেই আমরা খণ্ডতাবাদকে আমাদের চেতনা-প্রকোষ্ঠ থেকে সার্থকভাবে হঠাতে পারব।
আমরা যখন একটা দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করি, তখন আসলে সেই দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সমস্যাগুলিকে ধরবার চেষ্টা করি। সেখানে কর্পোরেট বাণিজ্য সংস্থার নরখাদক ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গেলেও আমাদের সেই আর্থসামাজিক বিশ্লেষণেরই সাহায্য নিতে হবে। সেটা না করে আমরা যখন বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাসকে তার জন্য দায়ী করে বসি, তার মানে হল আমরা খণ্ডতাবাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। সামাজিক অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত আমাদের নজরের বাইরে থেকে গেল। একই সমস্যা দেখা যায় পরিবেশ সমস্যা নিয়ে আলোচনার সময়ও। সেখানেও পরিবেশ দুষণের প্রধান কারক এবং সংগঠক হচ্ছে বড় বড় বহুজাতিক ব্যবসায়িক সংঘগুলি এবং তাদের চাপে অনুসৃত শিল্প ও অর্থনীতির বিকাশ সংক্রান্ত সরকারি নীতি সমূহ। তাদের সংকীর্ণ স্বার্থেই জল জঙ্গল বাতাস―এক কথায় মানব সমাজের সমস্ত সামূহিক সম্পদগুলি তাদের হাতে বিনা পয়সায় বা নামমাত্র মূল্যে তুলে দেওয়া হচ্ছে নির্বিচারে ধ্বংস করার জন্য। কিন্তু যেহেতু পরিবেশ দুষণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার সাধারণভাবে আমাদের চোখের সামনে পরিদৃশ্যমান থেকে একটা বাস্তব উপাদান হিসাবে ক্রিয়া করে থাকে, সরকার এবং বৃহৎ বাণিজ্যিক সংঘগুলি আড়ালে থেকে কাজ করে যায়, খণ্ডতাবাদীরা সামগ্রিক আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বিষয়টিকে না দেখে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারকেই শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন করে ধরে নিয়ে বিচার করেন এবং তাকেই সমগ্র দুষণের ঘটনার জন্য দায়ী করে বসেন। আর এর ফলে আসল অপরাধী আড়ালেই থেকে যেতে পারে।
আপাতত এরকম আর একটাই উদাহরণ দেব। ডাক্তার দাশগুপ্তর তথ্যসূত্র থেকে দেখা যাচ্ছে তিনি তথাকথিত গাইয়া তত্ত্বের প্রস্তাবক জেম্স লাভলকের চিন্তার দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত হয়েছেন। হতেই পারেন, দোষের কিছু নয়। পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে গিয়ে এই প্রযুক্তিবিদ পৃথিবীর সমগ্র বাস্তু-ব্যবস্থাকে যেভাবে একটা সজীবদেহতন্ত্র বলে গণ্য করেছেন তাতে আপাত অর্থে অখণ্ডতাবাদের একটা ছোঁয়া দেখতে পেয়ে তিনি খুশি হতেই পারেন। কিন্তু তারপর যখন ২০০৪ সাল থেকে সেই ইনিই আবার ইংল্যান্ডের পরমাণু বিদ্যুৎ ব্যবহারের নয়া উদ্যোগের পেছনে (বিশ্ব-উষ্ণায়ন-এর বিরোধিতা করার নামে) একজন অক্লান্ত প্রচারক হয়ে পড়লেন, তখন কি মনে হয় না, খণ্ডতাবাদ তাঁকেও গ্রাস করে নিয়েছিল এবং কর্পোরেটদের পায়ের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল? ১৯৬৮ সালে যখন তিনি প্রথম গাইয়া-তত্ত্বের কথা ভেবেছিলেন, তখন পরমাণু বিদ্যুতের পক্ষে বললে এই কথা উঠত না, কেন না, তখনও এর অনিরসনীয় সমস্যার কথা বিজ্ঞানীদের ভালো করে জানা হয়নি। কিন্তু ২০০৪ সালে তো আর এই কথা বলা যায় না! এবং চের্নোবিল ফুকুশিমার পরে তো আর এই সব কথা বলার কোনো অবকাশই নেই!!
অথ ক্যান্সার কথা!
অতঃপর ক্যান্সার! আমরা দেখব, ক্যান্সার রোগ এবং তার চিকিৎসার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে বসে ডাঃ স্থবির দাশগুপ্ত আরও কত ভয়ানকভাবে খণ্ডতাবাদের শিকার হয়ে পড়েন!
ক্যান্সার সম্পর্কে বলতে গিয়ে বর্তমান চিকিৎসা পদ্ধতি এবং আরও বেশি করে আধুনিক জীববিজ্ঞানের উপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন ডাঃ দাশগুপ্ত। “ইঁদুরকে ক্ষুদ্র মানুষ বলে ধরে নিয়েই আমরা আমাদের পরীক্ষানিরীক্ষাগুলো চালাতে থাকি। আর তা থেকে আহরিত তথ্যগুলো আমরা আরোপিত করি মনুষ্য দেহের ওপর। এর চেয়ে বেশি বিজ্ঞতা আজও আমরা অর্জন করে উঠতে পারিনি।” [দাশগুপ্ত ২০০৯, ৫৪] একইভাবে, “জিন-মিউটেশন দিয়ে কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক, চোখ আর হাতের মতো অভিনব অঙ্গ কীভাবে তৈরি হল, কীভাবে তাদের অতুলনীয় অভাবনীয় বৈশিষ্ট্যের উল্লম্ফন ঘটে গেল তা ব্যাখ্যা করা যায় না।” জিনতত্ত্বের এই অক্ষমতার খবর তো আগেই তিনি দিয়েছেন, এখানে এর পুনরুক্তির উদ্দেশ্য আলাদা, আরও এক ব্যর্থতার সংবাদ পাঠককে জানান দেওয়া: “তেমনই শুধু জিন মিউটেশন দিয়ে ক্যান্সারের হদিশ পাওয়াও অসম্ভব। ভালো জিন, খারাপ জিন, ভালো জিনকে রক্ষা করব, খারাপ জিনকে দূর করে দেব, ইত্যাদি বাগাড়ম্বর আসলে বহুনিন্দিত সৌজাত্যবাদী (eugenics) দৃষ্টিভঙ্গিরই নামান্তর। এই দৃষ্টিভঙ্গির কাছে জীব, জীবসত্তা, রোগ এবং স্বাস্থ্য, সবই যেন একটা যুদ্ধের পটভূমি।” [ঐ]
এই যুদ্ধে কি বিজ্ঞান বা চিকিৎসাবিজ্ঞান জয়লাভ করতে পারছে? না, “আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান তার বর্ণময়তা এবং নিরন্তর ক্রিয়াশীলতার উন্মাদনা সত্ত্বেও তার সারবত্তা হারাচ্ছে। জীবনের অমৃত মন্থন করতে গিয়ে চিরবিদ্রোহী আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান আজ যেন দিশাহারা। কত কিছু সে দিল, শুধু স্বস্তি দিতে পারল না। অথচ মানবসমাজ তো কেবল বৈভব চায়নি, সে তো প্রথমত স্বস্তিই চেয়েছিল।” [দাশগুপ্ত ২০০৯, ৫৪-৫৫]
এই অবধি এসে পৌঁছনোর পর তিনি কিছু অদ্ভুত ঘোষণা করতে থাকেন একের পর এক। জিনবিদ্যাকে নাকচ করতে করতে তিনি বলে ওঠেন: “এই গতিময় জিনোর্ধ্ব প্রক্রিয়াগুলোই যে জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করে তা আমাদের কাছে ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। উচ্চতর কোষবিদ্যা তাই নব-ডারউইনবাদী জিন-নিয়ন্ত্রণের তত্ত্ব পরিত্যাগ করেছে। তার বদলে সে স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনের (‘অটোপোয়েসিস’) কথা বলে।” [দাশগুপ্ত ২০০৯, ৫৫] আসলে কিন্তু জীবন প্রক্রিয়া আরও বুঝি অস্পষ্টতরই হয়ে উঠল। জিনের দ্বারা জীব দেহের সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রিত হওয়ার, অর্থাৎ, জিন সর্বস্ববাদের একপেশেমিকে বর্জন করতে গিয়ে নিয়ে আসা হল আর একটা বিপরীত একপেশে চিন্তাকে—জিন কিছুই নির্ধারণ করে না বা করতে পারে না। জীবদেহের সবই নিজে নিজে হতে থাকে। কোথাও কোনো কার্যকারণের অস্তিত্ব নেই। কেন না, “প্রাণ বা অন্যভাবে বলা যায়, জীবকোষের উদ্ভব ঘটেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। নানান উপাদানের স্বতঃস্ফূর্ত সংযোগের ফলেই তার আগমন। আর সেই প্রাণেরই অপর এক রূপ হল ক্যান্সার। ক্যান্সার কোষেরও উদ্ভব ঘটে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই।” [ঐ]
এই তাহলে কথা! এতক্ষণে স্পষ্ট হল। ক্যান্সার একটা স্বাভাবিক ঘটনা। জীবনের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততায় মানুষের শরীরে ক্যান্সার বাসা বাঁধে। এই ক্যান্সারের অনেক গুণ ডাক্তার দাশগুপ্তের স্বচ্ছ চোখে ধরা পড়ে: “ক্যান্সার কোনো অপার্থিব কোষ নয়। তাকে একটি অপার্থিব কোষ হিসাবে ভাবার মধ্যেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মূল সমস্যা লুকিয়ে আছে। ক্যান্সার কোষের জিনপ্রকৃতি অন্য সমস্ত কোষের মতোই, সেই কোষের সংখ্যাবৃদ্ধির গতি মোটেই অস্বাভাবিক নয়, তা অন্ত্র বা অস্থিমজ্জার কোষের তুলনায় দ্রুততরও নয়। ক্যান্সার কেবল কোষীয় বিবর্তনের একটি অভিব্যক্তি। ক্যান্সার হল এক জৈবিক অবভাস, একটা ফেনোমেনন; তাকে আলাদা করে চিকিৎসা করা যায় না, সে থাকে চিকিৎসার আওতার বাইরে।” [দাশগুপ্ত ২০০৯, ৫৭]
কিন্তু সকলে তো আর ডাঃ দাশগুপ্ত নন। তাঁরা অখণ্ডতাবাদী বৈদ্য নন, তাঁরা ডারউইনকে মানেন, নব-ডারউইনবাদ মেনে চলেন, আধুনিক জিনতত্ত্ব স্বীকার করেন। তাঁরা মানুষের জ্ঞানের শক্তিতে আস্থা রাখেন, ফলে তাঁরা চান এই “ক্যান্সার কোষ নামক বিকৃত, উদ্ধত, বর্বর পরজীবীটিকে মেরে কেটে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে”। [দাশগুপ্ত ২০০৯, ৫৬] “সুতরাং ক্যান্সারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়।”
ও হো হো! এখানে আর একটা কথাও আগেই বলে যাওয়া দরকার ছিল। স্থবিরবাবু এইখানে এসেও ডারউইন তত্ত্বের একটা স্ববিরোধিতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। ডারউইনবাদীরা নাকি মনে করেন, “ক্যান্সার কোষ হল প্রাকৃতিকভাবে নির্বাচিত। . . . তো তার নিজের যুক্তিতে, ক্যান্সার কোষ অন্যান্য কোষের তুলনায় যোগ্যতর বলেই প্রাকৃতিকভাবে নির্বাচিত। আর সে যুক্তি যদি মানতে হয় তাহলে ক্যান্সারের মারণচরিত্র নিয়ে প্রতিবাদ অবান্তর হয়ে যায়, কেন না, তা নিশ্চয়ই প্রকৃতির মনোগত কোনো মহান অভিপ্রায়।” [ঐ]
না, অনেক হল! এইবার সরাসরি আমাদের আসল কথায় যাওয়া দরকার। প্রথমেই বলি, আমার জানা এরকম কোনো ডারউইনপন্থী নেই, যিনি (১) ক্যান্সার কোষকে অপার্থিব ঘটনা বলে মনে করেন; (২) ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে ক্যান্সার কোষকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফসল বলে মনে করেন; (৩) ক্যান্সার কোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এগুলো সবই ডাঃ দাশগুপ্তের ডারউইন-ব্যাখ্যাজাত কল্প-ভাবনার ফসল।
দ্বিতীয় অভিযোগটি সম্পর্কে আরও দু কথা বলি। বিবর্তনবাদ অনুযায়ী ক্যান্সার কোষ প্রাকৃতিকভাবে নির্বাচিত হলে সমস্ত মানুষই ক্যান্সার কোষ শরীরে নিয়ে জন্মাচ্ছে বলে দেখা যেত। আমরা চারদিকে শুধু ক্যান্সার রোগীই দেখতে পেতাম। মানব সমাজের সৌভাগ্য যে তেমনটা আমরা দেখি না।
ক্যান্সার নিয়ে গবেষণা শুধু যে জীব-বিজ্ঞানীরা করছেন এমন নয়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারায় এই বিশেষ ধরনের কোষ উৎপাদন এবং বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে জানার বোঝার চেষ্টা চলছে। সেই প্রচেষ্টার মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক রকমের ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। আছে বলেই এতদিনেও তাকে ঠিক মতো ধরা যায়নি। আসলে ক্যান্সার গবেষণার ক্ষেত্রে বড় বড় কর্পোরেট ওষুধ সংস্থাগুলির যেমন বিপুল অঙ্কের বিনিয়োগ আছে তেমনই এক মুনাফাবাজির সংকীর্ণ লক্ষ্য থেকে তার উপর নানা ধরনের শেকলও পরানো আছে। ফলে এখনও এটা জানা যায়নি, কেন ক্যান্সার কোষগুলি তার ওই বিশেষ ধরনের আচরণ করে। কেন তারা আদি ভ্রূণ কোষের গঠনে ফিরে যেতে চায়, পার্শ্ববর্তী কোষগুলিকেও বিশেষায়িত চরিত্র বর্জন করিয়ে আদি ভ্রূণ-অবস্থায় পরিবর্তিত করতে থাকে। এটা অপার্থিব যেমন নয়, তেমনই এটা জীব কোষের স্বাভাবিক বিকাশও নয়। কোষের স্বাভাবিক বিকাশ ভ্রূণ অবস্থা থেকে বিশেষায়িত গঠন ও ক্রিয়াশীলতার দিকে। কর্কটায়ন তার বিপ্রতীপ যাত্রা, অধোগমন বলা যেতে পারে। আবার এটা অকারণ স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনও নয়। এর পেছনেও কার্যকারণ আছে। আমরা তা এখন পর্যন্ত জানতে না পারলেও আছে। কেন না, কোনো স্বাভাবিক বা স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনাও অকারণে ঘটে না। বিজ্ঞানের কাজই হল সেই কারণকে জানার চেষ্টা করা। আর মনে রাখা ভালো, দুনিয়ার সমস্ত ঘটনার পেছনেই কারণকার্য সম্বন্ধ কাজ করে—এই বোধ আমাদের মধ্যে এসেছে জগত সংসার সম্পর্কে “অনিবার্যতা” নামক এক অখণ্ডতাবাদী দার্শনিক ধারণা থেকেই। এই ধারণাই আমাদের যে কোনো ঘটনা থেকে তার কারণ হিসাবে অব্যবহিত আগের ঘটনাকে জানতে উদ্বুদ্ধ করে, আবার পরিণাম হিসাবে তার তাৎক্ষণিক পরবর্তী ঘটনাকেও বুঝতে প্ররোচিত করে। ক্যান্সার কোষকেও যখন বিজ্ঞানীরা এই কারণকার্য বিন্যাসে ফেলে বুঝবার চেষ্টা করেন, তখন অন্তত তার মধ্যে খণ্ডতাবাদ নেই। কেন না, এই হেতুবাদী মনন শুধু ডারউইনবাদ নয়, বিজ্ঞানের সমস্ত ধারারই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বেচারা ডারউইন এই অপরাধের জন্য একাকী দায়ী নন, তিনি এক বিশাল গণ অপরাধী বাহিনীর একজন সামান্য নিরীহ সদস্য মাত্র।
সমগ্র আলোচনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লে বোঝা যায়, ডাক্তারবাবুর আসল আপত্তি ক্যান্সার চিকিৎসার বর্তমান পদ্ধতি ও প্রকরণ নিয়ে। তাঁর বক্তব্য আর আমাদের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে বিচার করলে ধরা পড়বে, তাঁর সেই আপত্তির মধ্যে সত্যিই যথেষ্ট সারবত্তা আছে। এই মুহুর্তে ক্যান্সারের যে চিকিৎসা পদ্ধতি তা হল প্রধানত কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে শল্যায়ন। একথাও ঠিক যে কেমোথেরাপিতে যে সমস্ত ভেষজ এবং রেডিওথেরাপিতে যে তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, তা শুধু ক্যান্সার কোষই নয়, সুস্থ কোষ সমূহকেও আক্রমণ করে বসে। এই কারণেই দেখা যায়, চিকিৎসা শুরু করার পর ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর মধ্যে প্রথমে খানিকটা সুস্থ-সবল সতেজ হয়ে ওঠার লক্ষণ ফুটে উঠলেও কিছু দিন পর একটা সময় থেকে তার অবস্থার যেন দ্রুত অবনতি হতে থাকে এবং সে ধীরে ধীরে বহু-অঙ্গ বৈকল্যের শিকার হয়ে পড়তে শুরু করে। প্রলম্বিত মৃত্যুর সেই শেষের দিনগুলি খুবই মর্মন্তুদ! রোগীর শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা, আর পার্শ্ববর্তী মানুষদের অসহায় মনোবেদনা!!
হ্যাঁ, এই রাসায়নিক ওষুধগুলি নিঃসন্দেহেই বিষাক্ত। তবে কোন ওষুধটা নয়? পার্থক্য শুধু ক্ষতি করার মাত্রা ভেদে। প্রশ্ন হচ্ছে, রোগীর জন্য বিকল্পই বা কী? বিনা ওষুধে সারা শরীরে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে অবধারিত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা? খুব অল্প সংখ্যক মানুষই এইভাবে নিজেদের নিয়তির কোলে সঁপে দিতে পারেন। অন্য দিকে ব্যতিক্রম হিসাবেও কোনো রুগ্ন ব্যক্তি যদি এতে সম্মত হয়ে থাকেন, তাঁর বাড়ির লোকেরা পরিবার আত্মীয় স্বজন হাল ছেড়ে দিতে চাইবেন না। ফলে চিকিৎসা পাওয়ার এবং চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার একটা প্রচেষ্টা হবেই। তখন যদি স্থবিরবাবু বলেন, “ক্যান্সার হল কোষীয় বিবর্তনের পরিণতি, জীব হিসাবে মানুষের বিবর্তনের সাথে সে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। স্বাভাবিক কোষের সাথে ক্যান্সার কোষের মূল তফাত হল তার আচরণে। . . . কখনও সে থাকে ধীর গতি, কখনও উচ্ছ্বল, কখনও সে স্তিমিত, কখনও দুর্বার, কখনও হঠাৎ দমকা হাওয়া, কখনও সুদীর্ঘকালীন অলস!” [দাশগুপ্ত ২০০৯, ৫৭], রোগী বা তাঁর বাড়ির লোক তাতে বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা পাবেন না, তাঁরা তখন বরং অন্য চিকিৎসক খুঁজবেন। রক্ত ক্যান্সারের ক্ষেত্রে যেহেতু এখন অনেক বেশি সময় পাওয়া যাচ্ছে, মানুষ আশা করতে থাকেন, হয়ত তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর ক্যান্সারেরও একটা শ্রেয়তর চিকিৎসা পদ্ধতি বা ওষুধ আবিষ্কৃত হয়ে যেতেও পারে। সুতরাং যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণই আশ!
ঠিক এই জায়গাতে খেলছে কর্পোরেট সংস্থাগুলি। তারা বাস্তবের তুলনায় অনেক সময়ই আশা বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করতে থাকে। তার জন্য একটা কিছু তাৎক্ষণিক ম্যাজিক দেখাবার আয়োজন করতে চায়। বিজ্ঞানী গবেষক ও চিকিৎসকদের উপর তারা এর জন্য চাপ দিতে এবং প্রলোভন দেখাতে থাকে। চিকিৎসকদের একাংশও হয়ত বুঝে বা না বুঝে এই খেলার অংশীদার হয়ে ওঠেন। তাতে সত্যিকারের চিকিৎসা যতটা হয়, লোক ঠকানো কারবার অনেক বেশি হয়। তারা জানে, ঠিক মতো বিজ্ঞাপন ও বিপণন করতে পারলে মানুষ যত পয়সা লাগে ওষুধ কেনার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বেই। এই ভরসাতেই তো ‘আচ্ছে-দিন’-এর ফেরিওয়ালা সরকার নিশ্চিন্তে ক্যান্সারের ওষুধের দাম এক লাফে আট হাজার টাকা থেকে এক লক্ষ টাকায় বাড়িয়ে দিতে সাহস পেয়েছে।
এই মিথ্যা আশা স্তোক বিজ্ঞাপন বিপণন ও প্রলোভন ভিত্তিক যে ক্যান্সার চিকিৎসা ব্যবস্থা বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজ গড়ে তুলেছে, তার বিরুদ্ধে ডাঃ স্থবির দাশগুপ্তের সমস্ত অভিযোগ বিক্ষোভ ও রাগের সাথে আমরা সকলেই একমত। আমাদের আপত্তি তাঁর বিশ্লেষণের ফলাফলের সাথে। আমাদের তীব্র আপত্তি এর পেছনে ডারউইনকে টেনে আনার বিরুদ্ধে। আর আমাদের গভীর দুঃখ, অখণ্ডতাবাদের হয়ে বলতে বলতেই তাঁর এক অত্যন্ত সংকীর্ণ খণ্ডতাবাদের কূপে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলার জন্য। ডারউইনের বদলে লামার্কের তত্ত্ব জীববিজ্ঞানে গৃহীত হলেও কর্পোরেট সংস্থাগুলো এইভাবেই ব্যবসা করত। বিজ্ঞানীদের সকলেই যদি অখণ্ডতাবাদী দর্শন নিয়ে আপ্লুত হতেন, তাতেও সেই বাণিজ্য সঙ্ঘগুলির কিছুই আটকাত না। তারাই বিজ্ঞানের গবেষণায় পয়সা ঢালে, সুতরাং তারাই যে এর থেকে ফায়দা তোলারও রাস্তা বের করতে সদা সচেষ্ট থাকবে এ আর বেশি কথা কী! এবং সর্বোপরি . . .
না, এই কথাটা আলাদা করেই এবার বলা দরকার। ক্যান্সার সংক্রমণ একটা নিছকই মামুলি ঘটনা নয়। একটা কারণহীন পরিণতি নয়। আমরা এমন একটা আর্থসামাজিক পরিবেশের মধ্যে আছি, যেখানে প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন খাদ্য পানীয়ের মাধ্যমে আমাদের শরীরে ক্যান্সার-জনক রাসায়নিক উপাদান ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কৃষি উৎপাদনে, ফলের ঝুড়িতে, নরম পানীয়তে, নেশার সামগ্রীতে। দিচ্ছে সেই কর্পোরেট সংস্থাগুলি। সেই তথ্যগুলো যে ডাক্তার দাশগুপ্ত জানেন না তা নয়। সারা পৃথিবীতে যে ক্যান্সার ব্যাপক হারে বেড়ে চলেছে, তার পেছনে গত কয়েক দশকে এই খাদ্য পানীয় এবং নেশার বিভিন্ন সামগ্রীর কী বিপুল অবদান তা নিশ্চয়ই তাঁর অজানা নয়। অথচ, কর্পোরেট সংস্থার বিরুদ্ধে এত ক্ষোভ জমে থাকা সত্ত্বেও তাঁর এই বিশদ আলোচনায় সেই বিষয়টি এক ছটাক জায়গাও পেল না। এ কি নিতান্তই মনের ভুল? নাকি, তিনিও এক্ষেত্রে এক অন্য খণ্ডতাবাদী চিন্তার শিকার হয়ে গেলেন?
তবে আরও একটা জিনিস আমাদের ভাবায়। এমন সম্ভাবনাও আমরা মন থেকে সরিয়ে রাখতে পারি না যে এক অবিমিশ্র মানবিক অনুভূতি নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা করতে করতে আর তাদের শেষ পর্যন্ত করুণ হৃদয়ভেদী একমুখী পরিণতি দেখতে দেখতে তিনি এক রকম মানসিক বিষন্নতায় আচ্ছন্ন হয়েছেন। তখন তাঁকে, মনস্তত্ত্ববিদ সিগমুন্ড ফ্রয়েডের ভাষায়, তার কবল থেকে সাময়িক অব্যাহতি পাওয়ার আশায় এই বিষন্ন হতাশা থেকে উত্তরণ (sublimation)-এর পথ খুঁজতে হয়েছে। সাধারণ মানুষ যেমন সহজেই এই সব ক্ষেত্রে ঈশ্বরের লীলাখেলা ধরে নিয়ে, “ঠাকুর, এ তুমি কী করলে” বলে, সান্ত্বনা পায়, তিনি তো আর ততটা অবৈজ্ঞানিক সরল বিশ্বাসে স্থির হতে পারেন না। তাঁর একটু মননশীল পোতাশ্রয়ের দরকার হয়। খণ্ডতাবাদ, ডারউইন, বিবর্তনবাদ, জিনতত্ত্ব, চিকিৎসা শাস্ত্র, ইত্যাদি আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন উপচারের বিরুদ্ধে এই বিষোদ্গার হয়ত সেই উত্তরণের মায়া-সোপান হয়ে থাকতেও পারে।
অবশ্য এ আমাদের নিছকই অনুমান। ভুলও হতে পারে। কিন্তু আমরা মনেপ্রাণে চাই, এই অনুমান যেন ভুল না হয়!
শেষ কথা
পরিশেষে একটি সতর্কবাণী। আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আজ এক সভ্যতা ধ্বংসকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ। অর্থনীতিতে বাজারসর্বস্বতা ভোগবাদ পণ্যায়ন ও দুরাচার, রাজনীতিতে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ভ্রষ্টাচার ও পর্নায়ন, ব্যবসার নামে দ্রুত বিপুল মুনাফার লোভে শিক্ষা স্বাস্থ্য নিয়ে মানুষের জীবন জীবিকা নিয়ে চূড়ান্ত নির্মমতা, পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস―ইত্যাদি তারই পরিচয়। কিন্তু পাছে সারা বিশ্বের আম জনসাধারণ তাদের এই শয়তান-স্বরূপ ধরে ফেলে, তাই তাকে নানা রকম ক্যামোফ্লেজ ধারণ করতে হয়, ভুল উপচারকে মানুষের সামনে শত্রু সাজিয়ে এগিয়ে দিতে হয়। এই জন্যই সে কখনও জনসংখ্যা, কখনও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কখনও ধর্মবোধের হ্রাস, কখনও গরুর মাংস―ইত্যাদিকে এই সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির কারণ হিসাবে মানুষকে চেনাতে চেষ্টা করতে থাকে। আর জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতে যে সমস্ত চিন্তাশীল মানুষ না জেনেই এই জাতীয় কিছু ভ্রান্ত ধারণার বশে খণ্ড দৃষ্টিতে আংশিক জ্ঞানের ভিত্তিতে এই ধরনের তত্ত্ব চর্চা করে থাকেন, তাঁদেরই মতবাদকে ওরা “অখণ্ড” “অখণ্ড” বলে নানা ভাবে প্রচারের আলোয় এনে জনমনে উচ্চকিত করে দেয়। প্রবন্ধ বইপত্র বের করে দেয়, সেমিনার আলোচনাসভা কর্মশালা সম্মেলনের আয়োজন করতে আর্থিক ও অন্যান্যভাবে সাহায্য করে। আপাত আকর্ষণকারী কিছু কথার আড়ালে তাঁরা না জেনে না বুঝেই এই বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর স্বার্থে কাজ করে যেতে থাকেন। দুটো জায়গায় (অত্যন্ত সততার সাথে) হয়ত তাঁরা সমালোচনা করেন, কিন্তু আসল আসল জায়গাগুলোতে নিজেদের অজ্ঞাতসারে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে এদের বাঁচিয়ে যেতে থাকেন। মানুষ তাঁদের মতো জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের কথায় প্রভাবিত হয়ে ভুল জায়গায় শত্রু খুঁজতে ও আঘাত করতে থাকে।
এবার বোধ হয় সময় হয়েছে আমাদের সাবধান হওয়ার। ডারউইনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে এক সত্যকারের অখণ্ড দৃষ্টিতে বোঝার। ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের ব্যাপক অপপ্রয়োগ হয়ে চলেছে। কিছু ক্ষেত্রে ভুল বুঝে। ভুলভাবে বুঝে। আর বহু ক্ষেত্রেই সচেতনভাবে, শাসক শ্রেণির নিবিড় স্বার্থের কথা মাথায় রেখে। সুতরাং ওদের এগিয়ে দেওয়া জুতোয় পা গলানোর আগে দেখে নিন, ওটা সত্যিই আপনার পায়ের মাপের জুতো কিনা! ওটাই আপনার লাগবে কিনা!!
তথ্যসূত্র
স্থবির দাশগুপ্ত (২০১৫), “সরকারি স্বাস্থ্য-পরিষেবার বিকল্প কি করপোরেট?”; শ্রমজীবীভাষা, ৫ম বর্ষ দশম সংখ্যা (১ জুলাই ২০১৫)
স্থবির দাশগুপ্ত (২০০৯), “ডারউইন, আধুনিক জীববিদ্যা ও ক্যানসার”; বঙ্গদর্শন, জানুয়ারি ২০০৮-ডিসেম্বর ২০০৯।
Woese, C. R.; Kandler, O. & Wheelis, M. (1990), “Towards a natural system of organisms: proposal for the domains Archaea, Bacteria, and Eucarya”; Proceedings of the National Academy of Science, USA, 87 (12): 4576–79.
Barlow, Nora (ed. 1993), The Autobiography of Charles Darwin; Norton and Co., New York.
Cavalier-Smith, T. (2004), “Only six kingdoms of life”; Proceedings of the Royal Society of London, B, 271 (1545): 1251–62.
Pierre-François Verhulst (1838). “Notice sur la loique la population poursuitdans son accroissement”. Correspondance mathématique et physique 10: 113–121.
Mukhopadhyay, Ashoke (2003), “Malthus’ Population Theory: An Irony in the Annals of Science”; Breakthrough, Vol. 10 No. 2 (November 2003).
Mukhopadhyay, Ashoke (2012), Darwin’s Theory of Evolution; Bodhoday Mancha, Kolkata.
Wikipedia (2015), https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_evolutionary_history_of_life
Jacob Bronowsky (1989), The Ascent of Man; Futura Publications, London.
Maurice Bloch (2004), Marxism and Anthropology; Routledge and Kegan Paul, London.
Thomson, Keith (1998), “1798: Darwin and Malthus” American Scientist; May-June 1998; Vol. 86 No. 3, 226
“সাধারণের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক, সায়ান্সে ডিগ্রি-ধারী পণ্ডিত এ দেশে বিস্তর আছে যাদের মনের মধ্যে সায়ান্সের জমিনটা তলতলে, তাড়াতাড়ি যা-তা বিশ্বাস করতে তাদের অসাধারণ আগ্রহ, মেকি-সায়ান্সের মন্ত্র পড়িয়ে অন্ধ সংস্কারকে তারা সায়ান্সের জাতে তুলতে কুণ্ঠিত হয় না।”
[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ”; রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড; বিশ্বভারতী, কলকাতা; ২০০০, পৃঃ ৩৪০-৪১]

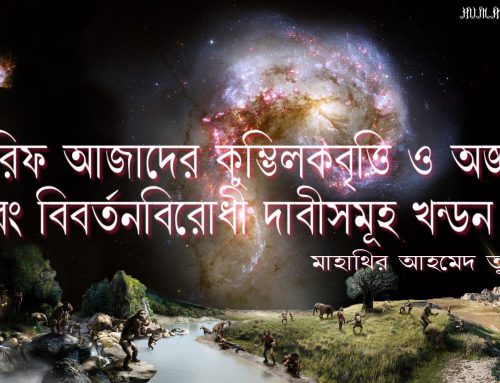

সংগ্রহে রাখলাম, অসংখ্য ধন্যবাদ। ডারউইনের চরিত্র দারুন ভাবে তুলে ধরেছেন।
আপনাদের ধন্যবাদ!
ধন্যবাদ। আপনার আরো লেখা চাই।
অসাধারণ!! বললেও কম বলা হয়। আমার ক্ষুদ্র জীবনে এরকম বিশ্লেষণধর্মী লেখা খুব কমই পড়েছি।
লেখাটি পড়ার পর মনে হল যে এত দ্রুত শেষ হয়ে গেল! আরো থাকলে ত নিজেকে আরো সমৃদ্ধ করতে পারতাম।
আর বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কর্পোরেট সংস্থাগুলো এমন সর্বগ্রাসী আয়োজন করে রেখেছে যে সবচেয়ে প্রথাবিরোধী, উদার, আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষেরাও শেষ বিচারে কর্পোরেট পুঁজিরই সেবা দাসত্ব করে যায়।
ধন্যবাদ ঋষভ। তবে ভুল বা ত্রুটি নজরে এলেও নির্দ্বিধায় জানাবেন।
মন্ত্রমুগ্ধের মত পড়ে গেলাম, অসাধারন একটা লেখা। একটা লেখার সমালোচনায় এত বিস্তৃত আর গভীর চিন্তা আর মননের উদাহরন আমার মনে হয় খুব বেশি নেই।