আমরা কারা, আমাদের অস্তিত্বের অর্থ কী, সব কিছুর শুরু কীভাবে! ঈশ্বরের ধারণা কোত্থেকে এলো!
God Hypothesis নিয়ে প্রাচীন যুগ থেকে দর্শন, ধর্ম এবং ২১শ শতকে বিজ্ঞানীরা যেমন রিচার্ড ডকিন্স, স্টিফেন হকিং, লরেন্স ক্রাউস, মিচিও কাকু অনেক লেখাই লিখেছেন, তবু ইচ্ছে হলো নিজের মত করে আজকে এই বিষয়েই কিছু লিখতে। এই বিষয়ে মুক্তমনা ব্লগে আমার ধারণা নিয়ে আগে লিখেছি যে কীভাবে ধর্মগুলো আসলে সত্যহীন, শান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। দর্শনের জগতে আমরা নীৎশের পরবর্তী লেখাগুলো দেখলে বুঝতে পারি কীভাবে পশ্চিমা দার্শনিকরাও ধর্ম বাদ দিয়ে দর্শন চর্চা করা শুরু করেছিলেন। মার্টিন হাইডেগার, জ্যাঁ-পল সার্ত্র বা আলবের কামু-র লেখাগুলো দেখলেই আমরা বুঝতে পারি কীভাবে সংগঠিত ধর্ম ছাড়াই তারা অস্তিত্বের অর্থ নির্মাণ করার চেষ্টা করেছিলেন ।
রিচার্ড ডকিন্স তাঁর বিখ্যাত বই The God Delusion-এ ‘God Hypothesis’ বা ‘ঈশ্বর-ধারণা’কে যুক্তির কষাঘাতে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। তাঁর মতে, মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও বিবর্তনের পেছনে কোনো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপস্থিতি “অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত” । এই প্রসঙ্গে একটা সহজ উদাহরণ দিই—ধরুন আপনার মোবাইল ফোনের স্ক্রিন কাজ করছে না; তখন কি আপনি ভাববেন, কোনো ভূত বা অলৌকিক শক্তি এর জন্য দায়ী? নিশ্চয়ই না। আপনি খুঁজবেন বাস্তব কোনো প্রযুক্তিগত কারণ।
একইভাবে, মহাবিশ্বের জটিলতা ব্যাখ্যা করতে ঈশ্বর নামের অলৌকিক ধারণার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই—এটা ডকিন্সের মূল বক্তব্যের সঙ্গেও সাযুজ্যপূর্ণ। বইটি প্রকাশের পর কয়েক মিলিয়ন কপি বিক্রি হয় এবং তা বিশ্বজুড়ে আলোচনার ঝড় তোলে। এই বই শুধু ঈশ্বরে অবিশ্বাস গড়ে তোলে না, বরং যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিকে নতুনভাবে চিন্তা করার আহ্বান জানায়।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যা ডকিন্স তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন, তা হলো—আমাদের মানব-মস্তিষ্কের চেতনা বা ‘consciousness’ গঠিত হতে কোটি কোটি বছর সময় লেগেছে, এবং তা ঘটেছে ধারাবাহিক বিবর্তনের মাধ্যমে। ডকিন্সের যুক্তি হলো, যদি ঈশ্বর নামে কোনো সত্তা সত্যিই থেকে থাকেন যিনি অতিমানবিক চেতনা বা জ্ঞান রাখেন, তবে তাকেও একইভাবে কোনো না কোনো বিবর্তনীয় প্রক্রিয়া পেরিয়ে এই উচ্চচেতনার স্তরে পৌঁছাতে হয়েছে—তাঁর অস্তিত্ব হঠাৎ করে, চিরন্তনভাবে, চেতনা-সহকারে “হয়ে যাওয়া” অসম্ভব।
এই ভাবনাটিকে আমরা স্টিফেন হকিং-এর The Grand Design বইয়ের ধারণার সঙ্গেও সংযুক্ত করে দেখতে পারি, যেখানে তিনি M-Theory-এর মাধ্যমে মহাবিশ্বের জন্মের ব্যাখ্যা দেন এবং multiverse বা বহু-বিশ্ব থাকার সম্ভাবনার কথাও বলেন। তাঁর মতে, কণার অনিশ্চয়তাজনিত চঞ্চলতা (quantum fluctuation) থেকেই শূন্যতার (quantum vacuum) ভেতরে অবিরতভাবে নতুন নতুন মহাবিশ্ব জন্ম নিচ্ছে—শূন্য থেকেই সব কিছু সৃষ্টি হচ্ছে।
সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবলে, ‘God Hypothesis’-এর ঈশ্বরকেও যদি আমরা ধরে নিই কোনোভাবে বাস্তব, তাহলে তাকেও সেই “নাথিংনেস” বা শূন্যতার ভেতর থেকেই জন্ম নিতে হবে, এবং পরে বিবর্তনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তাঁকে পৌঁছাতে হবে চেতনার উচ্চ শিখরে। এর বাইরে কোনো অলৌকিক শর্টকাট বা ব্যতিক্রমী ব্যাখ্যা যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞান কিংবা দার্শনিক বিচার গ্রহণ করতে চায় না।
এখন আমার মূল বক্তব্য হলো—অতীতের ধর্মীয় নেতারা কিংবা দার্শনিকরা আসলে এই জটিল প্রশ্নগুলোর কোনো পরিপূর্ণ উত্তর খুঁজে পাননি। তাঁদের মস্তিষ্ক তখনো বিবর্তনের যে স্তরে ছিল, তা দিয়ে তাঁরা ঈশ্বরের ধারণাকে ন্যায়সঙ্গত করতে চেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু প্রকৃত উত্তর তাঁদের জানা ছিল না—এবং অনেক সময় তাঁরা নিজেরাও তাঁদের চিন্তার সীমাবদ্ধতা টের পেয়েছিলেন।
ইসলামে একটি হাদিস আছে—যেখানে বলা হয়েছে, যদি কোনো মুসলমানের মনে প্রশ্ন জাগে: “আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?”—তবে সে যেন বলে, “আমি শয়তানের কুমন্ত্রণার থেকে আশ্রয় চাই।” যুক্তি এড়িয়ে যাবার এই হাদিস নিজেই বলে দেয়—এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নবী বা ধর্মীয় দার্শনিকদের কাছেও ছিল না। কারণ, আসলে এখানে কোনো শয়তান নেই—এই প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবেই জাগে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধান থেকে, এবং এই প্রশ্নই তাঁদের জন্য ছিল অস্বস্তির কারণ।
সেই কারণেই, ‘আইডিয়াল’ বা প্রকৃত দর্শন কেবল ধর্মীয় চিন্তার গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং, নীৎশে-র আগ পর্যন্ত দর্শন নিজের ভেতরেই উত্তরের সন্ধান চালিয়ে গেছে, কিন্তু চার্লস ডারউইনের On the Origin of Species প্রকাশের পর দর্শনের গতিপথ বদলে যায়। ডারউইনের এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পরেই নীৎশে তাঁর বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থগুলো লিখেছিলেন—যার মধ্যে তিনি “ঈশ্বরের মৃত্যু” ঘোষণা করে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিলেন নিজের অর্থ নিজেই নির্মাণ করতে।
আপনি বিজ্ঞানকে পছন্দ করুন বা না করুন, বিজ্ঞান সেই সব প্রশ্নের একটা পরোক্ষ কিন্তু ক্রমশ সুস্পষ্ট উত্তর দিতে শুরু করেছিল—যেগুলো হাজার বছর ধরে দর্শন ও ধর্মীয় চিন্তা ঘিরে রেখেছিল। সত্যটা তিতা লাগতে পারে, কিন্তু এটা মেনে নেওয়াই আমাদের নিরবচ্ছিন্ন বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি দেয়।
আমাদের সভ্যতা আজ যে অগ্রগতির অবস্থানে পৌঁছেছে, তার মূল কারণ এই সত্য-মেনে-নেওয়ার মানসিকতা। আমরা যদি সম্পূর্ণ ধর্মনির্ভর পৃথিবীতে বাস করতাম, তাহলে প্রতিটি পদক্ষেপেই অগ্রগতির পথে বাধাপ্রাপ্ত হতো। বিজ্ঞান ও মুক্তচিন্তার ওপর নির্ভর করেই মানব সভ্যতা আজ এই দূর পর্যন্ত এসেছে।
মহাবিশ্ব তার প্রাথমিক ভারসাম্য বা সাযুজ্য (symmetry) বিগ ব্যাং এবং পরবর্তীকালের ইনফ্লেশন বা তাৎক্ষণিক প্রসারণের মাধ্যমে ভেঙে ফেলার পর থেকেই, বিশৃঙ্খলা—অথবা পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় ‘এনট্রপি’—ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এই বিশৃঙ্খলার বৃদ্ধি কোনো দুর্ঘটনা নয়, বরং এটি মহাবিশ্বের অবধারিত গন্তব্য।
এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কোটি কোটি বছর পরে এক সময় মহাবিশ্ব এমন এক অবস্থা অর্জন করবে—যেখানে সবকিছু তাপগতীয় ভারসাম্যে পৌঁছে যাবে। যেভাবে আমরা গরম ও ঠান্ডা পানির মিশ্রণে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা দেখতে পাই, সেভাবেই মহাবিশ্বের প্রতিটি বিন্দু ধীরে ধীরে একটি অভিন্ন, শীতল, শান্ত তাপমাত্রায় পৌঁছাবে। এই অবস্থা কোনো বিস্ফোরণ বা পতনের নয়—বরং নিঃশব্দ, চূড়ান্ত শান্তির, কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত থাকবে তীব্র এক মৃত্যু-সঞ্জাত শূন্যতা।
এই পরিণতিকে বলা হয় heat death—যেখানে কোনো কার্যকরী শক্তি বিনিময় আর সম্ভব হবে না, কোনো কাঠামো থাকবে না, এবং চেতনা কিংবা প্রাণের কোনো রূপ টিকে থাকার পরিবেশ আর থাকবে না। এই পরিণতি, যদিও কোটি কোটি বছর দূরের ভবিষ্যৎ, তবুও এর দিকে আমাদের মহাবিশ্ব প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলেছে—বিচ্ছিন্নতা ও নিরবতার এক অনন্ত সমুদ্রে।
মানবসভ্যতা হাজার বছর ধরে এমন কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজে এসেছে—এই মহাবিশ্ব কেন আছে, আমরা কারা, আমাদের অস্তিত্বের অর্থ কী, সব কিছুর শুরু কীভাবে, এবং আদৌ কি কোনো পরিণতি আছে। ধর্ম এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে চেয়েছে অলৌকিক বিশ্বাস ও কর্তৃত্বের ওপর নির্ভর করে। দর্শন চেষ্টা করেছে যুক্তি ও চেতনার ভেতর দিয়ে এগোতে, কিন্তু বহুক্ষেত্রেই সেই উত্তরগুলো বাস্তব পরীক্ষার জগতে উত্তীর্ণ হয়নি।
অন্যদিকে, বিজ্ঞান আজ একের পর এক সেই প্রশ্নগুলোর বাস্তবসম্মত, পরীক্ষণযোগ্য উত্তর দিতে শুরু করেছে। মহাবিশ্বের উৎপত্তি, গঠন, বিকাশ ও ভবিষ্যৎ নিয়ে এখন আমাদের জ্ঞান কল্পনার স্তর ছাড়িয়ে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ভিত্তিতে দাঁড়িয়েছে। আমরা বুঝতে শিখেছি যে, বিশৃঙ্খলা, জটিলতা, এমনকি চেতনার উৎপত্তিও প্রকৃতির নিয়ম মেনে গড়ে উঠেছে—তাতে কোনো অলৌকিক ব্যাখ্যার দরকার নেই।
এই জ্ঞান অবশ্যই চ্যালেঞ্জিং, কারণ এটি বহু প্রাচীন বিশ্বাস ও আত্মতৃপ্তির ধারণাকে ভেঙে দেয়। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মধ্যেই নিহিত আছে সভ্যতার অগ্রগতি। যে উত্তর এক সময় ধর্ম আর দর্শন দিতে পারেনি, বিজ্ঞান সেই উত্তর খুঁজে এনে আমাদের বাস্তবতাকে আরও গভীরভাবে বুঝতে শেখাচ্ছে।
আজ বিজ্ঞান শুধু বস্তুগত জগত নয়, অস্তিত্বগত প্রশ্নের দিক থেকেও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শক।
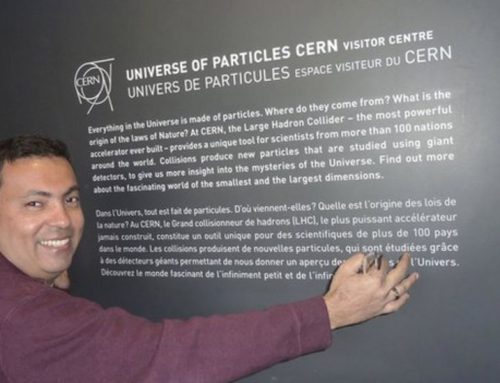
পড়া,জ্ঞান অর্জন করে অভিজ্ঞতা লাভ করা।