জীবনানন্দ দাশের “ঝরাপালক” কাব্যগ্রন্থে “অস্তচাঁদ” কবিতার দুটি পংক্তি এই রকমঃ
চুরি করে পিয়েছিনু ক্রীতদাসী বালিকার যৌবনের মধু!
সম্রাজ্ঞীর নির্দয় আঁখির দর্প বিদ্রূপ ভুলিয়া
জীবনানন্দ দাশের কবিতা প’ড়ে আমাদের মনে হয়, তিনি অতি ছোট্ট ও তুচ্ছ একটি কীটের হৃদয়ের ব্যথাও উপলব্ধি করতে পারেন। অনুভব করতে পারেন একটি ছোট্ট পাতা, একটি ক্ষুদ্র সবুজ ঘাসের বেদনাও। একটি ইঁদুর, একটি প্যাঁচার মনও তিনি নিরীক্ষণ করেন। যোজন-যোজন দূরের সুবিশাল জ্বলন্ত নক্ষত্রদের মর্মজ্বালা পর্যন্ত তিনি অনুধাবন করেন। শংখচিল, শালিক, হিজলের ডাল পাতা ও পাতা নড়ার নিঃশ্বাসের সাথে একাকার হয়ে তিনি এদের মনোজগতের গভীরের খবর নিতে ব্যগ্র হয়ে ওঠেন।
কীটের হৃদয়ের ব্যথা অনুভব করার মতো হৃদয় যে কবি ধারণ করেন সে কবিও কি ক্রীতদাসীদের সম্ভোগের বস্তুই মনে করেন? আবার শুধু দাসীই নয় কিন্তু! তিনি বলেছেন, “ক্রীতদাসী”। তার মানে তিনি দাসপ্রথায় পুরোই সমর্থন করতেন! হতদরিদ্র অসহায় নর-নারীদের ক্ষমতাশালীরা ধরে ধরে লোহার শেকলে বেঁধে হাটে-বাজারে নিয়ে বিক্রি করবে। তাদের কিনে নেবে সামর্থবানেরা। তাদের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করবে অকথ্য। তারপর ক্রীতদাসীদের ওপর যৌন নিপীড়ণ চালাবে ক্রেতা পুরুষ-মালিকপক্ষ। কীটের হৃদয়ের ব্যথা অনুভবকারী কবি জীবনানন্দ দাশের হৃদয়ের গভীরেও সেই একই কামনা বাসনা জেগে ওঠে – চুরি করে ক্রীতদাসী বালিকার যৌবনের মধু পান করার!
ঘাস লতা পাতা পাখি ফুল চিল প্যাঁচা ইত্যাদির প্রতি তাঁর সমবেদনা সহমর্মিতা ও প্রেমের শেষ নেই। কিন্তু ক্রীতদাসীর প্রতি তাঁর কোনো সমবেদনা সহমর্মিতা নেই, নেই কোনো প্রেমও। তিনি যদি কোনো দাসীর প্রেম পড়তেন তাহলে তো কথাই ছিল না। কিন্তু আমরা খুঁজে পাই না তাঁর কোনো রচনায় এমন সংবাদ। ক্রীতদাসী বালিকার যৌনবের মধু পান করার কামনা-বাসনা জাগে তাঁর শরীরে। তাও আবার চুরি করে, সম্রাজ্ঞীর নির্দয় আঁখির বিদ্রূপ উপেক্ষা করে। চুরি করে ক্রীতদাসী-সম্ভোগের মুহূর্তে সম্রাজ্ঞী দেখে ফেললে তাঁকে দৃষ্টি-কটাক্ষ করবেনই, এটাও তিনি জানেন। বেপরোয়া, ক্রীতদাসীর যৌবনের মধু-পিয়াসী কবি তা উপেক্ষা করেই ক্রীতদাসী বালিকার যৌবনের মধু পান করার খায়েস ব্যক্ত করেন।
পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে যৌন সম্পর্ক না হয়ে যদি শুধু একপক্ষের ইচ্ছায় হয় তাকে ধর্ষণ বলা হয়। কবি এখানে তা-ই করতে ব্যগ্র। ক্রীতদাসীটির যৌবনের মধু কবিকে পান করানোর ইচ্ছা আছে কিনা, তার সম্মতি আছে কিনা, এ ব্যাপারে কবির কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই।
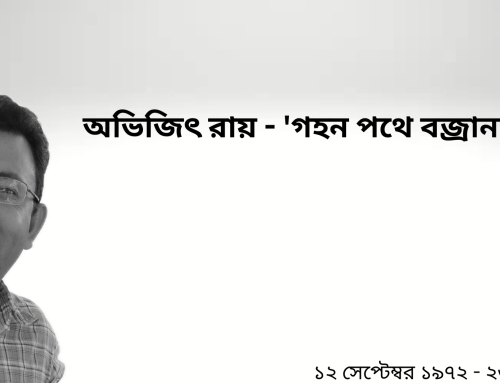
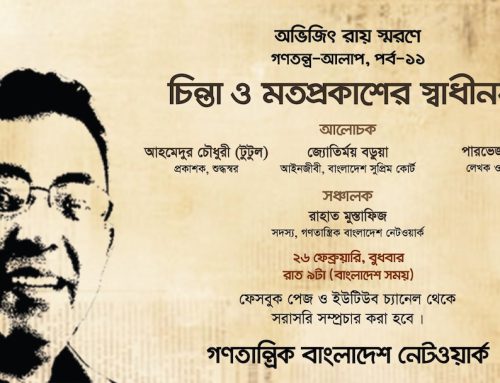
পুরো “অস্তচাঁদ” কবিতাটা:
ভালোবাসিয়াছি আমি অস্তচাঁদ, -ক্লান্ত শেষপ্রহরের শশী!
-অঘোর ঘুমের ঘোরে ঢলে যবে কালো নদী-ঢেউয়ের কলসী,
নিঝ্ঝুম বিছানার পরে
মেঘবৌ’র খোঁপাখসা জোছনাফুল চুপে চুপে ঝরে,-
চেয়ে থাকি চোখ তুলে’-যেন মোর পলাতকা প্রিয়া
মেঘের ঘোমটা তুলে’ প্রেত-চাঁদে সচকিতে ওঠে শিহরিয়া!
সে যেন দেখেছে মোরে জন্মে জন্মে ফিরে’ ফিরে’ ফিরে’
মাঠে ঘাটে একা একা, -বুনোহাঁস-জোনাকির ভিড়ে!
দুশ্চর দেউলে কোন্-কোন্ যক্ষ-প্রাসাদের তটে,
দূর উর-ব্যাবিলোন-মিশরের মরুভূ-সঙ্কটে,
কোথা পিরামিড তলে, ঈসিসের বেদিকার মূলে,
কেউটের মতো নীলা যেইখানে ফণা তুলে উঠিয়াছে ফুলে,
কোন্ মনভুলানিয়া পথচাওয়া দুলালীর মনে
আমারে দেখেছে জোছনা-চোর চোখে-অলস নয়নে!
আমারে দেখেছে সে যে আসরীয় সম্রাটের বেশে
প্রাসাদ-অলিন্দে যবে মহিমায় দাঁড়ায়েছি এসে-
হাতে তার হাত, পায়ে হাতিয়ার রাখি
কুমারীর পানে আমি তুলিয়াছি আনন্দের আরক্তিম আঁখি!
ভোরগেলাসের সুরা-তহুরা, ক’রেছি মোরা চুপে চুপে পান,
চকোরজুড়ির মতো কুহরিয়া গাহিয়াছি চাঁদিনীর গান!
পেয়ালায়-পায়েলায় সেই নিশি হয় নি উতলা,
নীল নিচোলের কোলে নাচে নাই আকাশের তলা!
নটীরা ঘুমায়েছিল পুরে পুরে, ঘুমের রাজবধূ-
চুরি করে পিয়েছিনু ক্রীতদাসী বালিকার যৌবনের মধু!
সম্রাজ্ঞীর নির্দয় আঁখির দর্প বিদ্রূপ ভুলিয়া
কৃষ্ণাতিথি-চাঁদিনীর তলে আমি ষোড়শীর উরু পরশিয়া
লভেছিনু উল্লাস-উতরোল!-আজ পড়ে মনে
সাধ-বিষাদের খেদ কত জন্মজন্মান্তের, রাতের নির্জনে!
আমি ছিনু ‘ক্রবেদুর’ কোন্ দূর ‘প্রভেন্স্’-প্রান্তরে!
-দেউলিয়া পায়দল্-অগোচর মনচোর-মানিনীর তরে
সারেঙের সুর মোর এমনি উদাস রাত্রে উঠিত ঝঙ্কারি!
আঙুরতলায় ঘেরা ঘুমঘোর ঘরখানা ছাড়ি
ঘুঘুর পাখনা মেলি মোর পানে আসিল পিয়ারা;
মেঘের ময়ূরপাখে জেগেছিল এলোমেলো তারা!
-‘অলিভ’ পাতার ফাঁকে চুন চোখে চেয়েছিল চাঁদ,
মিলননিশার শেষে-বৃশ্চিক, গোক্ষুরাফণা, বিষের বিস্বাদ!
স্পেইনের ‘সিয়েরা’য় ছিনু আমি দস্যু-অশ্বারোহী-
নির্মম-কৃতান্ত-কাল-তবু কী যে কাতর, বিরহী!
কোন্ রাজনন্দিনীর ঠোঁটে আমি এঁকেছিনু বর্বর চুম্বন!
অন্দরে পশিয়াছিনু অবেলার ঝড়ের মতন!
তখন রতনশেজে গিয়েছিল নিভে মধুরাতি,
নীল জানালার পাশে-ভাঙা হাটে-চাঁদের বেসাতি।
চুপে চুপে মুখে কার পড়েছিনু ঝুঁকে!
ব্যাধের মতন আমি টেনেছিনু বুকে
কোন্ ভীরু কপোতীর উড়ু-উড়ু ডানা!
-কালো মেঘে কেঁদেছিল অস্তচাঁদ-আলোর মোহানা!
বাংলার মাঠে ঘাটে ফিরেছিনু বেণু হাতে একা,
গঙ্গার তীরে কবে কার সাথে হয়েছিল দেখা!
‘ফুলটি ফুটিলে চাঁদিনী উঠিলে’ এমনই রূপালি রাতে
কদমতলায় দাঁড়াতাম গিয়ে বাঁশের বাঁশিটি হাতে!
অপরাজিতার ঝাড়ে- নদীপারে কিশোরী লুকায়ে বুঝি!-
মদনমোহন নয়ন আমার পেয়েছিল তারে খুঁজি!
তারই লাগি বেঁধেছিনু বাঁকা চুলে ময়ূরপাখার চূড়া,
তাহারই লাগিয়া শুঁড়ি সেজেছিনু-ঢেলে দিয়েছিনু সুরা!
তাহারই নধর অধর নিঙাড়ি উথলিল বুকে মধু,
জোনাকির সাথে ভেসে শেষরাতে দাঁড়াতাম দোরে বঁধু!
মনে পড়ে কি তা!-চাঁদ জানে যাহা, জানে যা কৃষ্ণাতিথির শশী,
বুকের আগুনে খুন চড়ে-মুখ চুন হয়ে যায় একেলা বসি!
আমি কবিতা খুব কম পড়ি, কবিতা পাঠক বলতে যা বলা যায়, আমি কিছুতেই তা নই। আমার বক্তব্য তাই কবিতা পাঠকদের বিশ্লেষনী ক্ষমতার ধারে কাছেও নয়।
জীবনানন্দের কবিতার একটা ব্যাপার আমি খেয়াল করেছি, তিনি উপমা এবং স্ট্রাইকিং শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন একেবারেই লাগামছাড়া। অনেকটা বর্তমানের উত্তরাধুনিক কবিতাম মত, আচমকা শব্দের ব্যবহার। কবিতার সারল্য থেকে সরে গিয়ে ব্যতিক্রমী কিছু তৈরীর প্রয়োজনে। এই “ক্রীতদাসী” শব্দটা ব্যবহারের সময় জীবনানন্দ দাসপ্রথা জাতীয় কিছু আদৌ মাথায় রেখেছিলেন কিনা, আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। শুনতে অন্যরকম লাগে, মাথায় আটকে যায়, এমন কিছু তৈরীই ভদ্রলোকের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো।
একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই:
“সেইখানে যুথচারী কয়েকটি নারী
ঘনিষ্ঠ চাঁদের নিচে চোখ আর চুলের সংকেতে
মেধাবিনী; দেশ আর বিদেশের পুরুষেরা
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের রক্তে আর উঠিবে না মেতে। ”
এখানে খেয়াল করে দেখুন, “যুথচারী কয়েকটি নারী”
আবার:
“তবুও পেঁচা জাগে;
গলিত স্থবির ব্যাঙ আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে।
আরেকটি প্রভাতের ইশারায় – অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে
টের পাই যুথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা
মশা তার অন্ধকার সংগ্রামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাসে”
এখানে ফের এসেছে “যুথচারী” শব্দ। যুথচারী নামক শব্দ বাংলায় তখন ছিলো না। “যুথ” শব্দটা ব্যবহৃত হতো সমষ্টি অর্থে, যেমন হস্তিযুথ বা যুথবদ্ধ। এবারে জীবনানন্দ একত্রে চরে বেড়ানো অর্থে প্রথম যুথচারী শব্দ ব্যবহার করেন সম্ভবত আমার দেয়া এই প্রথম কবিতাংশে, “যুথচারী কয়েকটি নারী”, যেটা পরে তার মনে ধরে যায়। যেই কারণে সামষ্টিক আঁধার বোঝাতে তিনি পরে “যুথচারী আঁধার” বলেছেন, বাংলা অর্থবাচক ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে এই যুথচারী আঁধার একেবারেই খাপছাড়া, “যুথবদ্ধ আঁধার” হলে সঠিক হতো। কিন্তু জীবনানন্দ কোনদিনও এভাবে ভাবেননি , কবিতা লেখার সময় তিনি যেভাবে যেই শব্দ মনে এসেছে সেইভাবে শব্দ ব্যবহারের একটা ধারা প্রচলন করেছেন। কবি কবিতা লিখবে, শুধুই ভাব প্রকাশ করবে, অর্থ নিয়ে মাথাব্যাথা থাকবে না, সেই মাথাব্যাথা পাঠকের, বাংলায় এই ধারার পাইওনিয়ার জীবনানন্দ।
তাই দাসপ্রথা সমর্থন করতেন জাতীয় অভিযোগ সম্ভবত জীবনানন্দের প্রতি অবিচার করা হয় সম্ভবত। উনি নিজেই জানতেন না উনি কি লিখছেন, এমনটাই আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস
সম্ভবত, কবির কল্পচিত্র অনুধাবনে আপনার আবাহনী অনুসন্ধান প্রকল্প ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। তিনি সামষ্টিক আঁধারের চলিষ্ণুতা বুঝাইতে যুথচারী শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। আঁধারের এ চলিষ্ণুতার প্রমাণ মিলে “নিরুদ্দেশে” শব্দটির ব্যবহারে। সুতরাং, অর্থবাচক ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে এই যুথচারী আঁধার যে একেবারেই খাপছাড়া তাহা বলা যায় না।
নীলাঞ্জনা আপনার লেখা ভালো লাগে। বরাবরেই মুক্তমনায় ঢুকে আপনার লেখা না পড়ে থাকতে পারিনা। অদ্ভুত সুন্দর লেখেন আপনি। জীবনান্দদাস আমারও প্রিয়তম কবিদের একজন। তবে কবিতার কয়েকটা লাইনেই কি কবিকে ক্রীতদাস প্রথার সমর্থ ভাবা যায়? এটা হয়তো বলাই যায় পুরুষ মানসিকতায় অনেক সময়ই নারীকে বাসনার বস্তু মনে করার প্রবনতা বেরিয়েই আসে, সামাজিক সংস্কার অনেক গীভরে পৌঁছে যায়। সেই সংস্কার থেকে অনেকে একটু একটু করে বেরিয়ে আসেন। জীবনানন্দের পরবর্তী কবিতা গুলোর মধ্যে এই নির্জলা নারী সম্ভোগের বাসনা কতখানি প্রকট এটাও দেখার প্রয়োজন আছে। এমন কি হতে পারে জীবনান্দদাস এই প্রথম পর্যায়ের কাব্য গ্রন্থ গুলোয় কিছুটা দিশেহারা ছিলেন, স্বকীয় কণ্ঠস্বর তখনও খুঁজে পাননি? ভালো থাকবেন, আরো লিখুন।
পুরো কবিতাটা দেয়া যাবে?
লেখাটা যেন হঠাৎই থেমে গেছে। আরও একটু সম্প্রপ্সারণ করা যেতো। যাহোক, দৃষ্টিভঙ্গিটিতে ভিন্নতা আছে।
সত্যি বলেছেন, দিদি। ছোট লেখা। আরেকটু বাড়ানো যেতো অবশ্য। ধব্যবাদ আপনার মন্তব্যের জন্য।
অনেকদিন পরে পোস্ট দিলাম, তা সত্য। তবে মুক্তমনায় নিত্যই আসি, দাদা। কবিতাটার কিছু অংশ দিয়ে দিলাম এখানে;
আমারে দেখেছে সে যে আসীরীয় সম্রাটের বেশে
প্রাসাদ-অলিন্দে যবে মহিমায় দাঁড়ায়েছি এসে,
হাতে তার হাত, পায়ে হাতিয়ার রাখি
কুমারীর পানে আমি তুলিয়াছি আনন্দের আরক্তিম আঁখি!
ভোরগেলাসের সুরা, তহুরা, করেছি মোরা চুপে চুপে পান,
চকোরজুড়ির মতো কুহরিয়া গাহিয়াছি চাঁদনীর গান!
পেয়ালায়-পায়েলায় সেই নিশি হয়নি উতলা,
নীল নিচোলের কোলে নাচে নাই আকাশের তলা।
নটীরা ঘুমায়েছিল পুরে পুরে, ঘুমে রাজবধূ,
চুরি করে পয়েছিনু ক্রীতদাসী বালিকার যৌবনের মধু!
সম্রাজ্ঞীর নির্দয় আঁখির দর্প বিদ্রূপ ভুলিয়া
অনেকদিন পরে নীলাঞ্জনা যে 🙂
অন্য চোখে লেখা ! “অস্তচাঁদ” কবিতা’ টা এখানে দিয়ে দিলে হতো । ভিন্নদৃষ্টি অন্য মতের ব্যপারটা একটু বুঝা যেত।