অভিজিৎ রায়ের শেষ বই দুটির একটি ছিল শূন্য থেকে মহাবিশ্ব যা তিনি মীজান রহমানের সাথে যৌথভাবে লিখেছিলেন। বইটি রচনা এবং নামকরণের ক্ষেত্রে উনারা লরেন্স ক্রাউসের A Universe from Nothing: Why There is Something rather than Nothing দ্বারা নিশ্চিতভাবেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। উনাদের সম্মানেই বইটির বাংলা অনুবাদ শুরু করছি। অনুবাদটা খুব গুরুত্বপূর্ণও; হাজার হোক বইটি সম্পর্কে ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক ইয়ান ম্যাকইউয়ান বলেছেন, “আমরা বিশ্বতত্ত্বের এমন একটি বিপ্লবের সময়ে বাস করছি যা কোপার্নিকাসের শুরু করা বিপ্লবের সমান বিস্ময়কর। এখানে বর্ণীত তার মনোহর, চমৎকার নির্যাসটুকু।” আর রিচার্ড ডকিন্স অতিরঞ্জিত করে হলেও বলেছেন, “যদি অতিপ্রাকৃতবাদের উপর জীববিজ্ঞানের সবচাইতে প্রাণঘাতি ঘা হয়ে থাকে ‘অন দি অরিজিন অফ স্পিসিস’ তবে হয়ত আমরা একসময় ‘আ ইউনিভার্স ফ্রম নাথিং’ কে বিশ্বতত্ত্বের সেইরকম ঘা হিসেবে দেখব।” খুব শীঘ্রই অনুবাদটি শেষ করতে পারব বলে মনে হয় না, তাও শুরু করে রাখলাম। পাদটীকাগুলো আমার নিজের।
উপক্রমণিকা
“Dream or nightmare, we have to live our experience as it is, and we have to live it awake. We live in a world which is penetrated through and through by science and which is both whole and real. We cannot turn it into a game simply by taking sides.”
— জেকব ব্রোনফ্স্কি (১৯০৮–১৯৭৪)
প্রথমেই খোলাখুলিভাবে বলে নিতে চাই যে, সৃষ্টির জন্য সৃষ্টিকর্তা লাগে এই ধারণা যা কি না বিশ্বের প্রতিটি ধর্মের মূলভিত্তি তার প্রতি আমার কোনো সহানুভূতি নেই। প্রতিদিনই সুন্দর ও অলৌকিক কিছু না কিছু হঠাৎ করে আবির্ভূত হয়, শীতের সকালের তুষারফলক থেকে শুরু করে শরতের পড়ন্ত বিকেলের হালকা বৃষ্টি পরবর্তী রোমাঞ্চকর রংধনু পর্যন্ত সবকিছু। অথচ অত্যন্ত মৌলবাদী ছাড়া আর কেউ বলবে না যে, এই প্রত্যেকটি জিনিসই পরম স্নেহ ও যত্নের সাথে, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে একটি স্বর্গীয় বুদ্ধিমত্তা সৃষ্টি করেছে। আসলে, অনেক সাধারণ মানুষ এবং বিজ্ঞানীই পদার্থবিজ্ঞানের সরল, সুন্দর নীতির মাধ্যমে আমাদের এসব ঘটনা ব্যাখ্যা করতে পারার আনন্দের সাথে পরিচিত।
অবশ্যই কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে, এবং অনেকে করেও, “পদার্থবিজ্ঞানের নীতিগুলো কোত্থেকে এসেছে?” এবং অনেকে আরো ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বলে, “এসব নীতি কে তৈরি করেছে?” প্রথম প্রশ্নটির উত্তর কেউ দিতে পারলেও প্রশ্নকারী আবার বলে বসে, “কিন্তু সেটাই বা কোত্থেকে এসেছে?” বা “ওটা কে সৃষ্টি করেছে?” এবং এভাবে চলতেই থাকে।
শেষ পর্যন্ত অনেক চিন্তাশীল মানুষই ‘প্রথম কারণ’ এর আপাত প্রয়োজনীয়তার দিকে ধাবিত হয়—প্লেটো, অ্যাকুইনাস, বা আধুনিক রোমান ক্যাথলিক চার্চ যেমন বলে থাকে—এবং সেই সূত্রে কোনো না কোনো স্বর্গীয় সত্তার অস্তিত্ব ধরে নেয়, যে সত্তা যা কিছু আছে বা থাকবে তার সবকিছুর স্রষ্টা, এবং অনন্তকাল ধরে ও সর্বত্র বিরাজমান। ((এই ‘প্রথম কারণ’ এর ধারণাটি ‘বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তি’ (cosmological argument) নামে পরিচিত যা প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্বে অনেক আলোচিত হয়, এবং যার একটি আধুনিক রিভিউ পাওয়া যাবে স্ট্যানফোর্ড এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ফিলোসফি তে।))
কিন্তু ‘প্রথম কারণ’ আরেকটি প্রশ্ন রেখেই দেয়, “সব সৃষ্টি করল যে জন তারে সৃষ্টি কে করেছে?” ((ক্রাউস লিখেছেন “Who created the creator?” আমি অনুবাদটি করলাম লালনের অনুরূপ প্রশ্নটি উদ্ধৃত করে। লালনের গানটি এরকম:
“সব সৃষ্টি করলো যে জন তারে সৃষ্টি কে করেছে,
সৃষ্টি ছাড়া কি রূপে সে সৃষ্টিকর্তা নাম ধরেছে।
সৃষ্টিকর্তা বলছ যারে লা শরিক হয় কেমন করে,
ভেবে দেখো পূর্বাপরে সৃষ্টি করলেই শরিক আছে।
চন্দ্র সূর্য যে গড়েছে তার খবর কে করেছে,
নীরেতে নিরঞ্জন আছে নীরের জন্ম কে দিয়েছে।
স্বরূপ শক্তি হয় যে জনা কে জানে তার ঠিক ঠিকানা,
জাহের বাতেন যে জানে না তার মনেতে প্যাঁচ পড়েছে।
আপনার শক্তির জোরে নিজশক্তির রূপ প্রকাশ করে,
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোরে নিতান্তই ভূতে পেয়েছে।”)) হাজার হোক, একটা সদা বিরাজমান স্রষ্টার এবং একটা স্রষ্টাবিহীন, সদা বিরাজমান মহাবিশ্বের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি দেয়ার মধ্যে পার্থক্য কোথায়?
এসব যুক্তি আমাকে সবসময়ই এক বিশেষজ্ঞের (কেউ বলে বার্ট্রান্ড রাসেল, ((বার্ট্রান্ড রাসেল তার ১৯২৭ সালের বক্তৃতা Why I Am Not A Christian এ বলেছিলেন, “If everything must have a cause, then God must have a cause. If there can be anything without a cause, it may just as well be the world as God, so that there cannot be any validity in that argument. It is exactly of the same nature as the Hindu’s view, that the world rested upon an elephant and the elephant rested upon a tortoise; and when they said, ‘How about the tortoise?’ the Indian said, ‘Suppose we change the subject.'”)) কেউ উইলিয়াম জেমস ((ভাষাবিদ জন আর. রস তার Constraints on Variables in Syntax অভিসন্দর্ভে এমন একটি গল্প উল্লেখ করেন যেখানে বক্তাটি ছিলেন মার্কিন দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমস।))) মহাবিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে বক্তৃতা দেয়ার সেই বিখ্যাত গল্পটির কথা মনে করিয়ে দেয়। তাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল এক মহিলা, যে বিশ্বাস করত এক বিশাল কচ্ছপ বিশ্বটাকে তুলে ধরে রেখেছে, যে কচ্ছপ দাঁড়িয়ে আছে আরেকটা কচ্ছপের উপর, যে দাঁড়িয়ে আছে আরো একটার উপর… এবং এভাবে “একেবারে নিচ পর্যন্ত” কেবল একের পর এক কচ্ছপই আছে। নিজেই নিজেকে সৃষ্টিকারী কোনো সৃষ্টিশীল সত্তার এমন অন্তহীন পুনরাবৃত্তি মহাবিশ্ব কোত্থেকে এসেছে সে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান একটুও বৃদ্ধি করে না, তা সেই কাল্পনিক সত্তাটি কচ্ছপের চেয়ে যতই শক্তিশালী হোক না কেন। তবে, মহাবিশ্বের জন্মের আসল প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে অনন্ত পুনরাবৃত্তির এই রূপকগল্পটি হয়ত একটি একক স্রষ্টার ধারণার চেয়ে বেশিই সফল।
পরের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপানোর এই চক্র ঈশ্বরে গিয়ে শেষ হয়, এমনটা বলে অনেকেই নতুন সংজ্ঞা তৈরির মাধ্যমে প্রশ্নটা মুছে ফেলতে চান, এবং মনে হতে পারে এতে অনন্ত পুনরাবৃত্তির মোক্ষম সমাধানও জুটে যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে আমার মন্ত্র হচ্ছে: মহাবিশ্ব যেমন আছে তেমনই, আমরা তা পছন্দ করি আর না-ই করি। ((ডেভিড হিউমের যুক্তি কাজে লাগিয়ে এমন একটি ধারণা প্রথম ব্যক্ত করেন বার্ট্রান্ড রাসেল। তিনি বলেছিলেন, মহাবিশ্ব “is just there, and that’s all.” সূত্র: Russell, Bertrand, and Frederick Copleston, 1964, “Debate on the Existence of God,” in John Hick (ed.), The Existence of God, New York: Macmillan.)) স্রষ্টার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব আমাদের আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভরশীল নয়। ঈশ্বর বা উদ্দেশ্য বিহীন বিশ্ব রূঢ় ও অর্থহীন মনে হতে পারে, কিন্তু কেবল সেই কারণেই ঈশ্বরকে আসলেই থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই।
একইভাবে, আমাদের মন হয়ত সহজে অসীম কোনোকিছু উপলব্ধি করতে পারে না (যদিও আমাদের মনের তৈরি গণিত তা বেশ সুন্দরভাবেই ফুটিয়ে তুলতে পারে ((গণিতে আমরা আসলেই ‘সুন্দরভাবে’ এটা ফুটিয়ে তুলতে পারি কি না তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। এক্ষেত্রে Natalie Wolchover এর Dispute over Infinity Divides Mathematicians প্রবন্ধটি পড়া যেতে পারে।))), কিন্তু তার মানে এই নয় যে অসীম নেই। আমাদের মহাবিশ্বই স্থানে বা কালে অসীম হতে পারে। কিংবা, একবার রিচার্ড ফাইনম্যান যেমন বলেছিলেন, পদার্থবিজ্ঞানের নীতিগুলো হয়ত একটা অসীমসংখ্যক স্তরবিশিষ্ট পেঁয়াজের মতো, এবং আমরা যখন নতুন কোনো আকারের জগতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করি তখন নতুন একটা স্তরের সূত্রগুলো কাজ শুরু করে। ((ফাইনম্যানের আসল উক্তিটা ছিল, “People say to me, ‘Are you looking for the ultimate laws of physics?’ No, I’m not, I’m just looking to find out more about the world and if it turns out there is a simple ultimate law which explains everything, so be it. That would be very nice to discover. If it turns out it’s like an onion with millions of layers and we’re just sick and tired of looking at the layers, then that’s the way it is, but whatever way it comes out it’s nature is there and she is going to come out the way she is, and therefore when we go to investigate it we shouldn’t predecide what it is we’re trying to do except to try to find out more about it.” সূত্র: Feynman, Richard P., and Jeffrey Robbins. The Pleasure of Finding Things Out: The Best Short Works of Richard P. Feynman. Cambridge, MA: Perseus, 1999.)) আমরা আসলেই জানি না!
নক্ষত্র, গ্যালাক্সি, মানুষ, এবং অজানা আরো অনেককিছু নিয়ে গঠিত আমাদের এই মহাবিশ্ব কোনো নকশা, পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্য ছাড়া উৎপন্ন হয়েছে, এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দুই হাজারেরও বেশি সময় ধরে যে চ্যালেঞ্জটি উত্থাপন করা হয়ে আসছে তা হলো, “কিছু না থাকার বদলে কেন কিছু আছে?” ((এই প্রশ্ন, বা সার্বিকভাবে নাস্তিত্ব/নাথিংনেস নিয়ে পাশ্চাত্যে প্রথম দার্শনিক আলোচনা শুরু করেছিলেন পার্মেনিদিস (খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতক) যাকে নিয়ে প্লেটো একটি বিখ্যাত সংলাপও লিখেছেন। সূত্র: Roy Sorensen, Nothingness, Stanford Encyclopedia of Philosophy.)) একে সচরাচর দার্শনিক বা ধর্মীয় প্রশ্ন হিসেবে উত্থাপন করা হলেও, মনে রাখতে হবে এটা সবার আগে প্রাকৃতিক বিশ্ব বিষয়ক একটা প্রশ্ন, এবং সুতরাং এটা সমাধানের চেষ্টা করা উচিত সবার আগে বিজ্ঞানের মাধ্যমে।
এই বইয়ের উদ্দেশ্য খুব সরল। আমি দেখাতে চাই আধুনিক বিজ্ঞান কিভাবে, বিভিন্ন রূপে, এই কোনোকিছু না থাকার বদলে থাকার প্রশ্নটির উপর আলোকপাত করতে পারে, এবং করেও চলেছে। আশ্চর্যরকমের সুন্দর পরীক্ষণমূলক পর্যবেক্ষণ এবং আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত তত্ত্বগুলো থেকে এযাবৎ যে উত্তরগুলো পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয়, নাস্তি (nothing) থেকে কিছু পাওয়া কোনো সমস্যা না। এমনকি, মহাবিশ্বের অস্তিত্বশীল হওয়ার জন্যই হয়ত নাস্তি থেকে কিছু তৈরি হওয়াটা ‘আবশ্যিক’ ছিল। উপরন্তু, সব লক্ষণ জানান দিচ্ছে যে, আমাদের মহাবিশ্বের পক্ষে এভাবেই উদ্ভূত হওয়া ‘সম্ভব’ ছিল।
এখানে ‘সম্ভব’ শব্দটার উপর আমি জোড় দিয়েছি, কারণ এই প্রশ্নের সন্দেহাতীত সমাধানের জন্য যত পরীক্ষণমূলক তথ্য দরকার তা হয়ত আমরা কখনোই পাবো না। কিন্তু নাস্তি থেকে যে একটা মহাবিশ্বের জন্ম ‘হতে পারে’, কেবল এই সত্যটাই অনেক তাৎপর্যপূর্ণ, অন্তত আমার কাছে।
আর কিছু বলার আগে “নাস্তি”-র ধারণাটা—যার বিস্তারিত কথা পরে হবে—নিয়ে কিছু কথা বলে নিতে চাই। কারণ, জানতে পেরেছি, গণমাধ্যমে এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার সময় আমার সাথে দ্বিমত পোষণকারী দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক দেরকে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা বিচলিত করে তা হলো, একজন বিজ্ঞানী হিসেবে সত্যিকার অর্থে “নাস্তি” কাকে বলে তা আমি জানি না। (সমুচিত জবাব হিসেবে এখানে বলতে চাই, ধর্মতাত্ত্বিকেরা কিছুরই বিশেষজ্ঞ না।)
তাদের কথা হলো, “নাস্তি” আমি যেমনটা বলেছি সেরকম কিচ্ছু না। নাস্তি হচ্ছে “অনস্তিত্ব,” যা অনেকটাই কুসংজ্ঞায়িত এবং অস্পষ্ট। এক্ষেত্রে সৃষ্টিবাদীদের সাথে তর্ক করতে গিয়ে প্রথম প্রথম “বুদ্ধিদীপ্ত নকশার” (intelligent design) সংজ্ঞা নিয়ে যে সমস্যায় পড়েছিলাম তার কথা মনে পড়ছে। পরে দেখা গিয়েছিল, এর আসলে কোনো স্পষ্ট সংজ্ঞাই নেই; এটা কী তা বলা সম্ভব না, কী নয় তা-ই কেবল বলা সম্ভব। “বুদ্ধিদীপ্ত নকশা” হচ্ছে বিবর্তনের বিরোধিতা করার সব ছুঁতোকে এক ছাতার তলায় জড়ো করার জন্য ব্যবহৃত একটা শব্দবন্ধ। একইভাবে, কিছু দার্শনিক এবং অনেক ধর্মতাত্ত্বিক বারংবার “নাস্তি” কে সংজ্ঞায়িত ও পুনঃসংজ্ঞায়িত যেভাবে করেন তা হলো, এটা বিজ্ঞানীরা এযাবৎ নাস্তি’র যতগুলো সংস্করণ উত্থাপন করেছেন তার কোনোটাই না।
কিন্তু আমার মতে ঠিক সেখানেই নিহিত আছে ধর্মতত্ত্বের সিংহভাগের এবং আধুনিক দর্শনের কিছু অংশের বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়াপনা। কারণ, “নাস্তি” বা “কিছু না” যেকোনো অর্থেই ঠিক “কিছু”-র মতোই ভৌত একটা ব্যাপার, বিশেষ করে যদি “কিছুর অনুপস্থিতি”-র মাধ্যমেই এর সংজ্ঞা দেয়া হয়। সুতরাং এই ভৌত রাশিগুলোর প্রকৃতি সূক্ষ্ণভাবে বুঝাটা আমাদের কর্তব্য। এবং যেকোনো সংজ্ঞা বিজ্ঞান ছাড়া কেবল কিছু শব্দের সমষ্টি হয়ে পড়ে।
এক শতাব্দী আগেও যদি কেউ “নাস্তি” বলতে কোনো বাস্তব-পদার্থসত্তা-হীন পরিপূর্ণ শূন্যস্থান বুঝাত তবে তার বিরুদ্ধে তেমন কোনো যুক্তি আসত না। কিন্তু গত শতাব্দীর আবিষ্কারগুলো আমাদের শিখিয়েছে যে, প্রকৃতির কর্মপদ্ধতি এত ভালো করে বুঝতে পারার আগে আমরা শূন্যস্থানকে যেমন অলঙ্ঘনীয় নাস্তিত্ব ((‘নাস্তিত্ব’ শব্দটির ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের ‘মৃত্যু’ কবিতা দ্বারা অনুপ্রাণিত।)) মনে করতাম এটা মোটেই তেমন না। এখন ধর্মীয় সমালোচকরা আমাকে বলছেন, শূন্যস্থানকে আমি “নাস্তি” ডাকতে পারব না, বরং একে ডাকতে হবে “কোয়ান্টাম শূন্যতা” যাতে তার থেকে দার্শনিক বা ধর্মতাত্ত্বিকদের আদর্শায়িত “নাস্তি”-র পার্থক্য করা যায়।
তবে তাই হোক। এবার যদি আমরা “নাস্তি” কে স্বয়ং স্থান এবং কালেরই অনুপস্থিতি হিসেবে বর্ণনা করি? এটা কি যথেষ্ট? আবারও, আমার মনে হয় এটা যথেষ্ট হতো… কোনো এক সময়। কিন্তু, সামনে যেমন বর্ণনা করব, আমরা যখন জেনেছি স্থান ও কাল নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবির্ভূত হতে পারে, তখন আমাদেরকে বলা হচ্ছে এই “নাস্তি” ও না কি কোনো নাস্তি না। এবং আরও বলা হলো, “বাস্তব” নাস্তি থেকে মুক্তি পেতে চাইলে ঐশ্বরিক কিছুর আশ্রয় নিতে হবে, এবং শেষ পর্যন্ত হুকুম জারি করা হলো যে, “নাস্তি” এমন জিনিস “যা থেকে একমাত্র ঈশ্বরই কিছু তৈরি করতে পারে।”
এ নিয়ে যাদের সাথে তর্ক করেছি তাদের অনেকেও বলেছেন, যদি কিছু তৈরি করার “বিভব” (potential) থাকে তাহলে সে অবস্থা সত্যিকারের নাস্তিত্ব না। এবং নিশ্চিতভাবেই প্রকৃতির নীতি যেহেতু এমন বিভব সরবরাহ করতে পারে সেহেতু অনস্তিত্ব ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে যায়। কিন্তু তারপর যদি আমি যুক্তি দেই যে নীতিগুলো নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত হয়েছে, যেমনটা আমি ভবিষ্যতে দেখাব হতেও পারে, তাহলে সেটাও তাদের জন্য পর্যাপ্ত হয় না। কারণ যে ব্যবস্থার মধ্যে এই নীতিগুলোর উদ্ভবের বিভব ছিল সেটাও সত্য নাস্তিত্ব হতে পারে না।
একেবারে নিচ পর্যন্ত কেবল কচ্ছপই মনে হচ্ছে? আমার মনে হয় না। কিন্তু কচ্ছপের উপমাটা আকর্ষণীয় এই কারণে যে এটা বুঝায়, বিজ্ঞান এমনভাবে খেলার মাঠ পাল্টে দিচ্ছে যে অনেকে অস্বস্তি বোধ করছেন। অবশ্যই, সেটাই বিজ্ঞানের (সক্রেটীয় সময়ে অনেকে হয়ত বলত “প্রাকৃতিক দর্শন”) উদ্দেশ্যগুলোর একটি। স্বস্তির অভাব মানে আমরা নতুন কোনো অন্তর্দৃষ্টির দ্বারপ্রান্তে। নিশ্চয়ই, “কিভাবে” বিষয়ক কঠিন প্রশ্ন এড়ানোর জন্য “ঈশ্বর” কে আবাহন করাটা কেবলই বুদ্ধিবৃত্তিক আলস্য। হাজার হোক, যদি সৃষ্টির কোনো বিভব না থাকত তবে ঈশ্বরই কোনোকিছু সৃষ্টি করতে পারত না। এমনটা বলা তো কেবলই শাব্দার্থিক ভাওতাবাজি যে, ঈশ্বর প্রকৃতির বাইরে অবস্থান করলে সম্ভাব্য অসীম প্রত্যাবৃত্তির হাত থেকে বাঁচা যায়, এবং তাই যে নাস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব উদ্ভূত হয়েছে স্বয়ং অস্তিত্বের “বিভব” তার অংশ নয়।
এখানে আমার মূল উদ্দেশ্য এইটা দেখানো যে, বিজ্ঞান খেলার মাঠ পাল্টে দিয়েছে, এবং তাই নাস্তিত্বের প্রকৃতি বিষয়ক এই বিমূর্ত এবং অকেজো বিতর্কগুলো প্রতিস্থাপিত হয়েছে আমাদের মহাবিশ্বের আসল জন্মরহস্য বর্ণনার কেজো ও কার্যকরি প্রচেষ্টা দিয়ে। আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য এই পরিবর্তনের সম্ভাব্য তাৎপর্যও আমি ব্যাখ্যা করব।
এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপারের প্রতিফলন। আমাদের মহাবিশ্ব কিভাবে বিবর্তিত হয় তা বুঝার ক্ষেত্রে ধর্ম ও ধর্মতত্ত্ব আদ্যোপান্ত অপ্রাসঙ্গিক। তারা প্রায়ই জল আরো ঘোলা করে; যেমন, প্রায়োগিক প্রমাণের উপর ভিত্তি করে নাস্তিত্বের কোনো সংজ্ঞা দেয়া ছাড়াই তারা এই বিষয়ক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে থাকে। মহাবিশ্বের উৎপত্তি আমরা এখনো পুরোপুরি না বুঝলেও এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে ভবিষ্যতে এই ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন আসবে। উপরন্তু, আমি মনে করি একই কথা ভবিষ্যতে সেই বিষয়গুলো বুঝার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে যেগুলোকে বর্তমানে ধর্ম নিজের এলাকা মনে করে, যেমন মানব নৈতিকতা।
প্রকৃতিকে আরো ভালো করে বুঝার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান কার্যকর ভূমিকা রাখতে পেরেছে কারণ বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত তিনটি মূলনীতির উপর: (১) প্রমাণ যেখানে নেয় সেখানেই যাও; (২) নিজের তত্ত্বকে সত্য প্রমাণের ইচ্ছা যতটা মিথ্যা প্রমাণের ইচ্ছাও ততটা থাকা চাই; (৩) সত্যের চূড়ান্ত নির্ণায়ক হচ্ছে পরীক্ষা, নিজের পূর্বতসিদ্ধ বিশ্বাস থেকে আহরিত স্বস্তি নয়, বা নিজের তাত্ত্বিক মডেলের উপর স্ব-আরোপিত সৌন্দর্য্য বা সৌষ্ঠবও নয়।
এখানে যে পরীক্ষাগুলোর ফলাফল বর্ণনা করব সেগুলো যেমন সময়োপযোগী তেমনি অপ্রত্যাশিত। আমাদের মহাবিশ্বের বিবর্তন বর্ণনা করতে গিয়ে বিজ্ঞান যে নকশী কাঁথা বুনে চলেছে তা মানুষের ফাঁদা যেকোনো কল্পনাশ্রয়ী গল্প বা ওহিযোগে প্রাপ্ত যেকোনো দৃশ্যকল্পের চেয়ে অনেক বেশি সমৃদ্ধ ও চিত্তাকর্ষক। প্রকৃতির বিস্মিত করার ক্ষমতা মানুষের কল্পনা’র যেকোনো সৃষ্টির চেয়ে অনেক বেশি।
গত কয়েক দশকে বিশ্বতত্ত্ব, কণা পদার্থবিজ্ঞান ও মহাকর্ষতত্ত্বে কিছু রোমাঞ্চকর নতুন আবিষ্কার আমাদের মহাবিশ্ব-দর্শন পুরো পাল্টে দিয়েছে, এবং মহাবিশ্বের জন্ম ও ভবিষ্যৎ বুঝার ক্ষেত্রে এদের তাৎপর্য চমকপ্রদ ও সুগভীর। সুতরাং লেখালেখির বিষয় হিসেবে বর্তমানে নাস্তি’র চেয়ে আকর্ষণীয় আর কিছু হতে পারে না।
এই বই লেখার প্রকৃত অনুপ্রেরণা পুরাণ ভঞ্জন বা বিশ্বাস আহত করার ইচ্ছা থেকে অতটা আসেনি, এসেছে আসলে আমাদের এই মহাবিশ্বকে আমরা যেমন বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ রূপে আবিষ্কার করেছি তা এবং স্বয়ং জ্ঞান উদ্যাপনের অভিলাষ থেকে।
আমাদের অনুসন্ধান আমাদেরকে প্রসরমান মহাবিশ্বের দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত ঘূর্ণিবেগে এক অভিযানে নিয়ে যাবে। আমরা বিচরণ করব মহাবিস্ফোরণের আদিমতম ক্ষণ থেকে শুরু করে সুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত, এবং যথাসাধ্য তুলে ধরব গত শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলো।
এই বই লেখার মূল প্রেরণা আসলে এসেছে মহাবিশ্ব সম্পর্কে একটা সুগভীর আবিষ্কার থেকে, যা গত তিন দশকের অধিকাংশ সময় জুড়ে আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে, এবং যে আবিষ্কারের ফল হিসেবে বেরিয়ে এসেছে একটা চমকপ্রদ অনুসিদ্ধান্ত: মহাবিশ্বের অধিকাংশ শক্তি এক রহস্যময়, এযাবৎ অনির্বচনীয় রূপে শূন্যস্থানের সর্বত্র বিরাজ করছে। এই আবিষ্কার যে আধুনিক বিশ্বতত্ত্বের ক্রীড়াক্ষেত্র পাল্টে দিয়েছে তা বলাটা মোটেও বাহুল্য হবে না।
একটা ব্যাপার হচ্ছে, মহাবিশ্ব যে একেবারে নাস্তি থেকে উদ্ভূত হতে পারে তার পক্ষে এই আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য নতুন সমর্থন জুগিয়েছে। তাছাড়া এটা আমাদেরকে অন্তত দুটি বিষয় সম্পূর্ণ নতুনভাবে ভাবতে প্ররোচিত করেছে: মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ বিবর্তন যে প্রক্রিয়াগুলো দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে সেগুলো সম্পর্কে আমাদের পূর্বানুমানসমূহ সঠিক কি না, এবং স্বয়ং প্রকৃতির নীতিগুলোই সত্যিকার অর্থে মৌলিক কি না। এই দুটি ব্যাপারই যার যার ক্ষেত্রে কেন কিছু না থাকার বদলে কিছু আছে সেই প্রশ্নকে আগের চেয়ে কম জবরদস্ত করে দিয়েছে, বা হয়ত একেবারেই জলবৎ তরলং করে দিয়েছে যা আমি বর্ণনা করার আশা রাখি।
বইটির আসল সূচনা ২০০৯ সালের অক্টোবরে লস এঞ্জেলেসে প্রদত্ত আমার একই নামের একটি বক্তৃতা থেকে। ((‘A Universe From Nothing’ by Lawrence Krauss, AAI 2009, YouTube.)) রিচার্ড ডকিন্স ফাউন্ডেশনের সৌজন্যে বক্তৃতাটির ভিডিও ইউটিউবে প্রকাশিত হয় এবং তার বিপুল জনপ্রিয়তা দেখে নিজেই বিস্মিত হয়ে যাই। এখন পর্যন্ত ভিডিওটি প্রায় আঠার লক্ষ বার দেখা হয়েছে, এবং এর বিভিন্ন অংশ নাস্তিক, আস্তিক উভয় সম্প্রদায় যার যার তর্ক-বিতর্কে ব্যবহার করে যাচ্ছেন।
বিষয়টাতে মানুষের আগ্রহ যেহেতু পরিষ্কার, এবং বক্তৃতাটির পর ইন্টারনেট এবং বিভিন্ন মিডিয়াতে যেহেতু এ নিয়ে কিছু বিভ্রান্তিকর ভাষ্যও তৈরি হয়েছে, সেহেতু ভাবলাম সেখানে ব্যক্ত করা ধারণাটি এই বইয়ে আরো পরিপূর্ণভাবে পরিবেশন করি। বক্তৃতাটির প্রায় পুরোটা জুড়ে ছিল বিশ্বতত্ত্বের সাম্প্রতিক বিপ্লব, বিশেষ করে স্থানের শক্তি ও জ্যামিতি বিষয়ক আবিষ্কারগুলো, যা মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দিয়েছে। এই বইয়ের প্রথম দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে সে কথাই থাকবে, কিন্তু তারপর আরো কিছু যোগ করব।
এর মধ্যে আমার যুক্তি গঠনকারী ধারণা ও পূর্বধারণা গুলো নিয়ে আরো ভেবেছি; অন্য যাদের সাথে এ নিয়ে আলোচনা করেছি তারা এমন উৎসাহ দেখিয়েছেন যা রীতিমত সংক্রামক; এবং আমি এখানে কণা পদার্থবিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারগুলো আরো গভীরভাবে আলোচনা করেছি, বিশেষ করে মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও প্রকৃতি বিষয়ক আবিষ্কারগুলো। এবং পরিশেষে যারা আমার যুক্তিগুলোর উদগ্র বিরোধিতা করেন তাদের সামনে সেগুলো তুলে ধরার মাধ্যমে নিজের যুক্তিকেই আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছি।
শেষ পর্যন্ত যে ধারণাগুলো এখানে বর্ণনা করেছি সেগুলো গঠন করতে গিয়ে আমার চিন্তাশীল পদার্থবিজ্ঞানী সহকর্মীদের সাথে আলোচনা ব্যাপকভাবে কাজে দিয়েছে। আমার সাথে বিস্তৃতভাবে আলোচনা ও যোগাযোগ রক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই অ্যালান গুথ ((Alan Guth আধুনিক বিশ্বতত্ত্বের সবচেয়ে আলোচিত অনুকল্প মহাজাগতিক স্ফীতি (cosmic inflation) এর প্রবর্তকদের একজন। অন্য দুই জন হলেন আন্দ্রেই লিন্দে এবং আলেক্সেই স্তারোবিনস্কি। স্ফীতিতত্ত্ব কখনো পরীক্ষণমূলকভাবে প্রমাণিত হলে এরা তিন জনই সম্ভবত নোবেল পুরস্কার পাবেন।)) এবং ফ্র্যাংক উইলচেক ((Frank Wilczek মার্কিন তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী যিনি সবল নিউক্লীয় বলের জন্য দায়ী সবল মিথস্ক্রিয়াতে ‘অসীমতটীয় স্বাধীনতা’ (asymptotic freedom) আবিষ্কারের জন্য ২০০৪ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।)) কে; সে আলোচনাগুলো কখনো আমার নিজের বিভ্রান্তি দূরীকরণে সহায়ক হয়েছে, আর কখনো আমার ধারণাগুলোকেই আরো পাকপোক্ত করতে সাহায্য করেছে।
ফ্রি প্রেস, সায়মন অ্যান্ড শাস্টার এর লেজলি মেরেডিথ এবং ডোমিনিক অ্যানফুসো এমন একটি বিষয়ে বই প্রকাশের আগ্রহ প্রকাশ করার পর উদ্বুদ্ধ হয়ে আমার বন্ধু এবং আমার দেখা সবচেয়ে শিক্ষিত ও মেধাবী ব্যক্তি ক্রিস্টোফার হিচেন্সের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম, এবং সে আমার কিছু যুক্তি বিজ্ঞান ও ধর্ম নিয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কগুলোতে ব্যবহার করেছিল। ((হিচেন্স ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে একটি বিতর্ক করেছিলেন উইলিয়াম লেইন ক্রেইগ এর সাথে: Debate – William Lane Craig vs Christopher Hitchens – Does God Exist?)) স্বাস্থ্য খারাপ থাকা সত্ত্বেও ক্রিস্টোফার এই বইয়ের একটি মুখবন্ধ লিখে দিতে রাজি হয়। সে জন্য আমি তার কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, তার স্বাস্থ্য শেষে এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে মুখবন্ধটা শেষ করা সর্বোচ্চ চেষ্টা সত্ত্বেও তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তবে পাশাপাশি রিচার্ড ডকিন্স বইটির একটি ‘শেষকথা’ লিখে দিতে রাজি হয়েছিল, যে কারণে বইটির সাথে জড়িত গুণী ব্যক্তির সংখ্যা রীতিমত বিব্রতকর পর্যায়ে পৌঁছেছিল। প্রথম খসড়া শেষ করার পর ডকিন্স সংক্ষেপে কিছু লিখে দেয় যার সৌন্দর্য্য ও স্বচ্ছতা ছিল একদিকে বিস্ময়কর, অন্যদিকে বিনয়াবনত করে দেয়ার মতো। আমার সশ্রদ্ধ বিস্ময় সে লেখার প্রতি। সুতরাং ক্রিস্টোফার এবং রিচার্ড, এবং বাকি সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই তাদের সাহায্য ও উৎসাহের জন্য, এবং আমাকে আবারো লেখার উদ্দেশ্যে কম্পিউটারের সামনে বসতে অনুপ্রাণিত করার জন্য।
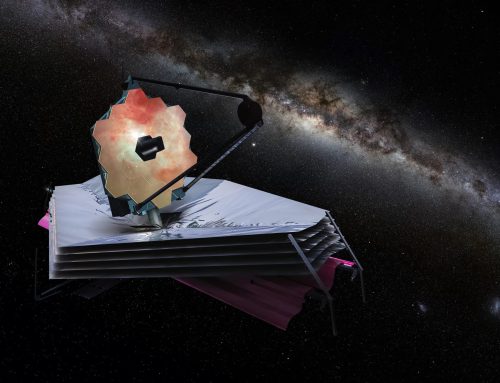


কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছিনা। মহা বিস্ফোরণের আগে স্থানকালের অস্তিত্ব ছিল না তাহলে অর্থাৎ স্থান ছিল না তাহলে কোয়ান্টাম শুণ্যতাটা ছিল কোথায়।
Khub bhalo kaj…baki porbo gulo kothay ?
বাংলা ব্লগে বাংলায় মন্তব্য করতে হবে।
অনুবাদের জন্য ধন্যবাদ। ঃ-)
অনেক ভাল লাগল,,,,, খুব তথ্যপুর্ন সাবলীল
অনুবাদ…..।চমৎকার লেখক আপনি,,,,
তাই বলে আপনার সাথে একমত না!!!!
///// বার্ট্রান্ড রাসেল তার
১৯২৭ সালের বক্তৃতা
Why I Am Not A Christian
এ বলেছিলেন, “If
everything must have a
cause, then God must
have a cause. If there can
be anything without a
cause, it may just as well
be the world as God, so
that there cannot be any
validity in that argument./////
জানিনা এই বক্তব্যের সাথে কতটুকু একমত
আপনি,,,,!!খুব সম্ভবত আপনি একমত।।
তবে শুনুন,, আমাদের বিশ্বাসকৃত আল্লাহ
আপনাদের অবিশ্বাসকৃত GOD এর মত কোনো
“thing” নয়।।
আমাদের আল্লাহ কে জানার কপিতয়
সংঙ্গা আছে যেমন
সূরা এখলাছ:1 – “বলুন, তিনি আল্লাহ, এক
(আহাদ)”
সূরা এখলাছ:2 – আল্লাহ অমুখাপেক্ষী,
সূরা এখলাছ:3 – তিনি কাউকে জন্ম দেননি
এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি
সূরা এখলাছ:4 – এবং তার সমতুল্য কেউ
নেই।
সুতরাং “thing” তো অনেক প্রকারের
আছে।।কিন্তু আল্লাহ এক এবং তিনি কোনো
“thing” এর সমতুল্য নন।।”thing”এর সাথে আল্লাহর তুলনা হয় না।সৃষ্টি এবং স্রষ্টার পার্থক্য এটাই যে সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার তুলনা করা যায় না।।
তাই এই রকমের লজিক যেমন “if everything
must have a cause, then ALLAH must have a
cause”সম্পুর্ন অগ্রহনযোগ্য এবং হাস্যকর।।কারন এখানে everything এর সাথে ALLAH এর তুলনা করা হল।।
সুতরাং বার্ট্রান্ড রাসেল এর ঐ রকমের
আর্গুমেন্ট মাঠে মারা গেল।।
ধন্যবাদ
ধন্যবাদ।
আর বার্ট্রান্ড রাসেলের যুক্তিকে “মাঠে মারতে পেরেছেন” জেনে ভালো লাগল। আশাকরি সেটা করতে গিয়ে আপনার জীবন আরো দীপান্বিত হয়েছে।
ভাল লাগল,,,,!!!!
অনেক শুভকামনা, এই গুরুত্বপূর্ণ বইটা বাংলায় অনুবাদ করা উদ্যোগ নেবার জন্য।
বোঝাই যাচ্ছে এটা বই এর প্রারম্ভিকা। মূল অংশ পড়ার অপেক্ষায় রইলাম। অনুবাদ ঝরঝরে। অনুবাদ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হচ্ছে, একেবারে নিজে থেকে কিছু লেখার বদলে অনুবাদ করতে গেলে ‘কায়িকশ্রম’টা কয়েক গুণ বেশি হয়। বিশেষ করে বিজ্ঞানের লেখায়, প্রতিটা লাইনে যে ধারনা সম্পর্কে লিখছি সেটা সম্পর্কে একটু ব্যাকগ্রাউণ্ড স্টাডি করা, লাইনটাকে বাংলায় সুসংহত ভাবে প্রকাশ ইত্যাদি অনেক বাড়তি চাপ থাকে।
এছাড়া (একটা নিতান্ত ব্যক্তিগত অভিমত) এই বিষয়ে যেহেতু বাংলায় অভিজিৎ দা এবং মীজান রহমান একটা বই প্রকাশ করেছেন। এবং বাংলায় সিরিয়াস বিজ্ঞানের বই এত কম যে বৈচিত্র বৃদ্ধির জন্য ইফোর্টটা একদম একই বিষয়ের বইতে না দিয়ে অন্য কোনো বিষয়ের বই অনুবাদে প্রয়োগ করলে ভালো হতো না?
শূন্য থেকে মহাবিশ্ব এবারই কিনলাম। অভিজিৎদা অটোগ্রাফ দিলেন। মহাদেশ বদলালাম বলে মেলায় কেনা কোনো বই-ই সঙ্গে নিতে পারিনি। বাড়ির লাইব্রেরীতে রয়ে গেছে। 🙁
অনুবাদ সম্পর্কে আমার উপলব্ধি আপনার উল্টো। আমি নিজে কিছু লেখার চেয়ে অনুবাদ করতে অনেক কম সময় নেই। কারণ নিজে কিছু লিখতে গেলে অনেক পড়াশোনা করতে হয়, এক লাইন লেখার আগে দশ বার ভাবতে হয় যেখানে অনুবাদের ক্ষেত্রে কেবল বাংলাকরণ নিয়ে ভাবলেই চলে। যেমন আমি ‘বাঙালি মুসলমানের প্রতি’ লিখেছি ১০ দিনে, ‘নাস্তি থেকে মহাবিশ্ব’ সমপরিমাণ অনুবাদ করেছি ২ দিনে, গোর্গিয়াসের সমপরিমাণ অনুবাদও করেছিলাম ২ দিনে। আর অনুবাদ এবং পাদটীকা সংযোজন এর ব্যাপারটাতে আমি খুবই মজা পাই।
আসলে অভিজিৎ দা ‘শূন্য থেকে মহাবিশ্ব’ লিখেছেন বলেই আমি এই অনুবাদটা শুরু করেছি। ‘শূন্য থেকে মহাবিশ্ব’ পড়ে অনেকেই ক্রাউস পড়ার ব্যাপারেও আগ্রহী হতে পারেন। এই বইটার বাংলা থাকলে মন্দ হয় না।
ওহ্, আমার নিজস্ব লেখার ক্ষেত্রে সাধারণত পুরো লেখাটা মাথার মধ্যে তৈরি হয়ে গেলে এক বসায় লিখে ফেলি। পড়াশুনা ঘাটাঘাটি এগুলো তাই লিখতে বসার আগেই হয়ে যায়। আর লেখা শেষে ফ্যাক্ট চেকিং এর সময় আরেকবার হয়। তাই নিজে কিছু লিখলে কায়িক শ্রম কম লাগলো বলে মনে হয়। অবশ্য আমার বেশিরভাগ লেখাই হালকা চালের।
অনুবাদ জারি থাক। (y)
সহজ সাবলীল দারুন অনুবাদ।
চলুক…।
সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন ? ইউরোপীয় দর্শন যা GOD নামক এক খামখেয়ালী রাজার মত সৃষ্টি কর্তার চিন্তা করে , তা এই যুক্তি তে ভ্রান্ত প্রমানিত হয়, কিন্তু ভারতীয় দর্শনে আপনার এই যুক্তি খাটে না. কারণ
“ব্রহ্ম” কোনো কর্তা বা পৃথক সত্তা নয় , যা শুধুমাত্র ব্রম্ভান্ডের একটি variable, যার সৃষ্টির কোনো প্রয়োজন নেই, এই সত্তাই একবার bigbang এর মাধ্যমে নিজেকে কেন্দ্রীভূত করে প্রসারিত হতে হতে পুনরায় big crunch এর মাধ্যমে নিজেকে কেন্দ্রীভূত করছে
ব্রহ্মের মতো ঈশ্বরের ধারণা শুধু ভারতেই তৈরি হয়েছে এটা ভুল কথা। এরিস্টটলের ‘প্রথম কারণ’, এবং ইবনে সিনা’র ‘আল্লাহ’ এর ধারণা উপনিষদের ব্রহ্মের ধারণা থেকে খুব বেশি আলাদা ছিল না।
এখানে লরেন্স ক্রাউস সৃষ্টিকর্তা বলতে শুধু ইব্রাহিমীয় ধর্মগুলোর ব্যক্তিরূপী ‘গড’ কেই বুঝাচ্ছেন না, সকল ধরণের প্রথম কারণের ধারণাকে বুঝাচ্ছেন, এবং এর মধ্যে ব্রহ্মও পড়তে পারে।
আপনি যেভাবে ব্রহ্মকে প্রকৃতিরই একটি চলক (ভ্যারিয়েবল) হিসেবে আখ্যায়িত করলেন সেটার সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই, এটা আপনার বিশ্বাস, বা হয়ত বেদান্তকারদের বিশ্বাস। জ্ঞানতত্ত্বে বিশ্বাস থেকে জ্ঞান কে সব সময়ই আলাদা হিসেবে দেখা হয়। এ ধরণের চলক যে বিশ্বাস থেকে উপরে উঠে কখনোই জ্ঞানের পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে না সেটা ইসলামী বিশ্বে গাজ্জালি যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি ইউরোপে ডেভিড হিউম এবং ইমানুয়েল কান্ট ও দেখিয়েছেন।
আপনার দ্বিতীয় কথা প্রসঙ্গে: প্রথম কথা আমাদের মহাবিশ্বের যে বিগক্রাঞ্চ বা মহাসংকোচন হবে না সে ব্যাপারে এখন প্রায় সবাই নিশ্চিত। সুতরাং ব্রহ্মের মহাসংকোচন ঘটাতে গেলে আপনাকে বিপদেই পড়তে হবে। আর যদি মহাসংকোচন ঘটেও, তারপরও আমার কথা হচ্ছে: যা নিজেকে মহাবিস্ফোরিত করে পরে আবার মহাসংকুচিত করে তাকে আমি ‘মহাবিশ্ব’ নামে ডাকি, এখন আপনি যদি সেটাকে ‘ব্রহ্ম’ বা অন্য যেকোনো নামে ডাকতে চান ডাকুন না। আমি ডাকতে রাজি নই। মহাবিশ্বের যথেষ্ট সুসংজ্ঞায়িত পরীক্ষণযোগ্য চলক থাকা সত্ত্বেও কেন তার আরেকটা অসংজ্ঞায়িত পরীক্ষণ-অযোগ্য চলক দরকার সেটা আমার বোধগম্য নয়।
ব্রহ্মান্ড নামের মধ্যেই রহস্য লুকিয়ে আছে . ব্রহ্ম + অন্ড = ব্রহ্মান্ড. অন্ড বলতে সৃষ্টির শুরুর প্রথম অবস্থা অর্থাৎ bigbang এর বিন্দু ভর বা pointmass বোঝানো হয়েছে.