সম্প্রতি প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার নিয়ে ব্যাপক প্রচার শুরু হয়েছে। আর এস এস-এর অনুগামী কোনো এক দীননাথ বাত্রা হিন্দিতে কিছু বই লিখে প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বহু দাবিদাওয়া উত্থাপন করেছিল। গুজরাতের বিজেপি সরকার তার সেই বইগুলিকে গুজরাতি ভাষায় অনুবাদ করে রাজ্যের স্কুলগুলোতে আবশ্যিক পাঠ্য হিসাবে ছাত্রদের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণ করে। সেই সব অনুদিত বইয়ের ভূমিকা লিখে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার গুরুত্ব ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দেন। তারপর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কিছু কাল পর মোদী নিজে মুম্বাইয়ের এক প্রাইভেট হাসপাতাল উদ্বোধন করতে গিয়ে গণেশের হাতির মুণ্ড উল্লেখ করে প্লাস্টিক সার্জারি এবং কর্ণের জন্মকথা শুনিয়ে জেনেটিক্স-এর যে কী বিরাট অগ্রগতি ভারতে এক কালে হয়েছিল, তা তুলে ধরেন। আশ্চর্যের কথা যে শ্রোতারা, যাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই বেশ কিছু পাশ করা ডাক্তারও ছিলেন, চা সিঙারা স্যান্ডুইচ বিরিয়ানির সাথে সাথে জ্ঞানী মোদীর এই বাণীগুলিও অক্লেশে খেয়ে হজম করে ফেলেন। সেই সঙ্গে সবচাইতে উৎকৃষ্ট ঘটনাটি ঘটে এই বছর ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে। সেখানে জাঁকজমক সহকারে একটা বিশেষ অধিবেশন রাখাই হয় প্রাচীন ভারতে ঋগবেদের যুগে কী কী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আয়ত্তে ছিল তার ব্যাখ্যানে। একজন পাইলট (বিজ্ঞানীদের সভায় পাইলট?) এসে দাবি করেন, সেকালে বিমান চলত। সেই থেকে . . .
আমরা মনে করি, যাঁরা যুক্তি তথ্য দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন, বেদের যুগে এই সব প্রযুক্তি ভারতে বিকশিত হয়নি, তাঁরা তর্কযুদ্ধটা করছেন অনেক পেছন থেকে। অনেকটাই আত্মরক্ষামূলক কায়দায়। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের তরফে এইভাবে আত্মরক্ষার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আমার মতে আসল প্রশ্ন আদৌ এটা নয় যে প্রাচীন ভারতে জিনতত্ত্ব বা প্লাস্টিক সার্জারি ছিল কি ছিল না। প্রশ্নটা হল, এই সব থাকা সেদিন সম্ভব ছিল কিনা। যাবতীয় যুক্তিতর্ক সেখান থেকে শুরু করতে হবে।
[১]
বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির বিকাশের একটা নির্দিষ্ট গতিপথ আছে। তাদের বিকাশ খাপছাড়াভাবে, এলোমেলোভাবে হয় না। তার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মানুষ মূলত প্রযুক্তিই আয়ত্ত করেছে। তার পেছনের তত্ত্ব তার জানা ছিল না সেদিন। সেই সব আনুষঙ্গিক তত্ত্ব সে জেনেছে ধীরে ধীরে, অনেক পরে। যেমন, মানুষ ধাতু ব্যবহার করছে প্রায় ছয় হাজার বছর আগে থেকে। কিন্তু ধাতু রসায়ন সে আয়ত্ত করেছে মাত্র দুশ বছর আগে। আজ থেকে মাত্র চারশ বছর আগেও পৃথিবীর কোথাও মানুষ আটটার বেশি ধাতুর পরিচয় পায়নি। সোনা রূপা লোহা টিন দস্তা তামা সিসা পারদ। সেই জন্যই কোনো দেশের জ্যোতিষশাস্ত্রকেই অষ্টধাতুর বেশি কিছু বলতে শোনা যায়নি। এমনকি এই ভারতেও। কিংবা যেমন, আগুনের ব্যবহার। মানুষের পূর্বপুরুষ আগুন আয়ত্ত করেছিল প্রায় ২৮-৩০ লক্ষ বছর আগে। আর দহন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানতে পেরেছে মাত্র দু-শ বছর বা তার কিছুকাল আগে থেকে—ল্যাভোয়াশিয়র কাজের মধ্য দিয়ে। একইভাবে মানুষ সমুদ্রের জলে জাহাজ ভাসিয়েছে বেশ কয়েক হাজার বছর আগে থেকে। কিন্তু উদস্থিতিবিদ্যার শুরু হয় আর্কিমিদিসের সময়ে, আর উদ্গতিবিদ্যা (hydrodynamics)-র শুরু হল সেই নিউটনের হাত ধরে।
এই অবস্থা বহাল ছিল যতক্ষণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমস্যাগুলি ছিল সহজ সরল। প্রকৃতিতে হাতের সামনে সাদামাটা যে সব জিনিসপত্র পাওয়া যায় তাদের নিয়ে যখন কাজ করতে হচ্ছে তখন প্রয়াস-ব্যর্থতা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কিছু কিছু জিনিস করে ফেলা সম্ভব ছিল। কিন্তু একটা সময় থেকে চাকা উলটো দিকে ঘুরতে শুরু করল। কোপারনিকাস-উত্তরকালে প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানের বিকাশের প্রক্রিয়াটা ধীরে ধীরে বিপরীত ক্রমে ঘটে চলেছে। প্রথমে এসেছে তত্ত্ব, মৌলিক ধারণা, মূল কিছু সত্য। তার ভিত্তিতে তাকে কাজে লাগানোর মতো প্রযুক্তিগত ভাবনা। যেমন, নিউটনের বলবিদ্যা থেকে এল যন্ত্রবিদ্যা এবং যান্ত্রিক প্রযুক্তির ব্যাপক অগ্রগতি। আলোকবিজ্ঞানের অগ্রগতির পথ বেয়ে এল নানা রকম দেখার যন্ত্রপাতি। লেন্স, টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ, আরও কত কী। একের পর এক। রসায়ন শাস্ত্রের বিকাশের ফলে বহু রকম রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি করার কায়দাকানুন মানুষ শিখে ফেলল। জীববিজ্ঞানের যত উন্নতি হতে লাগল, ততই চিকিৎসাশাস্ত্র ভেষজবিদ্যারও উন্নতি হয়ে চলল। ফ্যারাডে-ম্যাক্সওয়েল-এর কাজের আগে বিদ্যুৎ শক্তিকে ব্যবহার করার মতো কোনো প্রযুক্তি মানুষ করায়ত্ত করে উঠতে পারেনি। এইভাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ক্ষেত্রেই কথাটা সমানভাবে সত্য।
আসলে সমস্যাটাকে এইভাবে ভেবে দেখা যেতে পারে। ধরুন, জিন প্রযুক্তির কথা। এর জন্য আপনাকে জিনের ব্যাপারে জানতে হবে। জিন সম্পর্কে জানার অর্থ হল, জীব কোষ, তার ভেতরে নিউক্লিয়াস, তার ক্রোমোজোম, তার মধ্যেকার ডি-এন-এ আর-এন-এ, ইত্যাদি জানা দরকার। তার মানে হল জীবের অঙ্গসংস্থান শারীরতত্ত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে হবে। প্রাণীবিদ্যা উদ্ভিদবিদ্যার জ্ঞান বিকশিত হল না, কোষ সম্পর্কে কোনো ধারণা জন্মায়নি, অথচ জিনবিদ্যা এবং জিন প্রযুক্তি এগিয়ে গেছে—জ্ঞানের রাজ্যে এমনটা কখনও হয় না। একইভাবে, গরুর গাড়ি বা ঘোড়ায় টানা গাড়ি থেকে এক লাফে বাষ্পীয় ইঞ্জিন কিংবা পেট্রোল-ডিজেল চালিত গাড়ি এসে যেতে পারে না। মাঝখানে শক্তির ব্যবহার ও তার নিয়ম জানতে হবে, শক্তির উৎস হিসাবে বিভিন্ন জ্বালানির ভৌত-রাসায়নিক ধর্ম সম্বন্ধে জানতে হবে, ধাতুবিদ্যার বিকাশ ঘটতে হবে, তাপগতিবিদ্যার নিয়মকানুন সম্পর্কে অবহিত হতে হবে, এই রকম অনেক কিছু জানার পর তবে বাষ্পীয় ইঞ্জিন বা তেল-চালিত ইঞ্জিনের আবিষ্কার সম্ভব হতে পারে। কেউ যদি এই সব সহযোগী জ্ঞানের বিকাশের ইতিহাস অনুক্ত রেখে একটা বিশেষ কোনো আবিষ্কারের কথা বলতে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই নেই।
[২]
এবার আর এক দিক থেকেও বিষয়টাকে দেখা দরকার।
বিজ্ঞানের কোনো শাখাতেই একা একা বিকাশ ঘটে না। পৃথিবীর কোথাও এমনটা হয়নি যে, পদার্থবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে গেছে কিন্তু রসায়নের বিকাশ হয়নি, জীববিদ্যা স্থবির হয়ে আছে, গণিতের বিকাশ রুদ্ধ। এরকমটা হয়ত দু পাঁচ দশকের আগে-পরে হলে হতেও পারে। কিন্তু দু পাঁচ শতকের হতে পারে না। এটা কোনো কাকতলীয় ব্যাপার নয় যে কোপারনিকাসের বইটা যে বছর (১৫৪৩) বেরয়, সেই একই বছরে বেরিয়েছে ভেসালিউসের মানবশরীর-গঠন সংক্রান্ত বইটি। গ্যালিলেও যখন টেলিস্কোপ বানিয়ে বৃহস্পতির দিকে তাক করছেন, তখন তাঁকে (এবং সেই সঙ্গে আরও অনেককে) লেন্স সম্পর্কেও ভাবতে হয়েছে। নিউটন যখন আধুনিক পদার্থবিদ্যার বিকাশ ঘটাচ্ছেন, তখন তিনি একই সাথে আধুনিক ক্যালকুলাস গণিতেরও জন্ম দিচ্ছেন। এবং আরও অনেকেই গণিতের নতুন শাখার জন্ম দিচ্ছেন। সেই থেকে পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে যেন তাল মিলিয়েই আধুনিক গণিতের বিকাশ হয়ে চলেছিল।
প্রাচীন কালে কিছু দূর বিকশিত হওয়ার পর মধ্য যুগের এক বিস্তৃত সময় ধরে সারা পৃথিবীতেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ প্রায় অবরুদ্ধ হয়েছিল। কেন, সেই আলোচনায় আপাতত আমরা ঢুকছি না। ইউরোপে নবজারণের যুগে এসে আবার নতুন করে বিজ্ঞান যুক্তিবাদ এবং প্রযুক্তির বিকাশের দরজা খুলে গেল। তারপর থেকে প্রথমে ইউরোপে, পরে অন্যান্য দেশেও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এই বিকাশ অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। এই দিক থেকে দেখলে সহজেই বোঝা যাবে, যে দেশে যে সময়ে জিনতত্ত্বের বিকাশ ঘটবে, সেখানে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও অনুরূপ বিকাশ ঘটে যাওয়া প্রয়োজন এবং স্বাভাবিক। পদার্থবিজ্ঞান রসায়ন জীববিজ্ঞান গণিত ভূতত্ত্ব বিবর্তন-তত্ত্ব বংশগতিবিদ্যা ইত্যাদিতে কিছুই জানলাম না, কিন্তু কোষের মধ্যে জিন খুঁজে পেয়ে গেছি এবং তা নিয়ে নাড়াচাড়া করছি—এটা বাস্তবে সম্ভবই নয়। সাধারণ বুদ্ধিতেই একথা বেশ বোঝা উচিত। আবার সজীব কোষের ভেতরে জিন খুঁজবার বা নাড়াচাড়া করবার জন্য যে ধরনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিগুলো চাই সেগুলো আসবে পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞান থেকে, ধাতুবিদ্যার প্রায়োগিক বিকাশ থেকে, যন্ত্রপাতি নির্মাণের যথেষ্ট উন্নতির পথ ধরে। অন্য দিকে, যে ধরনের গবেষণাগারে এই জাতীয় খোঁজার কাজ পরিচালনা করা সম্ভব, তার জন্য চাই নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ। তার মানে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত জ্ঞান এবং বৃহদায়তন চলবিদ্যুৎ উৎপাদন করার মতো প্রযুক্তি তার আগে আয়ত্তাধীন হওয়া চাই, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই রকমভাবে বহু জিনিস নিয়ে ভাবতে হবে। কেউ যদি এই সব প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে শুধু দাবি করেন যে কোনো এক সময় অমুক জ্ঞান বা তমুক প্রযুক্তি বিকশিত হয়েছিল, তাহলে বুঝতে হবে, তিনি জানেনই না তিনি কী নিয়ে কথা বলছেন। তাঁদের এই সব বিষয়ে কথা বলারই অধিকার নেই।
[৩]
আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, পশ্চিমা দেশগুলিতে যে আবিষ্কারগুলি হয়ে গেছে বলে ইতিমধ্যেই জানা আছে, প্রাচীন ভারতে শুধু মাত্র সেই সব আবিষ্কারের কথাই শোনা যায়। এরকম দাবি কাউকে করতে শোনা বা দেখা যায় না যে আমরা অমুক জিনিসটা আবিষ্কার এবং উদ্ভাবন করে ফেলেছি; কিন্তু দ্যাখ, দ্যাখ, ওরা এখনও এটা করে উঠতে পারেনি। আরও আশ্চর্যের, আমাদের দেশের আবিষ্কার, সেই আদ্যিকালের ঘটনা, অথচ, তার নামটা শুধু পশ্চিমি দেশের দেওয়া তাই নয়, একেবারে টাটকা আধুনিক নাম।
তা না হলে, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, প্রাচীন ভারতে যখন গণেশের ধড়ে হাতির মুণ্ড লাগানো হয়েছিল, তার নাম প্লাস্টিক সার্জারি হতে যাবে কেন? যিনি বা যাঁরা এই রোমাঞ্চকর কাজটি করেছিলেন, তিনি বা তাঁরা খাঁটি আর্য সংস্কৃত ভাষায় একখানা শিরোনাম খুঁজে পেলেন না? এই যেমন, “অথঃ অন্যশরীরেতর মুণ্ডযোজন” বা এই জাতীয় কিছু? আবার প্রাচীন ভারতীয় মুনিঋষিরা যে জিনতত্ত্বের বিকাশ ঘটালেন, তার নাম তাঁরাও রাখলেন সেই জিন দিয়েই? কোষ-কীট, কোষাণু, কোষ-রেণু, এরকম শব্দ লাগালেন না? ব্যাপারটা কেমন যেন সন্দেহজনক বলে মনে হয় না? আমরা দেখেছি, প্রাচীন কালের মানুষেরা যে গাছপালা চিহ্নিত করেছিলেন তাদের নাম দেশি ভাষাতেই রেখেছিলেন। গাছকে বৃক্ষ বলেছেন, অশ্বত্থকে অশ্বত্থ বলেছেন, হর্তুকিকে হরিতকি বলেই ডেকেছেন, ছাতাকে ছত্রাক বলেছেন, ইত্যাদি। কোনো গ্রিক লাতিন আংরেজি নামে ডাকতে হয়নি। একইভাবে তাঁরা সিংহকে সিংহ বলেছেন, বাঘকে ব্যাঘ্র, বেড়ালকে মার্জার, কুকুরকে সারমেয়, ইত্যাদি আর্য সংস্কৃতির শব্দভূষণে সাজিয়েছেন, কোনো বিদেশি নামে আবাহন করেননি। সুতরাং বোঝাই যায়, সেকালে তাঁদের গ্রিক লাতিন নামের প্রতি কোনো বিশেষ প্রীতি ছিল না। জানার প্রশ্ন না হয় বাদই দিলাম।
এই অবস্থায়, যখন আমরা দেখি, এদেশীয় পণ্ডিতরাও অ্যামিবাকে অ্যামিবা, ডি-এন-এ-কে ডি-এন-এ, জিনকে জিন বলছেন, সহজ সরল মনে ধরে নিই, জিনিসগুলো এ দেশে নতুন; তাই এদের নামকরণে অসুবিধা হচ্ছে। নতুন পারিভাষিক নাম দিলে তাতে অনেক সময় বোঝাতে সুবিধা তো হয়ই না, বরং বাড়তি ঝামেলা হয়। তার থেকে পরদেশি নামগুলিই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিয়ে রাখছি। ছাত্ররা একবারেই এই নতুন বৈজ্ঞানিক শব্দগুলোর আন্তর্জাতিক নামকরণ জেনে যাচ্ছে।
কিন্তু যে সমস্ত আবিষ্কার বহুকাল আগেই এই দেশেই ঘটে গেছে, করেছেন এই দেশেরই মুনিঋষিরা, তাদের বেলায় বিদেশি নামকরণ কেন?
এই রহস্য ভেদ করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, আসলে আমাদের প্রাচীন জ্ঞানীরা শুধু মাত্র সেই সব জিনিসই জানতে বা আবিষ্কার করতে পেরেছেন, যেগুলো বিদেশিরা এখন একে একে আবিষ্কার করতে পেরেছে। এই প্রাচীন আবিষ্কারগুলির খবর যে সঙ্ঘ পরিবারই প্রথম আমাদের শোনালেন তা নয়। একেবারে সেই বঙ্কিমের আমল থেকেই এই কাণ্ড চলে আসছে। ডারউইন সাহেব জীব বিবর্তনের এক তত্ত্ব হাজির করলেন, যা নিয়ে সারা পৃথিবীতেই ঝড় উঠল। আমাদের দেশের একদল পণ্ডিতও খবর পেলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, এ তো আমাদের অনেক দিনের আবিষ্কার। জন্মান্তর, জাতকের গল্প, কত যোনিতে ভ্রমণ করে তবে মানব জনম—এমনি আরও কত সূত্র তার পাওয়া গেল। মজার কথা হচ্ছে, সূত্রগুলো কিন্তু সহস্রাধিক বছর ধরেই ছিল। কিন্তু তাতে যে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বিবর্তনের খবর ছিল, তা আমরা জানতাম না। ১৮৫৯ সালে ডারউইন যেই বললেন, অমনি আমরা জেনে গেলাম . . .।
কিংবা ধরুন, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। ইউরোপ থেকে ভারতে চালান হতে একটু সময় লেগেছে। একটু কঠিন কিনা। কিন্তু যেই না চালান হল, সাথে সাথে কিছু জ্ঞানবৃদ্ধ জেনে গেলেন, আরে? এও তো আসলে আমাদেরই জিনিস। ব্রহ্মার একদিন সাধারণ মানুষের কত কল্প মনে নেই? পুরাণেই তো লেখা আছে। মুশকিল হচ্ছে, লেখা তো আগে থেকেই ছিল। কম পক্ষে দেড় দুহাজার বছর আগে থেকেই। তখন কিন্তু জানা যায়নি, এর মধ্যে আপেক্ষিকতা নামক কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বীজ লুকনো আছে। বীজটা ধরা পড়ল যেই ওদের থেকে ব্যাপারটা আমাদের দেশে আমদানি হয়ে এল।
স্কুল জীবনে শোনা একটা চুটকি গল্পের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। ব্রিটিশ জার্মান আমেরিকান এবং জাপানি প্রকৌশলীদের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে কে কত সূক্ষ্ম জিনিস বানাতে পারে তা নিয়ে। প্রত্যেকেই দারুণ দারুণ সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনের কথা বলছে। হঠাৎ তাদের খেয়াল হল, সঙ্গে একজন ভারতীয় প্রযুক্তিবিদও বসে আছে, চুপচাপ সবার কথা শুনছে কিন্তু মুখে কিছু বলছে না। শুধু মুচকি মুচকি হাসছে। তারা সবাই মিলে তাকে চেপে ধরল, “তুমি কিছু বলছ না কেন ভাই? তোমরা কী বানাতে পার বল।” ভারতীয় কুশলী তখন এক গাল হেসে বলল, “আমরা একটাই জিনিস পারি। সেটা করা তোমাদের কারোরই সাধ্য নয়। তোমরা যে যাই বানাও, আমরা তার গায়ে ‘ভা-র-তে-তৈ-রি’ একটা ছাপ মেরে দিই।”
বোধ হয়, এখন সেই ছাপাখানার কাজ বেড়ে গেছে।
[৪]
চতুর্থ সমস্যাটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সকলেই জানেন, মানুষ যবে থেকে গ্রন্থাকারে নিজেদের চিন্তাভাবনা গুছিয়ে লিখতে শিখেছে, একটা ন্যূনতম শৃঙ্খলা সে আয়ত্ত করে নিয়েছে। যে বিষয়ের গ্রন্থ সেই গ্রন্থে সেই বিষয়ের উপরেই প্রধানত আলোচনা থাকে। গণিত নিয়ে যা কিছু সে লিখেছে তা গণিতের গ্রন্থেই লিখে রেখেছে। জ্যোতিষের কথা সে লিখেছে জ্যোতিষের গ্রন্থে। চিকিৎসা বিষয়ক সমস্যা নিয়ে আলোচনা রয়েছে এতদ্বিষয়ক গ্রন্থে। ভারতবর্ষ, এমনকি প্রাচীন ভারতও এই ব্যাপারে কোনো ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু আধুনিক কালে যাঁরা প্রাচীন ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানের যাবতীয় আবিষ্কার খুঁজে বেড়ান এবং খুঁজে পেয়েও যান, তাঁরা সকলেই সেই সব বিজ্ঞানের কথা যত্রতত্র খোঁজেন। হয়ত চুম্বক দেখলেন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, বিদ্যুৎ খুঁজলেন মহার্ণবতন্ত্রে, আপেক্ষিকতা ব্রহ্মাপুরাণে, গ্যোয়েডেল-এর উপপাদ্য শ্রীমদ্ভাগবতে, গণেশের প্লাস্টিক সার্জারি দুর্গাস্তোত্রে, জিনতত্ত্ব মহাভারতে, এইরকম আর কি। এইভাবে পৃথিবীর কোথাও বিজ্ঞানের কাজকর্ম হয়েছে কিনা, এমনকি প্রাচীন ভারতেও হয়েছে কিনা আমার জানা নেই।
সমস্যাটার গভীরতা বুঝবার জন্য আমি কয়েকটা উদ্ভট সাম্প্রতিক উদাহরণ বানিয়ে বলছি।
ধরুন যদি শোনেন, কেউ বার্ট্রান্ড রাশেলের রচনাবলিতে প্লাস্টিক সার্জারি খুঁজে পেয়েছে, জন ডিউইএর কোনো বইতে কোয়ান্টাম মেকানিক্স আছে বলে জেনেছে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য থেকে ডারউইন পাঠ করতে সক্ষম হয়েছে, আগাথা ক্রিস্টির রহস্য উপন্যাসে পিরিয়ডিক টেবিলের সন্ধান পেয়েছে—আপনার কী মনে হবে? নিশ্চয়ই তাকে পাগল বলে মনে হবে আপনার। কিংবা বিপরীতক্রমে, ধরুন, আপনি এই সব বিষয়ে খানিক জানতে চাইলেন, আর আপনাকে সেই ব্যক্তি এই সমস্ত উৎস গ্রন্থের সন্ধান দিলেন—তখনই বা আপনার কীরকম লাগবে? নিশ্চয় সেই ভদ্রলোককে খুব সুস্থ বলে মনে হবে না?
অথচ, যাঁরা আমাদের দেশে প্রাচীন ভারতের মুনিঋষিদের দ্বারা সমস্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন করিয়ে নিতে চাইছেন, তাঁদের সূত্রগ্রন্থগুলি ঠিক এই জাতের। বিজেপি সঙ্ঘ পরিবার বা এই জাতীয় লোকেরা যখন এইসব প্রচার করে, তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। তাদের কাছে বিষয়টা আদৌ যুক্তিতর্কের সমস্যাই নয়। তারা বলেই খালাশ। কিন্তু যাঁরা বিশ্বাস করেন, আমি এখানে তাঁদের এই সব দিক ভেবে দেখতে বলছি।
কিছু দিন আগে দেখলাম, একদল লোক দাবি করছেন, ঋগবেদে নাকি পিথাগোরাসের উপপাদ্যের কথা লেখা আছে। কথাটা সত্য হলে পিথাগোরাসের অন্তত এক হাজার বছর আগেই ভারতে এই উপপাদ্যটির জন্ম হয়ে যাওয়ার কথা। সাংঘাতিক ব্যাপার! পরিচিত দু-একজন আমাকে জিগ্যেস করলেন, “আপনি কি জানেন এই ব্যাপারে কিছু?”
আমি তাঁদের বলেছিলাম, “কিছু তো জানি নিশ্চয়ই। কিন্তু বলুন তো, ঋগবেদে পিথাগোরাসের উপপাদ্য কেন থাকবে? থাকার কি কথা? ওটা কি জ্যামিতির কোনো গ্রন্থ? গাণিতিক কোনো রচনা? ওতে এসব থাকবে কেন? আপনারা আশাই বা করেন কীভাবে যে ঋগবেদে এরকম কিছু থাকবে? আর যদি সত্যিই থাকত, তাহলে তা কি পিথাগোরাসের নামে থাকত? সে তো থাকত কোনো না কোনো বৈদিক ঋষির নাম ধরে। যাঁরা বলছেন, তাঁরা সেই নামটির কথা বলছেন না কেন? সংশ্লিষ্ট উপপাদ্য প্রসঙ্গে সেই পিথাগোরাসের নামই কেন ঘুরে ফিরে আসছে?” আর একটা কথাও ভাবতে বলেছিলাম। পিথাগোরাসের উপপাদ্যের প্রধান অনুষঙ্গ হল বর্গক্ষেত্রের ধারণা। ঋগবেদ হামাম দিস্তা দিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেললেও তাতে বর্গক্ষেত্রের কোনো উল্লেখই দেখতে পাবেন না কোথাও। কারণটা সেই একই। ওখানে এসব প্রসঙ্গ থাকার কথা নয়। উপপাদ্যটা আসবে কোত্থেকে?
এইভাবে সচেতন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে ভাবতে হবে। যুক্তি দিয়ে উত্তর খুঁজতে হবে। শুধু তথ্য দিয়ে খুঁজতে গেলে আপনাকে মাক্সম্যুলার-ওল্ডেনবার্গ যুগ্ম-সম্পাদিত পঞ্চাশ খণ্ডের সেই সুবিখ্যাত “প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থাবলি” নিয়ে বসে বসে ঘাঁটতে হবে। সময় থাকলে এবং হাতে অন্য কাজ না থাকলে সেটাও কোনো খারাপ কাজ নয়। তবে অতটা পরিশ্রম করে এই সব ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত যা জানতে পারবেন, একটু বুদ্ধি প্রয়োগ করে যুক্তি দিয়ে ভাবলে অনেক কম পরিশ্রম করেও তাই দেখতে পাবেন।
[৫]
নাঃ। বড্ড তাত্ত্বিক কচকচি হয়ে গেছে এ পর্যন্ত। এবার একটু বাস্তব ঘটনার দিকে নজর দেওয়া দরকার। যে দুচারটে ঘটনার খুব টাটকা টাটকা প্রচার চলছে চারদিকে তা নিয়ে এবার কিছুটা বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ করা যাক। তবে তার আগে, প্রথমেই একটা কথা বলে রাখি: বিজ্ঞানে গোঁজামিল চলে না। কেউ যে কখনও বিজ্ঞানের তত্ত্বেটত্ত্বে গুলতাপ্পি দেয় না, বা, পরীক্ষার ফলে কারচুপি করে না, এমন নয়; তবে বেশি দিন তা চলে না। কেন, সেটা বুঝে নেওয়া যাক। তারপর প্রাচীন ভারতের উদ্ভাবনী কীর্তিকাহিনির ভেতরকার গোঁজামিলগুলো নিয়েও কিছু কথা বলতে হবে।
বিজ্ঞানে প্রতিটি দাবির তিনটি করে পরীক্ষা দিতে হয়। প্রথম পরীক্ষা তার নিজের ভেতরে। যা দাবি করা হল, তার সমর্থনে যে সমস্ত তথ্য যুক্তি বিশ্লেষণ হিসাবনিকাশ উপস্থিত করা হয়েছে তার মধ্যে কোনো অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্য আছে কিনা। একে বলা যেতে পারে আভ্যন্তরীন সামঞ্জস্য (internal consistency)। সেই ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হলে যেতে হবে দ্বিতীয় পরীক্ষায়। সেখানে দেখতে হয়, এযাবত প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলির সাথে তার কোথাও কোনো রকম বিরোধ দেখা দিচ্ছে কিনা। একে বলা যায় পারস্পরিক সামঞ্জস্য (external consistency)। এটা একটা বড় পরীক্ষা। যদি এরকম বিরোধ না হয়, অর্থাৎ, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একবার হতে পারলে একটা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে অনেকটাই রাস্তা সাফ হয়ে গেল বলে ধরে নিতে হবে। আর সব শেষে আসে হাতে-কলমে পরীক্ষা এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ (experiment and application)। যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দাবি উত্থাপন করা হয়েছে, হয় সেই সিদ্ধান্তের পক্ষে সরাসরি, অথবা, তার থেকে নিষ্কাশিত কোনো উপসিদ্ধান্তের পক্ষে যাচাইয়ের উপযোগী এক বা একাধিক হাতে-কলমে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। যাচাইয়ের পরীক্ষায় যদি সে বাতিল হয়ে না যায়, তবে অন্তত কিছুদিনের জন্য সেই দাবিটি টিকে গেল। সেই সাথে যদি তার কোনো ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটানো যায়, তাহলে তো আরও খাসা। আর তার বিরুদ্ধে কিছু বলার প্রায় কোনো সুযোগই থাকে না। এত রকম কঠিন কঠোর পরীক্ষার ভেতর দিয়ে যেতে হয় বলেই বিজ্ঞানে যদি বা কেউ কখনও কিছু গোঁজামিল দিয়েও ফেলেন, তা বেশি দিন ধোপে টেকে না।
তার উপর বিজ্ঞানীদের ইদানিংকালে (গত চারশ বছর ধরে) বড় বড় সম্মেলনে মিলিত হয়ে পাঁচ জনের সামনে নিজের আবিষ্কারের কথা বলতে হয়। সেখানে সকলেই বসে থাকেন যেন ওঁত পেতে—কেউ সামান্য ভুল কিছু বললেই একেবারে চেপে ধরতে। সবচাইতে বড় ব্যাপার, তাতে কে বড় কে ছোট কোনো বাছবিচার হয় না। ১৯১২ সালের কথাই ভাবুন। আইনস্টাইন তখন খ্যাতির তুঙ্গে। সেখানে হল্যান্ডের পিটার ডিবাই কে, লোকে তখন ভালো করে জানেই না। সেই তিনি আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তাপের এক ফর্মুলায় সংশোধনী এনে বসলেন। সেটাই কিন্তু বিজ্ঞানে ডিবাই-মডেল নামে স্থায়ী জায়গা পেয়ে গেল। কারণ, উপরের ওই তিনটে যাচকাঠি। আইনস্টাইনের নামডাক কিন্তু তাঁর ফর্মুলাকে বাঁচাতে পারল না।
চলুন, এবার একটু গণেশের ব্যাপারটা নিয়ে বোঝার চেষ্টা করি।
প্রাচীন কালের ভারতীয় বদ্দিরা যে প্লাস্টিক সার্জারিতে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন তার নমুনা হল মুণ্ডহীন গণেশকে হাতির মাথা জুড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ করে তোলা। হ্যাঁ, একটাই মাত্র নমুনা। কয়েক হাজার বছরে এরকম কেস আর একটাও পাওয়া যায় না। না না, তাতে কী হয়েছে? তার জন্য এতে অবিশ্বাস করার কিছু নেই। গাঁজাখুরি গল্প বলে উড়িয়েও দিচ্ছি না। শুধু উপরে বলে আসা প্রথম দুটো যাচকাঠি প্রয়োগ করে দেখব একটু।
মানুষ আর হাতির ধড়ে যে অনেকখানি পার্থক্য সেটা আশা করি সকলেই মানবেন। আকারে পার্থক্যই আপাতত ধরছি। তাতে কী কী আসে যায় দেখা যাক। জুড়বার পর বেঁচে থাকতে গেলে রক্ত সংবহনের জন্য শিরা আর ধমনীর সংযুক্তি একটা বড় প্রয়োজন। হাত পা নাড়ার জন্য স্নায়ুতন্ত্রের কাঠামোতেও সামঞ্জস্য থাকা দরকার। হাতির শিরা আর ধমনীর সাথে মানুষের শিরা আর ধমনীগুলো কি মিলতে পারে? হাতির মাথা থেকে যে স্নায়ুগুলি নেমে আসছে, তারা কি মানুষের হাত বা পায়ের স্নায়ুর সাথে আকারে মিলবে? গণেশের মেরুদণ্ডের সাথে হাতির মেডালা? পেশীগুলোর কথা না হয় বাদই দিলাম। পক্ষান্তরে, মানুষের রক্তই যেখানে একজনেরটা আর একজনকে গ্রুপ না মিলিয়ে দেওয়া যায় না, সেখানে হাতির রক্তের সাথে মানুষেরটা না মিললে (মেলার যে প্রশ্নই নেই এটা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দিতে হবে না) মা দুর্গার বড় ছেলেটি বাঁচবে কী করে?
ব্যাসদেবের বা সেকালের অন্য কারোর এত সব জটিল বিষয় জানারও কথা নয়, ভাবারও কথা নয়। তাঁরা যেটুকু জানতেন, তার ভিত্তিতে লিখে বা বলেই খালাশ, শ্রোতারাও শুনেই আকুল। তখন নৃসিংহ প্রাণীও (থুড়ি, তিনি আবার নাকি ভগবানের এক অবতার-রূপ!) ছিল, মৎসকন্যাও ছিল। সুতরাং গণেশের . . . । কিন্তু ২০১৫ সালে যিনি এসব বলবেন, আর যাঁরা শুনবেন, তাঁদেরও কি না ভাবলে চলবে? আর যদি তাঁরা না ভেবেই এই সব কথা বলে এবং শুনে থাকেন, তাঁদের বুদ্ধি সম্পর্কে কী বলা হবে?
কর্ণ আর যিশুর জন্ম কাহিনিতে বেশ অনেকটাই মিল। দৈব সঙ্গমে শিশুর জন্ম, কিন্তু জননী দুজনই অক্ষতযোনী নিয়ে কৌমার্য রক্ষা করতে পারলেন। এর সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের জিনতত্ত্বকে মেলানো যাবে কী করে? যতক্ষণ দৈবী ব্যাপার হিসাবে ব্যাখ্যা করা হবে, ততক্ষণ তার বিচার একভাবে করতে হবে। আমরা বিজ্ঞান বা যুক্তির তরফে যাই বলি না কেন, যাঁরা মনে করেন, দুনিয়ায় অলৌকিক ঘটনা বলেও কিছু আছে, সব কিছুর ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দিতে পারে না, ইত্যাদি, তাঁরা নিজেদের মাঠে দাঁড়িয়েই কথা বলছেন। সেখানে মৌলিক বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নের ফয়সালা আগে না করা হলে আলোচনা এগোতেই পারবে না। কিন্তু যখন বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে বলার চেষ্টা করা হবে, তখন মাঠ বদলে ফেলা হচ্ছে। বিজ্ঞানের জায়গায় খেলতে এসে তো আর বলা যায় না, আমরা জিনের কথা বলব, কিন্তু ব্যাখ্যা দেব আমাদের মতো করে। এখানে জিন বললেই ক্রোমোজোমের কথাও বলতে হবে, ক্রোমোজোম বললে জনন কোষের প্রসঙ্গে যেতে হবে, জনন কোষ থেকে যৌন সঙ্গমের কথায় ঢুকতে হবে—এই হচ্ছে বিজ্ঞানের তরফে স্বাভাবিক যুক্তিপ্রক্রিয়ার অভিমুখ। আর এতদূর আসার পর যে আর কুন্তী এবং মেরির কৌমার্য সংক্রান্ত পৌরাণিক বক্তব্যকে বাঁচানো যাবে না, সে তো বলাই বাহুল্য।
গান্ধারীর শতপুত্র জন্মদানের পৌরাণিক কাহিনিকে যদি আধুনিক বিজ্ঞানের স্টেমসেল গবেষণার সাথে মেলাতে হয়, তাহলেও অনেক সমস্যা দেখা দেবে। সঙ্ঘ দপ্তরের একনিষ্ঠ কর্মী দীননাথ বাত্রা বা তার সুযোগ্য ছাত্র মাতাপুরকর সেই সব কথা ভেবে দেখেছে কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু বিষয়টা সকলের কাছে খোলসা করে বলা দরকার। গান্ধারীর শরীরের থেকে প্রাপ্ত কোষ থেকে যদি স্টেমসেল গবেষণার কৌশলে আদৌ কোনো সন্তানের জন্মদান সেদিন সত্যিই সম্ভব হয়ে থাকেও, সেই সন্তান (বা সন্তানেরা) কন্যাই হতে পারত, পুত্র নয়। কিন্তু যখনই কাহিনিতে বলা হল যে একশ পুত্র এবং একজন মাত্র কন্যা জন্ম নিয়েছে, তা স্টেমসেল প্রযুক্তির আওতার বাইরে চলে গেল। অন্য গবেষণার কথা বলুন, অন্য নাম দিন তার। কিন্তু স্টেমসেল প্রযুক্তি দিয়ে আপনাদের কাজ হবে না। তাছাড়া, এই জাতীয় সমস্যাগুলো একবারে ভেবে নিতে হবে: বিপদে পড়ে নাম বদলালে বা অন্য প্রযুক্তির কথা বললে লোকেই বা কী বলবে?
বিজ্ঞানের সঙ্গে না মেলালে বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হিসাবে দাবি না করলে কিন্তু এই সব পরস্পর-বিরোধিতার সমস্যা উঠবে না। এখন এই প্রাচীন-বিজ্ঞানের দাবিদারদেরই ঠিক করে নিতে হবে, তাঁরা কী করবেন। তাঁরা অলৌকিক পৌরাণিক ব্যাখ্যাতেই মজে থাকবেন, নাকি, সবেতেই বিজ্ঞানের একটা রাবার স্ট্যাম্প লাগানোর চেষ্টা চালিয়ে যাবেন?
[৬]
বিমানের ব্যাপারটা নিয়ে বোধ হয় বিজেপি-র মধ্যেই দ্বিমত আছে। মুম্বাইয়ের বিজ্ঞান কংগ্রেসে যখন সঙ্ঘ-মার্কা এক বিমান-চালক (নাগপুর কোম্পানির চোখে নিশ্চয়ই একজন আধুনিক ঋষি), দাবি করছিলেন, বৈদিক যুগে ভারতে বিমান চলত, ঠিক তখনই ফেসবুকে দেখলাম, রাইট-ভ্রাতৃদ্বয়-এর আগেই কে একজন মারাঠি প্রযুক্তিবিদ ১৯০৬ সালে নাকি ভারতেই প্রথম বিমান উড়িয়েছিলেন। এই নিয়ে কিঞ্চিত ধন্দে আছি। কেন না, স্টেমসেল বা জেনেটিক্স বা প্লাস্টিক সার্জারির তুলনায় প্রাচীন ভারতে বিমান আবিষ্কারের দাবিটা একটু বেশিই পাকা হওয়ার কথা ছিল। ঋগবেদেও সূর্যের সপ্তাশ্ব রথের কথা আছে; রামায়নে রাবণের পুষ্পক রথের বিবরণ তো যথেষ্টই রোমাঞ্চকর। জ্বালানি, বায়ুগতিবিদ্যা (aerodynamics) বা ওঠানামার দৌড়পথ (runway)-এর খোঁজখবর কিছু না থাকলেও বায়ুরথের একটা স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। এরকম একটা সুযোগ ছেড়ে দিয়ে বিমান আবিষ্কারের সুপ্রাচীন কৃতিত্ব কেন ওদের কেউ কেউ আড়াই বা তিন হাজার বছর বাদে পিছিয়ে দিতে চাইছে, আমার কাছে এখনও পরিষ্কার নয়।
সে যাই হোক, এখানে আবার একটু বিজ্ঞানের দিক থেকে কিছু সমস্যার কথা না বললেই নয়। দাবিটা বিজ্ঞান কংগ্রেসে করেছেন কিনা! কুম্ভমেলায় বসে মাইকে প্রচার করলে এত সব কথায় যেতাম না। মুচকি হেসে রিমোট ঘুরিয়ে অন্য চ্যানেলে চলে যেতাম।
প্রথম হচ্ছে জ্বালানির ব্যাপারটা। জলে নৌকা বা জাহাজ ভাসাতে জ্বালানি না হলেও যে চলে তা সকলেই জানেন। মানুষ গত আট-দশ হাজার বছর ধরেই জল পরিবহন ব্যবহার করে আসছে। নবপলীয় যুগান্তরের এ এক অন্যতম অনবদ্য উদ্ভাবন। বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের আগে অবধি, অর্থাৎ, অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগের আগে পর্যন্ত পাল-তোলা জাহাজই ছিল একমাত্র জাহাজ। হাওয়া এবং মানুষের শক্তিই ছিল তার একমাত্র বলপ্রয়োগের উৎস। জাহাজের ক্ষেত্রে গরু ঘোড়া মোষ ইত্যাদি পশুর পেশীশক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি পৃথিবীর কোনো দেশেই। কেন, তা নিয়ে বেশ চিত্তাকর্ষক আলোচনা হতে পারে। কয়লা-চালিত বাষ্প-পোত হচ্ছে প্রথম জাহাজ যেখানে জ্বালানির ব্যবহার করা হয়েছে। এখন পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানি ব্যবহার করা হয়।
উড়োজাহাজের ক্ষেত্রে জ্বালানি ছাড়া বেশিদূর যাওয়া সম্ভবই না। বেলুন বানিয়ে ওড়া সম্ভব, সামান্য এধার ওধারও করা যাবে। কিন্তু ইচ্ছামতো কোনো নির্দিষ্ট দূরত্বে উড়ে যাওয়া, এবং একটু বেশি দূরে ভ্রমণ করা একেবারেই সম্ভব নয়। বেশি ওজন নিয়েও ওড়া যায় না। বিস্তারিত আলোচনা না করে শুধু একটুখানি ইশারায় বলি: জলের তুলনায় বায়ুর ঘনত্ব বড্ড কম বলে আর্কিমেদিসের নীতি এবং নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র প্রয়োগের সুফল পাওয়ার প্রায় কোনো সুযোগই থাকে না বেলুন নিয়ে ওড়ার সময়। অতএব জ্বালানি ছাড়া গত্যন্তর নেই। দৈবশক্তিতে পুষ্পক রথ চালাতেই পারেন; কিন্তু তাতে আবার মর্ত্য মানুষের নশ্বর বিজ্ঞানকে টেনে আনা যাবে না। বিজ্ঞানে আর দৈবে বিপুল বৈরভাব যে!
বায়ুগতিবিদ্যা আয়ত্ত না করেও যে বিমান চালানো যাবে না, এটাও এখনকার দিনে প্রায় সাধারণ জ্ঞান। নিউটনের হাত ধরে উদ্গতিবিদ্যা আয়ত্ত করার পর যে সমুদ্রে দূরপাল্লার জাহাজ চলাচলে অনেক সুবিধা হয়েছিল, সেই খবরটা সঙ্ঘ পরিবারের বাইরে কমবেশি সকলেই জানেন। উড়োজাহাজ উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে আবার উড়ানের জন্য প্রধান সমস্যাই ছিল বায়ুগতিবিদ্যার কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে জেনে বুঝে কীভাবে ব্যবহার করা হবে তার বন্দোবস্ত করা। তার ডিজাইন সেইভাবে বানানো। যতক্ষণ এই কাজটি না করা গেছে, বাতাসে ভর করে মানুষ কোনো যান চালাতে পারেনি। প্রসঙ্গত, এই ব্যাপারে আগ্রহী পাঠকেরা নারায়ণ সান্যালের “হে হংসবলাকা” বইটির প্রথমার্ধ পড়ে দেখতে পারেন। অনেক আকর্ষণীয় তথ্য এবং চিন্তার খোরাক পাবেন।
এই বিষয়টা বুঝলে তবেই পরিষ্কার হবে, বিমানের উড়ানের জন্য একটা বেশ লম্বা দৌড়পথ কেন অবশ্য প্রয়োজন। সমতল ভূমির উপর দিয়ে দৌড়তে দৌড়তেই বায়ুগতিবিদ্যার নিয়মে এবং বিশেষ নকশার কারণে বিমানের নিচের তলের তুলনায় উপরের পৃষ্ঠদেশের উপর দিয়ে বায়ুপ্রবাহের চাপ কমে যেতে থাকে। আর তার ফলেই যে নিউটনের তৃতীয় সূত্র কার্যকর হয়ে তাকে এক সময় মাটি থেকে উপরে ভাসিয়ে দেয়—এই ব্যাপারটা সকলেই বুঝতে পারবেন। নামার সময়ও বিমান মাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই থেমে যেতে পারে না। নিউটনের প্রথম সূত্র অনুযায়ী তাকে গতিজাড্যের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে অনেকটা রাস্তা দৌড়ে যেতে হয়। তবে সে থামতে পারে।
এত কথা বলার কারণ হল, রামায়ণ বা অন্যত্র আকাশে ভ্রমনের উল্লেখ দেখিয়েই বিমানের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দাবি করা যায় না। উপরোক্ত সমস্যাত্রয়ের সমাধানের কী ব্যবস্থা হয়েছিল শাস্ত্রসকল থেকে তারও উল্লেখ খুঁজে বের করতে হবে। না হলে এটাকেও সাদামাটা পৌরাণিক দাবি হিসাবেই বাজারে চালাতে হবে। বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব বলে দাবি করা যাবে না।
[৭]
যুক্তি বা তথ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্ত আবিষ্কার খুঁজে পাওয়ার আজগুবি দাবিগুলি যে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না, এটা আশা করি আমি উপরের আলোচনায় বোঝাতে পেরেছি। সত্য নয় বলেই এটা করা যায় না। উলটে একটা আজগুবি দাবি উত্থাপন করতে গিয়ে তার সপক্ষে আরও পাঁচটা বাজে গল্প দাঁড় করাতে হবে। মিথ্যার উপর আরও বড় মিথ্যার বোঝা একের পর এক জমতে থাকবে। নিজেদেরকে ক্রমাগত হাস্যকর জায়গায় নিয়ে গিয়ে ফেলতে হবে।
প্রশ্ন হচ্ছে, এরকম দাবি উত্থাপনের প্রবণতা এল কোত্থেকে? সঙ্ঘ পরিবারই কি এর প্রধান কারিগর? এই প্রশ্নটিরও উত্তর খোঁজা দরকার।
না। ওদের অনেক কাল আগে থেকেই ভারতে একদল প্রাচীনপন্থী অধ্যাত্মবাদী বলে আসছিলেন, বেদে সব কিছু আছে। দুনিয়ার সমস্ত জ্ঞানের আকর হচ্ছে ঋগবেদ। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা এখন যা কিছু আবিষ্কার করছেন তার সব কিছুই খুঁজলে বেদে পাওয়া যাবে। যাবেই। পরে আর একদল আবার এতে একটু সংশোধন এনে বললেন, না, ঋগবেদেই সব আছে এমনটা হয়ত নয়, তবে অন্য নানা প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থগুলি মিলিয়ে দেখলে এর সমস্ত কিছু যে পাওয়া যাবে তাতে কোনো সন্দেহই নেই। এই চিন্তাধারা বহুকাল ধরেই আমাদের দেশের এক বিরাট অংশের বুদ্ধিজীবীদের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এক সময় যে রবীন্দ্রনাথও এ নিয়ে ব্যাপক রসিকতা করেছিলেন তাতেই বোঝা যায়, এর বিস্তার কতদিনের। সঙ্ঘ পরিবারের কুশীলবরা সেখান থেকেই এই ধারাটিকে আত্মস্থ করে নিয়ে এর সাথে তাদের নিজেদের অন্ধ বিশ্বাসজাত আরও অনেক মশলা যোগ করে দিয়েছে এবং দিচ্ছে।
এই চিন্তাধারাটির উৎপত্তি হয়েছিল এক প্রতি-ঔপনিবেশিক হীনম্মন্যতা থেকে, যার রেশ এখনও মিলিয়ে যায়নি শুধু নয়, বরং কিছু কিছু কারণে আরও শক্তিশালী হয়ে চলেছে। ইংরেজ আমলে একদিকে বিদেশি শাসকের অধীনে পদে পদে শাসিতের অবমাননার জ্বালা, অপর দিকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে সঠিক পথে সংগঠিত সংগ্রাম গড়ে তুলবার ব্যর্থতা—এই দুইয়ে মিলে এক মনস্তাত্ত্বিক সান্ত্বনার অবলম্বন হিসাবে বেদ-পুরাণের শ্রেয়তার সন্ধান। এ যেন অনেকটা সামনের দিকে যেতে না পেরে পিছন দিকে এগিয়ে চলা। বিশেষ করে, সিপাহি বিদ্রোহের পরাজয়ের ফলে এক নিদারুণ হীনম্মন্যতার গ্লানি যেন চেপে বসেছিল গোটা দেশের জনমানসে। সমসাময়িক কালে খুব কম সংখ্যক চিন্তাশীল ব্যক্তিই পেরেছিলেন এই মানসিকতার চক্র থেকে বেরিয়ে এসে সামনের দিকে তাকানোর মতো সাহস দেখাতে। বঙ্কিমচন্দ্রের “মা যা ছিলেন”, বিবেকানন্দের “হে ভারত ভুলিও না”, ইত্যাদি এই পশ্চাদ-দৃষ্টিপাতেরই রসময়-আবেগাশ্রিত আলাপ। তোমাদের বিজ্ঞান প্রযুক্তি অস্ত্রশস্ত্র, আর আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি, বেদান্ত, ব্রহ্ম, আদ্যাশক্তি মহামায়া। তোমাদেরটা জড়বাদ, দুদিন বই তো নয়। আমাদেরটা পারমার্থিক বিদ্যা, দেহাতীত, কালাতীত। এই রকম আর কি।
মুশকিল হল, ইংরেজদের অপরাবিদ্যার বাস্তব জোরটা এত বেশি যে বেশি দিন তাকেও পুরোপুরি পরমার্থ দিয়ে উপেক্ষা করে বসে থাকা যায় না। আম জনতাকেও বোঝানো যায় না। ফলে এর পর শুরু হল আর এক মানস-ক্রীড়া—ওরা যা কিছু আবিষ্কার করছে, উদ্ভাবন করছে, ও সব কোনোটাই নতুন কিছু নয়; এই সব আমরা অনেক আগেই করে রেখেছি। বিশ্বাস না হলে পুরনো শাস্ত্রগুলো খুলে খুলে দেখ। পাতা ওল্টাও আর পড়। সব আমাদের মুনিঋষিরা করে ফেলেছিলেন।
তা, সেগুলো সমস্ত গেল কোথায়?
প্রথমে তৈরি হয়েছিল ত্যাগ মাহাত্ম্যের গল্প। আমাদের ওসব পছন্দ হয়নি। আমাদের বনই পছন্দ। সেখানে তো আর বেশি কিছু লাগে না। তাই আবিষ্কার করেও সব আমরা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। জড়বাদ আমাদের সংস্কৃতিতে সহ্য হয়নি।
এটাও বেশিদিন চলল না। ইংরেজদের চালু করা সমস্ত জড় আমোদই আমাদের দেশের লোকে বেশ আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করেছে। তখন এল মুসলিম শাসনে হিন্দুদের ঐতিহ্যের সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার গল্প। ওরা প্রথমে মন্দির ভেঙেছে, তারপর আমাদের বিমান উড়িয়ে দিয়েছে, বিদ্যুৎ শিল্প নষ্ট করে দিয়েছে, আমাদের রেডিও ভেঙে দিয়েছে, ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ এই ধারণাটিকেও তীব্র ব্যঙ্গ করে সেই লেখাটি লিখেছিলেন।
বিজেপি বা সঙ্ঘ পরিবারের মহাচিন্তকরা এখন এই গল্পগুলোকে আশ্রয় করে তাদের থিসিসগুলি বাজারে ছাড়ছে এবং ছড়াচ্ছে। সব সময় যে সোচ্চারে বলছে তা নয়। কিন্তু ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিচ্ছে। আর কিছু মন্দির যে মুসলিম শাসকদের হাতে ভাঙা পড়েছিল, তার যখন পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য আছেই, তখন সমস্ত মন্দির ওরা ভেঙেছিল বললেই বা আটকায় কে? তারপর যদি বলা হয়, ওরা প্রাচীন ভারতের সব কিছু অর্জন নষ্ট করে দিয়েছে তাও এই সনাতন ঐতিহ্যের দেশে বহু লোকেই প্রথমে গোগ্রাসে খাবে। সুতরাং, বিমান জিন প্রযুক্তি স্টেমসেল আপেক্ষিকতা—সবই ছিল কিন্তু এখন আর নেই বললেও চলবে ভালোই।
এই হচ্ছে তাদের যাবতীয় আবিষ্কারের রহস্য। এই হচ্ছে তাদের প্রধান ভরসা। রবি ঠাকুরের পদ্যই লোকে এক আধটুক পড়ে। গানও দুচারখানা শোনে হয়ত। তাঁর গদ্য আর কটা লোকে পড়ে?
[৮]
আর একদল অধ্যাত্মবাদী ধর্মবিশ্বাসী চিন্তাবিদ আছেন, যাঁরা এতটা স্থূল সঙ্ঘমার্কা দাবিদাওয়া করেন না। তাঁরা সরাসরি বিজ্ঞানের কোনো তাত্ত্বিক আবিষ্কার বা বিশেষ কোনো প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ধারে কাছে না গিয়ে সাধারণভাবে দাবি করেন, আধুনিক বিজ্ঞান বস্তুজগত ও বিশ্বপ্রকৃতির জন্ম বিকাশ ও পরিবর্তনের সম্পর্কে যে ধ্যান ধারণা নিয়ম তুলে ধরছে, প্রাচীন ভারতীয় দর্শন, বিশেষ করে বেদান্ত নাকি সেই ধারণাগুলিই বহু প্রাচীন কালেই বলতে পেরেছিল।
এই দাবিটা আবার এমন যে বেশ কিছু বিদেশি পণ্ডিত ব্যক্তি, এমনকি খ্যাতনামা বিজ্ঞানীও, এর পৃষ্ঠপোষক। ফলে এর ইজ্জত অনেক বেশি। তাঁরা মনে করেন, আধুনিক বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণাগুলির সাথে প্রাচীন ভারতীয় বৈদান্তিক মতবাদের সাদৃশ্য নাকি খুবই প্রকট ও বিস্ময়কর।
আলোচ্য প্রসঙ্গে এই দাবিটিরও সত্যতা পরীক্ষা করার দরকার আছে।
ইউরোপের খ্রিস্টীয় ধর্ম দর্শনের ক্ষেত্রে একটা সুবিধা আছে। বাইবেলের দুটো ভাগ দেখে নিলেই জানা হয়ে যায় প্রাচীন জ্ঞানীরা কী কী জানতেন এবং বলে গেছেন। আদিম গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে যুদ্ধ খুনোখুনি লুটপাট থেকে প্রেম ভালোবাসা বিতরণ পর্যন্ত মানুষের চিন্তার উত্তরণের একটা বেশ স্পষ্ট ছবি তাতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞান নিয়ে, অণুপরমাণু নিয়ে বলার মতো কথা প্রায় নেই বললেই চলে। সেই জন্য এরকম দাবিও কেউ উত্থাপন করতে পারেন না যে আধুনিক বিজ্ঞানের কোনো হিরেমুক্তো তাতে ছড়ানো আছে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে একথা বলা যায় না। শুধু যদি বৈদিক ঔপনিষদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যের আয়তন বিবেচনায় রাখা যায়, সেটাই এক বিপুল ব্যাপার। বেদ চারখানা, উপনিষদ তেরটা (প্রাচীন ও প্রধান ধরে), পুরাণ অন্তত আঠেরটা। এদের প্রত্যেকটায় শুধু ধর্মবিশ্বাসের কথাই নেই; সেই সঙ্গে আছে খাদ্য পানীয় বিবাহ দাম্পত্য যৌনতা থেকে শুরু করে সৃষ্টি তত্ত্ব পর্যন্ত যাবতীয় জ্ঞানের কথা। প্রত্যেকটাই এক একটা (এখনকার ভাষায়) নলেজ ব্যাঙ্ক। এহ বাহ্য! এদের মধ্যে আবার এক একটা বিষয়ের বক্তব্যে পারস্পরিক কোনো মিল নেই। এ যা বলে ও তা বলে না। হয়ত উল্টোটাই বলে। এমনকি একই উপনিষদের মধ্যেও দু জায়গায় দু রকম সৃষ্টি তত্ত্বের হদিশ আছে। কোনটা যে প্রাচীন ভারতের জ্ঞান হিসাবে ধরা হবে, তা কে বলে দেবে?
যাঁরা উপরের দাবিগুলি করেন তাঁরা কী করেন? এটাও এক চরম কৌতুহলের বিষয়।
সহজ রাস্তা ধরেন। উকিলদের রাস্তা। যে মামলায় যে আইনের ধারা উপধারা অথবা যে পুরনো মামলার রায়ের উল্লেখে আদালতে সুবিধা হবে তাঁরা সেই ভাবেই কেস সাজিয়ে ফেলেন। আগের দিন কী বলেছেন, অন্য মামলায় তাঁর সওয়াল কী ছিল, কিংবা, এমনকি একই আইনের আগের দিন তিনি কী ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, তা নিয়ে তিনি থোড়াই পরোয়া করেন।
এখানেও তাই। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞজনেরা দেখে নেন, বিজ্ঞান এই মুহূর্তে কী বলছে। সেই অনুযায়ী তাঁরা উৎস গ্রন্থ বা প্রয়োজনীয় সূত্র হাতড়ে বেড়ান। যেমন, বিশ শতকের ষাটের দশকের আগে বিগ ব্যাং প্রচলিত বা জনপ্রিয় তত্ত্ব ছিল না। এই চিন্তাবিদরাও কেউ বেদ উপনিষদ পুরাণ থেকে সেই অনুযায়ী বিশ্বতত্ত্ব খোঁজেননি। আকাশ জল বা পরম শূন্য থেকেই জগত সৃষ্টির কথা বলেছেন। যখন থেকে বিজ্ঞানীরা বিগ ব্যাং-এর কথা বলতে শুরু করলেন, অমনি এই পণ্ডিতরাও প্রাচীন শাস্ত্র থেকে সেই উদ্ধৃতিগুলিই দিতে লাগলেন, যেগুলি এর সাথে খানিকটা মিলে যায়। গরম থেকে ঠান্ডায় যাওয়ার কথা যেখানে আছে সেই গুলোকে সামনে নিয়ে আসার দ্বারা। বিজ্ঞানে যদি অসীম ও সসীম ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকে, এঁরাও প্রাচীন পুঁথি থেকে অনন্ত ও সান্ত বিশ্ব সম্পর্কে যে দুরকম মতামত আছে তা তুলে ধরতে থাকেন।
এঁদের যাঁরা পাঠক, তাঁরাও স্বভাবতই বিশ্বাসী মানুষ। প্রাচীন ভারতের পুঁথিপত্রে আধুনিক জ্ঞানের হদিশ পেয়েই তাঁরা খুশি। তা নিয়ে ঝাড়াই বাছাই যুক্তি তর্ক বিচার বিশ্লেষণ তাঁদের পছন্দের জিনিস নয়। খ্যাতনামা বিদ্বান লোকেরা বলছেন, অতএব নিঃসংশয়ে মেনে নাও—এই হচ্ছে তাঁদের মনোভাব। ফলে চিন্তাটা সহজেই গ্রাহক পেয়ে যায়। বিজ্ঞানের পেশাগত দরবারে একটা পারস্পরিক-যাচাই প্রতি-যাচাইয়ের ব্যবস্থা আছে। সেটাকে কারোর পক্ষেই পাশ কাটিয়ে কোনো দাবি উত্থাপন করা সম্ভব নয়। এই জায়গায় সেই সমস্যা নেই। কোনো প্রকাশ্য মঞ্চে নিজের কথাকে যুক্তি তথ্য সূত্র দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে এবং প্রতর্কর সামনে পড়তে হচ্ছে না। কে মানল, কে মানল না, তাতে কিচ্ছু আসে যায় না। ওনারা বলে খালাশ, এনারা পড়ে খালাশ। দু পক্ষই খুশি।
যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক মানুষদের পক্ষে, আমাদের হচ্ছে মুশকিল। আমরা এত সহজে এই সব কথা মেনে নিতে পারি না। বিচার করতে চাই, যুক্তি তথ্য পেতে চাই। যথোপযুক্ত সূত্র পেতে চাই। সূত্রগুলিকেও যাচাই করে নিতে চাই। সমস্ত বিষয় বিশ্লেষণ করতে চাই। নিঃসন্দেহ হতে চাই। জ্ঞানের রাজ্যে, সত্যান্বেষণে ফাঁকি যে চলে না। ফাঁকি দেবই বা কাকে। সঠিকভাবে বাছবিচার করে না জানলে ঠকাতে হবে তো নিজেকেই। মিথ্যা জিনিস জেনে বসে থাকব। মাথায় ভুল জিনিসের আবর্জনা জমে থাকবে। দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাসের ফানুস—ফেটে গেলে যে বিচ্ছিরি পচা গন্ধ ছড়াবে। নিজেদেরই খারাপ লাগবে।
ফলে আমরা বিচার করতে বসে ভাবি: এত দুরূহ সব চিন্তা যাঁরা করতে পেরেছিলেন, তাঁরা দু তিন হাজার বছর ধরে একটাও ভালো রাস্তাঘাট বানাতে পারলেন না; মাটির রাস্তা নষ্ট করবে না—এইভাবে গরুর গাড়ির চাকার নকশা বদলাতে পারলেন না—এরকম হল কেন? লোডশেডিং-এর সময় মোমবাতি ধরাতে গিয়ে আবিষ্কার করি, গড়ে চারটে কাঠি নষ্ট না করে একটা কাঠিতে আগুন ধরাতে পারি না। প্লাগ-হোলে প্লাগ ঢোকাতে গিয়ে লক্ষ করি, কোনোটা এমন ঢিলে যে ভালো করে আটকায় না; আবার, কোনো কোনোটা এত টাইট যে ঢুকতেই চায় না। এরকমই বা কেন হয়? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সমস্যা যে দেশের জ্ঞানীরা সমাধান করে ফেলতে পেরেছিলেন দু তিন হাজার বছর আগে, তাদের বংশধররা এই সব ছোটখাটো ব্যাপারেও কেন ব্যর্থ? বেদ-বেদান্ত তপোবন বর্ণাশ্রম সরস্বতী আর এস এস ইত্যাদি প্রকরণগুলি না থাকা সত্ত্বেও জাপান যা করতে পেরেছে, চিন এখন যা করতে পারছে, আমাদের দেশের পক্ষে তার কিছুই করা সম্ভব হল না কেন?
আরও দু পা এগিয়ে গিয়ে ভাবি, আচ্ছা দেখা যাক, বেদান্তের কোনো সূত্র থেকে বিজ্ঞানের একটা সামান্য কোনো সূত্রও কি বের করা যায়? ‘তত্ত্বমসি’ থেকে নিউটনের গতিসূত্র? ‘অহম ব্রহ্মাস্মি’ থেকে বয়েলের গ্যাসের সূত্র? ‘সোহহং’ থেকে ফ্যারাডের কোনো একটা মাত্র নিয়ম? বা এই রকম অন্য একটা কিছু? প্রাচীন জ্ঞানের কোনোটা থেকে যদি আধুনিক জ্ঞানের একটা কিছুও বের করা যায়, তাহলে বুঝতে হবে, কিছুমাত্র হলেও সাদৃশ্য বা সাযুজ্য আছে। দাবিদারদের কেউ না কেউ নিশ্চয়ই সেই চেষ্টা করে রেখেছেন। খুঁজে বেড়াই। কিন্তু হায়! শুধু যে চেষ্টা করেন না তাই নয়, দাবিদাররা কেউ এমনকি বোঝেনও না যে এটা তাঁদের তরফে করে দেখানোর দরকার আছে। বৈদান্তিক মহাজ্ঞানীদের কী দুর্দশা!
তখন নিঃসন্দেহ হই, সমস্ত দাবিটাই ভুয়ো। মোদী কোম্পানির দাবিগুলি একটু বেশি রকম স্থূল। ঘাপলাবাজিটা ধরা সহজ। অধ্যাত্মবাদীদের দাবিগুলি সেই তুলনায় হয়ত একটু পালিশ করা। কিন্তু মূল চরিত্রে দুটো একই। সবই আন্তর্গ্রহ ভ্রাম্যমান জ্বালানি বিহীন বৈদিক বিমান!!
[৯]
শেষ করার আগে প্রাচীন ভারতের সত্যিকারের গর্ব করার মতো কিছু অর্জনের কথা তুলে ধরব। কেন না, প্রাচীন ভারতের গর্ব করার মতো কিছু সম্পদ নিশ্চয়ই আছে। তবে তা প্রাচীন যুগেরই অর্জন। তাই দিয়ে আজকের কাজও যেমন চলবে না, আজকের যুগের জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে তার তুলনা করাও চলে না। কিন্তু সমকালীন যুগের অর্থে তার গুরুত্ব খুবই বেশি।
তিনটি ক্ষেত্রে এই অর্জন সমকালীন বিশ্বের অনেক দেশের থেকেই এগিয়ে থাকবে। সাহিত্য, ভাষাবিজ্ঞান, গণিত। এক এক করে সবিস্তার বলি।
সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঋগবেদ প্রাচীন ভারতের একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে একদল অরণ্যচারী যুদ্ধবাজ পশুপালক ভ্রাম্যমান মানবগোষ্ঠী যে সম্পূর্ণ মুখে মুখে এই রকম একটা বিরাট কাব্যসম্ভার রচনা করতে পেরেছিল, তাকে শ্রুতি-স্মৃতি-আবৃত্তি-পুনরাবৃত্তির এক সামূহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রায় এক সহস্র বছর সংরক্ষণ করতে পেরেছিল, এবং অবশেষে লিপি উদ্ভাবন ও লিখন-কৌশল আয়ত্ত করার পর তাকে খণ্ডে খণ্ডে লিখে রাখতে পেরেছিল—এ জিনিস আমার জানায় বিশ্বের আর কোথাও ঘটেনি। এই বিশাল সাহিত্যকে ধর্মগ্রন্থ বানিয়ে এর প্রাপ্য মর্যাদা বোধ হয় পুরোটাই নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কেন না, ধর্মগ্রন্থ হিসাবে এর কোনো যোগ্যতাই নেই। না আছে পূজাপাঠ, না আছে আত্মা পরমাত্মার কথা, না স্বর্গ নরক, না পাপ পুণ্য, না মোক্ষলাভের কথা—ধর্মের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই সব কোনো অনুষঙ্গই এতে নেই। এতে আছে প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি, যথা, সূর্য, পাহাড়, নদী, ঊষা, অগ্নি, ইত্যাদির উচ্চ প্রশংসা ও প্রশস্তিমূলক কবিতা। তাদের কেন্দ্র করে নানা রকম আবেগের প্রকাশ। এতে আছে বিপুল ভোজনের ভালোমন্দের কথা। এতে রয়েছে খাদ্য শস্য সংগ্রহ ও লুটপাটের সমস্যার কথা। সূর্য পাহাড় নদী প্রমুখ যাদের দেবতা বলা হয়েছে তারা মানুষেরও অধম—হিংসা বিদ্বেষ লোভ ক্রোধ কামনা বাসনায় তারা মানুষের দশ হাত উপর দিয়ে যায়। প্রাচীন কালের মানুষের স্বতস্ফূর্ত কাব্য হিসাবে বৈদিক সূক্ত বা কবিতাগুলি সত্যিই অতুলনীয়। কিন্তু ধর্মীয় সাহিত্য বা শাস্ত্র হিসাবে প্রাচীনত্ব ছাড়া এর কোনো মূল্যই নেই।
এই শেষ কথাটা আর একটু স্পষ্ট করে বুঝে নেওয়া ভালো। পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমস্ত যুগের মানুষেরই প্রাচীনের প্রতি, প্রাচীনত্বের প্রতি একটা বিশেষ সম্ভ্রমবোধ কাজ করে। পুরাকালে আবার প্রাচীন মানেই ছিল পবিত্র। এই জন্যই পাথরের পাত্র, পাথরের মূর্তি খুব পবিত্র। এই জন্যই পূজাপার্বনে লোকে তামা কাঁসা পেতলের বাসনপত্র ব্যবহার করে। সেই একই আবেগ-সরণি ধরেই এই দেশের মানুষের কাছে ঋগবেদ তার প্রাচীনত্বের সুবাদে কাব্যসাহিত্যের পরিচয় খুইয়ে কালক্রমে ধর্মসাহিত্য হয়ে বসে আছে।
আর একটা জিনিসও খুব চিত্তাকর্ষক। হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই মনে করে, বেদই হিন্দুদের যাবতীয় ধর্মীয় রীতিনীতির উৎস। আর বাস্তবে, হিন্দুদের একটাও ধর্মীয় আচরণে অনুষ্ঠানে দেবদেবীতে ঋগবেদের বা সেই যুগের কোনো উপাদানই নেই। পূজাপাঠে বৈদিক মন্ত্র বলে যেগুলি উচ্চারিত হয় তারও সিংহভাগই আসলে অবৈদিক, বিভিন্ন পৌরাণিক উৎস থেকে সংগৃহীত। যেটুকু এদিক ওদিকে বেদের অংশ বলে দেখা যায়, তার মধ্যে ব্যাপক জোড়াতালির ছাপ একেবারে স্পষ্ট। বিশ্বাসের সঙ্গে আচরণের এতখানি অসামঞ্জস্য হিন্দু ধর্ম ছাড়া আর কোনো ধর্মেই দেখা যায় না। এই অসঙ্গতির একটাই কারণ—বৈদিক সাহিত্যের প্রকৃত ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপন করতে না পারা। কিন্তু এর সঠিক মূল্যমান জানলে এর জন্য গৌরবের ভাগ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।
দ্বিতীয়ত ভাষাবিজ্ঞান। সংস্কৃত বোধ হয় পৃথিবীর একমাত্র ধ্রুপদী ভাষা, যার জন্ম হয়েছে কিছু চিন্তাশীল মানুষের অত্যন্ত সুচিন্তিত বিচার বিশ্লেষণ সংশ্লেষণের হাত ধরে। বৈদিক ভাষা ছিল আদতে মৌখিক অসংগঠিত অবিন্যস্ত ভাষা। তার মধ্য থেকে শব্দমূল ধাতুমূল খুঁজে খুঁজে বের করে সমস্ত ভাষা কাঠামোকে সুন্দরভাবে ব্যাকরণ নির্মাণ করে সংগঠিত করার এটা একমাত্র উদাহরণ। সেই কারণেই এই ভাষার লিপি প্রকরণে প্রায় সমস্ত উচ্চারণ যোগ্য স্বরধ্বনি ও ব্যাঞ্জন ধ্বনিকে জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। স্বর ধ্বনিগুলি উচ্চারণের ক্রমপরিণতি অনুযায়ী বিন্যস্ত। অ আ ই ঈ উ ঊ এ ঐ ও ঔ ইত্যাদি। ব্যাঞ্জন ধ্বনিগুলিকেও মুখের ভেতরে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী এক চমৎকার ক্রমবিন্যাসে সাজানো হয়েছে। এই ভাষার সংগঠনে বিশ্লেষণী সূক্ষ্মতা আরও বেশি করে ধরা পড়ে যখন দেখি, র-ফলা থেকে রেফ এবং ঋ-কারকে আলাদা করে চেনানো হয়েছে। এবং এই সমস্ত বিকাশ ঘটেছে আজ থেকে আড়াই হাজার বছরেরও বেশি সময় আগে। এটা ভাবলেই তো আমাদের বুকটা গর্বে ভরে ওঠা উচিত।
তৃতীয়ত, গণিতে শূন্যের আবিষ্কার ও প্রয়োগ। সকলেই জানেন, আধুনিক গণিতে, এবং বিজ্ঞানেও, শূন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা। শূন্য ছাড়া বীজগণিতের বিকাশ ঘটানো প্রায় সম্ভব ছিল না। গাণিতিক ধারণা হিসাবে শূন্যের আবিষ্কার ঠিক কখন হয়েছিল তা বর্তমানে সঠিকভাবে বলা মুশকিল। ভারতীয় ইতিহাসবিদরা একে বহু প্রাচীন কালে ঠেলে দেবার চেষ্টা করলেও তার কোনো নিশ্চিত-দৃষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। শূন্য শব্দটির ব্যবহার অনেক দিনের হলেও তার মধ্যে কোনো গাণিতিক বোধ লক্ষ করা যায় না। আকাশ বা স্থান বোঝাতে শূন্যের ব্যবহার করা হলেও তার মধ্যে গাণিতিক শূন্যের পরিচয় নেই। মোটামুটি পঞ্চম শতকে আর্যভাটের সময় থেকে এর গাণিতিক ব্যবহার পরিদৃষ্ট হতে থাকে। কিন্তু আর্যভাটও শূন্যের ব্যবহার না করেই বহু অঙ্ক লিখে গেছেন। তথাপি, সেই সময় থেকে ধীরে ধীরে শূন্যকে ব্যবহার করে সংখ্যার স্থান-মান পাতন পদ্ধতি বিকশিত হতে শুরু করে। বড় বড় সংখ্যা লেখার ক্ষেত্রে এটা যে কত বড় একটা সুবিধা হয়ে দেখা দিয়েছিল, আজ আর অনেকেই বুঝতে পারবেন না, যদি সেই সময়ের অ-শূন্য সংখ্যা লিখন পদ্ধতির ব্যাপারে খোঁজখবর না রাখেন। এই শূন্যের ধারণা এবং তার ভিত্তিতে দশমিক স্থান-মান পাতন পদ্ধতি বাণিজ্যিক লেনদেনের সূত্রে ভারত থেকে আরব হয়ে ইউরোপে পৌঁছায় আনুমানিক নবম শতাব্দে। আর তারপরে, একাদশ শতক থেকেই দেখা যায়, বীজগণিতের ব্যাপক বিকাশ শুরু হয়ে যায় সেখানে। এই বিষয়টা সারা বিশ্বে বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইতিমধ্যেই অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নথীভুক্ত হয়ে আছে। আমরা যদি প্রাচীন ভারতের এই অবদানের জন্য গর্ব করি, কেউ তাতে আপত্তি জানাবে না।
এই তিনটি জায়গায় ভারতের অবদান একেবারেই অনন্য। কিন্তু এর বাইরেও প্রাচীন ভারতে আরও কিছু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটেছিল। যেমন, ধাতুবিদ্যা, ভেষজজ্ঞান, শল্য চিকিৎসা, ইত্যাদি। এই সব ক্ষেত্রে অগ্রগতির ইতিহাস পৃথিবীর আরও কিছু দেশের সঙ্গে সমান্তরালভাবে ঘটেছে। যাঁরা তথ্য এবং সত্যের ভিত্তিতে গর্ব প্রকাশ করতে চাইবেন, তাঁদের সে সম্পর্কে সতর্ক হয়ে দাবি পেশ করতে হবে।
[১০]
পরিশেষে, যেখান থেকে এই আলোচনা শুরু করেছিলাম সেখানে একবার ফিরে যাওয়া দরকার। প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অবদান। একে তো আমাদের মিথ্যা দাবির সংখ্যা বেড়ে গিয়ে সত্যিকারের অবদানগুলিকে কার্যত ভুলেই যাওয়া হচ্ছে। তার উপর আমরা যে বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মৌলিক অবদানের প্রশ্নে প্রথম বিশ্বের তুলনায় বহু যোজন পিছিয়ে আছি, এই সত্য তো কোনো মিথ্যা জাঁকজমক করেই ঢেকে রাখা যাবে না। আধুনিক পৃথিবীতে যা কিছু আবিষ্কার এবং উদ্ভাবন হচ্ছে—সে মাছ কাটা কাচিই হোক আর সেল ফোন—আমরা যে তার কোনো কিছুই নিজেরা অন্যদের আগে বানাতে পারছি না, সবই যে ওরা করে ফেলার পর আমরা শুধু নকল করছি, এই কথাটা ভুলে গেলে চলে না। যত দিন এই পরিস্থিতি বহাল থাকবে, আমাদের মিথ্যা দাবিই করে যেতে হবে।
কিন্তু যদি আমরা বুঝতে পারি, আমাদের গলদটা কোথায়, কেন আমরা মৌলিক আবিষ্কার করতে পারছি না, তাহলে অচিরে হয়ত মৌলিক কিছু একটা করে দেখাতে পারব। বিজেপি বা সঙ্ঘ পরিবার হয়ত আরও বেশ কিছু দিন চেষ্টা করে যাবে যাতে আমরা এটা করতে না পারি। মিথ্যা গর্ব আর মিথ্যা দাবিতেই আমরা সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকি। তবে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমরা আর কত কাল এই ভাবে নিজেদের ঠকাব। আর কত দিন আমরা উন্নত দুনিয়ার সামনে নিজেদের হাস্যাস্পদ করে রাখব।
সময় তার দাবি জানাতে শুরু করে দিয়েছে। Ж
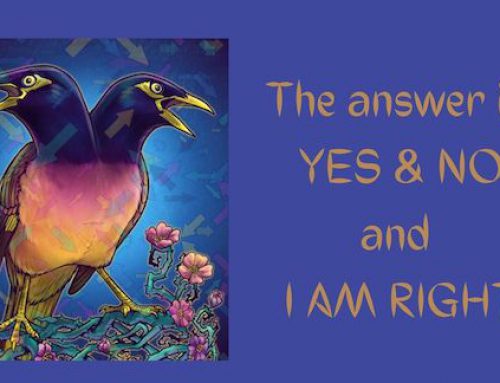
খুব ভালো লেখা।আমার নিজের মাথায় যে সব ভাবনা বহুকাল ধরে ঘুরছিল তার সবটাই এই লেখাতে পেয়ে গেলাম। সঙ্গে আর একটি জিনিষ যোগ করছি, বেদ লেখা হয়েছিল বৈদিক সংস্কৃততে, তার সাথে আধুনিক সংস্কৃতর ফারাক অনেকটাই, সেটা আপনিও উল্লেখ করেছেন, আমি বেদের বাংলা আর ইংরেজী অনুবাদ পড়ার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলাম অনুবাদকরা একেবারে প্রানখুলে আপন মনের মাধুরী মিশিয়েছেন জানি সেটাই স্বাভাবিক কিন্তু আমার মত অজ্ঞ লোকের পক্ষে সেটা অতীব পীড়াদায়ক।আমার যা মনে হল, বেদের অনুবাদ করতেগিয়ে পরবর্তী কালের পুরানের চিন্তাধারা যোগ করেই এই কান্ড ঘটেছে। শুধু তাই নয় অনেক জায়গায় দেখছিলাম একটি ঋক্ এর পুরোটাও কোন অজ্ঞাত কারনে অনুবাদ হয়নি। অনেক সময় কোন নদী বা গোষ্ঠীর নাম আধুনিক নাম দেওয়া আছে, সেটা আবার অন্য় অনুবাদক অন্য নাম লিখছেন।
চাকরী সুত্রে অনেক জায়গায় ঘুরতে হয়েছে, অনেকের সাথে মিশতে হয়েছে, দেখছিলাম দিল্লী-হরিয়ানা-রাজস্থান অঞ্চলে চন্দ্রবংশীয়-সূর্যবংশীয় বিপুল লড়াই আজও চলছে, এমনকি বর্তমান ভারতের রাজনীতিও তার দ্বারা অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত। যা খুঁজে পেলাম, কুরু-পান্ডব হল চন্দ্রবংশীয়, কৃষ্ণ হল তাদেরই তুতুভাই যাদব বংশীয়। রাম সূর্যবংশীয়।
ঋক্ বেদ হল চন্দ্রবংশীয় পুরুদের লেখা।মহাভারত ঐ চন্দ্রবংশীয় পুরুদের লেখা। সম্ভবত তারই জবাবে তৈরী হয়েছে সূর্যবংশীয়দের রামায়ন।
পড়ে খুব ভালো লাগলো। এবং কাজে ও লাগবে আজকের এই দুঃসময়ে। তাই অনেক ধন্যবাদ।
লেখাটা অনুবাদ করে সমস্ত আর এস এস নেতাদের পড়ানো উচিত।তাতেও এদের ধর্মান্ধতা কমবে কিনা সন্দেহ!
আপনাদের ধন্যবাদ। উৎসাহ পাচ্ছি আরও লেখার।@Mojahidul Islam + amiya + Suman.
চমত্কার সুখপাঠ্য লেখা। এক নিঃশ্বাসে পড়ে গেলাম, লেখার আকার এতটুকু ব্যাঘাত ঘটায়নি। বিজ্ঞান ভিত্তিক লেখা হওয়া সত্বেও লেখকের রসবোধ প্রশংসার দাবিদার। আরো লিখুন, ধন্যবাদ।
ধন্যবাদ
:good: