ফেসবুকে কয়েক দিন আগে একটা খবর পড়ে চমকে উঠলাম। বিহারের (ভারত) একটি গ্রামে বাবা-মা তাদের দুই যমজ কন্যার একজনকে পুড়িয়ে মেরেছে আর একজনকে সুস্থ করে তোলার অভিপ্রায়ে। সন্তানদুটি দীর্ঘদিন ধরে অসুখে ভুগছিল। কিছুতেই ভালো হচ্ছিল না। শেষে তারা নিরুপায় হয়ে এক তান্ত্রিক বাবার কাছে যায়। সে পরামর্শ দেয়, ভগবান নাকি কোনো কারণে সেই বাবা-মার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে এদের ফেরত চাইছে। তাই ওরা ভালো হচ্ছে না। হবেও না। অন্তত একজনকে ভগবানের কাছে ফেরত দিতে হবে। তাহলেই একমাত্র অপর সন্তানটি সুস্থ হয়ে উঠবে। তারপরেই একদিন বড় সড় আয়োজন করে হোমানল জ্বালিয়ে গায়ে তেল ঢেলে একটি মেয়েকে পুড়িয়ে মারে সেই অশিক্ষিত বাবা আর মা নিজের হাতে। সেই তান্ত্রিক সাধু(?)বাবা নাকি এখন ফেরার। কিংবা মন্ত্রবলে অদৃশ্য?
অনেক রাত বলে সেদিন দুই চোখ কচলে ভালো করে খবরটা আরও কয়েকবার পড়লাম। তারপর দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারের দিকে দৃষ্টি ফেললাম। না। ঠিকই আছে। ২০১৪। একবিংশ শতাব্দের বেশ ভেতরেই ঢুকে এসেছি আমরা। অথচ …
[ক]
তখন মনে হয়েছিল, বিজ্ঞান-মনস্কতা নিয়ে বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মী হিসাবে প্রকাশ্য দরবারে আবার দুচার কথা বলার চেষ্টা করা উচিৎ। হয়ত কিছু কাজ হতে পারে। মানুষের মধ্যে নতুন করে ভাবনা চিন্তা শুরু হতে পারে।
তবে সেই সঙ্গে একথাও মনে হল, বিজ্ঞান-মনস্কতা কাকে বলে এই প্রশ্ন এখনকার দিনের একটা বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের ই-পত্রিকার পাতায় উত্থাপন করা বেশ বিপজ্জনক। পাঠকরা যথেষ্ট মনঃক্ষুণ্ণ হতে পারেন। উত্তেজিত হয়ে বলতেই পারেন, “আরে মশাই, আজকাল আমরা ভূত-প্রেত মানি না, ঠাকুর দেবতা মানি না, প্রায় কোনো আচার-বিচারে নেই, বন্ধুদের খেতে বসে জাতপাত বিচার করি না, হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা করি না, ল্যাপটপ মোবাইল ডাটাকার্ড দিয়ে সারা দুনিয়ার সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রাখি, আর আমাদের আপনি এখন বিজ্ঞানমনস্কতা শেখাতে বসেছেন? যান যান, ফালতু নিজের আর আমাদের কাজের সময় নষ্ট করবেন না। এর থেকে বরং সোনা ব্যাঙ নিয়ে কিছু লিখুন। বাচ্চাদের কাজে লাগতেও পারে।”
এটা তেমন ভুল কথাও কিছু তো নয়। উপর থেকে দেখলে মনে হয়, ভারতীয় সমাজ মনে হয় বেশ আধুনিক হয়ে উঠেছে। আধুনিক হয়ে ওঠার সাথে বিজ্ঞান-মনস্ক হওয়ারও যে একটা সিধা-সম্বন্ধ আছে তা তো আর কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। অসুখবিসুখ হলে আজকাল সাধারণত অজ পাড়াগাঁয়ের লোকেও জল-পড়া তেলপড়ার দিকে যায় না। সরকারি হাসপাতালেও যায় না। শহরের নামিদামি প্রাইভেট হাসপাতালেই ছোটে। ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ মতো নানারকম টেস্ট করায়, অন্তত করাতে আপত্তি করে না। প্রচুর ভিজিট দিয়ে নামডাকওয়ালা স্পেশালিস্ট ডাক্তার দেখায়। তাঁদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী দামি দামি ওষুধপত্র কেনে। শুধু ট্যাক্সিওয়ালা বা অটোওয়ালা নয়, রিকশাওয়ালার হাতেও আজকাল মোবাইল দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, শুধু ভিভিআইপি-রাই নয়, আমাদের মতো সাধারণ ছাপোষা গেরস্ত লোকেরাও এখন জীবনের প্রতিটি ইঞ্চিতে প্রতিটি মুহূর্তে বিজ্ঞানকে জড়িয়ে এবং মানিয়ে নিয়েছে। এরকম অবস্থায় শিক্ষিত মানুষদের সামনে যদি বলি বিজ্ঞানমনস্কতা নিয়ে কিছু বলব, তাঁরা ভালোমন্দ কিছু মনে তো করতে পারেনই। তার জন্য তাঁদের কাউকে দোষ দেওয়া উচিৎ না।
কিন্তু আবার কিছু টুকরো টুকরো ঘটনার স্মৃতি এমনভাবে মনে ভিড় করে আসে, তাদেরকেও তাড়ানো যায় না যে। ওই বিহারের ঘটনাটা যেমন। কিংবা এই যে কিছুদিন আগে,গত বছর, ডাঃ নরেন্দ্র দাভোলকর মহারাষ্ট্রে আততায়ীদের হাতে নৃশংসভাবে প্রকাশ্য রাজপথে খুন হয়ে গেলেন। তাঁর অপরাধ, তিনি বহুদিন ধরে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে শুধু আন্দোলন করছিলেন তা নয়, রাজ্য সরকারকে দিয়ে একটা কুসংস্কার বিরোধী আইন প্রবর্তন করাতেও চেষ্টা করছিলেন যাতে মন্ত্রতন্ত্র বুজরুকি দিয়ে লোক ঠকানো না যায়। যাতে বিহারের মতো―
[খ]
বিহারে অমনটা ঘটতে পারে। মহারাষ্ট্রেও সম্ভব। তাই বলে পশ্চিমবাংলায়? কদাচ নয়, কুত্রাপি নয়। অন্তত বেশ কিছু শিক্ষিত মানুষকে আমি এরকম কথা বলতে শুনেছি। তাঁরা সত্যিই বিশ্বাস করেন, পশ্চিমবাংলা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় শিক্ষায় চেতনায় যুক্তিবোধে বেশ কয়েক কদম এগিয়ে আছে। প্রয়োজনের তুলনায় তা কম হতে পারে। কিন্তু কুসংস্কারের নিরিখে আমরা বাঙালিরা সামান্য হলেও বৈজ্ঞানিক মনোভাবনার দিকে এগিয়ে রয়েছি।
তাই কি? এই আপত্তিটা আবার আমি মানতে পারলাম না। কেন তা বলবার জন্যই এত ধানাই পানাই করছি। একে তো কুসংস্কারের কোনো অভাব নেই আমাদের চারপাশে, বাড়িঘরে, আত্মীয় স্বজন পরিচিতদের মধ্যে। ভাদ্র বা পৌষ মাসে বিয়ে করেন, ছেলের পৈতে দেন, বাচ্চার মুখেভাত হয়―এমন ঘটনা আজ অবধি আমার পোড়া চোখে পড়েনি। শুধু বিহার নয়, পশ্চিমবাংলারও মফস্বল বা গ্রামগঞ্জের রাস্তায় গাড়ি নিয়ে চলতে চলতে এপার থেকে ওপারে রাস্তা ডিঙিয়ে বেড়াল চলে গেলে গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষা করেন না, এরকম গাড়িওয়ালা মালিক এবং/অথবা ড্রাইভার খুব বেশি দেখেছি বলে আমি মনে করতে পারছি না। আর সর্বোপরি, বিজ্ঞানমনস্কতা মানে তো কেবলমাত্র কুসংস্কার থেকে মুক্তি নয়, জীবনের আরও নানা আনাচে-কানাচে যুক্তি ও বিজ্ঞানবোধের প্রয়োগ। সেই হিসাব করলে আমরা কোথায় পড়ে আছি দেখা উচিৎ না?
বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। সেদিন আমি আর আমাদের বিজ্ঞান সংগঠনের এক সহকর্মী গিয়েছিলাম কলকাতার আশেপাশের মফস্বলের একটা বড় স্কুলে। বিজ্ঞান অবিজ্ঞান কুসংস্কার ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে বক্তৃতা দেবার কর্মসূচি ছিল। অনেক দিন ধরে এসব নিয়ে আমি বিজ্ঞান আন্দোলনের একজন কর্মী হিসাবে নানা জায়গায় বক্তৃতা দিতে গিয়েছি। ঘন্টা দেড় দুই সময় পেলে এই বিষয়ে খুব জমিয়ে বলতে পারি, যেখানে যাই একেবারে চুটিয়ে বলি, বলার মাঝখানে এবং শেষে শ্রোতাদের তরফে প্রচুর হাততালি পাই। সভার শেষে নিজের ভেতরে একটা কেমন তৃপ্তিবোধ কাজ করে, মনে হতে থাকে, দেশের যাবতীয় কুসংস্কারকে যেন একেবারে হিটলারি ব্লিতস্ক্রিগ-কায়দায় যুদ্ধ করে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছি।
সেদিনও আমার সেরকমই অনুভূতি হয়েছিল। এটুকু মনে আছে, দিনটা ছিল কৃষ্ণা পক্ষের চতুর্থী, সন্ধের দিকে যখন আমরা বেরতে যাচ্ছি, তখনও চাঁদমামা পুবাকাশে উদিত হয়নি। কিছুই না ভেবে খুব সাদামাটা ভাবে কাছাকাছি একজন ছাত্রকে দেখতে পেয়ে জিগ্যেস করলাম, পুব দিকটা কোন দিকে। ছেলেটি আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। মুখচোখের ভাবে মনে হল, ওকে আমি রাজা আলেকজান্দারের জন্মদিন কবে জিগ্যেস করেছি। যা তার জানার কথা নয়। আর এটা যে তার জানার কথা নয় তা আমার তো অন্তত জানা থাকার কথা। অতঃপর সে একজন শিক্ষক মহাশয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, যদি কোনো হাত পা মাথা নড়াচড়ার ইসারায় কিছু আভাস পাওয়া যায়। না, হল না। কোনো শিক্ষকই এতটা ছেলেমানুষি ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে চাইলেন না। নিজেকে কেমন যেন উজবেক মনে হল। কুসংস্কার-টুসংস্কার নিয়ে যাদের জন্য এত লড়াই করলাম, সেই সব সৈন্যসামন্তরা যে পূর্বদিক কোনটা এখনও তাই জানে না।
একজন শিক্ষিকা এগিয়ে এসে আমাকে তাড়াতাড়ি বললেন, “না স্যর, আসলে ছাত্ররা তো কেউ আর এতক্ষণ স্কুলে থাকে না। তাই স্কুল ক্যাম্পাসে চাঁদ কোন দিকে ওঠে দেখেনি। ইন ফ্যাক্ট, আমরা কেউই তা দেখিনি বা লক্ষ করিনি।”
তা বটে। অকাট্য যুক্তি! স্কুলের ছাত্ররা কিংবা শিক্ষকরা সন্ধেবেলায় যদি কখনও স্কুলের ক্যাম্পাসে চাঁদ উঠতে না-ই দেখে থাকেন, তাহলে স্কুলের ক্যাম্পাসের পূর্ব দিক চিনবেন কী করে?
… একজ্যাক্টলি!
যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক পাঠকবৃন্দ, আপনারা এবার মনে মনে যা ভাবছেন, আমি বুঝেছি। আমিও এই প্রশ্নে আপনাদের সঙ্গে পুরোপুরি একমত।
দিনের বেলায় সূর্যকে দেখে তো পুব দিকটা চেনার কথা। চাঁদের জন্য তো আর আলাদা কোনো পূর্ব দিক নেই। তাও কি ছাত্ররা দেখেনি? সেই সব মাস্টারমশাই এবং দিদিমনিরা দেখেননি? সেই দেখার কথা মনে পড়ল না? কিন্তু এক ধরনের কাপুরুষোচিত লজ্জায় এই প্রশ্নটা কেন জানি না কিছুতেই আমি সেদিন ওনাদের কাউকে উদ্দেশ করে আর জিগ্যেস করে উঠতে পারলাম না। আমার ধারণা, আপনারাও কেউ তখন ওখানে থাকলে করতে পারতেন না। আমার মতোই আপনাদেরও অনেকের চোখের সামনে ভেসে উঠত আমাদের স্কুলগুলোতে ভূগোল শিক্ষার নিত্যকর্মপদ্ধতি। পুস্তক পাঠ। লক্ষ্মীর পাঁচালি পাঠের মতন করে পঠন এবং তারই ভিত্তিতে পরীক্ষণ। ক্লাশে মৌখিক প্রশ্নোত্তর। পরীক্ষার খাতায় লিখিত উত্তর। টিক ক্রস হ্যাঁ না ঠিক ভুল। শূন্যস্থান পূরণ। সেই অনুযায়ী নম্বর। ভালো রেজাল্ট, মাঝারি ফল, খারাপ নম্বর। নদী পাহাড় পশ্চিম বঙ্গ এশিয়া আফ্রিকা কৃষ্ণ সাগর আন্টার্কটিকা সাহারা নায়াগ্রা—সব আমরা ছাত্ররা উত্তরপত্রে লিখে দিয়ে থাকি কিছুই স্বচক্ষে না দেখে, না বুঝে। না, সব জায়গায় গিয়ে গিয়ে চাক্ষুস দেখার প্রশ্নই ওঠে না। আমি সে কথা বলছিও না। কিন্তু মানচিত্রে বা ছবিতেও তো দেখা যায়। দেখানো যায়। তাও দেখিনি। আজও কেউ দেখে না। দেখানো হয় না। দরকার হয় না। সূর্য যে পুব দিকে ওঠে তা বলা বা জানা বা খাতায় লেখার জন্য পুব দিক কোনটা না জানলেও যে চলে―এই মহৎ উপলব্ধিই আমাদের ভূগোল শিক্ষার প্রথম ও প্রধান কথা। এমনকি শেষ কথাও।
প্রাথমিক স্তরের স্কুলপাঠ্য ভূগোলে খানিকটা জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটা বুনিয়াদি পরিচয় দেওয়া থাকে। বছরের বিভিন্ন সময়ে এক আধবার ছাত্রদের সন্ধ্যা বা রাতের আকাশ দেখানোর উদ্যোগ নিয়ে বইতে পড়া জিনিসগুলোকে, কৃত্তিকা শ্রবণা কালপুরুষ ধ্রুবতারা মঙ্গল বৃহস্পতি শুক্রকে চিনিয়ে দেওয়া, খুব কষ্টকর নয়। কিন্তু সেটুকুও করা হয় না। যে সমস্ত বাবা-মা স্কুলে ক্লাশ না হওয়া নিয়ে মাস্টারমশাইরা ভাল করে পড়াচ্ছেন না বলে প্রতিবাদে সমালোচনায় সোচ্চার, তাঁরাও এই ব্যাপারে চুপচাপ। বাড়িতে প্রাইভেট টিউটর এসে ভূগোল পড়ালে তিনিও সন্তানকে আকাশ চেনাচ্ছেন কিনা তা নিয়ে তাঁরা আদৌ ভাবিত নন। মাথা উপরে তুলে কিছু দেখা নয়, মাথা নিচু করে টেবিলের উপরে বই খাতার পৃষ্ঠায় নজর দিতেই তাঁরা ছেলেমেয়েকে শেখাতে চান। সাধে কি আর আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের অনেকের নজরই নীচের দিকে চলে যায়?
আর এইজন্যই আমরা প্রায় কেউই জানি না আমরা যাকে আমাদের ডান হাত বলি সেটা কেন দক্ষিণ হস্ত। বাঁ হাতকে কেন দক্ষিণ হস্ত বলা হল না? তা কি নিতান্তই কাকতালীয়?
চলুন, এবার একটা অন্য দৃশ্যপটে যাওয়া যাক।
এক বন্ধুর বাড়িতে গেছি। তাঁর পুত্র, ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র, মন দিয়ে সোচ্চারে ইতিহাসের পড়া মুখস্থ করছিল, “আলেকজান্দার বন্দি রাজা পুরুকে প্রশ্ন করিলেন, আপনি আমার নিকট কীরূপ ব্যবহার আশা করেন? পুরু বীরের মতো উত্তর দিলেন, একজন রাজা আর একজন রাজার সহিত যেরূপ ব্যবহার আশা করিয়া থাকে। এই কথা শুনিয়া আলেকজান্দার খুশি হইয়া পুরুকে মুক্তি দিলেন এবং ভারতবিজয় সফল করিয়াও তা অধিকার না করিয়াই দেশে ফিরিয়া গেলেন।” মনে পড়ে গেল, আমরাও ছোট বেলায় এই রকম ইতিহাস কাহিনি মুখস্থ করেছি, পরীক্ষার খাতায় লিখেছি, ভালো নম্বরও পেয়েছি। অনেক কাল পরে কিঞ্চিত বুদ্ধিশুদ্ধি হওয়ার পর আমার মনের মধ্যে একটা নিরীহ প্রশ্ন জেগেছিল, এ কি সত্যিই সম্ভব? হাজার হাজার মাইল রাস্তা ঠেঙিয়ে―আর রাস্তা মানে তো এখনকার মতো বাঁধানো পাকা সড়ক নয়, বনজঙ্গল নদী পাহাড় মালভূমির ভেতর দিয়ে কোনোরকম পায়ে চলার সরু পথ―তার মধ্য দিয়ে সুদূর ম্যাসিদনিয়া থেকে পঞ্জাব পর্যন্ত কষ্ট করে এসে স্রেফ পুরু রাজের বীররসে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে একজন দিগ্বিজয়ী রাজা নব অর্জিত ভূখণ্ড ছেড়ে চলে যাবে? এল কেন তবে এ্যাদ্দুর? এ কি বিশ্বাসযোগ্য?
তখন আবার আমার মনে হয়েছিল, না, ইতিহাস পড়তে হলে, পড়ে বুঝতে হলে, হাতের সামনে সংশ্লিষ্ট ভূগোল বইও খুলে রাখতে হবে। আলেকজান্দার কেন চলে গিয়েছিল বুঝতে হলে পশ্চিম এশিয়ার, ভূমধ্যসাগর থেকে শতদ্রু নদীর পাড় পর্যন্ত, ভৌত মানচিত্রটা খুলে দেখতে হবে। তখন সন্দেহ দেখা দেবে, সেই প্রাচীন কালে অতদূর থেকে ওই মানচিত্রওয়ালা জায়গাগুলো পেরিয়ে ম্যাসিদনিয়ার সিংহাসনে বসে পারস্য আফঘানিস্তান ধরে রেখে পঞ্জাব শাসন করা গ্রিকদের পক্ষে আদৌ সেইকালে সম্ভব ছিল কিনা। আর এইভাবে ইতিহাস পড়তে শিখলে তখন বোঝা যাবে, পুরুর সেই বহুপঠিত সংলাপটি সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে অতি উপাদেয় উপচার হলেও ইতিহাস সাহিত্যের পক্ষে একেবারেই কোনো লোভনীয় উপাদান নয়। এতে আমাদের জাতীয় আবেগে সুড়সুড়ি দিতে সুবিধা হয় ঠিকই, কিন্তু বুদ্ধির গোড়ায় ধুনো দেওয়ার ধুনুচির আগুন শিক্ষাজীবনের একেবারে শুরুতেই নিবিয়ে দেওয়া হয়।
এইভাবে ইতিহাস পাঠ করতে শিখলে তবেই বোঝা যাবে, মধ্য যুগের ভারতে সুলতান বা মোগল আমলের সম্রাটরা দিল্লি থেকে এগিয়ে পূর্বদিকে যতটা রাজ্য বিস্তার করেছে, দক্ষিণ দিকে ততটা যায়নি কেন। পাহাড় মালভূমি বনজঙ্গল ভেদ করে স্থলপথ ধরে সাম্রাজ্য বিস্তার বা রক্ষা যে সুবিধাজনক নয়, নদী বা সমুদ্রপথ ধরে সমতল বরাবর এগোনোই যে তখনকার সৈন্য চলাচলের পক্ষে সুবিধাজনক ব্যাপার ছিল, এবং সেই অনুযায়ীই যে বিহার বা বাংলার দিকে যত সহজে তারা আসতে পেরেছে, দক্ষিণে তত সহজে যেতে পারত না―এটা বোঝা যাবে।
সোজা কথায় বলতে গেলে, ইতিহাস ভূগোলও আমাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পড়া এবং পড়ানো উচিৎ, কিন্তু আমরা পড়িও না, পড়াইও না। বিজ্ঞানমনস্কতা এখানেও প্রতিদিন দুরমুস হয়ে চলেছে।
[গ]
এপর্যন্ত পড়ে কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, বিজ্ঞান-মনস্কতার কথা বলতে বসে আমি স্রেফ ভূগোল আর ইতিহাস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম কেন? বিজ্ঞান নিয়ে এখন অবধি একটাও কথা তো পাড়িনি। বিজ্ঞান বাদ দিয়ে বিজ্ঞান-বোধ হয় নাকি? বিজ্ঞান মানে বিশেষ জ্ঞান যা পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত―এই সব কথা তো বলছি না। বিজ্ঞান মানে সব কিছুকে যুক্তি তর্ক করে বিচার বিশ্লেষণ করে তবে গ্রহণ করতে হবে―সেই সব পুরনো কাসুন্দির কথা তুলছি না তো? ধান ভানতে বসে শিবের গীত গাইছি কেন?
সেই কথাই এবার বলব। তারও কারণ আছে।
বিজ্ঞান-মনস্কতা মানে নিছক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সচেতনতা নয়, প্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষতা বা সপ্রতিভতা নয়। বিজ্ঞান-মনস্কতা মানে হল বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি, যুক্তিশীল মননচর্চা, বৈচারিক চিন্তাকৌশল। ব্যাপারটা এমন নয় যে শুধু বিজ্ঞানের ছাত্রদেরই বিজ্ঞান-মনস্ক হওয়া প্রয়োজন, অন্য বিষয়ের ছাত্রদের বিজ্ঞান-বোধ না থাকলেও চলবে। বিজ্ঞানের কোনো বিষয় নিয়ে পড়ি বা না পড়ি, শিক্ষকতা গবেষণা করি বা না করি, সবাইকেই সব কিছু বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির আধারে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। বিজ্ঞান আর বৈজ্ঞানিক মানসিকতা পরস্পর সম্পর্কিত হলেও দুটো ঠিক এক জিনিস নয়। একটা হলেই আর একটা হয় না। আপনা আপনি হয় না। একজন বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে, গবেষণা করে, চর্চা করে, ছাত্র পড়ায়―কিন্তু হাতের আঙুল ভর্তি আংটি; পঞ্চধাতু, অষ্টধাতু, রুবি, নীলা, বৈদুর্যমণি। একটা হয়ত মঙ্গলকে ভয় দেখাচ্ছে, আর একটা হয়ত আবার ভাইরাস ব্যাকটিরিয়াদের শাসন করার কাজে ব্যস্ত, তৃতীয়টার উদ্দেশ্য কোনো জটিল মামলায় জজ সাহেবের মন জেতা, ইত্যাদি―এমন তো আকছারই দেখা যায়। যাঁরা এইরকম আংটি পরেন, ধাতুরত্ন ধারণ করেন, তার পক্ষে তাঁরা আবার কত বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেন! বস্তুর উপর বস্তুর কি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নেই? জীবাণুদের বিরুদ্ধে রসায়ন-শাস্ত্র রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করতে বলছে না? কিংবা, সব শেষে একখানা মোক্ষম অবধারিত প্রশ্ন, “বিজ্ঞান কি সব জানে?” আর অন্যরা জানুন বা না জানুন, বিজ্ঞানের লোকেরা তো জানেনই―যে বিজ্ঞান এখনও সব জানে না, আর কখনও সব জানবে বলে মনে করে না। সুতরাং …
এমন অনেককেই দেখা যায়, যারা ভগবান মানে না কিন্তু যাদের ভূতের ভয় আছে। কিংবা তাদের হয়ত ভূত-প্রেতে ঘোর অবিশ্বাস, অথচ ছেলেমেয়ের কোনো সময় কঠিন অসুখবিসুখ হলে মা কালীর থানে বা রাস্তার মোড়ের শনিঠাকুরের বেদীতে অথবা কোন গাজীসাহেবের মাজারে দু-পাঁচ টাকার বাতাসা মানত করে রাখে। আবার এমনও বহু লোককে দেখা যায়, যাঁদের পড়াশুনো হয়ত কলা বিভাগে, কিন্তু খাদ্যাখাদ্য বাছবিচারে রান্নার উপকরণে ছেলেমেয়ের পোশাক বা স্বাস্থ্যের প্রশ্নে তাঁরা অত্যন্ত যুক্তিশীল এবং বিজ্ঞান-মনস্ক।
ধরুন, টিভিতে বিজ্ঞাপনে দেখাচ্ছে, কমপ্ল্যান খেলে একটি ছেলে বা মেয়ে দ্বিগুণ তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠবে, লম্বা হবে। বহু লোক বিশ্বাস করছে। তারা বেশিরভাগ লক্ষই করছে না, যে স্কেল দিয়ে বৃদ্ধিটা দেখানো হচ্ছে, তাতে চার ফুট পর্যন্ত মাপটা ফুটে দেখিয়ে বৃদ্ধি দেখানো হচ্ছে সেন্টিমিটারে। কেন? এরকম স্কেল বাজারে হয় নাকি? কারোর উচ্চতা আপনি বলেন চার ফুট পাঁচ সেন্টিমিটার? তার মানে বিজ্ঞাপনটায় গোলমাল আছে। বা কোনো গূঢ় মতলব আছে। কজন সাধারণ মানুষ এটা খেয়াল করেছে? এই ধরনের একটা সাধারণ চালাকি বোঝার জন্য কি বিজ্ঞান পড়ার বিশেষ দরকার আছে? রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা অ্যাকাউন্টেন্সিতে অনার্স নিয়ে পড়লে এটা বোঝা যাবে না? বরং বাস্তবে আমরা দেখছি, বিজ্ঞানের ছাত্ররাও এটা ধরতে পারছে না। তাদেরও একটা বিরাট অংশ এই সব বিজ্ঞাপনী চালাকিতে ভিরমি খেয়ে যাচ্ছে। এবং লম্বা হওয়ার জন্য রোজ রোজ কমপ্ল্যান খাচ্ছে। অথবা অন্য কিছু খাচ্ছে। এই প্রশ্নটা তারা করছে না, স্বাস্থ্যবান হওয়া বা লম্বা হওয়ার যে জৈবিক প্রক্রিয়া, এই ধরনের কৌটোবন্দি পানীয় তার উপরে কীভাবে প্রভাব ফেলে। অথবা আদৌ ফেলতে পারে কিনা।
রাজশেখর বসু তাঁর একটি বৈজ্ঞানিক মনোভাব সংক্রান্ত প্রবন্ধে দেখিয়েছিলেন, বিজ্ঞাপনে কীভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে ঠকানো হয়। কোনো একটি মাথার তেলের কোম্পানি তাদের বিজ্ঞাপনে লিখেছিল, “ইহাতে পারদ নাই।” যেন, অন্য সব প্রস্তুতকারকের তেলে ভেজাল হিসাবে পারদ থাকার কথা। আজ বেঁচে থাকলে তিনি দেখতে পেতেন, সেই সাবেকি কায়দাটা আজও মরেনি। আজ আবার কোনো এক তেল উৎপাদকের হয়ে টালি-পাড়ার একজন বিখ্যাত ফিল্মি নায়ক বলছেন, তাঁদের বিজ্ঞাপিত তেলে নাকি অ্যামোনিয়া নেই। এই রকম অসংখ্য বিজ্ঞাপনী চালাকি ছড়ানোর পেছনেও আছে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান-মনস্কতার অভাব সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয়।
[ঘ]
এবার কয়েকটা কাজের কথায় আসা যাক।
বিজ্ঞান-মনস্কতার প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি কী কী?
অবিশ্বাস, ভয়, কৌতূহল, সংশয়, প্রশ্ন, … ।
সে কি? কী বলছেন মশাই? এসব তো নেতিবাচক লক্ষণ।
ঠিক তাই। বিজ্ঞান-মনস্কদের যে লোকে নাস্তিক বলে জানেন নিশ্চয়ই। সেটা এই কারণেই বলে। সব ব্যাপারেই শুরুতে তারা খালি বলে—না, না, না, নাস্তি, নাস্তি, নাস্তি, …। এতে বিশ্বাস করতে পারছি না, ওটা বলতে ভয় পাচ্ছি পাছে ভুল প্রমাণ হয়ে যায়, অমুক তত্ত্বটায় ঘোরতর সন্দেহ আছে ঠিক হবে কিনা, …, ইত্যাদি। আর কেবলই বলেন, জানি না, খানিকটা জানা গেছে, অনেক কিছু এখনও জানায় বাকি আছে, অল্প অল্প করে জানা যাচ্ছে, এই রকম আর কি। সহজে কোনো প্রস্তাবে কিছুতেই হ্যাঁ বলতে পারেন না বিজ্ঞান জগতের লোকেরা। একেবারে বলেন না তা নয়, তবে না-এর তুলনায় হ্যাঁ-এর সংখ্যা খুব কম। মাইকেল ফ্যারাডের দেওয়া গড় হিসাবে, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দশটা প্রস্তাবের নটাতেই নাকি ওনারা না বলে দেন। একটাতে অতি কষ্টে হ্যাঁ বলেন। সায় দেবার ব্যাপারে বড্ড কিপটে। বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যান। দেখবেন, প্রতিটি ব্যাপারে খালি প্রশ্ন, প্রশ্নের পর প্রশ্ন। কী ভয়ানক সন্দেহবাতিক ভাবা যায় না। কারোর সঙ্গে কারোর ব্যক্তিগত ঝগড়াঝাঁটি আছে, ব্যাপারটা এমন নয় কিন্তু। হয়ত বাইরে গলায় গলায় ভাব। কিন্তু বিজ্ঞানের সমস্যা এলে, পরীক্ষার ফলাফলের কথা উঠলে অমনি তক্কাতক্কি শুরু হয়ে যায়। সহজে থামতে যায় না। তাঁদের শুধু ভীষণ ভয়, পাছে কিছু একটা ভ্রান্ত তত্ত্ব সম্মেলনে গৃহীত হয়ে যায়।
তুলনায় একটা ধর্মের জলসায় গিয়ে দেখুন। কোনো একজন বড় ধার্মিক সাধুর বচনামৃত শ্রবণ বা পাঠ করুন। বার বার কী দেখতে পাবেন? বিশ্বাস, নির্ভাবনা, নিঃসন্দেহ, নিস্তর্ক, মেনে নেবার আগ্রহ, … । যেমন এদেশে তেমনই পশ্চিমাদের দেশে। আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন বলতেন, “বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর”, লাতিনে ওরা বলত “Credo ut intelligam” (বিশ্বাস করলে তবেই আমি বুঝতে পারব)। এগুলো সবই হচ্ছে ইতিবাচক লক্ষণ। সব কিছুতেই হ্যাঁ বলবার ঝোঁক বা ইচ্ছা। এই জন্যই ধর্মে বিশ্বাসীদের লোকে আস্তিক বলে। তারা সব কিছু সহজে মেনে নেয়, বিশ্বাস করে, তাদের কোনো ব্যাপারেই খুব একটা সন্দেহ হয় না, প্রশ্নও জাগে না। তাদের মনে কোনো কিছুই গভীরে গিয়ে জানার খুব একটা ইচ্ছা নেই।
শিবদুর্গার তিনটি ছেলে মেয়ে স্বাভাবিক, কিন্তু গণেশের বেলায় হাতির মুন্ডু হয়ে গেল। তা-ই কোটি কোটি লোক দু তিন হাজার বছর ধরে মেনে এসেছে। সন্দেহ করেনি, প্রশ্নও তোলেনি।
আচ্ছা, সে না হয় পুরা কালের কথা। কিন্তু এই সেদিন যে পাথরমূর্তি গণেশের শুঁড় দিয়ে দুধ পানের গল্প সারা ভারতে ছড়িয়ে গেল, শুধু সাধারণ পিকলু-ন্যাবলা-পাচি নয়, বহু ডক্টরেট, অফিসার, ম্যানেজার, আইনজ্ঞ তথা ভিআইপি যে গ্লাশে দুধ আর হাতে চামচ নিয়ে রাস্তায় লম্বা লাইনে আম আদমিদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লেন, সারা দেশে এক দিনে মাত্র কয়েক ঘন্টায় কম বেশি বাহাত্তর লক্ষ লিটার দুধ মাটিতে গড়াগড়ি খেল, তার পেছনেও তো সেই আদি অকৃত্রিম বিশ্বাস। প্রশ্ন বা সন্দেহ নেই। মেনে নেবার কী অসীম আগ্রহ।
বিজ্ঞান-মনস্কতা এই বিশ্বাসকেই বদলাতে চায়। তার বক্তব্য, আগেভাগেই কোনো বিবৃতিতে বিশ্বাস না করে, প্রথমে প্রশ্ন কর, নানা দিক থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বুঝবার চেষ্টা কর, সমস্ত সন্দেহ মোচন হলে তবে মানবে। তথ্য যুক্তি প্রমাণ ও প্রয়োগ―এই হল বিজ্ঞান তথা বিজ্ঞান-মনস্কতার প্রধান চারটে স্তম্ভ। নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করে বাস্তব তথ্য যোগাড় কর, তার মধ্যে তুলনা করে হিসাবনিকাশ করে মাপজোক করে যুক্তি দিয়ে সাজিয়ে মূল পরিঘটনাটিকে দেখার চেষ্টা কর। হাতে কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রমাণ করা যায় কিনা দেখ। যে সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসছে তাকে কোন জায়গায় কীভাবে প্রয়োগ করা যায় দেখ, অর্থাৎ, তাকে কাজে লাগানো যায় কিনা দেখ। তারপর সেই সিদ্ধান্তকে গ্রহণ কর।
আমার অবশ্য ইদানিং মাঝে মাঝে মনে হয়, আস্তিক নাস্তিক কথাজোড়ার অন্য রকম অর্থও থাকা সম্ভব। যে বিচারের ধারায় যুক্তিবুদ্ধি স্বভাবগতভাবে অস্তমিত হয়ে যায় তাই হল আস্তিক দর্শন। পক্ষান্তরে, যে ধরনের চিন্তাধারার মধ্যে যুক্তিতর্ক প্রমাণ ও প্রয়োগের বুদ্ধি আবশ্যিকভাবে ন্যস্ত রয়েছে, তাকে বলা হয় নাস্তিক দর্শন।
তা, এইভাবে ভাবলেই বা ক্ষতি কী?
[ঙ]
বরং লাভ আছে। এই দুটো বিচারধারার মধ্যে মৌল পার্থক্যটা ঠিকমতো বোঝার দরকার আছে। কেন না, অনেক সময়ই কিছু লোককে বলতে শোনা যায়, ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের নাকি কোনো বিরোধ নেই। বিরোধ নাকি দুই তরফেরই কট্টরপন্থীদের মধ্যে। সত্যিকারের ধর্মের সারকথা যে মেনে চলে সে নাকি বিজ্ঞানের সত্য জানতে কখনও পরাঙ্মুখ হয় না, আপত্তিও করে না, বরং সত্য জানতেই চায়। সত্যিকারের বড় বিজ্ঞানীদেরও নাকি ধর্মের প্রতি কোনো অসহিষ্ণুতা নেই, তাঁরা নাকি ধর্মকে বুঝতে চান, অনেকে নিজেরাই ধর্মপ্রাণ হয়ে থাকেন। ইত্যাদি।
এই বক্তব্যে আমার দ্বিবিধ আপত্তি আছে। আপত্তিটা নিছক ব্যক্তিগত বিশ্বাসের জায়গায় গিয়ে নয়। যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে ধর্মে বিশ্বাস করেন কিন্তু বিজ্ঞানের কাজটা বিজ্ঞানের নিয়মেই করেন, তাঁদের এই বিশ্বাস-আচরণের দ্বিভাজন (dichotomy) নিয়েই আমার প্রথম আপত্তি। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী বিজ্ঞান চর্চা করা যায় না বলেই তো তাঁদের জোড়াতালি দিতে হয়। ধর্মাচরণে বৈজ্ঞানিক বহু উপচার কাজে লাগানো যায়। কিন্তু বিজ্ঞানের গবেষণায় বা প্রয়োগে ধর্মের তিলাংশও ব্যবহার করার উপায় নেই। কাজে দেবে না। বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়ে মাইক বাজিয়ে আপনি পুজো করতে পারেন, আজান দিতে পারেন। কিন্তু পুজোর প্রসাদ বা ফকিরের জলপড়া দিয়ে আপনি একটা ফোঁড়ার ব্যথাও কমাতে পারবেন না। অক্ষয় কুমার দত্তের ফরমুলা অনুযায়ী বলতে পারি, জ্বর হলে আপনি মা কালীর নাম করতে পারেন, প্যারাসিটামল খেতে পারেন, আবার মা কালীর নাম নিতে নিতে প্যারাসিটামল খেতে পারেন। জ্বর কমার হলে ওই ওষুধেই কমবে। মা কালীর নামের মাহাত্ম্যে নয়। বীজগণিতের সমীকরণের আকারে লিখলে কালীনামের ফলাফল শেষ অবধি শূন্যই হবে।
হ্যাঁ, এর মধ্যে ফরাসি যুক্তিবাদী দার্শনিক ভোলতেয়ারের সেই বিখ্যাত রসিকতারও ছাপ আছে। কে একজন তাঁকে বলেছিল, “আচ্ছা মশাই, মন্ত্র দিয়ে কি কাউকে মেরে ফেলা যায়?”
“যায়, অবশ্যই যায়। তবে সঙ্গে আর একটা জিনিসও লাগবে।”
“আর কী লাগবে?”
“তেমন কিছু নয়, উপযুক্ত পরিমাণে কিছুটা সেঁকো বিষ। তাহলে মন্ত্রের কাজ ভালো হবে।”
বিজ্ঞানের সাথে যে কোনো প্রকারের অন্ধ বিশ্বাসের একমাত্র এরকম সমন্বয়ই করা যায়। ধর্মের ক্ষেত্রেও এটা সত্য।
সুতরাং, কোনো বড় বিজ্ঞানী হয়ত বলতে পারেন, অনেক কিছু জানার পরেও আমাদের এত জানতে বাকি যে জগতের রহস্য যেন আরও নিগূঢ় হয়ে উঠছে। প্রকৃতিজগতের এই অটুট শৃঙ্খলা, এত রকম জটিলতা―এসবের ব্যাখ্যা হয় না একজন সুপারপাওয়ারের কথা ধরে না নিলে। তখনও আমাদের প্রশ্ন থেকেই যাবে, ধরে নিলেই কি সমস্ত রহস্যের ব্যাখ্যা হয়? সকলেই জানেন, হয় না। একটি বাস্তব পরিঘটনার পেছনে আর একটি কোনো আরও মৌলিক ও বাস্তব পরিঘটনাকে খুঁজে পেলে দ্বিতীয়টার সাহায্যে প্রথমটার ব্যাখ্যা হয়। মেঘ কীভাবে উৎপন্ন হয় জানলে বৃষ্টির একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অন্যত্র সেই জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটানো সম্ভব হয়। কিন্তু ভগবান আমাদের বৃষ্টি দেন বললে নতুন কী জানা যায়? বৃষ্টি সম্পর্কে আমাদের এক দানাও জ্ঞান বাড়ে না। সেই জানা কাজেও লাগে না। যা জানি না, ঐশী শক্তি ঘটাচ্ছেন ধরে নিলেও তা অজানা এবং অধরাই থাকে। ঈশ্বরের বদলে দৈত্যদানো বসালেও একই কথা। আবার অক্ষয় কুমারের ফরমুলায় বলতে হবে, জ্ঞানের জগতে একজন সুপারপাওয়ার আছে ধরে নেবার ফলও সেই শূন্যই। তবে আর তা ধরে নিয়ে লাভ কী? অর্থাৎ, প্রশ্নটা ঝগড়ার নয়, ফলাফলের।
দ্বিতীয়ত, জ্ঞানের সাথে জ্ঞানের সমন্বয় হয়। জ্ঞানের সাথে অজ্ঞতার কোনো সমন্বয় হয় কি? হয় না বলেই বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের সমন্বয় সম্ভব নয়। যুক্তিবাদের সাথে কুসংস্কারের সমন্বয় সম্ভব হয় না। একটা চাইলে আর একটাকে ছাড়তে হবেই। ধর্ম হিন্দুকে বলে, গোমাংস ভক্ষণ করিও না, উহাতে মহাপাপ; ধর্ম মুসলমানকে বলে, কদাচ ভুলিও না, শুয়রের মাংস ভয়ানক হারাম। আর খাদ্য সংক্রান্ত বিজ্ঞান থেকে জানা যায়, রক্তচাপ হৃদরোগ ইউরিক অ্যাসিড ইত্যাদির সমস্যা না থাকলে বাল্য কৈশোর যৌবনে এই দুই (এবং আরও নানা) প্রকারের মাংস খাওয়া মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে শুধু ভালো নয়, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অশিক্ষিত ধর্মান্ধ গোঁড়া হিন্দু-মুসলমানের কথা ছেড়ে দিন, শিক্ষিত উদার মনস্ক কতজন এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে আগ্রহী হবেন? বা আদৌ হয়ে থাকেন? এইভাবে দেখলে বোঝা যাবে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞান মনস্ক হতে চাইলে সেই সব ক্ষেত্রেই ধর্মমনস্কতাকে ছাড়িয়ে আসতে হবে। তা না হলে যেটা হবে সেটা আরও হাস্যকর। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি তাঁদের শিক্ষার মালমশলা কাজে লাগিয়ে সেই ধর্মান্ধতার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু করবেন। অশৌচ পালনের সাথে ব্যাক্টিরিয়া নিধন, দাড়ি রাখলে গালে মশার কামড়ের হাত থেকে অব্যাহতি, … এমনি ধারা আরও কত কিছু।
উল্টোটা তাঁরা কেউ করবেন না।
কোনো বিজ্ঞানশিক্ষিত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিই কখনও বলবেন না, অন্তত এযাবত আমি কাউকে বলতে শুনিনি, “আমাদের ঈশ্বর ভক্তির সঙ্গে আমরা কে কী খাই তার কোনোই সম্পর্ক নেই।” যুক্তিটা নিতান্তই সহজ। ঈশ্বর আমাদের মুরগিও দিয়েছেন, কলাও দিয়েছেন; গরুও দিয়েছেন, লেটুস পাতাও তৈরি করেছেন; ফুলকপিও বানিয়েছেন, শুয়রও পয়দা করেছেন। ধর্মপ্রাণ লোকেরা বলেন, যিনি আল্লাহ তিনিই ভগবান তিনিই তো নাকি গড। নামে ভিন্ন হলেও আসলে সেই এক পরম করুণাময় তিনি [তা না হলে দুনিয়ায় অনেক ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হত; সেটা আবার সমস্ত ধর্মের পক্ষেই যথেষ্ট অস্বস্তিকর হয়ে যেত]। সবই যখন সেই তাঁরই সৃষ্টি, তাঁর একটা জিনিস খেলে ভালো আর অন্য একটা খেলে দোষ হবে কেন? বিশেষ করে যখন এক ধর্মের নিষিদ্ধ খাদ্যগুলো অন্য ধর্মের ঈশ্বর বিশ্বাসীরা খেয়েদেয়ে দিব্যি হাজার হাজার বছর ধরে হজমও করেছে, টিকেও রয়েছে? ভগবান যদি দিল্লিতে বলেন, “টমেটো খাও, এটি খুব ভাল খাদ্য”; আর বিজয়ওয়াদায় বলেন, “খবরদার, কদাচ টমেটো খেও না, খেলেই পাপ হবে”―তাঁর সম্পর্কে আপনার ধারণা কী দাঁড়াবে? খাদ্যাখাদ্য নিয়ে ধর্মবিশ্বাসীদের কেউ এইভাবে বলতে পারলে, ঈশ্বরব্যঞ্জনার কথাটা সত্য না হলেও একটা সমন্বয়ের আভাস অন্তত পাওয়া যেত। সেটুকুও আজ অবধি পাইনি।
আরও একটা জলজ্যান্ত উদাহরণ দিই। ভারতে প্রতিবছর সাগরমেলায় বা প্রতি চার বছর অন্তর কুম্ভমেলায় লক্ষ লক্ষ লোক জড়ো হয়ে যে পবিত্র গঙ্গাস্নান করে তাতে সংশ্লিষ্ট জায়গায় ব্যাপক পরিবেশ দুষণ হয়। এই অসংখ্য মানুষের ফেলে যাওয়া বর্জ্য থেকে নদী সমুদ্র ও মেলার চারপাশের জল মাটি বায়ুর দীর্ঘমেয়াদি অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যায়। অনেক সময় ব্যাপক দুর্ঘটনাটা ঘটে, বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি হয় (আরবে যারা হজ করতে যায় তাদের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য)। আজ পর্যন্ত কোনো একজন ধর্মপ্রাণ শিক্ষিত চিন্তাশীল মানুষকে বলতে শুনেছেন কি কেউ, “না, এরকম জমায়েত ভালো নয়। ব্যক্তি স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের স্বাস্থ্য–কোনোটার পক্ষেই ভালো নয়”? কেউ কি বলেছেন, “ভগবান বল, আল্লাহ বল তিনি সর্বত্র বিরাজমান; তাঁকে খুঁজতে বা পেতে কোনো একটা বিশেষ জায়গায় যেতে হবে কেন? তুমি যেখানে আছ, সেখানেও তিনি আছেন। সেখানেই তাঁর পূজাপাঠ আরাধনা কর”? আমার জানা নেই। যদি ধর্মে বিশ্বাসী একজনও কেউ সাহস করে এসব কথা বলতে পারতেন, তাহলে বুঝতাম, সমন্বয়ের সামান্য হলেও সম্ভাবনা আছে। কিন্তু না। ধর্মে বিশ্বাসী কেউই তা বলতে পারেন না। পারেন না কেন না, তাঁরাও জানেন, শুধু একজন আপনভোলা ঈশ্বর নিয়ে ধর্ম হয় না। বাকি সমস্ত আচার বিচার প্রথা প্রকরণ মিলিয়েই ধর্ম। অন্তত সমষ্টির জন্য ধর্ম মানে তাই।
এই অবস্থায় বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করার একটাই মানে। তা হল, ধর্মবিশ্বাসীরা তাঁদের বিশ্বাস ও আচরণ থেকে এক চুলও নড়বেন না; বিজ্ঞান অনুরাগী যুক্তিবাদীদেরই তাঁদের জায়গা থেকে সরে আসতে হবে। মেনে নিতে হবে, হ্যাঁ, ধর্মে কিছু কিছু সত্য থাকলে থাকতেও পারে। ধর্মগ্রন্থে অনেক ভাল ভাল কথা আছে। ঈশ্বর বিশ্বাস থাকলে বিজ্ঞানের তো আর তেমন কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। অতএব আপাতত না হয় এরকম একটি প্রতিপাদ্যকে মেনে নেওয়াই যাক। আমার মনে হয়, বিজ্ঞানমনস্কতার তরফে এরকম ছাড় দেবার কোনো প্রয়োজন দকার্তের সময়ে থাকলেও আজ আর নেই। আমাদের পক্ষ থেকে সত্যটা স্পষ্ট উচ্চারণে বলতে পারা উচিৎ।
[চ]
পরিশেষে এ-ও দেখা দরকার, মানুষের জ্ঞান কোন রাস্তাতে বাড়ছে। যতদিন মানুষ শুধু ধর্মে গুরুতে মান্যগ্রন্থে বিশ্বাস করেছে ততদিন তার জ্ঞানের বিকাশ কতটা হয়েছে, আর যবে থেকে মানুষ জিজ্ঞাসার পথে, সংশয়ের পথে জানতে শুরু করেছে তখন থেকে তার জ্ঞানের বৃদ্ধি ও বিকাশের হার কী। এই তুলনায় গেলেই বোঝা যাবে কোনটা সত্যিকারের জানার পথ, আর কোন পথে হাঁটলে বিহারের ঘটনায় গিয়ে পৌঁছতে হবে। শুধু পদার্থবিজ্ঞান রসায়ন গণিত জ্যামিতি জীববিদ্যা ভূতত্ত্ব নৃতত্ত্ব ইত্যাদি নয়, ইতিহাস ভূগোল পুরাতত্ত্ব ভাষাতত্ত্ব অর্থনীতি―সব ক্ষেত্রে প্রশ্ন করে করে উত্তর খুঁজতে খুঁজতে, একের পর এক সন্দেহ নিরসন করতে করতে, মানুষ জানছে। মানুষের জ্ঞান সমৃদ্ধতর হচ্ছে। এই পথ ছেড়ে দেওয়ার মানে হল এযাবত যা জেনেছেন তাকে একটা গুদামঘরে ঢুকিয়ে দরজায় তালা মেরে চলে আসা।
আমাদের দেশের ছাত্রদেরও তাই প্রশ্ন করতে শেখাতে হবে। শুধু বিজ্ঞানের বিষয় নয়, ইতিহাস ভূগোলও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শেখাতে হবে। সূর্য চন্দ্রকেও চেনাতে হবে। দিক চেনাতে হবে। ছোটবেলা থেকেই যেন দিকভ্রষ্ট হয়ে না যায়। ইতিহাসের শিক্ষককেও ক্লাশে সংশ্লিষ্ট ভূগোলের মানচিত্র নিয়ে ঢুকতে হবে। শিক্ষার মধ্যে আরও অনেক কিছু করতে হবে, করা যায়। বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, শিক্ষার সমস্ত প্রকোষ্ঠেই বিজ্ঞানকে নিয়ে যেতে হবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিকে নিয়ে যেতে হবে। বিজ্ঞান-মনস্কতা বৃদ্ধির আর কোনো শর্টকাট রাস্তা নেই।
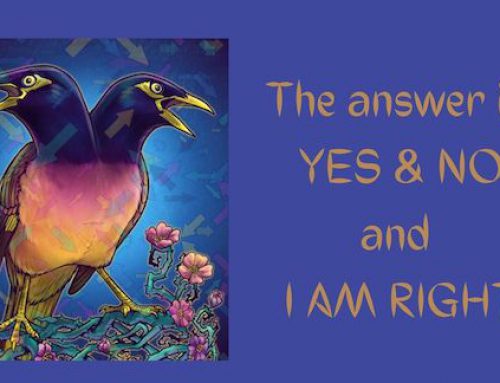
অশোক বাবু আপনার কাছ থেকে আরো লেখা চাই।
সহমত (y)
চমৎকার লেখনী… (F)
এই লেখার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ঠ নয় তবুও হরবংশ রাই বচ্চনের দুটো লাইন তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারছিনা,
“ধর্মগ্রন্থ সৰ জলাচুকি হ্যায় জিসকি অন্তর কি জোয়ালা
মন্দির, মসজিদ, গির্জে সবকো তোড় চুকা যো মতওয়ালা
পণ্ডিত, মোমিন, পাদ্রীওকে ফান্দকো যো কাট চুকা
কর সকতি হ্যায় আজ উসিকা স্বোয়াগত মেরি মধুশালা।”
আমার ক্ষুদ্র মধুশালায় আপনাকে সুস্বাগতম। :guru:
যাঁরা পড়েছেন এবং উতসাহিত করেছেন এই সুযোগে তাঁদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ইসলামিক বিজ্ঞানের নামে যে ভণ্ডামি চলে সে ব্যাপারে যাঁদের আগ্রহ আছে তাঁরা পাকিস্তানের বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী পারভেজ আমির আলি হুডভয়-এর লেখা “Islam and Science” (Zed Books, London and New Jersey, 1991) গ্রন্থটি সংগ্রহ করে পড়ে নিতে পারেন। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের পক্ষে অসম্ভব ভালো একটি রচনা এটি। তবে এরকম ভণ্ডামি শুধু ইসলামী মৌলবাদীদের একচেটিয়া কীর্তি নয়, হিন্দু বা খ্রিস্টান মৌলবাদীরাও বেদ বা বাইবেল-এ আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করার মরিয়া প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের সকলের শুধু একটাই সমস্যা। যদি বলা হয়, “আপনারা আপনাদের ছেলেমেয়েদের নাস্তিক স্কুল-কলেজে না পাঠিয়ে বৈদিক-কোরাণিক-বাইবেলিক বিজ্ঞান পড়াতে পাঠান”, অমনি তাঁদের মুখ ভার হয়ে যায়।
অদ্ভূত সুন্দর একটি লেখা। সমাজে বিজ্ঞান মনস্কতা বাড়াতে এধরেনর লেখার কোন বিকল্প নেই। কথাটা একদম ঠিক, যে শুধু বিজ্ঞান পড়লেই বিজ্ঞান মনষ্ক হওয়া যায় না।
এই বিষয় গুলো দরকার। সেটা কলা, বানিজ্য, ভূগোল, ইতিহাস সব কিছুতেই। এমনকি দৈন্দিন জীবনাচড়নেও। লেখক কে অসংখ্য ধন্যবাদ লেখাটির জন্যে।
চমৎকার লেখাটির জন্য ধন্যবাদ।
খুবই ভীতিকর সংবাদ কোনই সন্দেহ নেই। আচ্ছা যাকে পুড়িয়ে মেরেছে তার কি গায়ের রঙ কালো বা চেহারা খারাপ? ভারতীয় উপমহাদেশে গায়ের রঙ নিয়ে যে নোংরা অবসেসন আছে, সেটা কে না জানে।
এখানে যদি অপেক্ষাকৃত কালো সন্তানটিকেই উতসর্গ করে নিজের বাবা মা, তাহলে মনে হয় এইসব সমাজের পরিবর্তন হতে আরো এক হাজার বছর লাগবে।
শুনেছি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি কোরানিক বিজ্ঞান নামে একটা অদ্ভুত বিষয় পড়ানো হয়। নিউ ইয়র্কে কয়েকটা বিল্ডিঙের গায়ে লেখা দেখেছিলাম, ‘খ্রিস্টান সায়েন্স ল্যাবরেটরি’।
বোধগম্য নয় এসব হাসির ব্যাপার স্যাপার। চমৎকার লিখেছেন। ধন্যবাদ লেখাটির জন্য।
@তামান্না ঝুমু,
এইডা তো অতি উত্তম জিনিস। এইডা কি বাংলাদেশের কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলছেন? সেটা হলে একবার অবশ্যই গিয়ে দেখে আসব যে কোরানিক বিজ্ঞান টা কি জিনিস :hahahee:
:hahahee:
আপনি আমেরিকায় থাকেন না? সেক্ষেত্রে দেরী না করে এখনই খোঁজ নিন যে এই ল্যাবরেটরিতে কি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে খ্রিষ্টান তৈরির ব্যবস্থা আছে কিনা।
এই দুনিয়া যে দিন দিন গোল্লায় যাচ্ছে, এইগুলা না জানলে বিশ্বাসই হত না। আগে হুজুররা বলতেন যে বিজ্ঞানীদের মাথা ঘোরে, আর এখন সুবিধা করতে না পারায় সব কিছুতে খালি বিজ্ঞান লাগায়ে দিতেছে। হাহাহাহা। 😀
@অর্ফিউস,
সকল ইছলামি বিশ্ববিদ্যালয় এই ব্যাপারে ভাই ভাই শুনেছি। আপনি এক্ষুনি গিয়ে দেখে ছওয়াব হাছিল করুন।
বাইরের লেবেল দেখে তাই তো মনে হয়। ভেতরে গিয়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে খ্রিস্টান তৈরির রেসিপিটা দেখে নিলে মন্দ হয় না আসলে। তাহাড়া ছওয়াব হাছিলের ব্যাপারও রয়েছে।
@তামান্না ঝুমু,
আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে তো আর কথাই নেই। এদের ল্যাঞ্জা ধরেই আমরা ১৬ কোটি তৌহিদি জনতা নিজেদের আখেরাতের রাস্তা ক্লিয়ার করব ইনশাল্লাহ।
অবশ্যই যান খ্রিষ্টান বিজ্ঞান অর্জন করে সওয়াব নিয়ে আসেন, এদিকে আমি ইসলামী বিজ্ঞান আয়ত্ব করি। আমরা সবাই সওয়াব ভাগাভাগি করে নেব,
যেন সবাই জান্নাতে যেয়ে অনন্ত জীবন যৌবন উপভোগ করি।
পুনশ্চঃ আপনার জান্নাতে যেয়ে বিশেষ লাভ নেই, কারন মেয়েদের জন্য জান্নাতে মুলা ছাড়া কিছুই নেই। কাজেই আপনার সওয়াবের ভাগ যদি ইয়ে মানে ধার দেন, তাহলে জান্নাতে গিয়ে সুদে আসলে শোধ করব ইনশাল্লাহ। এতে পরোপকারের জন্য আরো বেশি করে সওয়াব পাবেন 😛 :hahahee:
অসাধারন লিখেছেন। (Y)
এই ধরনের শিক্ষিত ধৰ্মান্ধ অনলাইন জগৎ-এ বহু দেখা যায়। :))
দুর মশাই, এতবড় একখানা প্রবন্ধ লিখলেন, একটু বোর টোর তো হতে দেবেন, না কি? দু’ হাত খুলে (আমি শোল্ডার সকেট থেকে খুলে ফেলতে বলছি না) লিখুন। এরকম আরো লেখা চাই।
কোন বেদপ্রেমী বাংলা ব্লগে পড়েছিলাম, গনেশের ধড়ে হাতির মাথা নাকি প্রাচীন ভারতের শল্য চিকিতসা দক্ষতার নমুনা।
শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা যখন কোরানিক বিজ্ঞান, বৈদিক বিজ্ঞান প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লাগেন, তখন নির্ভেজাল বিজ্ঞানকে মানুষের মনে অবস্থান দেয়ানো একটু কঠিনই হয়ে পড়ে।
@এনালিস্ট, উতসাহ দেবার জন্য ধন্যবাদ। সুপাঠক পেলে এবং তাঁদের প্রশ্রয় থাকলে অবশ্যই আরও লেখা যাবে।