কিছু ভুল ধারণার অপনোদন
মূল পাঁচটি সূত্র মনোবিজ্ঞানের সকল গবেষণায় প্রয়োগ করে সন্তোষজনক ফল লাভ সম্ভব যদিও এখন পর্যন্ত সেগুলো আমাদের যথেষ্ট সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এর অন্যতম কারণ বেশ কিছু ভুল ধারণার কারণে মনোবিজ্ঞানের এই এপ্রোচটিকে শুরুতেই অবজ্ঞা করা এবং এড়িয়ে চলা। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত অধিকাংশ ভুল ধারণার মূল উৎস অনেকদিন ধরে চলে আসা “নেচার/নার্চার বিতর্ক”। একে অন্যভাবে বলা যায় প্রকৃতি বনাম প্রতিবেশ, জীববিজ্ঞান বনাম সংস্কৃতি, যুক্তি বা শিক্ষা বনাম স্বজ্ঞা বিতর্ক। কিন্তু অনেক দিক দিয়ে এসব বিতর্কের গোড়ায় গলদ থেকে যায়। আর বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানকে কোনভাবেই এ ধরণের আরেকটি বিতর্কের উস্কানিদাতা হিসেবে গ্রহণ করে ঠিক হবে না। এজন্য প্রথমেই নেচার/নার্চার থেকে উদ্ভূত ভুল ধারণাগুলোর অবসান ঘটা প্রয়োজন।
সর্বজনীন নকশার উপর গুরুত্বারোপ
বিকাশের এক পর্যায়ে নির্দিষ্ট কোন প্রজাতির সকল জীবের মধ্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে মানুষের কথাই বলা যাক। “গ্রে’স এনাটমি” বইয়ের যেকোন পৃষ্ঠা খুললেই মানব শারীরস্থানের গাদি গাদি ছবি দেখা যাবে। এগুলো কিন্তু সর্বজনীন ছবি, এই অঙ্গগুলো সব মানুষের শরীরে একই রকম। পরিমাণগত দিক দিয়ে কোন দুটি পাকস্থলি একরকম না। তাদের আকার, আকৃতি, ভর, হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিঃসরণের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু কার্যকরি নকশার দিক দিয়ে তারা সবাই এক, সবার পাকস্থলির এক দিকে ইসোফেগাস এবং অন্যদিকে ক্ষুদ্রান্ত্র আছে, সবগুলোই খাবার হজমের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে। অর্থাৎ তাদের কার্যকরি নকশা বা ফাংশনাল ডিজাইনে কোন পার্থক্য নেই। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান এই সর্বজনীন নকশা বা আর্কিটেকচার নিয়ে কাজ করে। এখানে এমন সব বৈশিষ্ট্য নির্বাচিত করা হয় যা এক প্রজাতির সকল জীবের মধ্যেই সমান বৈশিষ্ট্য নিয়ে আছে। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান কেবল এই সর্বজনীন ভৌত নকশার দিকেই নজর দেয়।
বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান কোনভাবেই স্বভাব বংশগতিবিদ্যা নয়
স্বভাব বংশগতিবিদ্যা তথা বিহেভিয়ার জেনেটিক্স একই প্রজাতির বিভিন্ন জীবের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে কাজ করে। একই পরিবেশে বসবাসকারী একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যগুলোর শতকরা কত ভাগ তাদের জিনের পার্থক্যের কারণে হয় সেটা বের করাই স্বভাব বংশগতিবিদ্যার কাজ। সেদিক থেকে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের কাজ প্রায় উল্টো। এক্ষেত্রে আমরা একই প্রজাতির সকল জীবের মধ্যে বিরাজমান সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে কাজ করি। এখানে সর্বজনীন কার্যকরি নকশাটাই মুখ্য। একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য অবশ্যই থাকবে, তাদের অনেক ছোটখাট বৈশিষ্ট্যেও পার্থক্য থাকবে; কিন্তু জটিল অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য সব একই হবে। তাদের ব্যক্তিত্বে তেমন কোন পার্থক্য দেখা যাবে না। এখানে ব্যক্তিত্ব বলতে আসলে মনুষ্যত্বই বোঝানো হচ্ছে। এই সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যগুলোর সমন্বয়ে যে “psychic unity of humankind” তৈরী হয় সেটাই বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের বিবেচ্য বিষয়।
জিন বনাম পরিবেশ বিতর্ক অর্থহীন
অজ্ঞতাবশত অনেককে প্রশ্ন করতে দেখা যায়, কোন জীবের ফিনোটাইপ নির্ধারণে কার অবদান বেশি, পরিবেশ না জিন? এটা আসলে অর্থহীন প্রশ্ন। ফিনোটাইপ তৈরীতে পরিবেশ এবং জিন দুটোই লাগে। এই প্রশ্নকে আরেকটি অর্বাচীন প্রশ্নের সাথে তুলনা করা যায়, আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পরিমাপে কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, দৈর্ঘ্য না প্রস্থ? দুটো মিলেই ক্ষেত্রফল, যেকোন একটি বাদ দিলে ফলাফল হবে শূন্য। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জিন এবং পরিবেশের সম্পর্ককে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়: জিন পরিবেশকে ফিনোটাইপ গঠনে অবদান রাখতে সাহায্য করে। স্বভাব বংশগতিবিদ্যায় পরিবেশ মানে বর্তমান পরিবেশ যার ভিত্তিতে গবেষণা করা হচ্ছে। কিন্তু বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানে পরিবেশ মানে জটিল অভিযোজনগত সমস্যার সমাধান যে সুদীর্ঘ পরিবেশে ঘটেছে সেই পরিবেশ। মোটকথা এটাকে ইইএ বলা যায়। ব্যাপারটাকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমেও ব্যাখ্যা করা যায়। পরিবেশ পরিবর্তনের কারণেই প্রাকৃতিক নির্বাচন কাজ করতে পারে এবং এর মাধ্যমে একসময় জিনের সহায়তায় ফিনোটাইপে পরিবর্তন আসে।
এই ভ্রান্ত বিতর্কের আরেকটি বড় কারণ পপুলেশনের সাথে স্বতন্ত্র জীব গুলিয়ে ফেলা। একটি চারা জলসমৃদ্ধ স্থানে রোপণ করলে যে বৈশিষ্ট্যের গাছ হবে, মরুভূমিতে রোপণ করলে তা হবে না। তার মানে এই না যে তাদের জটিল অভিযোজনে কোন পার্থক্য এসেছে। জটিল অভিযোজনগত সমস্যার সমাধানের প্রশ্ন কেবল পপুলেশনের ক্ষেত্রে আসে এবং এক্ষেত্রে পরিবেশ ও জিনের প্রভাব উপরের অনুচ্ছেদেই আলোচনা করা হয়েছে। নির্দিষ্ট কোন পরিবেশ ব্যক্তির ওপর অনেক প্রভাবই ফেলতে পারে, এতে তার ফিনোটাইপে পরিবর্তনও আসতে পারে, কিন্তু এর ওপর ভিত্তি করে জিন-পরিবেশ সরলীকরণ করার প্রচেষ্টা অবান্তর।
বিবর্তিত নকশা আর জন্মকালীন অবস্থা এক নয়
অনেকে মনে করেন, আমাদের ফিনোটাইপের কোন বৈশিষ্ট্য বিবর্তিত নকশার অংশ বলা মানে এই বলা যে, জন্ম থেকেই শিশুর মধ্যে তা থাকে। ফিনোটাইপের ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই ঠিক না। দাঁতের উদাহরণ দেয়াই যথেষ্ট। শিশু দাঁত নিয়ে জন্মায় না বা দাঁত জন্মাতে শিখেও না। কিন্তু এটা তার বিবর্তিত নকশার অংশ। বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ যে আর্কিটেকচার লাভ করেছে সে অনুসারেই দাঁত, স্তন বা দাড়ি ওঠে। এই ভুল ধারণা আরও বড় ভুল ধারণার জন্ম দেয়। যেমন অনেকে মনে করে, সংস্কৃতিতে যদি এমন কোন উপাদান পাওয়া যায় যা মানুষের স্বভাবে আছে তবে ধরে নিতে হবে সংস্কৃতি থেকেই সেটা স্বভাবে এসেছে। যেমন ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় কম কাঁদে- এটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেকে বলে থাকেন, শিশুরা টিভিতে কেবল মেয়েদেরই কাঁদতে দেখে, টিভির ছেলেরা প্রায় কখনই কাঁদে না। সংস্কৃতি থেকে এই না কাঁদার বৈশিষ্ট্যটা মানুষের স্বভাবে চলে যায়। ছেলে শিশু যেহেতু না কাঁদার বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায় না সেহেতু তারা ধরে নেয় এটা তার বিবর্তিত নকশার অংশ না। আর বিবর্তনের প্রভাব না থাকা মানেই সংস্কৃতি থেকে সেটা ছেলেদের মধ্যে যায়। কিন্তু যখন আমরা ধরে নেব, জন্মের সময় না থাকা সত্ত্বেও অনেক বৈশিষ্ট্য বিবর্তিত নকশার অংশ হতে পারে তখন এহেন ব্যাখ্যার অবকাশ থাকবে না। এই ব্যাখ্যা অনেকটা এরকম আর কি- কিশোরীদের স্তন বাড়তে শুরু করে কারণ তারা টিভি-সিনেমা এবং বাস্তবেও বারবার দেখে কৈশোরে মেয়েদের স্তন বাড়তে শুরু করে, সংস্কৃতি থেকেই এই স্বভাব মানুষের মধ্যে যায়। এ ব্যাখ্যা যেমন হাস্যকর কাঁদার ব্যাখ্যাটাও তেমনি হাস্যকর।
বিশেষায়িত বর্তনী নিয়ে রাজনীতি করা উচিত না
অনেকে বলে, মানুষ সবকিছুই পরিবেশ-প্রতিবেশ থেকে শিখে- এই তত্ত্ব গণতান্ত্রিক এবং সকল মানুষের সমানাধিকারের সমর্থক। কিন্তু বিবর্তনের মাধ্যমে অসংখ্য বিশেষায়িত বর্তনী তৈরী হয়েছে ভেবে নিলে গণতন্ত্র ব্যহত হবে। কারণ সেক্ষেত্রে জন্মসূত্রেই একেকজন একেক ধরণের বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মাবে। এ ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। কারণ এই বিশেষায়িত বর্তনীগুলো সব মানুষের মধ্যে সমানভাবে উপস্থিত। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান যেসব বিশেষায়িত বর্তনীর কথা বলে সেগুলোর সংজ্ঞাই হচ্ছে, একটি প্রজাতির সকল জীবের মধ্যে সমানভাবে উপস্থিত তথা তথা সর্বজনীন বর্তনী। সুতরাং গণতন্ত্র বা মানবাধিকার ব্যহত হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। এমনকি এটা মানবাধিকারের সহায়ক। কারণ বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে আমরা জোড়ালোভাবে ঘোষণা করতে পারি যে পৃথিবীতে বংশ-গোত্র-বর্ণ বা ধর্মে কোন ভেদাভেদ নেই।
সহজাত বনাম অর্জিত বিতর্কও অর্থহীন
বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সহজাত এবং অর্জিত গুণাবলি নিয়ে তর্ক করা অর্থহীন। কারণ যেকোন কিছু অর্জন করা বা শেখার জন্য একটি বিশেষায়িত প্রক্রিয়া বা কৌশল প্রয়োজন। তিন পাউন্ড ময়দা কোনকিছু শিখতে পারে না, অথচ তিন পাউন্ড মস্তিষ্ক অনেক কিছু শিখতে পারে। কারণ মস্তিষ্কে শেখার জন্য কিছু কৌশল আছে। এই কৌশলগুলো অবশ্যই মানুষ কোনভাবে অর্জন করেনি বরং বিবর্তনের মাধ্যমে এটা তার মধ্যে তৈরী হয়েছে। এটাকে আমরা বলতে পারি “সহজাত অর্জন কৌশল” বা “শিক্ষাগত স্বজ্ঞা”। এই স্বজ্ঞা না থাকলে আমরা কোনকিছুই শিখতে পারতাম না। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান এসব স্বজ্ঞা নিয়ে কাজ করে, সামাজিক শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে তার কোন আগ্রহ নেই। সমাজ-সাংস্কৃতিক অর্জন যেহেতু বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের ডোমেইনের বাইরে সুতরাং এর সাথে সহজাত স্বজ্ঞার ঠোকাঠুকি অপ্রাসঙ্গিক।
বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান কি নয়?
বেশ কিছু ভুল ধারণার অপনোদন করা হয়েছে। ভুল ধারণা পোষণ এবং পরবর্তীতে সেগুলো সংশোধনের মাধ্যমেই আমরা বুঝতে পারি বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান কি নিয়ে কাজ করে এবং কি নিয়ে কাজ করে না। প্রথমত, এটা প্রমিত সমাজবিজ্ঞান মডেলের একেবারে বিপরীত। প্রমিত মডেলে যেখানে মস্তিষ্ককে গুটিকতক জেনারেল পার্পাস এবং কন্টেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট কৌশলের সমষ্টি হিসেবে বিবেচনা করা হয় সেখানে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানে তাকে ধরে নেয়া হয় অসংখ্য বিশেষায়িত বর্তনীর সমন্বয়ে গঠিত কর্মক্ষম যন্ত্র হিসেবে। দ্বিতীয়ত, এর সাথে মানব স্বভাবের বিবর্তন গবেষণার সম্পর্ক নেই। স্বভাব নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ধরে নেয়া হয়, নির্দিষ্ট প্রাতিবেশিক আবেদনে সাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে ফিটনেস-ম্যাক্সিমাইজেশন বলে একটা ব্যাপার আছে যা নির্ধারণ করে কিছু জেনারেল পার্পাস কৌশল।
যুক্তিগত স্বজ্ঞা নিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা
ইতিমধ্যে দুই ধরণের স্বজ্ঞার কথা বলা হয়েছে যেগুলোকে আগে পরিবেশ প্রভাবিত অর্জন বলে ধরে নেয়া হতো। স্বজ্ঞা দুটি হচ্ছে: যুক্তিগত স্বজ্ঞা (reasoning instincts) এবং শিক্ষাগত স্বজ্ঞা (learning instincts)। মানুষ যুক্তি এবং শিক্ষা দ্বারা চালিত হয় এটা সত্যি, কিন্তু এই যুক্তি এবং শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে অসংখ্য জটিল জটিল স্বজ্ঞার সমন্বিত পরীশ্রমের ফল। এটিই বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানকেন্দ্রিক গবেষণার মূল বিষয়। কসমাইডস এবং টুবি তাদের প্রাইমারে যুক্তিগত স্বজ্ঞা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন, এসব স্বজ্ঞা যে বিবর্তনের ফলে অভিযোজিত বিভিন্ন কৌশলের ওপর নির্ভর করে সেটা প্রমাণ করেছেন। প্রমাণ করতে গিয়ে তারা কিছু খাতা-কলমভিত্তিক পরীক্ষণের আশ্রয় নিয়েছেন। অনেক মানুষের ওপর পরীক্ষাটি করে প্রায় একই ধরণের ফল পাওয়া গেছে।
মানুষ অনেক কাজেই যুক্তি ব্যবহার করে। কসমাইডস ও টুবি প্রথমেই “সামাজিক লেনদেন” কে বেছে নিয়েছেন। কারণ এই কাজটিই মানুষ সবচেয়ে বেশি করে এবং এর ওপর বিবর্তনের প্রভাব অনেক বেশি। মানুষের প্রায় সব লেনদেনই শর্তসাপেক্ষ। নিঃশর্ত দানের প্রবণতা খুব বেশি দেখা যায় না। সেবিকার সেবা নিঃশর্ত, দাতার দান নিঃশর্ত কিন্তু সমাজে ব্যতিক্রম, অধিকাংশ লেনদেনই শর্তসাপেক্ষ। মানুষ মূলত দুই ধরণের লেনদেন করে- সাহায্য বা ক্ষতি। তার সব লেনদেনই হয় কাউকে সাহায্য করার জন্য নয়তো কারও ক্ষতি করার জন্য। এগুলো শর্তাধীন- শর্তাধীন সাহায্য এবং শর্তাধীন ক্ষতিগুলোকে বিবর্তনের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কসমাইডস এ টুবি এ নিয়েই গবেষণা করছেন। তারা প্রাইমারে সামাজিক লেনদেনে যুক্তিগত স্বজ্ঞার ব্যবহার নিয়ে করা একটি পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন।
প্রতারক খুঁজে বের করা
সামাজিক লেনদেন নিয়ে অর্থনীতিবিদরা ইতিমধ্যেই অনেক গবেষণা করেছেন। বানিজ্য নিয়ে তাদের মতবাদের সাথে বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানীদের সামাজিক লেনদেন বিষয়ক মতবাদের মিল আছে। “গেম থিওরি” এবং “প্রিজনার্স ডিলেমা” জাতীয় তত্ত্ব বর্তমানে অনেকটাই বিকশিত। এগুলোর মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি, নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রতারকদের চিহ্নিত করতে না পারলে কোন সমাজে সামাজিক লেনদেনের বিকাশ ঘটে না। সমাজের মানুষের মধ্যে যেসব বৌদ্ধিক যন্ত্র আছে তা দিয়ে যতদিন না স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতারক খুঁজে বের করার কোন উপায় বাতলানো যাচ্ছে ততদিন সমাজটি আঁধারেই থেকে যাবে, কারণ প্রতারকদের সমাজ থেকে বিতাড়ন না করলে তাদের ভিত মজবুত হতে পারে না। বিভিন্ন গবেষণাপত্রে প্রতারক বলতে এমন সব ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যারা সমাজের দেয়া সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে কিন্তু এর বিনিময়ে নির্ধারিত শর্ত বা দায়িত্বগুলো পালন করে না।
প্রস্তর যুগের শিকারী-সংগ্রাহক পূর্বপুরুষদের মধ্যে এই গুণটি থাকা আবশ্যক ছিল। তাই ধরে নেয়া যায় প্রতারকদের চিহ্নিত করার জন্য মানুষের মস্তিষ্কে একটি বিশেষায়িত বর্তনী আছে যা অবশ্যই অভিযোজনের মাধ্যমে বিবর্তিত হয়েছে। এটি একটি প্রকল্প মাত্র যা “ওয়াসন সিলেকশন টাস্ক” প্যারাডাইমের মাধ্যমে প্রমাণ করা যায়। এই প্যারাডাইমে মানুষকে মোডাস পনেন্স নীতি কোথায় লংঘিত হয়েছে তা ধরতে বলা হয়। ক হলে খ হবে- এই নীতি কোথায় লংঘিত হয়েছে সে প্রশ্ন অনেক ব্যক্তিকে করা হয় এবং তাদের শতকরা কতভাগ কোন ধরণের উত্তর দেয় সেটা লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়।
লিডা কসমাইডস ও জন টুবি কেমব্রিজ শহরকে কেন্দ্র করে এমন একটি পরীক্ষা চালিয়েছেন: ধরা যাক কেমব্রিজ শহর কর্তৃপক্ষ আমাকে শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থার ডেমোগ্রাফিক্স গবেষণার দায়িত্ব দিল। কেমব্রিজের পার্শ্ববর্তী দুটি শহর হচ্ছে বস্টন ও আর্লিংটন। আমি পূর্বতন রেকর্ড ঘেটে দেখলাম, কেউ কেমব্রিজ থেকে বস্টন গেলে, সাবওয়ে দিয়ে যায়।

উপরের কার্ডগুলোতে কেমব্রিজবাসীদের সম্পর্কে দুটি তথ্য আছে। কার্ডের এক পাশে লেখা আছে সে কোথায় গেছে, আরেক পাশে লেখা আছে কিভাবে গেছে। আমরা জানি কেমব্রিজবাসীরা বস্টনে গেলে সাবওয়ে দিয়ে যায়। এখন এই কার্ডগুলোতে কোন নিয়ম ভাঙা হয়েছে কি-না তা বুঝতে হলে কোন একটি বা দুটি কার্ড উল্টিয়ে দেখতে হবে। যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, সাবওয়ে দিয়ে বস্টনে না গেলেই নিয়ম ভঙ্গ হবে। তাই যুক্তি বলে নিয়ম লংঘন ধরার জন্য বস্টন কার্ড উল্টিয়ে দেখতে হবে অন্য পাশে সাবওয়ে আছে কি-না, এবং ক্যাব কার্ড উল্টিয়ে দেখতে হবে অন্য পাশে বস্টন আছে কি-না। মোটকথা ক হলে খ হয়- এমন যুক্তির ক্ষেত্রে ক হয়েছে কিন্তু খ হয়নি এটাই খুঁজতে হবে।
মানুষের মস্তিষ্ক যদি যুক্তি প্রমাণের এই সাধারণ নিয়ম মেনে চলত তাহলে এমনটাই হতো। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় শতকরা ২৫ ভাগেরও কম ব্যক্তি এই কাজ করে। বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়ার পরও এই হার খুব একটা বাড়ে না। এমনকি ক-খ এর জায়গায় প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা বসালেও মানুষ একই ভুল করে। কারণ তাদের স্বজ্ঞা এমনটি করার জন্য প্রস্তুত নয়। বিভিন্ন শর্তাধীন সামাজিক লেনদেন দিয়ে এই প্রকল্প পরীক্ষা করার পরই আমরা বিস্মিত হয়েছি। যখনই ক এবং খ এর স্থলে প্রতারণা বিষয়ক কোন লেনদেন বসানো হয় তখনই মানুষের কর্মদক্ষতা অস্বভাবিকরকম বেড়ে যায়। প্রতারণা বিষয়ক মোডাস পনেন্স এমন হতে পারে: যদি এই আইসক্রিম খাও তাহলে তোমাকে নিজের মশারি নিজে টানাতে হবে। মোটকথা, যখনই সমস্যাটা এমন হয়- যদি “ক” সুবিধাটি গ্রহণ কর তাহলে তোমাকে অবশ্যই “খ” দায়িত্বটি পালন করতে হবে- তখনই মানুষের সঠিক কার্ড উল্টানের প্রবণতা অস্বাভাবিকরকম বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে সঠিক কার্ড উল্টানো ব্যক্তির সংখ্যা শতকরা ৬৫-৮০ ভাগ হয়ে থাকে, অথচ অন্য কোন পরীক্ষায় ফলাফল এর ধারেকাছেও আসে না। এ ধরণের পরীক্ষায় প্রায় সবাই সফল হয়, অর্থাৎ “সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছে” (আইসক্রিম) এবং “দায়িত্ব পালন করা হয়নি” (মশারি)- এই কার্ড দুটি উল্টায়।
এতেই অনেকাংশে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের মস্তিষ্কে প্রতারণা সংশ্লিষ্ট সমস্যা দ্রুত সমাধান করার জন্য এক ধরণের বিশেষায়িত স্নায়বিক বর্তনী আছে। পরীক্ষাগুলোতে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে, অর্থাৎ কার্ড দেখানোর সাথে সাথেই উল্টাতে বলা হয়েছে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, প্রতারণা টের পেলে মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবেই সক্রিয় হয়ে ওঠে যা বিশেষায়িত বর্তনীর প্রমাণ। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, হংকং-এর সাধারণ মানুষ, ইকুয়েডরের স্কুলছাত্র কিংবা ইকুয়েডরীয় আমাজনের আদিবাসী যাদের মধ্যেই এ ধরণের পরীক্ষা করা হয়েছে তারাই এ ধরণের ফলাফল দিয়েছে, প্রতারণা দেখলেই নড়েচড়ে বসেছে।
মানুষের এই প্রতারণা সনাক্তকরণ যন্ত্র এতই সক্রিয় যে সে কখনও কখনও এমন কাজ করে বসে যেটা যৌক্তিক দিক দিয়ে ভুল হলেও প্রতারক চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর। উদাহণ হিসেবে মোডাস টলেন্স এর কথা উল্লেখ করা যায়। আইসক্রিম-মশারি সমস্যাটা ছিল মোডাস পনেন্স। এটা উল্টিয়ে যদি এমন রা হয়: মশারি (খ) টানালে, তুমি আইসক্রিম (ক) খেতে পারবে, তাহলে যুক্তি অনুসারে কার্ড উল্টানোও উল্টে যাওয়ার কথা। বস্টন-সাবওয়ে সমস্যার নিয়ম অনুসারে এক্ষেত্রে “মশারি টানিয়েছে” এবং “আইসক্রিম খায়নি” কার্ড দুটো উল্টানোর কথা। নিয়মের লংঘন বুঝতে হলে এমনটিই করতে হবে। কিন্তু এমনটি করলে প্রতারক ধরা যাবে না। কারণ মশারি টানিয়েছে কার্ড উল্টিয়ে যদি দেখি আইসক্রিম খায়নি তবে বুঝে যাব নিয়ম লংঘিত হয়েছে, কিন্তু প্রতারক ধরা যাবে না। কারণ এটা প্রতারণা না। সে দায়িত্ব পালন করেছে এবং সুবিধাও নেয়নি, এটা বরং পরার্থপরতা। এজন্যই অধিকাংশ মানুষ স্বজ্ঞার তাড়নায় এই সমস্যার ক্ষেত্রেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে “মশারি টানায়নি” এবং “আইসক্রিম খেয়েছে” কার্ড দুটো উল্টায়। কারণ এভাবেই সহজে প্রতারক ধরা যায়।

উপরের ছবিতে পরীক্ষাগুলোর সারাংশ টানা হয়েছে। চারটি কার্ডে এবার বস্টন-সাবওয়ের বদলে সামাজিক লেনদেনে প্রতারণার শর্ত বসানো হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে অধিকাংশ ব্যক্তি “ক” এবং “খ নয়” কার্ড দুটি উল্টায় এবং এটাই যৌক্তিক। উল্টো ক্ষেত্রে যুক্তি অনুসারে “ক” এবং “খ নয়” কার্ড দুটি উল্টানোর কথা। কিন্তু স্বজ্ঞানুরাগী মানুষ এবারও “খ” এবং “ক নয়” কার্ড দুটি উল্টায়।
*****
সামাজিক লেনদেন বিষয়ক সমস্যায় যুক্তিগত স্বজ্ঞার ব্যবহার নিয়ে গবেষণার মাধ্যমেই কসমাইডস এবং টুবি “সামাজিক চুক্তি এলগরিদম” (Social contract algorithm) প্রতিষ্ঠা করেছেন। ওয়াসন সিলেকশন টাস্কের বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে সব ধরণের সামাজিক লেনদেন নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মাধ্যমেই ডিজাইন এভিডেন্স তথা ফর্ম এবং ফাংশনের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা গেছে। তাই বর্তমানে অনেক মনোবিজ্ঞানীই মনে করেন, মানুষের সামাজিক লেনদেন বিষয়ক যুক্তিগত স্বজ্ঞা অনেকগুলো জটিল এবং বিশেষায়িত স্নায়বিক বর্তনী বা কৌশলের সমন্বয়ে গঠিত। ডিজাইন এভিডেন্স নিয়ে বিজ্ঞানীরা আশাবাদী। কারণ ইতিমধ্যেই মস্তিষ্কের এই অংশের এলগরিদম তৈরী করে ফেলা হচ্ছে। একজন প্রকৌশলী এটা করলে যেখানে যা বসাতো মস্তিষ্কেও হয়ত তেমন কিছু বিন্যাস আছে যা ভবিষ্যৎ গবেষণার দুয়ার খুলে দেবে।
প্রতারণার মত এমন আবেগী একটা বিষয়ে এহেন কঠোর যুক্তি আরোপ দেখে অনেকেই মর্মাহত বা বিস্মিত হতে পারেন। কিন্তু বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা তাদের অবস্থান পরিবর্তনের কোন কারণ দেখেন না। আসলে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানে “আবেগ” এবং “বুদ্ধি”-র মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই, সবই স্বজ্ঞার জটিল ক্রিয়ার ফসল। অভিযোজনবাদী তত্ত্বের মাধ্যমেও আবেগের ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব: মস্তিষ্কের বৌদ্ধিক তন্ত্রে অনেক ধরণের বিশেষায়িত বর্তনী আছে যারা পৃথক পৃথক কাজ করে। কিন্তু মানুষকে মানুষ করে তোলার জন্য এই বর্তনী বা কৌশলগুলোর সমন্বয় আবশ্যক। এমন অনেক সমস্যা আছে যেগুলো সমাধানের জন্য এদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং পারস্পরিক সহযোগিতা আবশ্যক। আবেগকে এমন একটি “মোড অভ অপারেশন” বলা যায় যে এই সহাবস্থান ও সহযোগিতা নিশ্চিত করে। অবশ্য মিথস্ক্রিয়াজনিত সকল মোড অভ অপারেশনকেই আবেগ বলা ভুল হবে, বরং বলা উচিত যেসব মিথস্ক্রিয়ায় ঝামেলা বাঁধলে মানুষকে অনেক মূল্য দিতে হয় সেগুলোর ক্ষেত্রেই আবেগ কাজ করে। আবেগ সে হিসেবে সবচেয়ে সূক্ষ্ণ বৌদ্ধিক অপারেশন। অস্তিত্ববাদী সাহিত্যিক জঁ পল সার্ত্র বলেছিলেন, “মানুষ হচ্ছে এক ঝুলি অপ্রয়োজনীয় আবেগ”। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা এটা মানতে পারেন না, তারা বরং সমর্থন দেন দার্শনিক ও গণিতবিদ পাসকালের কথাকে, “আত্মারও যুক্তি আছে, এমন যুক্তি যা স্বয়ং যুক্তিও জানে না।” একালের বিখ্যাত চলচ্চিত্র সমালোচক রজার ইবার্টের লেখাতেও এ কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায়, “তোমার বুদ্ধি অনিশ্চয়তায় ভুগতে পারে, কিন্তু আবেগ কখনও তোমাকে মিথ্যে বলবে না।”
আবেগ সহ মানব মস্তিষ্কের সব বিষয়ে তথা গোটা মানব স্বত্ত্বাকে ব্যবচ্ছেদ করার কাজ শুরু করেছে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান। তবে এখনও তার অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। ডেভিড জে বুলার মনোবিজ্ঞানের এই নতুন এপ্রোচটিকে “পপ এভল্যুশনারি সাইকোলজি” (জনপ্রিয় বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান) নামে আখ্যায়িত করে তার মৌলিক পাঁচটি হেত্বাভাস ধরিয়ে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে আসলে মৌলিক পাঁচ সূত্রের পাঁচটিকেই আরও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে বলেছেন। তারপরও বলা যায় এই নববিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কারণ এর মাধ্যমে গর্ভাবস্থায় অসুস্থতা, নৈসর্গ্যিক চেতনা যার মাধ্যমে আমরা প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হই, সামষ্টিক আগ্রাসন, অজাচার এড়িয়ে চলা, বিরক্তি, খাদ্য সন্ধান এবং এরকম অসংখ্য কাজের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব। ভবিষ্যতে মনের জগতে মানুষের আগ্রাসন চলতেই থাকবে, যতোই অপ্রীতিকর হোক না কেন ব্যাপারটা।
[সমাপ্ত]
<< প্রথম পর্ব | দ্বিতীয় পর্ব

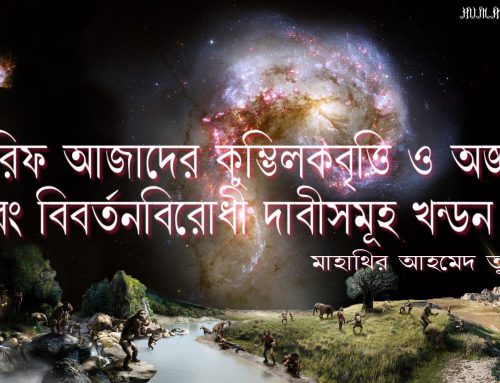

শিক্ষানবিস,
এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ! এটা দিয়ে আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে। আসলে তোমার এই পর্বটা খুবই কাজের, এখানে যে ভুল ধারণাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছো সেটা থেকে অনেকেই এ বিষয়ে তাদের ভুল ধারণাগুলো শুধরে নিতে পারবেন। আর একেবারে শুধুরে না গেলেও, কি বিষয়ে সন্দেহ বা ভুল ধারণা আছে সেটা অন্ততভাবে বোঝা যাবে।
এবার আসি আসল কথায়, এই বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান নিয়ে অনেক হাসাহাসি করেছি, মনে হয় এ প্রসঙ্গে আমার অবস্থানটা পরিষ্কার করা প্রয়োজন।
আমার মতে এটা একটা খুবই নতুন শাখা এবং অনেক কিছুই এখনও প্রমাণিত নয়। আমি একদিকে যেমন সামাজবিজ্ঞানীদের ( সবাই নয়) ব্ল্যংক স্লেট মার্কা মনোভাবের বিরোধী তেমনি আবার মনে করি শুধু বিশুদ্ধ বিজ্ঞান দিয়েও (সব বিজ্ঞানী যে এটা বলছে তা বলছি না) মানব মন এবং তার যৌক্তিক স্বত্তাকে ব্যখ্যা করা যাবে না। এটা একটা জটিল বিষয় তুমি ঠিকই বলেছো,
তবে, আমার মতে, শুধু ‘জটিল স্নায়বিক বর্তনীর জটিল যোগসাজোশ’ ই নয়, এর সাথে পরিবেশ, মানুষের অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক শিক্ষালব্ধ জ্ঞান এবং তার প্রভাবকেও যোগ করতে হবে। এর কোনটা,কতখানি, কার উপর প্রভাব ফেলছে এটা না জেনে সিদ্ধান্ত নেওইয়াটা বোধ হয় কঠিন। তুমি আবার লেখার এক জায়গায় বলেছ,
…
এ বিষয়টা নিয়েই আমি এখনও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারিনা ( আমি পারলাম কি পারলাম না তা তে অবশ্যই কিছু এসে যায় নাঃ), আমার ভুল হতে পারে, তবে এখনো মনে হয়, বিবর্তনীয় কারণগুলোর সাথে মানুষের উপর চেতনাতে সমাজ-সাংস্কৃতিক একটা প্রভাব থেকেই যায়।
তোমার আগের পর্বে কাউকে ভালো লাগার প্রসংগ এসেছে। আমরা এই ‘ভালো লাগাটা’কে এতদিন পর্যন্ত ‘বিমূর্ত মন’ দিয়ে বিচার করে এসেছি। কিন্তু এটা তো আসলে যৌন নির্বাচন (sexual selection) এরই অংশ। এক্ষেত্রে অবশ্যই বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। এর পিছনে যে আসলে একটা প্রজাতির টিকে থাকার বিষয়টা নির্ভর করতে পারে তা বিবর্তনীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে না বিচার করলে কিন্তু হিসেবে একটা বিশাল বড় ফাঁক রয়ে যাবে। এখন আবার ধর,মানুষের ক্ষেত্রে এই ধরণের সরলীকরণ ( শুধুমাত্র বিবর্তন দিয়ে হিসেব করা) সবসময় খাটে কিনা সেটাও ভেবে দেখতে হবে। এতদিন মানব সমাজে বিপরীত লিঙ্গের একজন আরেকজনকে পছন্দ করা মানে ছিল যে ( যদি সেই সময়কার সমাজে সেটা গ্রহণযোগ্য হয়, অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, অনেক সমাজেই তুমি পছন্দ করলেই বিয়ে করতে বা একসাথে থাকতে পারবে তার গ্যারান্টি নেই) তারা বংশবৃদ্ধি করবে এবং ভবিষ্যতের প্রজন্মে কতখানি উপযুক্ত জিন রেখে যেতে সক্ষম হবে। সেক্ষেত্রে তারা কিভাবে এবং কি ধরণের সঙ্গী নির্বাচন করছে তার উপর তাদের প্রজাতির টিকে থাকা নির্ভর করবে, যেটা এখনো বেশীরভাগ প্রাণীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু মানুষের সভ্যতা যতই এগুচ্ছে ততই এই বংশবৃদ্ধির ব্যাপারটা কিন্তু ভিন্ন রূপ ধারণ করছে। এখনকার বেশীরভাগ উন্নত দেশেই জনসংখ্যার হার নেগেটিভে চলে গেছে, অনেক দম্পতিই আছে যারা কোন বাচ্চাকাচ্চাই হওয়ায় না। তাহলে এখানে প্রশ্ন চলে আসবে তাদের সঙ্গী নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান কিভাবে কাজ করবে, এখানে তো মানুষ পরিবেশগত বা শিক্ষাগত কারণে তার নিজের বিবর্তনের বিরুদ্ধেই কাজ করছে। এরকম আরও উদাহরণ দেওয়া যায়, তবে সময় নেই বলে আজকে আর বেশী কথা বাড়াচ্ছি না।
আমাদের দেশে বাংলায় এখনই এধরণের বিষয় নিয়ে বই বের করাতেও আমার কিছু আপত্তি আছে। আমাদের দেশে যেখানে মানুষের বিবর্তন নিয়েই বিন্দুমাত্র ধারণা নেই, সেখানে এরকম একটা নবীন এবং স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে এখনই বাংলায় বই বের করাটা আমার কাছে সঠিক মনে হয় না। মনে হয় এতে করে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা বাড়ে। যেমন ধর, অন্যান্য অনেক দেশেই একটা বই বের হলে তার পিয়ার রিভিউ হয়, পাল্টা বক্তব্য নিয়ে আলোচনা হয়, ভুল থাকলে তা ধরিয়ে দেওয়া হয়, আবার নতুন তথ্যের ভিত্তিতে তা আবার সংশোধনও করে নেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের দেশে তা হয় না, এসব নিয়ে আলোচনা হয় না, খুব বেশী হলে কিছু গালাগালি হবে তারপর বইটা ওই রকমভাবেই থেকে যাবে। তাহলে এখন প্রশ্ন দাঁড়াবে, বিজ্ঞানের ‘কাটিং এজ’ ব্যাপারগুলো নিয়ে বাংলায় বই লেখা হবে (এমনিতেই হয় না, সে আলোচনায় না হয় নাই বা গেলাম) না? হ্যা অবশ্যই হবে, কিন্তু আমার কাছে এ বিষয়টা এখনও সেখানে পৌঁছেছে বলে মনে হয় না। কিন্তু এটা একান্তই আমার নিজস্ব মতামত। যারা এই বিষয় নিয়ে বই লিখতে চায়, তারা লিখুক, আমার বলা না বলায় কি বা এসে যাবে ঃ)।
তোমার পুরা লেখাটা থেকে কিন্তু একটা কথা আমার মাথায় আটকে গেল, সেটার কথা না বলে আমার মন্তব্যটা শেষ করা যাচ্ছে না ঃ)
দারুণ একটা উক্তি!!! আমি আসলেই যেন তিন পাউন্ডের এক দলা ময়াদা আর সেই পরিমাণ বড় একটা মস্তিষ্ক পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি। কথাটা কি অনুবাদ করলা নাকি তোমার ‘তিন পাউন্ড মস্তিষ্ক’ থেকে বেরুলো। তবে যেখান থেকেই বের হোক না কেন, কথাটা কিন্তু চমৎকার 🙂
লেখাটার জন্য ধন্যবাদ, তোমার বাজে কথা শুনতে শুনতেই শেষ পর্যন্ত এটা নিয়ে কিছুটা হলেও পড়তে এবং চিন্তা করতে বাধ্য হলাম। তবে আমার করা মন্তব্যগুলা পড়ে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের লোকজন ( এই ব্লগে তো আবার তারা সং খ্যার অনেক ভারী) যে কি ধরণের গালি দিবে সেটা ভেবেই এখন ভয় লাগছে।
চমৎকার বিশ্লেষণ বন্যা আপা। এতোদিনে পরিষ্কার করলেন আপনার স্ট্যান্ডটা। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানে অনেক সংশয় আছে এখনও। আমি শেষ প্যারায় একটু উল্লেখ করছি কেবল:
এটা নিয়ে আরও ডিটেল লেখা দরকার। সীমাবদ্ধতাগুলো নিয়ে অভিজিৎদা আরও লিখবেন আশাকরি।
এই সিরিজের দ্বিতীয় পর্বে আপনার মন্তব্যের জবাবে উল্টাপাল্টা কথা বলছি অনেক। সরি……….
এখানে আমার একটু কথা আছে। স্নায়বিক বর্তনীর সাথে পরিবেশের প্রভাব যোগ করার কথা বলেছেন। এটা সম্পূর্ণ যৌক্তিকই মনে হচ্ছে। কিন্তু যদ্দূর মনে হয় বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান চাইলেও এটা করতে পারবে না, অন্তত তাদের বর্তমান স্ট্যান্ড দেখে তাই বোঝা যাচ্ছে। এখানে লিডা ও কসমাইডস কিন্তু পরিবেশের প্রভাব অস্বীকার করেননি, বরং বলেছেন পরিবেশের প্রভাব বিষয়ক গবেষণা বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের ডোমেইনের বাইরে, সেটা অন্য কোথাও আলোচনা করতে হবে। বিবর্তন যতটুকু তৈরি করেছে কেবল সেটুকু নিয়েই বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান কাজ করবে মনে হচ্ছে। তবে এভাবে কাজ করলে অনেককিছুর ব্যাখ্যাই একপাক্ষিক এবং অসম্পূর্ণ হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আরও এক বা একাধিক শাখার সহায়তার প্রয়োজন হবে ব্যাখ্যটাকে পূর্ণতা দিতে।
তবে যৌন নির্বাচন নিয়ে আপনি যে উদাহরণ দিলেন সেটা খুবই যৌক্তিক মনে হচ্ছে। মানুষ আধুনিক সমাজের প্রেক্ষাপটে এমন অনেক কিছুই করছে যা ঠিক বিবর্তনীয় ধারায় পড়ে না। এক্ষেত্রে মনে হয় মানুষের দার্শনিক ও নৈতিক প্রগতি এবং অভিযোজন করার অস্বাভাবিক ক্ষমতা কাজে দিয়েছে। এগুলো নিয়ে আরও আলোচনার মাধ্যমে নিশ্চয়ই বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান আরও সূক্ষ্ণ হবে ভবিষ্যতে।
বাংলায় এ নিয়ে এখনই বই লেখার ব্যাপারে আপনার কথায় যুক্তি আছে। অভিজিৎদা কি বলে দেখি। বই লেখার সিদ্ধান্ত কিন্তু আমার না। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান নিয়ে আলাদা বই লেখার সিদ্ধান্ত অভিজিৎদার…
তিন পাউন্ডের উপমাটা আমার মাথা থেকে আসে নাই, এটা হুবহু অনুবাদ লিডা কসমাইডস এর প্রাইমার থেকে। আসলে প্রাইমারের হুবহু অনুকরণেই এটা লেখা তবে বেশ খানিকটা সংক্ষেপিত। তিন পাউন্ডের এই উপমাটা আমারও খুব ভাল লাগছিলো।
আপনার বলা কথাগুলা বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের লোকজন খুব ভালভাবেই নিবে বলে আমার ধারণা। আর এখানে কিন্তু আমি একেবারেই কোন বাজে কথা বলি নাই। আবারও সরি আগে বাজে কথা বলার জন্য… 🙂