লিখেছেনঃ সুজন বড়ুয়া(qb sujon)
শূন্যতা শব্দটি শুনলেই আমাদের মনে এক ধরনের ভয়, দ্বিধা বা অস্তিত্বহীনতার অনুভব জেগে ওঠে। অথচ এই একই শূন্যতা দর্শনের পরিসরে কখনো আশ্রয়, কখনো মুক্তি, আবার কখনো এক ধরণের অস্তিত্ব-নাকচের কাব্যিক অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে। এই প্রবন্ধটি সেই শূন্যতার দুই ভিন্ন ব্যাখ্যার দিকে দৃষ্টি দেয়, পাশ্চাত্যের নিহিলিজম এবং প্রাচ্যের বৌদ্ধ নির্বাণ। একদিকে আছে ‘সবই অর্থহীন’ বলে ঘোষণা দেওয়া এক ধ্বংসচিন্তা, অন্যদিকে আছে ‘সবই অনিত্য, অনাত্মা’, এই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে তৃষ্ণামুক্তি ও মুক্তির প্রতিশ্রুতি। কিন্তু এ দুটির মাঝে পার্থক্য কি কেবল ভাষার, নাকি দৃষ্টিভঙ্গির? কিংবা এই দুইয়ের মধ্যে কোনো গভীর গোপন আত্মীয়তা আছে কি? লেখাটি ঠিক সেই দ্বিধা ও গভীরতায় পাঠককে আমন্ত্রণ জানায়, নির্বাণ ও নিহিলিজমের অনির্ণেয় সংলাপে।
নির্বাণ ও নিহিলিজম, শব্দ দুটি উচ্চারণেই যেন এক ধরণের রুদ্ধশ্বাস শূন্যতার আভাস মেলে। কিন্তু বাস্তবতা কি এতটা সরল? অথবা বলা ভালো, দর্শন কি কখনো সরল হতে পারে? এই প্রশ্ন নিয়েই আমাদের আজকের বিশ্লেষণ।
নির্বাণ শব্দটি এসেছে পালি ভাষা থেকে, যার সংস্কৃত প্রতিশব্দ ‘निर्वाण’। বৌদ্ধ দর্শনে এর অর্থ এক ধরণের সর্বাঙ্গীন নির্বাপিত অবস্থা, আত্মতৃপ্তি নয়, বরং তৃষ্ণার সম্পূর্ণ অবসান, লোভ-ঘৃণা-মোহের অনুপস্থিতি। অন্যদিকে, পাশ্চাত্য দর্শনে ‘nihilism’ হলো এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নেই, নৈতিকতার কোনো মৌলিক ভিত্তি নেই, এমনকি সত্য বা জ্ঞানও সন্দেহসাপেক্ষ।
এখানে প্রশ্ন ওঠে, এই দুই অবস্থার মাঝে কি কোনো মিল আছে, নাকি বিরাট এক দার্শনিক বিভাজন? কেউ কেউ বলেন, বুদ্ধের নির্বাণ হলো আত্ম-অতিক্রমের চূড়ান্ত পর্যায়, যেখানে নিজস্বতা লুপ্ত হয়, কিন্তু একধরণের শ্রেষ্ঠতর অস্তিত্বে পৌঁছানো যায়। অন্যদিকে, নিহিলিজম হলো আত্ম-ধ্বংসের এক মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা, যেখানে ব্যক্তিত্ব শুধু নিজেই নয়, পুরো বাস্তবতাকেই অর্থহীন মনে করে।
তবে এই কথাগুলো কেবল সংজ্ঞার খেলায় আটকে থাকলে ভুল হবে। বৌদ্ধ দর্শনে ‘অনাত্মবাদ’ বা ‘পুথগল-শূন্যতা’ এমন এক অবস্থান তৈরি করে, যেখানে আত্মা বলে কিছু নেই, বরং ‘পঞ্চস্কন্ধ’ বা পাঁচটি উপাদান মাত্র। এই অনাত্মবাদের ভিত্তিতেই নির্বাণ বোঝা যায়, যেখানে ‘আমি’র মোহ ভেঙে পড়ে। কিন্তু এই আত্মহীনতার দর্শন কি আসলে অস্তিত্বহীনতার অনুমোদন দেয়?
নির্বাণ যদি হয় শূন্যতার উপলব্ধি, তবে নিহিলিজম সেই শূন্যতার ভয়। নির্বাণ যেখানে বলছে, সব কিছু অনিত্য, তাই মুক্তি তৃষ্ণাহীনতায়; সেখানে নিহিলিজম বলছে, সব অনর্থক, তাই আত্মবিনাশ অনিবার্য।
তবে কেউ কেউ বলেন, বুদ্ধ নিজেও ছিলেন এক প্রকার ‘র্যাডিকাল রিয়ালিস্ট’; তিনি ‘সত্য’কে চিরস্থায়ী মানতেন না, আবার পুরোপুরি নাকচও করতেন না। সেইখানে নিহিলিজম আর নির্বাণের মাঝে একটি সূক্ষ্ম রেখা, যা একদিকে টানে অস্তিত্বের অস্বীকারের দিকে, অন্যদিকে টানে নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ চেতনার দিকে।
নির্বাণ এক প্রকার দার্শনিক প্রতিশ্রুতি, তুমি নিজের সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারো। নিহিলিজম হলো সেই প্রতিশ্রুতির অপত্যাজন, তুমি কিছুতেই যেতে পারো না, কারণ যাওয়ার কোনো অর্থ নেই।
আবার, জীবনের প্রশ্নে যখন বলা হয়, “সব অনিত্য, সব দুঃখ, সব অনাত্মা,” তখন এক ধরণের অপার শূন্যতার অনুভূতি জন্ম নেয়। এই শূন্যতা (sunyata) যদি ঠিকভাবে উপলব্ধ হয়, তখন তা সৃষ্টি করে এক ধরণের মৈত্রি, সহানুভূতি এবং দায়িত্ববোধ। আর যদি এই শূন্যতাকে ঠিকভাবে ধরা না যায়, তখন তা রূপ নেয় ঊনতা, বিষণ্নতা এবং অনস্তিত্ববাদে।
এইখানেই নিহিলিজম ও নির্বাণের প্রকৃত ফারাক। নির্বাণ হলো শূন্যতা থেকে দায়বদ্ধতার জন্ম, আর নিহিলিজম হলো শূন্যতা থেকে অবসাদের বিস্তার। একদিকে বুদ্ধ বলছেন, “তুমি কিছু নও, তাই তুমি সব হতে পারো।” অন্যদিকে নিহিলিস্ট বলছে, “তুমি কিছু নও, এবং তাই কিছুই হতে পারবে না।”
তাই, প্রশ্ন কেবল দার্শনিক নয়, অস্তিত্বগতও, তুমি কি সেই শূন্যতার মুখোমুখি হতে পারো, যা কিছু না হয়েও সবকিছু ধারণ করে?
জগৎ এক আশ্চর্য নৈঃশব্দ্যের নাট্যমঞ্চ, যেখানে দৃশ্যমান প্রতিটি ঘটনাই একেকটি ভাষাহীন সংলাপ, আর মানুষের মন সেই সংলাপ বোঝার নিরন্তর চেষ্টা। এখানে সত্য বলে কিছু নেই, আছে শুধু ব্যাখ্যার খেলা। এই ব্যাখ্যাকে ঘিরেই গড়ে ওঠে বিশ্বাস, গড়ে ওঠে দর্শন, গড়ে ওঠে জীবন-ব্যবস্থা। অথচ এই ব্যাখ্যার ভেতরেই লুকিয়ে থাকে অসংখ্য অদৃশ্য প্রশ্ন, যা কখনো মুখ ফুটে বলে না: “কেন? কিভাবে? কার জন্য?” এই প্রশ্নগুলোর সামনে দাঁড়িয়েই গড়ে ওঠে নাস্তিকতা, সংশয়বাদ, নির্বাণবাদ, আর তারই প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও চিরন্তন সত্যের দাবি করা দর্শনগুলো।
বৌদ্ধ ধর্ম, এই পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ও সংযত ধর্মব্যবস্থা, একদিকে যেমন আত্মনিবৃত্তি, দয়া ও শূন্যতার মর্মবাণী শোনায়, অন্যদিকে ঠিক তেমনই সে সৃষ্টি করেছে এক গভীর নির্বাণের জগত, যার প্রতিটি স্তম্ভ চিন্তার, ত্যাগের, ও রহস্যময় নৈঃসঙ্গ্যের উপর দাঁড়ানো। একে নির্বাণ বলা যায় কি না, সেটাই প্রশ্ন। কারণ বৌদ্ধ ধর্ম, এক অর্থে, নিরাকারতা ও অনাসক্তির নামে এক বিশাল আধ্যাত্মিক কাঠামো নির্মাণ করেছে, যা নিজেই নিজেকে নাকচ করার মাঝেও টিকে আছে। এই নিজেকে নাকচ করেও টিকে থাকার অবস্থানটাই আসলে নির্বাণবাদের সঙ্গে এক ধরনের গোপন আত্মীয়তার জন্ম দেয়।
নির্বাণবাদ বা Deconstruction, আমাদের শেখায় কিভাবে ভাষা, ধারণা ও প্রতিষ্ঠিত সত্যের ভেতরেই লুকিয়ে থাকে বিপরীতমুখী দ্বন্দ্ব। Derrida-এর ভাষায়, কোনো পাঠই নিরপেক্ষ নয়, কারণ প্রতিটি শব্দের মধ্যে এক ধরনের ভাঙনের সম্ভাবনা লুকানো থাকে। ঠিক এই দৃষ্টিকোণ থেকেই যখন বৌদ্ধ ধর্মের দিকে তাকানো হয়, তখন দেখা যায়, বুদ্ধ নিজে কোনও চূড়ান্ত সত্যের ঘোষণা দেননি, বরং সব ধরনের চূড়ান্ততাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলেছেন। তিনি আত্মার অস্তিত্বকে নাকচ করেছেন, ঈশ্বরের ধারণাকে পাশ কাটিয়ে গেছেন, এমনকি নিজেকেও পরিত্রাতা বলেননি। অথচ সেই ‘নাকচ করা’ বা ‘নিষেধ’ এর মাঝেই গড়ে উঠেছে এক জটিল ধর্মব্যবস্থা, এক বিশাল ত্রিপিটক সাহিত্য, হাজার বছরের ধ্যান ও সাধনার কাঠামো। প্রশ্ন আসে, তাহলে কি বুদ্ধ নিজেই অনিচ্ছাকৃত নির্মাতা? অথবা নির্মাণের বিপক্ষে থেকেও নির্মাণের দিকে ঠেলে দেওয়া এক অসামান্য দার্শনিক?
এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, বৌদ্ধ ধর্ম নিজের অজান্তেই একটি নির্মাণ। এমনকি ‘শূন্যতা’ নামক ধারণাটিও এক ধরনের গূঢ় নির্মাণ; কারণ শূন্যতাও যদি ব্যাখ্যার মাধ্যমে বোঝানো হয়, তবে তা আর শূন্য থাকে না, বরং তা হয়ে ওঠে একটি অর্থপূর্ণ নির্মিত কাঠামো। Derrida যেভাবে বলেন, “différance never arrives fully,” ঠিক তেমনই বৌদ্ধ ধর্মের শূন্যতাও কখনো পুরোপুরি ধরা যায় না, বরং তা ব্যাখ্যার মাধ্যমে ছায়ার মতো সরে যায়।
তবে এখানেই রয়েছে দ্বিধা। Derrida নির্মাণকে ভাঙতে বলেন, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম ভাঙে না, বরং এক নতুন কাঠামো দাঁড় করায়, ধর্মচক্র, সংঘ, সাধনা, নির্বাণ। Derrida ভাষার ঘূর্ণিপাকে ঢুকে পড়েন, আর বুদ্ধ সংজ্ঞার বাইরে বের হয়ে যেতে চান। Derrida প্রশ্ন করেন শব্দের ভেতরের দ্যোতনার সত্যতা, আর বুদ্ধ প্রশ্ন করেন সমস্ত সত্ত্বার স্থায়ীত্বকে। এই দুই প্রশ্নকারী যেন দুটি সমান্তরাল পথ, একটি পশ্চিমা, একটি প্রাচ্য; কিন্তু দুজনেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন এক অসীম অনিশ্চয়তার দিকে।
বৌদ্ধ ধর্ম এখানে নির্মাণবাদী চিন্তার সহযাত্রী হলেও পুরোপুরি নির্মাণ নয়, এমন নয় যে বুদ্ধ Derrida-র মতো ভাষা নিয়ে পরীক্ষা করেছেন বা পাঠের মধ্যে নিহিত শক্তিকে বিশ্লেষণ করেছেন। বুদ্ধ বরং জীবন ও দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করতে করতে এক ধরনের অস্তিত্ববাদী নির্জনতার দিকে হেঁটে গেছেন। Derrida থাকেন পাঠে, বুদ্ধ থাকেন প্রত্যক্ষানুভবে। Derrida খনন করেন পাঠের মধ্যে, বুদ্ধ খনন করেন চৈতন্যের গভীরে। সেইজন্য Derrida যদি হন জটিল বিশ্লেষণের স্থপতি, তবে বুদ্ধ হচ্ছেন অভিজ্ঞতার অন্তঃস্থ আত্মদর্শী।
তবে এখানেই প্রশ্ন আসে, এই যে বুদ্ধ সব ভেঙে দেন, সবকিছু নাকচ করেন, তার মধ্যেও এক ‘রহস্যময় প্রস্থান’ রেখে যান, যা আমাদের আবার টেনে আনে এক নতুন নির্মাণের দিকে। যেমন ধরুন, নির্বাণ, যা সব চাহিদার মুক্তি, সব দুঃখের পরিসমাপ্তি, কিন্তু সেটি কী? ভাষাহীনতা? অনস্তিত্ব? অথচ বুদ্ধ নির্বাণকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে শব্দ ব্যবহার করেছেন, তা-ই তো এক নির্মাণ! Derrida হয়তো বলতেন, “নির্বাণ একটি আপেক্ষিক দ্যোতনা, যাকে আপনি যতই ধরতে যান, তা ততই পিছিয়ে যায়।” Derrida যেমন “presence of absence” এর কথা বলেন, বুদ্ধ তেমনি বলেন, অনিত্য, অনাত্মা। দুই পথেই খোঁজ চলে এমন কিছু যার অস্তিত্বের মধ্যে লুকিয়ে আছে অনুপস্থিতির ধ্বনি।
এই জায়গায় এসে বৌদ্ধ ধর্ম নির্মাণবাদের একটি শান্ত ও স্নিগ্ধ সংস্করণ হয়ে ওঠে। Derrida যেখানে ভাঙেন, প্রশ্ন করেন, কাঠামো সরিয়ে দেন, বুদ্ধ সেখানে ধীরে ধীরে সব মুছে দেন, নিঃশব্দ করে দেন, এবং শেষে কিছুই না বলার মধ্য দিয়েই সর্বোচ্চ কথাটি বলে ফেলেন। Derrida যেখানে পাঠকের হাত ধরে একটি কুয়াশার ভেতর নিয়ে যান, বুদ্ধ সেখানে ধ্যানের মাধ্যমে সেই কুয়াশা সরাতে বলেন। তাই বৌদ্ধ ধর্মে নির্মাণ আছে, কিন্তু তা জোরালো নয়; বরং এক ধরনের নৈঃশব্দ্যময় নির্মাণ, যেখানে পাঠ নেই, শুধু অনুভব আছে।
কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকেই যায়, এই অনুভবও তো শেখাতে হয়, তাও তো এক কাঠামো, এক নির্দিষ্ট পদ্ধতি, এক সামাজিক সন্ন্যাস-প্রথা, এক সমষ্টিগত বৌদ্ধচর্চা। তাহলে কি আমরা নির্মাণ থেকে কখনোই বের হতে পারি না? Derrida যেমন বলেন, “There is nothing outside the text,” তেমন কি বুদ্ধও বলতে চেয়েছেন, “There is nothing outside the suffering”? তাহলে এই সমগ্র ধর্মই কি দুঃখ-নিরপেক্ষ এক নির্মাণ?
এই প্রবন্ধের মূল কৌতূহল এখানেই, আমরা কি নির্মাণ থেকে একেবারে বেরিয়ে আসতে পারি? বৌদ্ধ ধর্ম কি সত্যিই এক নির্মাণবিরোধী দর্শন, নাকি এটি একটি সূক্ষ্ম নির্মাণ, যেটি নিজেকে নাকচ করার মধ্যেই গোপন এক নির্মিত কাঠামো দাঁড় করায়?
এই প্রশ্নের কোনো একক উত্তর নেই। Derrida যেমন এক কথায় কোনো কিছু বলেন না, বুদ্ধও তেমন নীরব থেকে উত্তর দেন। আমরা শুধু তাদের মাঝে সংলাপ খুঁজে পাই, যেটা আমাদের চিন্তাকে আরও বহু জায়গায় নিয়ে যায়। এই প্রশ্নমালা, এই অস্পষ্টতা, এই দ্বিধাই হয়তো সত্যের সবচেয়ে গভীর আকার। Derrida যেমন বলেন, “truth is a movement,” তেমনি বুদ্ধও বলেন, “সব কিছু অনিত্য।” তাই হয়তো সত্য কোনো শেষ গন্তব্য নয়, সত্য এক যাত্রা, এক ধ্বংস এবং গোপনে আবার নতুন নির্মাণ।
বৌদ্ধ ধর্ম তাই এক অদ্ভুত প্যারাডক্স, যেখানে শূন্যতার মধ্যেও শব্দ আছে, নীরবতার মাঝেও পদ্ধতি আছে, আর নাকচ করার মধ্যেই এক অনিবার্য নির্মাণ। Derrida হয়তো হেসে বলতেন, “You deconstructed nothing; you only constructed a subtler frame.” আর বুদ্ধ হয়তো বলতেন, “যা কিছু নির্মাণ, তা-ও অনিত্য। তবে তার মধ্য দিয়েই তুমি ছুঁয়ে যেতে পারো নির্গমন।”
এই লেখার শুরুতে আমি বলেছিলাম জগৎ এক নৈঃশব্দ্যের নাট্যমঞ্চ। এখন বলতে পারি, এই মঞ্চের পেছনে একটি সূক্ষ্ম নির্মাতা আছেন, যিনি নিজেই বলেন, “আমি নেই।”
শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন থেকেই যায়, আমরা কী সত্যিই কোনো “নির্মাণ” এর বাইরে যেতে পারি? আমরা যে দর্শনেরই অনুসারী হই না কেন, তা কি শেষ পর্যন্ত কোনো না কোনো কাঠামো, ভাষা, বা সংস্কৃতির গর্ভেই গঠিত নয়? Derrida যেমন বলেন, “শব্দের বাইরেও কিছু নেই,” ঠিক তেমনি বৌদ্ধ চিন্তা যেন ইঙ্গিত করে, “দুঃখ ছাড়া কিছু নেই,” এবং এই দুঃখের উপলব্ধিই শেষ পর্যন্ত মুক্তির দিকনির্দেশ। তা হলে কি দুঃখই ভাষার সমতুল, আর নির্বাণ সেই ভাষাহীনতার স্বপ্ন?
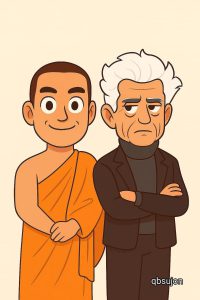
Bah shundor likhechen, amio ekjon nihilist
খুব সুন্দর এবং পরিপাটি লেখার ধরন,