লেখক : প্রীতম চৌধুরী
উৎসর্গ পত্র :
প্রয়াত ড. অভিজিৎ রায়।
বাংলাদেশে হাতে গোনা মুষ্টিমেয় যে সমস্ত লেখকেরা আধুনিক বিজ্ঞানের প্রান্তিক জ্ঞান এবং তথ্যের নিরিখে সুসংবদ্ধ বিশ্লেষণ সাধারণ পাঠকদের দুয়ারে নিত্য পৌঁছে দিচ্ছেন , অভিজিৎ রায় নিঃসন্দেহে ছিলেন তাদের শীর্ষস্থানীয় কাণ্ডারি। বিজ্ঞান এবং দর্শনের জগতে তার অবাধ বিচলন দেখে ইন্টারনেটের বাংলা ব্লগ সাইটগুলোতে তার গুণমুগ্ধ পাঠকেরা তাকে অভিহিত করতেন ‘বাংলাদেশের রিচার্ড ডকিন্স’ অভিধায়। কেউ বা তাকে আখ্যায়িত করতেন ‘শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান লেখক’ (এ পার ওপার দুপার বাংলা মিলিয়েই) হিসেবে । বিজ্ঞানের জটিল অথচ রোমাঞ্চকর বিষয়গুলোকে কথাশিল্পের মনোমুগ্ধকর ভঙ্গিতে প্রকাশ করা সহজ কাজ নয়। অথচ এই কঠিন কাজটি খুব সহজেই নিবিষ্ট মনে করে চলতেন অভিজিৎ রায়। তার অপূর্ব প্রকাশভঙ্গী, আর সহজ সরল সাবলীল অথচ ব্যতিক্রমধর্মী উপস্থাপনা বিজ্ঞানের জটিল ধারণাগুলোকে নিয়ে গিয়েছে সুন্দর এক শৈল্পিক স্তরে – যা তাকে দিয়েছে পাঠকপ্রিয়তা আর সুপরিচিতি।
বিজ্ঞান লেখার পাশাপাশি ড. অভিজিৎ রায়ের আরেকটি পরিচিতি আছে। তিনি বিজ্ঞানমনস্ক, অনুসন্ধিৎসু, সমাজ সচেতন, সত্যসন্ধানে আপোষহীন এবং নির্ভীক। বিজ্ঞান, মানবতাবাদ ও যুক্তিবাদের আলোকে সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তার বহুদিনের। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, বিজ্ঞান বিষয়ে উঁচু ডিগ্রী লাভ আর বিজ্ঞান সচেতনতা সম্পূর্ণভাবে আলাদা দুটো জিনিস। অভিজিৎ রায় প্রচলিত এ বিশ্বাসটি কখনোই মানতে চাননি না যে, ‘বাংলাদেশের শিক্ষার্থী, তরুণ-তরুণী ও সাধারণ মানুষেরা বিজ্ঞানবিমুখ।’ বরং তার অভিমত ছিল, সহজ ও সাবলীলভাবে বিজ্ঞানকে উপস্থাপন করার মতো যথেষ্ট সংখ্যক মেধাবী লোকের উপস্থিতি নেই বলেই আমাদের দেশে বিজ্ঞান সচেতনতার এত অভাব।
মাঝেসাঝে টুকটাক যে লেখা লেখার চেষ্টা করছি তার পেছনের অনুপ্রেরণা ব্যক্তি এই অভিজিৎ রায়। অনেকবারই অনেক আড্ডায় আমি বলেছি “অভিজিৎ দা, আমার গুরু দ্রোণ। ”
যতদূর জানি, অভিজিৎ দার সাম্প্রতিকতম কাজ ছিলো কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন থিওরি নিয়ে। এবারের বইমেলায় তার এ সম্পর্কিত বইও প্রকাশ হয়, ‘শূন্য থেকে মহাবিশ্ব’।
অভিজিৎ দাকে উৎসর্গ করে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন সম্পর্কে কিছু লেখার চেষ্টা করলাম ।
***************************************************
” বেধেছে এমনও ঘর, শূন্যের ওপর পোস্তা করে… ”
মহাবিশ্ব কিভাবে সৃষ্টি হল?- এ প্রশ্নের একটি সাধারণ উত্তর আমাদের সবারই জানা – বিগ ব্যাং নামের এক অভাবনীয় বিস্ফোরণ এর মাধ্যমে।
মূল আলোচনা অর্থাৎ বিগ ব্যাং এর আগে কি ছিল তা শুরু করার আগে CMB সম্পর্কে কিছু বলব। বিগ ব্যাং বিস্ফোরণের পর একটা বিশাল পরিমাণের বিকিরণ ছড়িয়ে পড়ে মহাবিশ্বে। মহাবিশ্বের ক্রম সম্প্রসারণের সাথে সাথে এই বিকিরণের তীব্রতাও ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং এটা এখনও কমছে। একভাবে বলতে গেলে এই বিকিরণকে বলা যায় আমাদের আদিম মহাবিশ্বের ছবি। এই বিকিরণকেই বলা হয় CMB বা Cosmic Microwave Background। ১৯৬৪ সালে বিজ্ঞানী আরনো পেঞ্জিয়াস এবং রবার্ট উইলসন সর্বপ্রথম CMB-র অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। CMB আমাদের মহাবিশ্বের সৃষ্টির প্রথম কিছু মুহূর্তের তথ্য ধারণ করে বলে জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানীদের কাছে তার গুরুত্ব অসীম। যেই অতি ক্ষুদ্র কণা থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টি তাকে বলা হয় ইনফ্লাটন ( Inflaton )। ইনফ্লাটনের প্রাথমিক অবস্থা ছিল অনেক সুবিন্যস্ত আর এই কণা ধারণ করছিলো বিশাল পরিমাণ শক্তি। যদি ইনফ্লাটনকে একটি কোয়ান্টাম কণিকা ধরে নেয়া হয় তাহলে বলা যায় অন্য সব কোয়ান্টাম কণার মত ইনফ্লাটনের ও নিজস্ব কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন ( সহজ ভাবে বলতে গেলে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন বলতে কোন নির্দিষ্ট বিন্দুতে খুব অল্প সময়ের জন্যে শক্তির পরিবর্তন কে বোঝায়। ) আছে যার প্রভাবে মহাবিশ্বের প্রথম সময়গুলোতে স্পেসটাইমের বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে। আর প্রাথমিক পর্যায়ে ইনফ্লাটনের কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন এর মত অতিক্ষুদ্র ঘটনার নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় সৃষ্টি হয় আমাদের আজকের দেখা বস্তুজগত। কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের ফলে CMB ফোটনেরও ( প্রতিটি বিকিরণ মাত্রই ফোটন) তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটে, এই ঘটনাকে বলা হয় CMB Anisotropies Spectrum ( এখানে Anisotropy বলতে বোঝানো হচ্ছে যে এই তাপমাত্রার পরিবর্তন দিকনির্ভরশীল ছিল, অর্থাৎ বিভিন্ন দিকে এই তাপমাত্রার পরিবর্তন সমান ছিল না।) এখন মজার ব্যাপার হল Standard Model অনুযায়ী এই ধরণের পরিবর্তন হওয়ার কথা না। এটাকে আর একটু সহজ ভাবে বলি, ইনফ্লাটনের কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন তখনই সম্ভব যখন ইনফ্লাটনকে আমরা কোয়ান্টাম কণিকা হিসেবে ধরব, Standard Model মহাবিশ্বের এই প্রাথমিক অবস্থাকে কোয়ান্টাম কণা হিসেবে বিবেচনা করে না। এখন দেখার ব্যাপারটি হচ্ছে Standard Model মহাবিশ্বে তাপমাত্রা আর বস্তুকণার পরিমাণের মধ্যে একটা প্রতিসাম্যের কথা বলে কিন্তু সেই প্রতিসাম্য মহাবিশ্বে অনুপস্থিত। এর একটা পার্শ্বিক কারণ হিসেবে CMB Anisotropies Spectrum কে দায়ী করা হয়, যদিও এটা একটা গাণিতিক অনুমান, সত্যি ধরে নেয়া হলে বলা যায় হয়ত ইনফ্লাটন কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনুসরণ করেছে।
শূন্য থেকে কীভাবে মহাবিশ্ব উদ্ভূত হতে পারে সেটা জানতে হলে প্রথমে আমাদের কোয়ান্টাম শূন্যতার ব্যাপারটি বুঝতে হবে। আসলে খুব কম কথায় বললে, কোয়ান্টাম তত্ত্বানুযায়ী শূন্যতাকে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। শূন্যতা মানে আক্ষরিক অর্থে শূন্য নয়- পদার্থ বিজ্ঞানীদের মতে যে শূন্য-দেশকে আপাত: দৃষ্টিতে শান্ত, সমাহিত মনে হচ্ছে, তার সূক্ষ্মস্তরে সবসময়ই নানান প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে। এর মধ্যে নিহিত শক্তি থেকে পদার্থ-কণা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হচ্ছে, আবার তারা নিজেকে সেই শক্তিতে বিলীন করে দিচ্ছে। যেমন, শূন্যাবস্থা থেকে সামান্য সময়ের ঝলকানির মধ্যে ইলেকট্রন এবং পজিট্রন (পদার্থ-প্রতি পদার্থ যুগল) থেকে পদার্থ তৈরি হয়েই আবার তা শূন্যতায় মিলিয়ে যেতে পারে। এই ইলেকট্রন এবং পজিট্রনের মধ্যকার ব্যবধান থাকে ১০^-১০ সেন্টিমিটারেরও কম, এবং পুরো ব্যাপারটার স্থায়িত্বকাল মাত্র ১০^-২১ সেকেন্ড। ব্যাপারটাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে ‘ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশন’।
ভ্যাকুয়াম বলতে আসলে আমরা কি বুঝি? এইটি হল কোন ভৌত ব্যবস্থার সর্বনিম্ন শক্তিস্তর বা এনার্জি স্টেট। চিরায়ত বিবরণে আমরা যদি একটি পাত্র থেকে সবকিছু বের করে ফেলি এবং এর তাপমাত্রা কমিয়ে পরম শুণ্য বা এ্যাবসোলিউট জিরোতে নিয়ে আসি তাহলে আমরা যা পাব তা হল বিশুদ্ধ শুণ্যতা–ভৌত কণিকা বা শক্তিমুক্ত সার্বক্ষণিক শুণ্য সর্বনিম্ন শক্তির একটি অবস্থা বা স্টেট। একটি ক্লাসিক্যাল বা চিরায়ত ছন্দিত স্পন্দক বা হার্মোনিক অসিলেটর পরম শুণ্য তাপমাত্রায় “জমে” যাবে–এর স্পন্দন বা দোলাদুলি যাবে বন্ধ হয়ে। আর সে কারণে এর শক্তির পরিমাণও হবে শুণ্য। অন্যদিকে একটি কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল হার্মোনিক অসিলেটরের শক্তি পরম শুণ্য তাপমাত্রাতেও শুণ্য হবেনা। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়। নন-রিলেটিভিস্টিক কোয়ান্টাম বলবিদ্যাজাত ভ্যাকুয়াম এবং কোয়ান্টাম ক্ষেত্রজাত ভ্যাকুয়াম ঠিক এক জিনিস নয়। এর কারণ হল ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের ফলাফলস্বরূপ শুণ্যতায় প্রতিনিয়ত মৌল-কণিকার সৃষ্টি এবং নাশ হচ্ছে।
আইনস্টাইন তার মহাবিশ্বকে প্রথমে ‘স্থিতিশীল’ একটা রূপ দেয়ার জন্য একটা ধ্রুবক যোগ করেছিলেন, তারপর সেটাকে ‘জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল বলে বাদও দিয়েছিলেন। কিন্তু ছয় দশক পরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এবং গুপ্ত শক্তি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখলেন, আইনস্টাইন আসলে ভুল ছিলেন না।
‘রহস্যময়’ এই শূন্য শক্তি কিংবা ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটি গড়ে উঠেছে হাইজেনবার্গের বিখ্যাত অনিশ্চয়তা তত্ত্বের কাঁধে ভর করে। ১৯২৭ সালে জার্মান পদার্থবিদ ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ গাণিতিকভাবে প্রমাণ করে দেখান যে, কোন বস্তুর অবস্থান এবং ভরবেগ যুগপৎ একসাথে নিশ্চিত ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বস্তুর অবস্থান ঠিক ঠাক মত মাপতে গেলে দেখা যাবে, ভরবেগের তথ্য যাচ্ছে হারিয়ে, আবার ভরবেগ চুলচেরা ভাবে পরিমাপ করতে গেলে বস্তুর অবস্থান অজানাই থেকে যাবে। কাজেই হাইজেনবার্গের এই সূত্র সত্যি হয়ে থাকলে, এমনকি ‘পরম শূন্যে’ও একটি কণার ‘ফ্লাকচুয়েশন’ বজায় থাকার কথা, কারণ কণাটি নিশ্চল হয়ে যাওয়ার অর্থই হবে এর অবস্থান এবং ভরবেগ সম্বন্ধে আমাদেরকে নিশ্চিত তথ্য জানিয়ে দেওয়া, যা প্রকারান্তরে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ত্বের লঙ্ঘন ।কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম হয় নি । ১৯৪৮ সালে ডাচ পদার্থবিদ হেনরিক কাসিমির বলেছিলেন, কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন সত্যি হয়ে থাকলে দুটো ধাতব পাত খুব কাছাকাছি আনা হলে দেখা যাবে তারা একে অন্যকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করেছে। এর কারণ হচ্ছে, ধাতব পাত গুলোর মধ্যকার সঙ্কীর্ণ স্থানটিতে ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের ফলে খুব উচ্চ কম্পাঙ্কের তড়িচ্চুম্বকীয় ‘মোড’-এর উদ্ভব ঘটে যা ধাতব পাতগুলোকে একে অপরের দিকে আকর্ষণে বাধ্য করে। এ ব্যাপারটিই পরবর্তীতে মার্কস স্প্যার্ণে, স্টিভ লেমোরাক্স প্রমুখ বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়।
বিংশ শতকের শুরুর দিক পর্যন্ত মহাবিশ্ব উৎপত্তিতে যে একটি বা বেশ কয়েকটি অলৌকিক ঘটনার প্রয়োজন ছিল তা বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত মানতেন । আমরা জানি মহাবিশ্ব বিপুল পরিমাণ পদার্থ দিয়ে গঠিত। আর পদার্থের ধর্ম হল এর ভর। বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত ধারণা করা হতো, ভরের সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই, এটি শুধু এক রূপ থেকে আরেকরূপে পরিবর্তিত হয়। শক্তির নিত্যতার সূত্রের মতো এটি ভরের নিত্যতার সূত্র । সুতরাং এই বিপুল পরিমাণ ভর দেখে সবাই ধারণা করে নিয়েছিলেন একদম শুরুতে ভর সৃষ্টি হবার মতো অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল, যা সরাসরি ভরের নিত্যতার সূত্রের লঙ্ঘন। এবং এটি ঘটেছিল মাত্র একবারই- মহাবিশ্বের সূচনাকালে ।
কিন্তু না । শক্তির নিত্যতা বা ভরের সূত্রের লংঘন ঘটেনি কখনও ।
শক্তির নিত্যতা সূত্র বা তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র অনুযায়ী আমরা জানি শক্তিকে অন্য কোথাও থেকে আসতে হবে।তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র অনুযায়ী একটি বদ্ধ সিস্টেমে মোট শক্তির পরিমাপ স্থির থাকলেই কেবল শক্তি এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হয়। মজার এবং আসলেই দারুণ মজার ব্যাপার হচ্ছে, মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ শূন্য[ । বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তার ১৯৮৮ এর সর্বাধিক বিক্রিত বই, ‘কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস’ (A Brief History of Time)-এ উল্লেখ করেছেন, যদি এমন একটা মহাবিশ্ব ধরে নেওয়া যায়, যেটা মহাশূন্যে মোটামুটি সমসত্ত্ব, তাহলে দেখানো সম্ভব, যে ঋণাত্মক মহাকর্ষীয় শক্তি এবং ধনাত্মক মহাকর্ষীয় শক্তি ঠিক ঠিক কাটাকাটি যায়। তাই মহাবিশ্বের মোট শক্তি থাকে শূন্য[ । বিশেষ করে, পরিমাপের অতি সূক্ষ্ম বিচ্যুতি ধরে নিলেও, ক্ষুদ্র কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তার মধ্যে, মহাবিশ্বের গড় শক্তির ঘনত্ব ঠিক ততটাই দেখা যায়, যতটা হতো সবকিছু একটা শূন্য শক্তির আদি অবস্থা থেকে শুরু হলে ।
ইনফ্লেশনারি বিগ ব্যাং মডেল
মূলত অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন , বিগ ব্যাং এর মত একটা ঘটনা ঘটার ব্যাপক শক্তি কীভাবে আসল ??? এই থিওরী টা হল সেই প্রশ্নেরই উত্তর ।
এখানে আমরা একটু সহজ কথা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করব – সেটা আমাদের চেনা জানা নদীর গতিপথ থেকে। নদীগুলো সাধারনতঃ পাহাড় পর্বত থেকে সৃষ্টি হয়ে নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে অবশেষে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে – এ আমরা সবাই জানি। আমাদের পদ্মা নদীর কথাই ধরি। এই নদী হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যায়। তার পরে দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে ভারতে প্রবেশের সময় এর নাম হয় গঙ্গা। এই গঙ্গা নামে ভারতের উত্তরপ্রদেশ ও বিহার রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে টয়ে এক সময় বাংলাদেশে প্রবেশ করে পদ্মা নাম ধারন করে,মুর্শিদাবাদ জেলায়। তারপর সেটা চাঁদপুরের কাছে এসে মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয়ে শেষ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়ে। দেশের অন্যান্য নদীগুলোও তাই। যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র – এসেছে কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবর থেকে, মেঘনা- এসেছে আসামের লুসাই পাহাড় থেকে তারপর নানা পথ পেরিয়ে কোন না কোন সাগরে গিয়ে পড়ছে। কিন্তু কথা হচ্ছে কেন নদীরা শেষ পর্যন্ত সাগরের বুকে গিয়ে আশ্রয় খোঁজে? কারণ, বিজ্ঞানীরা বলেন – যে যাই করুক না কেন, দিন শেষে সবাই আসলে ‘লোয়ার এনার্জি স্টেটে’ থাকতে চায়। এই যে আমরা সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটনি করে এসে রাতে বিছানায় গা এলিয়ে দেই – এই জন্যেই। কারণ শুয়ে থাকার মাধ্যমেই আমরা আমাদের দেহের সবচেয়ে নিচু শক্তিস্তরে আমাদের অবস্থান নিশ্চিত করি। নদীরাও তাই চায়। পাহাড় পর্বত বেয়ে সাড়া জীবন চলতে চাওয়ার চেয়ে সাগরের বুকে থাকাই তার কাছে পছন্দের, কেননা সেখানে সে সবচেয়ে কম শক্তিস্তরের জায়গাটা খুঁজে নিতে পারে। ধরা যাক, এই সাগরের এই সবচেয়ে কম শক্তিস্তরের জায়গাটাকে আমরা নাম দিলাম প্রকৃত শূন্যতা বা ‘ট্রু ভ্যাকুয়াম’। এখন কথা হচ্ছে, সবসময়ই যে নদীরা সাগরে তথা প্রকৃত ভ্যাকুয়ামের মধ্যে গিয়ে পড়তে পারে তা কিন্তু নয়। ধরা যাক, ফারাক্কা বাঁধের মত কোন বাঁধ কোন একটা নদীর বুকে আছে। ফলে নদীর পানি সাগর পর্যন্ত না পৌঁছে বাঁধেই আটকে থাকবে। বাঁধের উদাহরণের মতই আমাদের বিছানায় ঘুমানোর উদাহরণেও এ ধরণের অস্থায়ী অবস্থা তৈরি করতে পারি। পুরোপুরি বিছানায় গা এলিয়ে দেবার বদলে চেয়ারে কিছুক্ষণ ঝিমিয়ে নিতে পারি। আমাদের এই বিছানার বদলে চেয়ারে মানে খানিকটা উঁচু শক্তিস্তরে বসে ঝিমানো, কিংবা নদী একদম নীচে সাগরে না এসে একটু উঁচুতে বাঁধ পর্যন্ত গিয়ে আটকে থাকা – এই ধরণের অবস্থাকে বলা যেতে পারে ‘ফল্স ভ্যাকুয়াম’।নদীতে বাঁধ দিয়ে মানে সাময়িক সময়ের জন্য পানি আটকে দিয়ে আমরা তৈরি করতে পারি এক ধরণের ফলস ভ্যাকুয়ামের মত ক্ষেত্র। বাঁধ যত শক্ত পোক্তই হোক না কেন, একে কেউ সাগরের মত প্রকৃত ভ্যাকুয়াম ভেবে নেবেন না যেন! বাঁধের উপরে পড়ছে পানির অবিরত চাপ। বাঁধের মুখ খুলে দিলেই কিংবা বাঁধে সামান্য চিড় ধরলেই সেই বাঁধ ছত্রখান হয়ে ভেঙে চুরে পানিকে বয়ে নিয়ে যাবে সাগরের বুকে। আসলে মহাবিশ্বের শুরুতে ‘ফলস ভ্যাকুয়াম’ বা মেকি শূন্যতা নামের অদ্ভুতুড়ে জিনিসটা ছিল বলেই কিন্তু ঋণাত্মক চাপ এসে মহাবিশ্বকে এত দ্রুত প্রসারিত করে দিতে পেরেছে।
আমাদের মহাবিশ্বের মেকি শূন্যতার পথ পাড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে প্রকৃত শূন্যতায় এসে পৌঁছানোর ব্যাপারটা যদি সঠিক হয়, তবে সেই প্রকৃত শূন্যতার অবস্থানে হিগসের একটা নির্দিষ্ট মান থাকবে, যেখানে মহাবিশ্বের শক্তি ঘনত্ব হবে সর্বনিম্ন।
হিগস ক্ষেত্র এক ধরণের অতিশীতীভূত (supercool) অবস্থার মধ্য দিয়ে গিয়ে তার দশার পরিবর্তন ঘটায়, ফলে সে সময়টায় প্রতিসাম্যতার ভাঙ্গন সাময়িক সময়ের জন্য হলেও যেন চেপে চুপে রাখা যায়। ‘অতিশীতীভূত অবস্থা’, ‘প্রতিসাম্যতার ভাঙ্গন’ এই কঠিন কঠিন শব্দ শুনে ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই। পুরো ব্যাপারটাকে সহজ কথা দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। একে অনেকটা পানির দশা পরিবর্তনের সাথে তুলনা করা যায়। সাধারণ তাপমাত্রায় পানি তরল অবস্থায় থাকে। যে দিক থেকেই তাকাই না কেন, পানিকে একই রকম লাগে আমাদের। বিজ্ঞানের ভাষায় বললে বলা যায়, তরল অবস্থায় পানি সব দিক থেকেই থাকে প্রতিসম । পানিকে শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ঠাণ্ডা করলে তা বরফে পরিণত হয়, এ আমরা জানি, আর হরহামেশাই দেখি। কিন্তু যেটা অনেকেই জানিনা তা হল – বরফে পরিণত হওয়া মানেই কিন্তু এর প্রতিসাম্যতা ভেঙ্গে পড়া। যে কোন বরফের চাই নিয়ে পরীক্ষা করলেই দেখা যায়, এর বিভিন্ন অক্ষ বরাবর অণুর সাজসজ্জা ভিন্ন হয়। তাই বলা যায় – তরল অবস্থায় পানির যে প্রতিসমতা বজায় ছিল তা ভেঙ্গে পড়ে পানি বরফে পরিণত হয়ে গেলেই। তবে, একটু সতর্ক হলে আমরা কিন্তু পানির এই সহজাতভাবে বরফে পরিণত হওয়া ঠেকাতে পারি। এ জন্য অবশ্য দরকার অতিমাত্রায় বিশুদ্ধ পানি যোগাড় করে একে অতিদ্রুত বরফ গলনের তাপমাত্রার নীচে নিয়ে যাওয়া। এভাবে খুব তাড়াতাড়ি পানিকে ঠাণ্ডা করলে অনেকসময় দেখা যায়, পানি শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নীচেও বরফে পরিণত না হয়ে আগের মতই তরল অবস্থাতেই থেকে যাচ্ছে। তরলের এই দশাকে ‘অধিতরল’ অবস্থা বলতে পারি আমরা। গুথ ভাবলেন, মহাবিশ্বও নিশ্চয় এভাবেই কাজ করেছিল শুরুতে। তাপমাত্রা ক্রান্তিমানের চেয়ে নীচে নেমে গেলেও প্রতিসাম্যতা বজায় ছিল, আর মহাবিশ্ব ছিল সাময়িক সময়ের জন্য অস্থায়ী দশায় মানে মেকি শূন্যতায় বন্দি হয়ে। কিন্তু এ ব্যাপারটা ঘটার জন্য সুপ্ততাপের মাধ্যমে অতিরিক্ত শক্তির যে যোগানটা এসেছিল, সেটাই দিয়েছিল বিকর্ষণমূলক ধাক্কা, অনেকটা আইনস্টাইনের সেই মহাজাগতিক ধ্রুবকের মতোই। মহাজাগতিক ধ্রুবকের মত আচরণ বললেও, আসলে মাত্রাগত ভাবে এর সাথে আইনস্টাইনের ধ্রুবকের পার্থক্য অনেক। গুথ এবং হেনরির গণনা থেকে যেটা বেরুলো সেটার মান আইনস্টাইন যা অনুমান করেছিলেন তার চেয়ে ১০^১০০ গুন বেশি। এই তীব্র বিকর্ষণ শক্তি তৈরি হয়েছিল বলেই মহাবিশ্ব এইভাবে এতটা দ্রুত বিবর্ধিত হতে পেরেছিল। ‘এতটা দ্রুত’ বলছি বটে, কিন্তু ঠিক কতটা দ্রুত? বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যেই মহাবিশ্বের আকার বেড়ে গিয়েছিল মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন গুন (১ এর পরে ৩০টা শূন্য)।
অনেক বগরবগর হলো। এবার সমাপ্তি টানা দরকার।
এই লেখাটা মূলত অভিজিৎ রায়ের বই “শূন্য থেকে মহাবিশ্ব” ও মুক্তমনায় প্রকাশিত বেশ কিছু আর্টিকেল থেকে সংগ্রহ করে নিজের মত সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে লেখা ।
অর্থাৎ আবার সেই গুরুর কাছ থেকেই ধার করা!
অভিজিৎ রায়কে হারানোর ক্ষতি সম্ভবত আর কখনোই পূরণ হবে না।

[ সংযুক্ত ছবিটা উপরে ফলস এবং ট্রু ভ্যাকুয়াম সংক্রান্ত ত্রিমাত্রিক ছবিটির দ্বিমাত্রিকরণ হিসেবে নেয়া যেতে পারে। ]
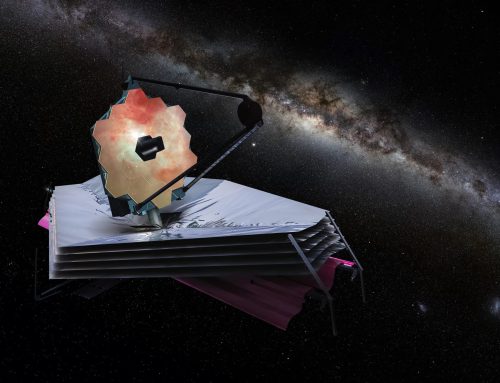

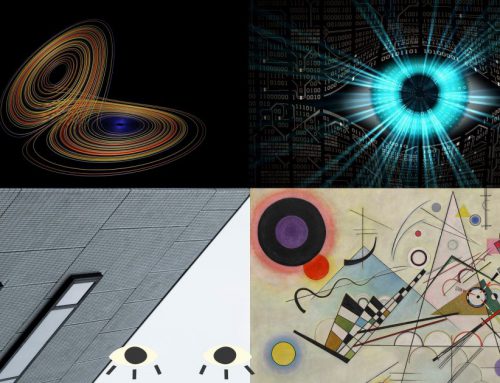
নিজের অজান্তেই মুক্তমনায় অভিজিৎ দা’র জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানের সেই প্রাঞ্জল লেখা খুঁজে বেড়াই। আজ সেরকমই একটা পেয়ে ভাল লাগলো। আরো বড় পরিসরে লেখা আশা করছি।
এধরনের লেখা আরও লিখুন। কলম চলতে থাকুক অবিরাম।
অনেক দিন পর মুক্তমনায় এসে প্রথমেই এটা পড়ে ভাল লাগলো। আশা করি সামনে আরো এমন গুছানো লেখা পড়তে পারবো। 🙂
বিজ্ঞানের কাটখোট্টা লেখাগুলো যে প্রাঞ্জল, সহজপাঠ্য করে পাঠকের নিকট উপস্থাপন করে পাঠককে বিজ্ঞান চর্চায় ও বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলা যায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের পরম স্বজন ড.অভিজিৎ রায়। কতই না পরিশ্রম করেছেন আমাদেরকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তা থেকে বের করে মুক্তদর্শনে মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তিচিন্তার চর্চার সংগ্রামী পথকে বিকশিত করার জন্য।
ধন্যবাদ প্রীতম চমৎকার লেখাটির জন্য।
বিজ্ঞানের নানান বিষয় নিয়ে আরো লেখা পাব আশা করি। 🙂
উৎসর্গপত্রের প্রথম বাক্যটা নিয়ে কিছু কথা।
‘হাতে গোনা’ এর পরে আবার ‘মুষ্টিমেয়’ বলা দরকার নেই। দুটোই একই কথা বোঝাচ্ছে। আর ইংরেজীর মত বাংলায় আগে একাধিক বুঝালে বিশেষ্যের পরে বহুবচন হয় না। যেমন-
“দশ জন লেখক এখানে বসে আছেন” খেয়াল করুন “দশ জন ‘লেখকরা’ এখানে বসে আছেন” বলা হচ্ছে না। আবার, “লেখকরা এসে পড়েছেন” এটা ঠিক কারণ একাধিক লেখক উপস্থিত হয়েছেন।
অনেক ধন্যবাদ। সামনের লেখাগুলো লেখার সময় মাথায় রাখবো।
@প্রীতম,
বিজ্ঞানের কাটখোট্টা লেখাগুলো যে প্রাঞ্জল, সহজপাঠ্য করে পাঠকের নিকট উপস্থাপন করে পাঠককে বিজ্ঞান চর্চায় ও বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলা যায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের পরম স্বজন ড.অভিজিৎ রায়।
কতই না পরিশ্রম
করেছেন আমাদেরকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তা থেকে বের করে মুক্তদর্শনে মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তিচিন্তার চর্চার সংগ্রামী পথকে বিকশিত করার জন্য।
ধন্যবাদ প্রীতম চমৎকার লেখাটির জন্য।
উৎসাহ প্রদানের জন্য অনেক ধন্যবাদ।
লেখাটি তথ্যপূর্ন। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে কঠিন কথাগুলো সহজে প্রকাশ করবার জন্য । 🙂