ডাইনোসর প্রভিন্সিয়াল পার্কের তথ্যকেন্দ্রটিতে রাখা বিভিন্ন নমুনা দেখে বেরিয়ে আসার পর জানলাম যে কাছাকাছিই আছে জন ওয়ের নামের একজন আফ্রিকান-আমেরিকানের কেবিন। আলবার্টার র্যাঞ্চিং-র ইতিহাসে তিনি একজন লিজেন্ড। যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধ শেষে টেক্সাসে র্যাঞ্চিং শিখেছেন, তারপর সেখান থেকে পশুর পাল তাড়িয়ে তাড়িয়ে একেবারে দু’হাজার মাইল দূরের আলবার্টায় এসে থিতু হয়েছেন। উত্তর আমেরিকার সেই সময়ের ইতিহাসে কালো মানুষদের গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনার ঘটনা কম হলেও ইনি সগৌরবে জায়গা করে নিয়েছেন! এ থেকেই বোঝা যায় কেমন বর্ণাঢ্য চরিত্রের মানুষ ছিলেন তিনি। দুঃখজনক-ভাবে, তথ্যকেন্দ্রটির সংগ্রহ দেখতে দেখতেই সময় শেষ, তাই সেবার আর কেবিনটি দেখা হল না।
তথ্যকেন্দ্রের বাইরে একটা খোলা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে ডক্টর ব্রিঙ্কম্যান আর তাঁর দুই সহকর্মীর সাথে পরিচিত হলাম। এখান থেকে পার্কটির চারদিকের দৃশ্য বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। পাহাড় উপত্যকা, উন্মুক্ত শিলা, বালু, খাল যার কোনটি শুকনো, কোনটিতে ক্ষীণ জলের ধারা– সব মিলিয়ে আমার দেখা এক অভূতপূর্ব দৃশ্যই বটে। গবেষকরা খুব সংক্ষেপে যার যার কাজের বর্ণনা দিলেন। বললেন যে দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেয়া জায়গাগুলোর পাশাপাশি আমরা পার্কের ভেতরে গবেষণার জন্য সংরক্ষিত কিছু কিছু জায়গায় যাব যেখানে সাধারণত টুরিস্টদের নেয়া হয় না। পার্ক কর্মীরা এদিকটায় কম আসেন, তাই দলছুট হওয়া যাবে না। চারদিকের দৃশ্য একই রকম হওয়ায় পথ হারালে এই বিরান ভূমির বুনো পরিবেশে একা একা রাত কাটান সুখকর হবে না। আর যেহেতু জায়গাটিতে র্যাটলস্নেক আছে তাই সতর্ক থাকতে হবে, জুতা খুলে চলাফেরা করা চলবে না। ওনারা যে জায়গাগুলোতে আমাদের নিয়ে যাবেন, সেখানে গবেষণার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাই পড়ে থাকা ফসিল সাবধানে ধরে দেখতে পারব, তবে পকেটে ভরা থেকে বিরত থাকতে হবে; আলবার্টার আইন এবিষয়ে খুবই কড়া।

ছবি ৫ঃহ্যাডরোসর পরিবার। ইনসেটে শিল্পীর কল্পনায় হ্যাডরোসরের বাসা। (অন্তর্জাল থেকে পাওয়া তথ্য আর ছবি ব্যবহার করে সম্পাদিত)
প্রায় পঁচাত্তর মিলিয়ন বছর আগে পার্কটিতে হ্যাডরোসরদের (বড় আকৃতির তৃণভোজী ডাইনোসর, আরও তথ্য পরবর্তী পর্বে) বিশাল কলোনি ছিল (ছবি ৫)। পার্কের যে অংশে আমরা যাচ্ছি সেখানে কিছু ডিমের খোসার ফসিলসহ শিশু ডাইনোসরের হাড়ের ফসিল পাওয়া গিয়েছে। এই ধরনের ফসিল কেবল পার্কের এই জায়গাটিতেই পাওয়া গেছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা যে এখানেই হ্যাডরোসরগুলো দলবেঁধে বাসা বানাত, ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা তুলে লালন-পালন করতো। অবশ্য এমনও হতে পারে যে ফসিলগুলো নদী বা হিমবাহর মাধ্যমে অন্য জায়গা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে এখানে এসেছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা মোটামুটি নিশ্চিত যে তা ঘটেনি, কেননা ফসিলের নমুনাগুলো প্রায় অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে, স্থানান্তরিত হয়ে এলে সেগুলো এরকম অক্ষত থাকত না। একইভাবে ডাইনোসরের ডিমের খোসাগুলোও এই এলাকাতেই ফসিলায়িত হয়েছে। সাধারণত: ডিমের খোসার ফসিল সহজে পাওয়া যায় না, মাটির অম্লত্ব বেশী হলে ডিমের খোসা ফসিলে পরিণত হওয়ার আগেই গলে যায়। কিন্তু শেষ জুরাসিক কালের একটি প্রাচীন নদীর মোহনা হওয়ায় সেসময় এই এলাকাটিতে মিঠা পানির ঝিনুকের বিশাল আবাস ছিল; মৃত ঝিনুকের খোলের মূল খনিজ উপাদান ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা লাইম (ডিমের খোসারও মূল খনিজ) জমতে থাকা পলির সাথে মিশে পলিকে ক্ষারধর্মী করে তুলেছিল। পরবর্তীতে পানির উপরে জেগে উঠার পর হ্যাডরোসরের দল এলাকাটিকে বাসা বানানোর জন্য নির্বাচন করে। মাটি অম্লধর্মী না হয়ে ক্ষারধর্মী হওয়ার কারণেই খুব সম্ভব ডাইনোসরের ডিমের খোসাগুলোর গলে যাওয়া বিলম্বিত হয়ে ফসিলায়নের সুবিধা হয়েছে।
আলোচনার শেষ পর্যায়ে গবেষকদের একজন বললেন যে কদিন আগেই সেখানে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। এধরনের বৃষ্টিতে পার্কের নালাগুলোতে হটাতই ঢলের পানি আসে। ঢলের পানির তোড় নরম মাটির স্তর সরিয়ে নীচের জমে থাকা ফসিলগুলোকে বের করে আনে। এজন্যই সেদিন তাঁরা নতুন ফসিল খুঁজে পাওয়ার আশায় মাটির দিকে সতর্ক নজর রাখবেন। এরপর গবেষকদের পিছু নিয়ে আমরা একটা ক্রমশ ঢালু হয়ে যাওয়া পথ ধরে পার্কের ভেতরে ঢুকে পড়লাম।
পার্কের ভেতর দিয়ে বালি আর কাঁকড় বিছানো আঁকা-বাঁকা পথ সামনে এগিয়ে বাঁক নিয়ে ঢিবির আড়ালে হারিয়ে গেছে। চারদিকে ছোট-বড় ঢিবি। কোনটা দেখে মনে হয় পুরোটাই বালু দিয়ে তৈরি, আবার কোনটায় বালু আর পাথরের পর্যায়ক্রমিক স্তর। কোন ঢিবি একেবারে ন্যাড়া আবার কোনটার উপর সবুজ ঘাসের ছোঁয়া। কতগুলো ঢিবির উপরে চ্যাপ্টা পাথরের একটা স্তর আর নীচে কেবল বালু, দেখে মনে হয় ঢিবিগুলো যেন হ্যাট পরে বসে আছে। এগুলোকে হুডু (hoodoo) বলে (ছবি ৬)। একটা বালুর ঢিবির গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম যে যেমন ভেবেছিলাম তেমন ঝুরঝুরে নয়, দৃঢ় আর শিরিষ কাগজের মত খরখরে। ঢিবি গুলোর মাঝখানের সমতল জায়গাগুলোতে প্রচুর প্রেইরী সেজের (Artemisia ludoviciana) ঝোপ। সুদর্শন এই বুনো প্রজাতির রূপালী-সবুজ পাতা খাওয়া যায়। আদিবাসীরা এই পাতা তাদের আচার-অনুষ্ঠানেও ব্যবহার করে থাকেন। দেখতে বাজারে পাওয়া সেজ পাতার চেয়ে কিছুটা আলাদা রকমের হলেও ডলে দেখলাম যে গন্ধ প্রায় একই রকম। ডগার কিছু নরম পাতা ছিঁড়ে নিলাম সন্ধ্যার বারবিকিউর জন্য।
কিছুক্ষণের মধ্যেই মূল পথ ছেড়ে আমরা পাশের নিচু পাথুরে জমিতে নেমে এলাম। খানিক দূর এগিয়ে গবেষকদের একজন একটা শুকিয়ে যাওয়া খালের মত জায়গায় থেমে দেখালেন আদি যুগের ঝিনুকের ফসিল। উপরে শক্ত শিলা আর নীচে কয়েক স্তরে বিস্তর ফসিলায়িত ঝিনুক জমে আছে (ছবি ৭)। ঢলের পানি খালের দু’পাশের শিলার স্তরগুলোকে কেটে বয়ে যাওয়ায় ঝিনুকের ফসিলগুলো বেরিয়ে এসেছে। খালের পাড়ে শক্ত বেলে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে দুপুরের খাবার খেতে খেতেই আমরা ফসিল গবেষণার ‘অ-আ’ সম্পর্কে কিছুটা ধারনা পেয়ে গেলাম।

ছবি ৭ঃ পাথরের স্তরের নীচে শুকনো কাদার ভেতরে ক্রিটেশিয়াস কালের ফসিলায়িত ঝিনুকের খোল। বেশীরভাগ খোলের চওড়া পাশটি দেখা যাচ্ছে। জীবিত ঝিনুক খোলের একপাশ বালুতে গেড়ে খোলের দু’অংশের মাঝখানের চেরা দিকটি খাড়া করে রাখে বলেই খোলের এই অবস্থান। ইনসেটে এখনকার সময়ের জীবিত (*) আর মৃত (x) ঝিনুক দেখানো হয়েছে।
প্রথমেই শুনলাম কিভাবে ফসিল তৈরি হয়। একটি ভাল ফসিল তৈরির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হচ্ছে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় নমুনার প্রাকৃতিক সংরক্ষণ। নমুনা হতে পারে মৃত প্রাণী বা উদ্ভিদের অংশ, তাদের ছাপ বা ছাঁচ, এমনকি বর্জ্য পদার্থ। আসলে এমন কোন চিহ্ন যা কোন জীবের একসময়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানান দেয় তাই ফসিল। ফসিলের যেমন প্রকারভেদ আছে, তেমনি তার গঠনের প্রক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তবে সাধারণভাবে সংরক্ষিত নমুনার আদি উপাদান আশেপাশের খনিজ দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়ে ফসিলে রূপান্তরিত হয়। প্রাণী বা উদ্ভিদের সহজে পচনশীল নয় এমন অংশের ফসিলই বেশী পাওয়া যায়। এর মধ্যে রয়েছে গাছের কাঠ, আঠা, প্রাণীর হাড়, দাঁত ইত্যাদি।
এখানে বলে রাখা ভাল যে ক্ষেত্র-বিশেষে দ্রুত পচনশীল নমুনা যেমন গাছের পাতা বা প্রাণীর শরীরের নরম কলাও পচনের আগেই সংরক্ষিত হয়ে সরাসরি ফসিলে পরিণত হতে পারে। উদাহরণ হিসাবে প্রথম পর্বে আলোচিত নডোসরাসের ফসিলটির কথা বলা যায়। ধারনা করা হচ্ছে যে হটাত আসা পাহাড়ি ঢলের পানিতে ডুবে পশ্চিমের উঁচু ভূমিতে চরে বেড়ানো এই নডোসরাসটির মৃত্যু হয়। এরপর পানির তোড় মৃতদেহটি নদীতে নিয়ে ফেলে। পাকস্থলীর ব্যাকটেরিয়ার তৈরি গ্যাসে পেট ফেঁপে কয়েকদিন নদীতে ভেসে থাকার পর এটি আলবার্টার অগভীর সাগরে চলে আসে। সেখানে পচন ধরে সামুদ্রিক প্রাণীদের খাবার হওয়ার আগেই দেহটি উপকূলের কাছে অপেক্ষাকৃত শান্ত পানিতে ডুবে গিয়ে পলির নীচে চাপা পড়ে যায়। এরপর ঠাণ্ডা পরিবেশে সংরক্ষিত হয়ে ধীরে ধীরে মৃতদেহটি ফসিলে পরিণত হতে শুরু করে।
সেদিন ফসিল নিয়ে এমনি টুকটাক কিছু কথার পর শুরু হল আদিকালের ঝিনুক নিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব। আমাদের দলের একজন জিজ্ঞেস করলেন,
ঝিনুকগুলো কি শুরু থেকেই এখানেই ছিল নাকি সে যুগের নদীর স্রোত ঝিনুকের খোলগুলোকে এখানে এনে ফেলেছে?
: আমাদের ধারণা শুরু থেকেই এখানে ছিল। জুরাসিক কালের শেষ থেকে প্যালিওজিন কালের শুরু পর্যন্ত এই অঞ্চলটি অগভীর সাগরে এসে মিলে যাওয়া নদীর মোহনা ছিল। এই মিষ্টি পানির ঝিনুকগুলো মোহনার হাল্কা লবণাক্ত পানিতেই জন্মাত।
আর কোন প্রমাণ আছে যে ঝিনুকগুলো এখানেই জন্মেছে, নদীর স্রোতের সাথে আসেনি? প্রশ্ন শুনে মনে হল যে গবেষকের আগের উত্তরে প্রশ্নকারী পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন।
: প্রমাণ আছে; আমরা এখানকার ঝিনুকের স্তরগুলোর একটি জায়গায় প্রধানত একধরনের প্রজাতিই পাই, যার মানে ঝিনুকগুলো সেই জায়গায় দলবেঁধে থাকতো। দূর থেকে নদীর স্রোতের সাথে এলে সব প্রজাতির ঝিনুকের খোল মিলেমিশে এক হয়ে যেত; সেটা হয় নি এখানে।
এরপর আরেক জনের প্রশ্ন, আচ্ছা, ঝিনুকের স্তরগুলো কি বিভিন্ন সময়ে মরে যাওয়া ঝিনুকের খোল ফসিলায়িত হয়ে তৈরি?
: খুব সম্ভব না; আসলে এগুলো সব একসাথে হটাত মারা যাওয়ার পর ফসিলায়িত হয়েছে।
আপনি বলছেন, সব একসাথে মারা গিয়েছিল, কিন্তু কি করে বুঝলেন?
: ফসিলায়িত খোলগুলোর অবস্থান দেখুন, বেশীরভাগ খোলেরই চওড়া পাশটি দেখা যাচ্ছে। জীবিত ঝিনুক খোলের একপাশ বালুতে গেড়ে খোলের দু’অংশের মাঝখানের চেরা দিকটি খাড়া করে রাখে বলেই পাশ থেকে দেখলে খোলের এই অবস্থান চোখে পড়বে (ছবি ৭)। তবে কাদায় চাপা পড়া পর্যন্ত যে বেঁচে ছিল তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ উপরের পাথুরে স্তরে ঢেউ খেলানো দাগগুলো। এই ঝিনুকগুলোর মারা যাওয়ার কারণ হটাত বন্যা বা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে কাদার স্তরের নীচে চাপা পড়া। জীবিত ঝিনুক কাদার নীচে থাকতে চাইবে না। ওরা হাঁচড়ে-পাঁচরে কাদার নীচ থেকে উপর দিকে উঠে আসবে। উপরের কাদার স্তর পরে জমে গিয়ে পাথর হলেও কাদার ভেতর দিয়ে ঝিনুকের উঠে আসার চিহ্ন, ঢেউ খেলানো নকশাগুলো সংরক্ষিত হয়ে গিয়েছে। এই নকশাগুলোও এক রকমের ফসিল (ছবি ৮)।
কাদার উপরে ওঠে আসার পর কি ওরা বেঁচে গিয়েছিল?
: সম্ভাবনা কম। কাদার উপরে পানি ছিল না, রোদে-তাপে শুকিয়ে মরার সম্ভাবনাই বেশী।

ছবি ৮ঃ কাদায় চাপা পড়া ঝিনুক কাদার স্তর ভেদ করে উপরে উঠে এসেছিল। চাপা দেয়া কাদার উপরের অংশ পাথর হয়ে ধরে রেখেছে ঝিনুকের চলার পথের চিহ্ন (^)। যে ঝিনুকগুলো উপরে উঠতে পারে নি তাদের ফসিলায়িত খোল পাথরের স্তরের নীচে দেখা যাচ্ছে। ইনসেটঃ উপরের পাথরের স্তর সরে গিয়ে বের হয়ে এসেছে ফসিলায়িত ঝিনুকের খোল।
আলোচনাটি শুনে বোঝা গেল যে কেবল মাঠে থাকা নমুনার নিবিড় পর্যবেক্ষণ আর সেই পর্যবেক্ষণের যৌক্তিক বিশ্লেষণ করেই ফসিল বিজ্ঞানীরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বের করে এনেছেন! কথা শুনতে শুনতে লক্ষ্য করলাম কাছেই কিছু ঝিনুকের ফসিল মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে (ছবি ৮, ইনসেট)। দেখে মনে হচ্ছিল কদিন আগেই যেন কোন জেলে মাছ ধরে জাল পরিষ্কার করার পর ঝিনুকগুলো এখানে ফেলে গেছে; শৈশবে দেশের বাড়িতে বড়দের সাথে মাছ ধরতে গিয়ে এমন দৃশ্য অনেক দেখেছি। আসলে আমার অনভিজ্ঞ চোখে ফসিলায়িত ঝিনুকের খোলগুলোর সাথে এখনকার ঝিনুকের খোলের সাদৃশ্য এতো বেশী ছিল যে হাতে তুলে নেয়ার পরও বিশ্বাস হচ্ছিল না যে এগুলো একালের নয়, এদের বয়স প্রায় পঁচাত্তর মিলিয়ন বছর। বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম যে এমন কিছু ছুঁয়ে দেখছি, যার ভেতরের প্রাণীটি যখন জীবিত ছিল তখন মানুষের উপস্থিতি তো বহু দূরের কথা, স্তন্যপায়ীদের আদিপুরুষেরাই সবেমাত্র পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে। তবে বিস্মিত হওয়ার মতো আরও কিছু বাকি ছিল। (চলবে)
(লেখাটি কয়েক বছর আগে শুরু করলেও অতি সম্প্রতি শেষ করতে পেরেছি। কয়েকটি পর্বে এটি প্রকাশিত হবে। কাজী রহমান আর নীলাঞ্জনাকে অনেক ধন্যবাদ, তাঁদের লেখা দেয়ার অনুরোধে উৎসাহিত হয়েছি। সূত্রের উল্লেখ না থাকা সব ছবিই সহকর্মী ডির্ক হাবমাখার এই লেখার জন্য তুলে দিয়েছেন)


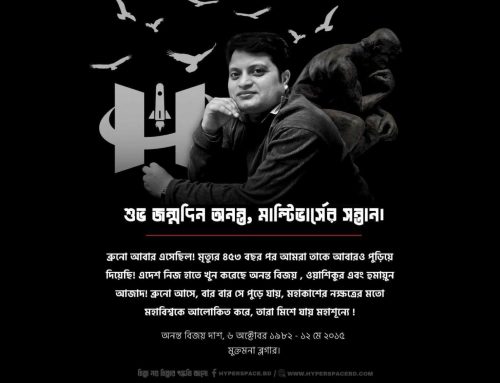
আবারও অনেক ধন্যবাদ! কলোরাডোর ডাইনোসর মনুমেন্ট দেখার সুযোগের অপেক্ষায় থাকলাম :)।
তৃতীয় পর্বের ঘষা-মাজা চলছে; আপাততঃ তিন পর্বেই শেষ করার প্ল্যান, তবে পাঠকদের আগ্রহ থাকলে আরও একটা পর্ব যোগ করার ইচ্ছে আছে।
আপনার সিরিজটি চমৎকার হচ্ছে। এত খুঁটিনাটি যে আমাদের জন্য তুলে ধরছেন তার জন্য ধন্যবাদ। ফসিল কীভাবে হয় সেটা এই লেখা থেকে বোঝা যাচ্ছে। আমার নিজের একবার খুব অল্প সময়ের জন্য কলোরাডোর ডাইনোসর ন্যাশানাল মনুমেন্টে যাবার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে একটি ছোট পাহাড়ের গা ঘেঁষে ১৫০ মিলিয়ন বছর আগের ফসিলকে সেখানে রেখেই তার একপাশে একটা প্যাভিলিয়ন করা হয়েছে যাতে পুরো দৃশ্যটা দর্শক বুঝে নিতে পারে। পরবর্তী অধ্যায়ের অপেক্ষায়।