একসময় মেলবোর্নে একটা ইনকাম ট্যাক্স ফার্মে কাজ করতাম। জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়াতে ব্যক্তিগত ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করার সময়। কিছু কিছু আয়করদাতাকে ট্যাক্স অফিস পরিস্থিতিভেদে একটু বেশী সময় দিলেও, বাংলাদেশের মত সাধারনভাবে সকলের জন্য সময় বাড়ানোর নজির খুবই কম। ট্যাক্স কনসালটেন্ট অনেকটা ডাক্তারের মত – রোগী নিজের ভালোর জন্যই বাধ্য হয়ে সব কথা ডাক্তারকে খুলে বলে। ব্যক্তিগত গোপন প্রসঙ্গও বাদ পড়ে না। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়ার ট্যাক্স অফিসের সর্বব্যাপী বিচরনকারী লম্বা হাতের ভয় তো আছেই। কাজেই, ক্লায়েন্টের সঙ্গে অনেক কথা বলতে হয়, অনেক প্রিয়-অপ্রিয় প্রশ্ন করতে হয়। আয়কর নিয়ে নানা সাদাকালোরঙিন অভিজ্ঞতা লিখতে বসলাম আজ।
জিজ্ঞাসাবাদ কিম্বা আলাপচারিতার একেবারে প্রথমেই আসে একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য, যা ওই ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ নাও জানতে পারে, যেমন জন্মতারিখ, ট্যাক্স ফাইল নাম্বার, ব্যাঙ্ক একাউন্ট নম্বর ও ব্যালান্স, ঠিকানা, কোন পড়াশুনা করছে কি না, আগে কি পড়াশুনা করেছে, পড়াশুনার লোন আছে কি-না, এসব প্রশ্ন। আইডেন্টিটি ফ্রড এইসব পশ্চিমের দেশে আজকাল একটা বড় সমস্যা, কাজেই দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় একজন আরেকজনকে এই সব বিষয়ে কখনো প্রশ্ন করে না। আমার নিজের অফিসের এক সহকর্মী তো তার ছেলে কোন স্কুলে পড়ে সেকথাও আমাকে বলতে রাজী হয় নি। প্রাইভেসীর এতদুর পর্যন্ত দৌড় দেখে আমরা অভ্যস্ত না হলেও অল্পদিনেই ‘যষ্মিন দেশে যদাচার’ নীতি মেনে চলতে শিখি। তবে আমার কাজের সুবাদে সব ক্লায়েন্টকে এই সব প্রশ্ন করতে হয়। ব্যাপারটাতে আমি বেশ মজা পাই। অস্ট্রেলিয়াতে প্রাইভেসী আইন বেশ কড়া বলে তারাও নির্ভয়ে সব কথা বলে। কারন ক্লায়েন্টের ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহার মারাত্নক অপরাধ, আর সেটা করে জেলে যাওয়ার শখ আমার বা অন্য কারোই সাধারনত থাকে না। একবার এক তরুন পুলিশ অফিসার তার হাতে গ্রেফতারকৃত এক তরুনীর ফোন নাম্বার অফিসিয়াল রেকর্ড থেকে টুকে নিয়ে কয়েকমাস পরে তাকে ওই নাম্বারে ফোন করে প্রেম নিবেদন করেছিল। মেয়েটি এতে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করায় ওই বেচারার চাকুরী চলে যায়, এবং মিডিয়াতে বেশ ফলাও করে এই কাহিনী প্রচার হয়। প্রাইভেসী আইনের প্রয়োগ যে কত ব্যাপক হতে পারে, তা এদেশে না আসলে হয়তো জানা হত না।
যা হোক, আমার প্রশ্নবাণ একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্নেই থেমে থাকে না, এর পরে তা পারিবারিক সম্পর্কের দিকে উঁকিঝুঁকি মারে। পার্টনার বা স্পাউস (বিবাহিত বা ডি-ফ্যাক্টো, অর্থাৎ স্রেফ একসাথে বসবাস করে এরকম, যাই হোক না কেন) আছে কি-না, বাচ্চা আছে কি-না (ক্লায়েন্ট বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক, বয়স ১৫ বা ৯৫ হোক, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাধ্যতামুলক), চাইল্ড সাপোর্ট দিচ্ছে কি-না (অর্থাৎ পার্টনারের সঙ্গে সেপারেশানের পরে বাচ্চার ভরন-পোষনের জন্য মাসে মাসে টাকা দিচ্ছে কি-না), গত ১২ মাসে বিদেশে গিয়েছিল কি-না, কতদিন ছিল, গতবছর কি একই পার্টনার ছিল কিনা, কি গাড়ী চালায় এবং তার মডেল কি, দাম কত, নিজের বাড়ি নাকি ভাড়ায় থাকে, ইত্যাকার নানান প্রশ্ন। খুব কাঠখোট্টা অথবা মেজাজী ক্লায়েন্ট না হলে, এক ঘন্টার একেকটা এপয়েন্টমেন্টে ক্লায়েন্টের সঙ্গে আমার একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক তৈরী হয়ে যায়। মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন, ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও আশা-আকাংখার কথা, ভাবনার কথা জানা হয় – বেশ উপভোগ করি আমি বিষয়টা। কিছু খারাপ অভিজ্ঞতাও যে নেই তা নয়, তবে তা খুবই নগন্য।
একবার এক ক্লায়েন্টের ট্যাক্স রিটার্ন করলাম, যার নাম ছিল ইন্দিরা পার্সেভিচ ডকিচ। এপয়েন্টমেন্ট বুকে নাম লেখা ছিল শুধু ইন্দিরা। আমি ভাবলাম, নিশ্চয় কোন ভারতীয় অথবা নিদেনপক্ষে কোন হিন্দু মেয়ে হবে। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় যে স্বর্নকেশী দীর্ঘাঙ্গিনী আমার অফিসের দরজায় কড়া নাড়ল, তাকে ইন্দিরা নামের কারো সঙ্গে মেলাতে পারলাম না কিছুতেই। সম্বিত ফিরতেই শুনলাম, সে তার নাম বলছে ইন্দিরা ডকিচ। আমি শুরু করলাম নাম সম্পর্কে প্রশ্ন দিয়ে। আমাদের কোম্পানীর পলিসি অনুযায়ী প্রয়োজনের বাইরে অপ্রাসঙ্গিক ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা বারন, তবে কেতাবের কথা দিয়ে আসলে বাস্তবতা চলে না সবসময়। ইন্দিরাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নামের ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু খুলে বল। ইন্দিরা বিরক্ত বা অবাক হল না মোটেও আমার প্রশ্ন শুনে। বলল, তুমিতো ইন্ডিয়ান, কাজেই তুমি আসল ইন্দিরাকে ভালো করেই জান। আর আমার বাবা-মা প্রাক্তন যুগোশ্লাভিয়ার লোক। তারা জোসেফ টিটোর আমলের লোক, যে সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন পন্ডিত নেহেরু। কোল্ড ওয়্যারের সেই সময়ে ভারত এবং যুগোশ্লাভিয়া ছিল জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মুল হোতা, ফলে নেহেরুর নাম যুগোশ্লাভিয়াতে খুবই পরিচিত ছিল। নেহেরুর মেয়ের নামে আমার নাম রাখেন আমার বাবা-মা। আমি বললাম, টিটো নামটা কয়েক দশক আগে বাংলাদেশ/ভারতেও খুব জনপ্রিয় ছিল, যদিও এর পেছনের কারন তোমাদের টিটো কি-না তা বলতে পারি না।
এভাবে ইতিহাসের পাঠ আরো অনেক ক্লায়েন্টের কাছেই পেয়েছি। একবার এক ক্লায়েন্ট পেলাম, যার নাম ছিল ক্রিস্টোফার ফাইজ (Faiz) মুল্লা (Mulla). পুরোদস্তুর শেতাঙ্গ ককেশীয়ান চেহারা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ক্রিস, তোমার সারনেইম কি ইংলিশ, স্কটিশ বা আইরিশ, নাকি কন্টিনেন্টাল ইউরোপীয়ান? আমি জানতাম, এই সারনেইমটার মধ্যে অন্য গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু সরাসরি সেটা না বলে একটু ঘুরিয়ে কথা জিজ্ঞেস করে কথা বের করবার চেষ্টা আর কি। ক্রিস উলটা আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি ইন্ডিয়ান? আমি বলি, হ্যাঁ। ক্রিস তখন খুলে বসে তার গল্পের ঝাঁপি, যা শোনার পরে আমরা অনেকটা একে অপরের আত্নীয়তার সুত্রে আবদ্ধ হয়ে গেলাম। ক্রিসের আদিপুরুষের নিবাস আফগানিস্তানের কান্দাহারে। তারা ১৮৫০ সালেরও আগে ততকালীন ভারতবর্ষ থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমিয়েছিলেন উট চালক হিসেবে। এক হিসেবে তারাই অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম দক্ষ অভিবাসী বা স্কিল্ড মাইগ্রেন্ট, কারন এই আফগানদেরকে এদেশে আনা হয়েছিল রুক্ষ মরুভুমিময় ও পাথুরে মধ্য অস্ট্রেলিয়ায় পরিব্রাজকদেরকে বহন করতে তাদের উটের উপযোগীতার কারনে। তখনও মোটরগাড়ি বা আকাশযান আবিস্কার হয় নি, কাজেই উটের মতন ভারবাহী ও কষ্টসহিষ্ণু প্রানীই ছিল ভরসা আবিষ্কারক ও পরিব্রাজকদের। অস্ট্রেলিয়ার উপকুলবর্তী এলাকাগুলি ছাড়া বাকী প্রায় পুরোটাই তখনো অজানা তথা অনাবিষ্কৃত। পথঘাট নেই, খাবার ও পানীয় নেই, এমন পরিবেশকে মোকাবিলা করার জন্য ভারত থেকে উট এবং সঙ্গে উটচালক আমদানী হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায়, ১৮৩৮ থেকে ১৯০৩ সালের মধ্যে।
অনধিক ৩০০০ জন উটচালক এসেছিলেন সেই সময়ে, যাদের সবাই ছিলেন মুসলিম, এবং তারা দেশে তাদের পরিবারকে ফেলে এসেছিলেন। এ সমস্ত উটচালকেরা মরুভূমিতে কাজ করার পদ্ধতি জানতেন। তাদের প্রাণান্তকর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমির মধ্য দিয়ে সড়ক নির্মিত হয়, খনি আবিস্কৃত হয় এবং সুচারুরূপে খনি থেকে মাল আনা নেয়ার কাজ সম্পাদিত হয়। অস্ট্রেলিয়া এসমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ দ্বারা সমৃদ্ধশালী হতে থাকে। অথচ সাদা অস্ট্রেলিয়ানরা ভারতীয় উটচালক এবং আদি অস্ট্রেলিয়ান এবোরিজিনদেরকে একই রকম ঘৃনার দৃষ্টিতে দেখত, ফলে এই দুই কমিউনিটি পরস্পরকে কাছে টেনে নিয়েছিল। এবোরিজিনদের মত আফগানরাও বাস করতেন শহরের বাহিরে তৈরী বস্তিতে, যেগুলোকে ঘান টাউন (Ghan Town) বা আফগান জনপদ বলা হত। অনেক উটচালক এবোরিজিনদেরকে বিয়েশাদি করে সংসার পেতে বসেন রীতিমত। অস্ট্রেলিয়ায় মুসলিম উটচালকদের ইতিহাস অনেক বড়, আর এটা নিয়ে ইমিগ্রেশান মিউজিয়াম একটা প্রদর্শনীও করেছিল গতবছর। আকাশপাড়ায় খুঁজলে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসের আদি পর্বে তাদের অসামান্য অবদান সম্পর্কে, তবে ক্রিসের গল্প এইখানে এসে মোড় নেয় ইতিহাসের আরেক কালো অধ্যায়ের দিকে।
অস্ট্রেলিয়ার বিনির্মান ও উন্নতিতে আফগান উটচালকদের মূখ্য ভূমিকা থাকলেও তাদের সাথে বৃটিশ অভিবাসীদের আচরণ প্রথম থেকেই ভাল ছিল না। ১৯২০ সালের দিকে যখন সড়ক নির্মান কাজ শেষ হয়ে যায় এবং খনিসমূহ আবিস্কৃত হয়ে যায়, তখন উটেরও প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়, এ অবস্থায় সেই আফগানদের অন্য রোজগারের সুযোগ না দিয়ে তাদেরকে অস্ট্রেলিয়াতে বসবাস করতে দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়। তাদের অনেকে দেশে ফিরে আসে। আর যারা রয়ে যায়, তারা অসহায় অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করে। অনেকে মুলধারার সঙ্গে মিশে যাওয়ার জন্য পেশা, ধর্ম এবং নাম পরিবর্তন করে ফেলে। তার ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই এই কমিউনিটি তার পরিচয় হারিয়ে ফেলে। অনেকে তাদের জন্মস্থানের বা আত্নপরিচয়ের শেষ অবলম্বন হিসেবে নামের একাংশ রেখে দেয়, যার ফলে আজকের এই জগাখিচুরী নাম, ক্রিস মুল্লা। নিশ্চয়ই ক্রিসের পুর্বপুরুষেরা মোল্লা নামে অভিহিত হতেন, যার বিকৃত রুপ আজকের এই মুল্লা। আর ক্রিস মুল্লা ইতিহাসের এক সাক্ষী হিসেবে আমার সামনে হাজির, এ এক অন্যরকম অনুভুতি।
এইখানে একটা নোট দেওয়া দরকার। অফিসিয়ালি আমরা বাংলাদেশের মানুষ, তবে মেলবোর্নে এসে এত রকমারী চেহারার মানুষের মধ্যে আমাদের পরিচয় দাঁড়িয়ে গেছে ‘ইন্ডিয়ান’ হিসেবে, চেহারার মিলের কারনে। বাংলাদেশী বলুন, পাকিস্তানী বলুন, ভারতের পাঞ্জাবী বলুন, আর শ্রীলংকার তামিলই বলুন, সবারই এক পরিচয়, ‘ইন্ডিয়ান’। পাসপোর্ট হাতে করে ঘুরে বেড়ানো তো আর সম্ভব নয়, কাজেই কেউ যখন আমাকে ভারতীয় মনে করে, তখন উপযুক্ত পরিস্থিতি-স্থান-কাল-পাত্র ছাড়া তাদেরকে শোধরাতে যাই না, সেটা সময় ও শ্রমের অপচয় হবে মনে করে। আসলেই তাই। গড়পড়তা সাধারন শেতাঙ্গ মেলবোর্নবাসীর কাছে আমরা ভারতীয়। অনেক রেস্টুরেন্টে গেলে আমরা মাংস খাই কি না সেটা খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে, কারন অনেকেরই ধারনা, ভারতীয়রা সবাই ভেজিটেরিয়ান। যদিও কেউ কেউ ইংরেজী বলার ধরন থেকে ভারতীয় ও বাংলাদেশীদেরকে আলাদা করতে পারে, তবে তাদের সংখ্যা খুবই নগন্য। অবশ্য তাদেরই বা দোষ কি, আমরাও যেমনটা মধ্যপ্রাচ্যের সব মানুষকে একই রকম মনে করি। আমাদের চোখে সবাই আরব, কারন তাদের চেহারা ও ভাষা একই, অথচ লেবানীজ, সিরিয়ান ও ইরাকীদের মধ্যে যোজন যোজন পার্থক্য, যা আমাদের খালি চোখে ধরা পড়ে না।
এমন কিছু ক্লায়েন্ট পাই, যারা ট্যাক্স রেট এত বেশী কেন সেই প্রশ্ন করে বসে আমাকে, যেন আমি ট্যাক্স অফিসের বড়কর্তা! এদেশে ট্যাক্স রেট বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বেশী। ব্যক্তিগত আয়ের উপরে ট্যাক্সের হার বাংলাদেশে ০, ১০, ১৫, ২০ এবং সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ হয়ে থাকে, আর অস্ট্রেলিয়ায় সেটা ০, ১৯, ৩২.৫০, ৩৭ এবং সর্বোচ্চ ৪৫%। কারো বার্ষিক আয় ৩৭,০০০ ডলার ছাড়ালেই ৩২.৫০% ট্যাক্স, যা আয়ের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। বার্ষিক আয় ১৮০,০০০ এর উপরে হলে ১৮০,০০০+ আয়ের প্রায় অর্ধেকই নিয়ে যায় ট্যাক্স অফিস। কাজেই অনেকেই প্রশ্ন করে, এত বেশী স্যালারীর কাজ করে তাহলে ফায়দাটা কি? যৌক্তিক প্রশ্ন। আমাকে উত্তর দিতে হয় ডিপ্লোম্যাটিক কায়দায়। এদেশের মানুষজন আবার সরকার অথবা যেকোন ধরনের কর্তৃপক্ষকেই অপছন্দ করে, কাজেই সরকারের চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার করলে তাদের সহানুভুতি পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।
আমি শুরু করি এভাবেঃ ট্যাক্স না দিলে টনি এবট যে টিভির পর্দায় মুখ দেখিয়ে বেড়াচ্ছে রোজ রোজ, তা সম্ভব হবে কি করে? তবে শুধু টনি এবট নয়, তুমি-আমিও উপকার পাচ্ছি এই ট্যাক্স থেকে। এই যে রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, এসবের টাকা আসে তো তোমাদের দেওয়া ট্যাক্স থেকেই। বেশীর ভাগ ক্লায়েন্ট এই পর্যন্ত শুনে বোঝার ভাণ করে চুপ করে যায়, যদিও উপার্জিত ডলার ট্যাক্স অফিস নিয়ে যাচ্ছে দেখে তাদের মনটা খচখচ করতে থাকে। ট্যাক্স অফিসকে তো আর বাগে পায় না, কাজেই আমাকেই সামনে পেয়ে হয়তো ট্যাক্স অফিসের দালাল মনে করে গালিগালাজ করতে থাকে মনে মনে। তবে কিছু ক্লায়েন্ট নাছোড়বান্দা, তারা এর পরেও প্রশ্ন চালিয়ে যায়। বলে যে, তারা ট্যাক্স দিতে রাজী, তবে সবার ট্যাক্স রেট সমান হতে হবে! অনেকে বলে, দেশে বেকার ভাতা দেওয়া বন্ধ করতে হবে, কারন সেটা নাকি মানুষকে অলস বানাচ্ছে আর বসে বসে সরকারী পয়সা খাওয়ার উতসাহ যোগাচ্ছে। কথাটা সর্বৈব মিথ্যা নয়-এদেশে একদল মানুষ আছে যারা আসলেই বেকার ভাতা খাওয়াটাকে পেশা হিসেবে নিয়েছে।
যে পরিমান টাকা দেওয়া হয় মাসে, তাতে একটু গরীবী হালে হলেও চলে যায় বা চালায়ে নেয় অনেকে, আর বাচ্চাকাচ্চা থাকলে তাদের জন্যও মাসে মাসে টাকা পায়, সব মিলিয়ে নেহায়েত খারাপ না। যারা সিঙ্গেল মাদার বা কুমারী মা, (কুমারী বলাটা ঠিক হল না বোধ হয়, মাতা মেরী বা মরিয়ম তো দুনিয়ায় একটাই। সম্ভবতঃ সঠিক ভাষান্তর হবে অবিবাহিতা মাতা) তারা সাধারন বেকারদের চেয়ে বেশী পান, সঙ্গে আবার বাচ্চার জন্য টাকা, পাবলিক ট্রান্সপোর্টে কনসেশান, সব মিলে কাজ না করলেও বেশ ভালোই চলে। এর উপরে আছে চাইল্ড সাপোর্ট, অর্থাৎ যে পুরুষ পার্টনারের ঔরস্যজাত বাচ্চা, তার আয়ের পরিমান বেশী হলে তাকেও কিছু টাকা দিতে হয় ঐ অবিবাহিতা মাকে, বাচ্চার লালন পালনের জন্য। এক ক্লায়েন্ট তো আমাকে বলে বসল, সে নিজে সপ্তাহে ৬ দিন কাজ করে, আর তার আগের গার্লফ্রেন্ড এক বাচ্চা নিয়ে মহানন্দে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ায়। কেমন বৈষম্যমুলক সিস্টেম! আমি বলি, ‘সব সিস্টেমকেই কিছু মানুষ অপব্যবহার করবে, যদিও সেটা আইনসঙ্গতভাবেই, কিন্তু তার জন্য কি আর পুরো সিস্টেমকে দোষ দেওয়া চলে? তাছাড়া, তোমাদের দেশে তো সবাই একটা ন্যুনতম স্ট্যান্ডার্ডের জীবন যাপন করে, অথচ ভারত কিম্বা আফ্রিকায় অনেক দেশে মানুষ না খেয়েও মারা যায়। তোমরা কাজ করে ট্যাক্স দিচ্ছ বলেই কিন্তু সরকার সবার দেখাশোনা করতে পারছে, আবার তুমি নিজেওতো রিটায়ারমেন্টের পরে পেনসান পাবে।
এভাবে যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী সবাই দেয় এবং যার যার প্রয়োজন অনুযায়ী সবাই পায় বলেই সমাজে সম্পদের পুনর্বন্টন হচ্ছে, যা না হলে সমাজের বৈষম্য দিন দিন আরো বাড়ত’। কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না, শেষে কাষ্ঠ হাসি হেসে বিদায় নেয়। বিদায় নেওয়ার আগে আমাকে আরো একটা অপ্রিয় কাজটা করতে হয়, ফি নিতে হয়। তখন অনেকের ভাবটা থাকে এরকমঃ ট্যাক্স দিতে পারলাম এত টাকা, আর সামান্য ট্যাক্স কনসাল্টেন্টের ফি দিতে বাধবে কেন! কথায় বলে, অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর।
আগেই যেমনটা বলেছি, এদেশে একজন আয়করদাতা সিঙ্গেল নাকি তার পার্টনার আছে, সেটা ইনকাম ট্যাক্সের সময়ের এক বড় প্রশ্ন। এদেশে পার্টনার অথবা স্পাউস কথাটা ব্যবহার করে, হাজবেন্ড বা ওয়াইফ নয়, কারন বিয়ে না করেও দুজন মানুষ একসঙ্গে থাকতে পারে এবং নিজেদেরকে পরিবার হিসেবে দাবী করতে পারে। আবার, কেউ বিয়ে করে থাকলেও, ম্যারেজ সার্টিফিকেট জাতীয় কোন কাগজের বালাই নেই, পারস্পরিক মৌখিক স্বীকৃতিই যথেষ্ঠ। সেজন্য ট্যাক্স অফিস কারো বৈবাহিক অবস্থা জিজ্ঞেস করে না, শুধু জিজ্ঞেস করে পার্টনার ছিল কি না, থাকলে কতজন (একসঙ্গে একাধিক পার্টনার থাকতে পারবে না), কোন কোন তারিখের মধ্যে। এরকমও পেয়েছি, যেখানে বছরের শুরু থেকে প্রথম ছয় মাস এক পার্টনার, পরের ছয় মাস আরেকজন পার্টনার। এখানেই শেষ নয়, পার্টনার সেম-সেক্সও হতে পারবে, অর্থাৎ একজন পুরুষ আরেকজন পুরুষকে অথবা একজন নারী আরেকজন নারীকে তার পার্টনার দাবী করতে পারবে, যদিও এদেশে সেম-সেক্স বিয়ে এখনও আইনগতভাবে বৈধ নয়। প্রথম দিকে দুএকবার ক্লায়েন্টকে পার্টনারের কথা জিজ্ঞেস করার সময় সেম-সেক্স পার্টনার হলে আমার একটু কেমন যেন খটকা লাগত, পরে অবশ্য সেটা গা-সহা হয়ে গিয়েছিল।
অস্ট্রেলিয়াতে মুসলিমরা এসেছেন মুলতঃ দক্ষিন এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের নানান দেশ, উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, পুর্ব ইউরোপের কিছু দেশ, মালয়েশিয়, ইন্দোনেশিয়া এসব দেশ থেকে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে অনেক অমুসলিমও এসেছেন এখানে, যাদের নাম এং ভাষা দুইই আরবী। কাজেই কারো নাম আরবী হলেই যে সে মুসলিম, তা নয়। আবার, কারো ধর্ম ইসলাম হলেও তার নাম আরবী নাও হতে পারে। অনেক ক্লায়েন্ট, যারা আরবী ভাষাভাষী দেশের লোক, তারা আমার নাম দেখেই আন্দাজ করে যে আমি মুসলিম। আবার অনেক ক্লায়েন্টের নাম দেখে আন্দাজ করার উপায় নেই তারা কোন ধর্মের। আমি অনেক ক্লায়েন্ট পেয়েছি খলিল, রফিক, আহমেদ, এই সব নামের, যারা মুসলিম নয়। আবার একবার এক দীর্ঘদেহী শেতাঙ্গ ক্লায়েন্ট আমাকে অবাক করে দিয়ে সালাম দিয়ে বসল, আমার নাম দেখেই। প্রশ্ন করলাম, কি করে এত নিশ্চিত হলে যে আমি মুসলিম? তার নিখুঁত উত্তর, ইন্ডিয়ায় আরবী নামধারী অমুসলিম নেই একটাও। কথা সত্যি। সে নিজে ছিল মুসলিম, যদিও তার যুগোশ্লাভ নাম দেখে আমার সাত পুরুষেরও উপায় ছিল না সেটা আন্দাজ করা।
ভাষা মানুষকে একসূত্রে বাঁধতে বেশ বড় ভূমিকা রাখে। আমি অনেক শক্তমুখের ক্লায়েন্টকে তাদের ভাষায় হ্যালো/স্বাগতম বলেই নরম করে ফেলি। ভাষা দিয়ে আলাপ শুরু হয়। অনেকেই তাদের বাবা-মা’র ভাষা বলতে, পড়তে ও লিখতে পারে। আবার অনেক ইতালিয়ান, গ্রীক, আরব, পোলিশ বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলিয়ানকে আক্ষেপ করতে দেখেছি এই নিয়ে – তারা বাবা-মা’র ভাষায় শুধু কথা বলতে পারে, কিন্তু সেই ভাষার সাথে সত্যিকারের কোন পরিচয় নেই। ফলে আগ্রহ থাকা সত্বেও তাদের বাবা-মা’র আগের দেশের সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিষয়ে জানাটা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তাদের জন্য। তারা আমার মত ওই হাই-হ্যালোতেই সীমাবদ্ধ। একবার এক বাঙালী মেয়েকে পেয়েছিলাম, যে আমাকে ফোনে তার নাম বলল, ন্যাবানিটা ছাহা। আমি শুনেই বুঝলাম, এ তো নবনীতা সাহা – বাঙালীর নাম। জিজ্ঞেস করলাম, বাংলা বলতে পারেন? সে ভাঙা ভাঙা বাংলিশে বলল, হ্যাঁ আমি বেঙ্গলি, কিন্টু বাংলা ভালো পাড়ি না। আমার বাবা-মা’ড় সাথে বাংলা বলি। পরে শুনলাম, সে বাবা-মা’র সাথে থাকে না। এরপরে যা হয়, অস্ট্রেলিয়ান জীবনে অভ্যস্ত এসব ছেলেমেয়েরা আর তাদের বাবা-মা’র ভাষায় কথা বলার কাউকে খুঁজে পায় না। ভাষাটা হারিয়ে যায়। ন্যাবানিটা ছাহাদের বাচ্চারা বাংলাভাষার নামটাই জানতে পারে না। মাত্র এক প্রজন্ম পরেই বাংলাভাষার অপমৃত্যু। অথচ তার বাংলা অক্ষরজ্ঞান থাকলে এবং পড়ার অভ্যাস থাকলে সে পরিবারের বাইরে পা দেওয়ার পরে কখনো বাবা-মা’র জীবন ও জগত নিয়ে কৌতুহল বোধ করলে তখন এ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারত। আজকে তাদের বাংলার প্রতি যতই নাক সিঁটকানো ভাব থাকুক, আমি নিশ্চিত যে আমাদের বাচ্চারা সেই কৌতুহল একদিন বোধ করবেই। তখন বাংলা নতুন করে শেখাটা তাদের ব্যস্ত জীবনে পাহাড়সম হবে – তারা সেই কৌতুহল আর মেটাবে না তাদের জীবনের ব্যস্ততার তাল মেলাতে গিয়ে। অথচ বাংলা অক্ষরজ্ঞান থাকলে, হাতের কাছে দু’একটা বাংলা বই থাকলে, পড়ার অভ্যাস থাকলে তারা হয়তো সে সময় নতুন আগ্রহে বাংলাদেশকে জানতে চেষ্টা করবে, পূর্বপুরুষকে বুঝতে চেষ্টা করবে, এবং তাদের অস্ট্রেলিয়ান ভয়েস দিয়ে বাবা-মা’র সংগ্রামের কথা অন্যদেরকে গর্ব করে বলতেও পারবে। ভিয়েতনামীজ/ইতালিয়ান/গ্রীকদের কমিউনিটিতে এখন সেটা হচ্ছেও। এলিস পাঙ ও আমরা পায়ালিচের মত দ্বিতীয় প্রজন্মের লেখকেরা অভিবাসীদের সংগ্রামের কথা লিখছেন এই দেশে, তাদের নিজেদের ভাষা-সংস্কৃতির জানাশোনা এবং অস্ট্রেলিয়া্ন ভয়েস থাকার সুবাদে।
এমনি আরো কত অভিজ্ঞতা হলো! এমন ক্লায়েন্ট পেয়েছি যারা বাংলাদেশের নামই শোনেনি, আবার এমন ক্লায়েন্ট পেয়েছি যারা খুলনা, সিলেট পর্যন্ত চেনে। এমন মানুষ পেয়েছি যারা মাল্টিকালচারাল অস্ট্রেলিয়াকে স্বাগত জানায়, আবার অনেকে আছেন যারা এশিয়ান (ইন্ডিয়ান সমেত) অভিবাসীদের আন-অস্ট্রেলিয়ান ভ্যালুজ নিয়ে চিন্তিত (আন-অস্ট্রেলিয়ান বা অস্ট্রেলিয়ান ভ্যালুজ আসলে কি বস্তু, তা আমি এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। পরের কোন ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

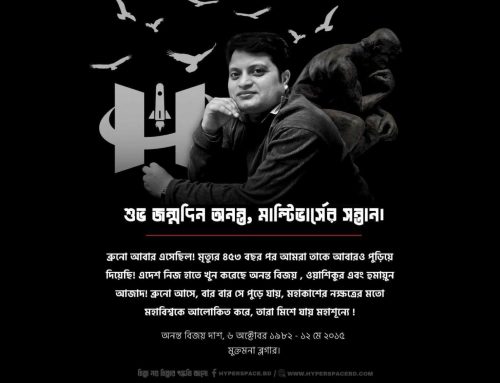
চমৎকার!
মজা লাগলো পড়ে। বিজ্ঞান, ধর্ম, ইতিহাস এসব বহু-চর্চিত বিষয়ের পাশাপাশি এমন অন্যকিছু নিয়ে আরও লেখা আসুক মুক্তমনায়। নতুন দেশ, নতুন মানুষ, বিশেষতঃ নতুন সংস্কৃতি নিয়ে পড়তে খুব ভালো লাগে। আপনার মতো যাদের দেশের বাইরের অভিজ্ঞতা আছে তারা প্লিজ আরো ঘনঘন সেসব অভিজ্ঞতার কথা লিখুন।
আজ অবদি আয়কর দেওয়া হলো না। আয়ই নাই আবার কর। বাটে পড়ে বাংলাদেশে ইনকাম ট্যাক্সের রেজিস্ট্রেশন করেছিলাম। আয়কর দেবার যোগ্য না হওয়া স্বত্তেও শুধু গিয়ানজাম দেখে গত তিন বছর রিটার্ন দেখানো হয় নি আলসেমিতে 🙁
অসুবিধা নেই, সময় যখন আসবে তখন দিবেন। সবাই ট্যাক্স দিলে এবং সেই ট্যাক্সের সুষম ব্যবহার হলেই না দেশ এগুবে।
প্রাবাসীদের সন্তানরা হালকা-পাতলা বাংলা বুঝতে এবং বলতে পারলেও এক সময় ওরা বাংলা ভুলে যায়। ওদেরকে বাংলা লিখতে-পড়তে শেখানোও খুব কষ্টকর, মোটামুটি অসম্ভব বলা চলে। আর ওদের সন্তানেরা ত বাংলার নামও শোনে না। এভাবে মাত্র এক প্রজন্ম পরেই বাংলাভাষা হারিয়ে যায় বাংলাভাষী উত্তরসূরীদের কাছ থেকে। এই বাস্তবতার কথা ভাবলে বুকে মোচড় দেয়। কিন্তু কী করা যাবে?
চেষ্টা, চেষ্টা আর চেষ্টা। চেষ্টা করার চেষ্টা করছি।
ধন্যবাদ মেহেদী। ভাল লেগেছে জেনে ভাল লাগল, যদিও শিরোনামের ব্যাপারটা ভাবাচ্ছে।
শিরোনাম দেখে প্রথমে ভেবেছিলাম বাজেটে Vat on Education নিয়ে কিছু হয়ত লেখা। ভেতরে পুরোপুরি ভিন্ন। ভাল লেগেছে লেখাটা, অন্য দেশ নিয়ে কিছু জানার আগ্রহ সবসময়ই বোধ করি। ধন্যবাদ।