১৩/১/ রাত ২-৪৭ মি.।
ফেব্রুয়ারিতে মাকে চিকিৎসার জন্যে ভারতে নেওয়া হল; মার অবস্থা তখন অবনতির পথে, সামনে আমার এস.এস.সি পরীক্ষা – নিজেকে ভুলিয়ে রাখার একটা ভালো উপলক্ষ পেয়েছিলাম। সকালে মাকে মেহেরপুর থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হল। আমি তখন মল্লিক পাড়ায় মামুন ভাইয়ের কাছে প্রাইভেট পড়তাম; সেদিন পড়া শেষ না করেই চলে আসলাম। আমি মার পাশের সিটে সহযাত্রীর মতো বসে ছিলাম- অনেকক্ষণ। খুব বেশি কথা বলার সুযোগ পাইনি সেদিন, মা খুব চিন্তামগ্ন ছিলেন। মার চোখে মুখে সেই প্রথম বারের মতন অনুভব করলাম বেঁচে থাকার ভয়ংকর আকুতি। আমি যখন গাড়ি থেকে নেমে আসলাম মা চোখের ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন – ভয় নেই, আমার কিছুই হবে না। আমার ভয় উবে গেল নিমিষেই। বাস ছেড়ে দিল – আমি পিছন পিছন সাইকেল চালিয়ে অনেকদূর গিয়েছিলাম। কিছুদূর যেতেই আমাদের ব্যবধান বেড়ে গেল, বাসটি এক ঝটকায় আমাকে ছিটকে দৃষ্টির অলক্ষ্যে নেই হয়ে গেল। তখন মেহেরপুরের ওয়াবদার চারপাশের মাঠে কাশফুলের বন্যা হয়েছিল যেন। আমি সাইকেল নিয়ে জমির আইল ধরে কাশফুলের নদীতে নেমে পড়লাম। হালকা বাতাসে বাড়ি খেয়ে সাদা শুভ্র কাশফুল প্রজাপতি হয়ে সূর্যের আলোর মাঝে লুকোচুরি খেলছিল। সকালের সূর্য তখন কচি খোকার মতন খিলখিল করে হেসে উঠছে। আমি ওদের মাঝখানে গিয়ে বসলাম। আমার হাতে গালে কপালে মাথায় ছুঁয়ে গেল সাদা প্রজাপতিগুলো। ওদের মমতার স্পর্শ নিজেকে খুব হালকা মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমি মানুষ থেকে, সভ্যতা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি, এখানেই কেটে যাবে আমার অনন্তকাল। কারণ ছাড়াই আমার গাল বেয়ে কয়েক ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। পৃথিবীর বাইরে এসে পৃথিবীটাকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করলাম সেদিন – না, অতটা মন্দ না পৃথিবী নামক জায়গাটা। ফিরে আসলাম বাড়িতে, বুক পকেটে রয়ে গেল একগুচ্ছ শুভ্র কাশফুল।
মা যতদিন ভারতে ছিলেন, খুব ফাকা মনে হচ্ছিল চারপাশ। কাউকে জিজ্ঞেস করতাম না- মা কেমন আছে, কবে আসবে। শুধু সন্ধ্যের আগ দিয়ে কাশবনে গিয়ে চুপ মেরে বসে থাকতাম। মা আসার পর আর কোনদিন ওখানে যাইনি। মা যেদিন বাড়িতে আসলেন, আমি দূর থেকে মাকে দেখছিলাম। তাঁকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। ১লা এপ্রিল রাতে ডায়েরীতে লিখে রাখি – ‘এ মাসেই আমার জীবনের খুব মূল্যবান কিছু একটা হারাতে যাচ্ছি!’ এপ্রিল মাসের বাকিটা দিন মার খুব কষ্টে গত হয়েছে – বিশেষ করে রাত। প্রতিদিন শেষ রাত অবধি তল পেটের তীব্র ব্যথায় প্রচন্ড-বীভৎস ভাবে চিৎকার করতেন। এখনো অন্ধকারে কান পাতলে সেই ভয়ংকর শব্দ আমি শুনতে পাই। আমি তখন থাকতাম ওপরের ঘরে; মা যতক্ষণ যন্ত্রণায় কোকাতো আমি ততক্ষণ বারান্দায় বসে থাকতাম – নিশ্চুপ, বৃক্ষের মতন মৃতের ভান করে, পাশের ঘরে খালিদ (আমার ছোট ভাই) ঘুমানোর ভান করে পড়ে থাকতো। এত কষ্টের মাঝেও সৃষ্টিকর্তার ওপর মার এত অগাধ বিশ্বাস আর আস্থা দেখে আমি আশ্চর্য না হয়ে পারতাম না। ব্যথা যত তীব্র হত মা বলত – ‘আল্লাহ তুমি আমাকে দুনিয়াতে যত ইচ্ছে কষ্ট দাও তবু আমাকে গোরের আজাব থেকে মুক্তি দিয়ো। আমি দুনিয়ার কষ্ট সহ্য করতে পারবো, কবরের আজাব পারব না।’ কল্পিত সঙ্গীত যদি সবচেয়ে মধুর হয়, কল্পিত আঘাতও যে সবচেয়ে তিক্ত হবে সেটাই স্বাভাবিক! তা না হলে, দুনিয়ায় যে জীবন মা যাপন করে এসেছে তাতে করে আর কোনও কষ্টই কষ্ট মনে হবার কথা নয়। শারীরিক-মানসিক কোন কষ্টই মানুষটাকে জয় করতে পারেনি; কোথা থেকে যেন একটা বিশ্বাস এসে সবকিছু শান্তিময় করে তুলতো! মা কষ্টে ছটফট করতে করতে কখনো কখনো একদম স্তব্ধ হয়ে যেতেন, ঘরের ভিতরে মাঝে মধ্যে টিকটিকির ঠিকঠিক শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা যেত না। আমি জানতাম, মা চলে যায়নি, তার কষ্টও আগের মতোই আছে। সে শুধু ক্লান্ত, এই যা। কিংবা সে কিছুক্ষণের জন্যে ভালো থাকার ভান করছে। আমি অপেক্ষা করতাম। তাঁর নীরবতা আমাকে জাগিয়ে তুলত। ঘরের আসবাবপত্র ও এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাপড়চোপড়ের সাথে আমি কথা বলতাম। মা কিছুক্ষণ পর বলত, ‘এখনো জেগে আছিস!’ কিংবা, দিন হলে, ‘আজ স্কুলে যাসনি?’ আমি কোনও কথা না বলে উপরে আমার ঘরে চলে আসতাম। রোজ রোজ একই উত্তর দিতে ভাল লাগতো না। মাঝে মধ্যে রাতে হারিকেনের কাচে কাপড় গরম করে মার তলপেটে সেঁকে দিতাম, একটু শান্তি পেতেন, বোধহয়। একদিন প্রায় ভোর রাত অবধি আমি আর বাবা পালা করে মার পেট সেঁকে দিয়েছিলাম, মা কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন – তাঁর জন্যে এর বেশি কিছু করার সুযোগ আমি আর পাইনি, খুব সম্ভবত বাবাও।
তখন মার টক খাওয়া নিষেধ ছিল। লিভার সিরোসিস হলে লিভারে প্রচুর পানি জমে, এ জন্যেই বোধহয়। কিন্তু মা শুনবে না। আমি জীবনে কখনো মাকে ডাক্তারের নির্দেশ মেনে চলতে দেখিনি। মা অনুরোধ করতো টক আঙুর আর কদবেল এনে দিতে। আমি বেরিয়ে পড়তাম সন্ধানে। তখন টক আঙুর আর কদবেলের সময় না। মেহেরপুরের প্রতিটা দোকানের আঙুর চেখে দেখতাম, প্রায় প্রতিদিনই। যে আঙুরই আনি, মা ছুড়ে ফেলে দেয়, বলে – ‘না, একটুও টক না। তোদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না।’ মা আমাকে বকাবকি করতেন। আমাদের বাড়ি থেকে বহু দূরে একটি কদবেল গাছ ছিল, আমি ঐ পনের দিনে তিনবার গেছি ঐ গাছটির কাছে – যদি এর মধ্যে ভুল করে হলেও একটি পেয়ে যাই! মিরাকল যে পৃথিবীতে একেবারে ঘটে না, তা তো নয়। গাছটির কাছে কত ভিক্ষে চেয়েছি, শোনেনি। প্রকৃতি মানুষের ভাষা বোঝেনা বোধহয়। বুঝলে সেদিন ও আমাকে ফেলতে পারত না। মাকে আমি টক আঙুর, কদবেল কিছুই এনে দিতে পারিনি। মা জেনে গেছেন- আমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না, আমিও মেনে নিয়েছি তা। প্রথম দিকে বাজারে কদবেল আর টক আঙুর দেখলে বুকের ভেতরটা জ্বলে যেত, ইচ্ছে করত পৃথিবীর সব আঙুর আর কদবেলের গাছ পুড়িয়ে ছাই করে দিতে। এখন আর কিছু মনে হয় না।
এক সন্ধ্যায়, মা আমাকে আর খালিদকে ডেকে বললেন – ‘আমি না থাকলে তোরা কি করবিরে !’ আমি ধমকের সুরে বলেছিলাম – কি সব আবোল-তাবোল বকছ ! তুমি না থাকলে, তুমি যেখানে যাবে তোমার সাথে সাথে আমরাও যাবো। আমার কথা শুনে মা হেসেছিলেন; বলেছিলেন – ‘পাগল! শোন্, আমি মারা গেলে তোরা আমার পাশে কাঁদবিনা, আমি সহ্য করতে পারবো না।’ এ কথাগুলো হওয়ার কিছুদিন পর (২৫/৪/২০০২ তারিখে) মা আমাকে তাঁর ড্রয়ারের চাবি দিয়ে বললেন – ‘নে, ড্রয়ারের চাবিটা রাখ; কিছু টাকা আছে, তোর আববাকে জানাবিনা। কোনও বোনের কাছে রেখে দিবি আর টুকটাক হাত খরচ লাগলে চেয়ে নিবি; ওরা তো নিজের টাকা সবসময় দিতে পারবে না। তাছাড়া তোর আববার কাছে টাকা গেলেই পানি হয়ে যায়। আর তোর আববাকে আমি চিনি, আমি মরে গেলে সে আবার বিয়ে করতে চাইবে, তোরা কেউ বাধা দিবি না। তোদেরকে আমি আল্লাহর কাছে রেখে গেলাম, এর থেকে নিশ্চিন্ত আর কিসেই বা হতে পারি!’ সেদিন মা যতক্ষণ কথা বললেন আমি আর একটা শব্দও করিনি, করতে পারিনি। শুধু মনে পড়ে বাথরুমে ঝর্না ছেড়ে অনেকক্ষণ কেঁদেছিলাম সেদিন।
মা তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে খুব ভালো ভাবেই অবগত ছিলেন। খুব কম মানুষই মৃত্যুর সাথে দিনক্ষণ ঠিক করে শান্তিপূর্ণভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারে, মা পেরেছিলেন। শেষের দিকটাই সে জীবন মৃত্যুর ঠিক মাঝখানটাই অবস্থান করেছিল। দুই জগতের সাথেই তাঁর তখন সমান সম্পর্ক। আমাকে চাবিটা দেওয়ার ঠিক দুই দিন পরেই মা চলে গেলেন। ড্রয়ারে আমি ৬৫ হাজার টাকা পেয়েছিলাম। টাকাটা আমি আমার এক বোনকে দিয়েছিলাম। সে আবার বাবাকে দিয়ে দেয়। পরে শুনেছি, টাকার কিছু অংশ বাবা পরবর্তীতে তাঁর বিয়েতে খরচ করেছিল, কিছুটা আমাদের পেছনে, কিছুটা সংসারে। আমাদের অবশ্য খুব বেশি সমস্যা হয়নি কারণ মা আগে থেকেই বোনদের কাছে কম বেশি টাকা রেখেছিল যাতে করে আমি আর খালিদ অন্তত এই একটা জায়গায় অভাব বোধ না করি। ব্যাংকে আমার আর খালিদের জন্যে বিপদআপদ বাবদ ১ লক্ষ টাকা রেখে যাওয়ার কথা অবশ্য আগে থেকেই জানতাম।
৩/২, রাত ১ টা।
মা যেদিন চলে গেলো –
প্রচন্ড গরমের আবহে কোথায় থেকে যেন ঠান্ডা হিমশীতল বাতাস আসছিল। আমাদের দুটো দো-তোলা বাড়ী; দুটোই প্রায় মার গোছানো অর্থ ও সাধনাই বানানো। অথচ মা মারা গেলেন ছোট্ট একটা স্টোর রুমে (আমাদের সুবিধার জন্যে মা নিজেই বেছে নিয়েছিলেন রুমটি)। আমরা ছিলাম ৪ ভাই ৮ বোন; মা যখন শেষ বারের মতন আমাদের দেখতে চাইলেন – আমি এবং আমার দুটো বোন তাঁর পাশে ছিলাম, বাবা ছিলেন রান্না ঘরে। মার অসুস্থ অবস্থায় রান্নার দিকটা বাবাও কিছুটা সামলাতেন। বাবাকে দেখতে চাইলেন ঠিকই কিন্তু ততক্ষণে শেষবারের মতন কলেমা পড়া ও আল্লাহর নাম নেওয়া হয়ে গেছে। আমি তখন উপরে সিনেমা দেখছিলাম। আমি কান্নাকাটির শব্দ শুনে, টিভি অন রেখেই নিচে নেমে আসলাম। নামার সময় হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে আমার ডান কানের কিছুটা অংশ ছিঁড়ে গেল। আমার আসার কিছুক্ষণ পর বাবাও এলেন। আমি মার এক হাত শক্ত করে ধরলাম অন্যটি বাবা। খালিদ মার খারাপ অবস্থার খবর নিয়ে ইতোমধ্যে আমার সাইকেল নিয়ে গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে। আমি যখন ক্লাস এইটে উঠলাম মা তখন এই ফনিক্স সাইকেলটি কিনে দিয়েছিল। মা যখন নিস্তব্ধ-নিথর হয়ে পড়ল – রান্না ঘর থেকে বিড়ালের মিউ মিউ শব্দ গেল থেমে, সানসেটে বসে থাকা পায়রা দুটো ঝটপট করে উড়ে গেল, বরই গাছের পাখিগুলোর কিচির-মিচির শব্দ থেমে গেল; ক্ষণিকের জন্যে যেন পৃথিবীর সবকিছুই থমকে গেল, সহসা আমার বোনদের কান্নাই প্রাণ ফিরে পেল প্রকৃতি; আমি তখনো আশা হারাইনি। সত্যি বলতে, যদিও জানতাম, মার হাতে সময় বেশি নেই, তবুও মা এভাবে চলে যাবে, বিশ্বাস করতে পারছিলাম না কিছুতেই। খুব কাছ থেকে মার চলে যাওয়া দেখলাম, তবুও টের পেলাম না কিছুই। মার চেহারা আস্তে আস্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আর কোনো কষ্ট নেই, বেদনা নেই, নেই কোনও আনন্দ। আছে শুধু নীরবতা। থমথমে নীরবতা। এটাই কি তবে জীবন?
আমরা তখনই মাকে নিয়ে গ্রামের বাড়ি রওনা হলাম। মাঝপথে দেখি খালিদ মার খারাপ অবস্থার খবর গ্রামে দিয়ে আবার ফিরে আসছে। ওকে আবার ফিরে যেতে হল গ্রামে। একদিন মা-ই আমাদের শহরে নিয়ে এসেছিল আজ আবার মা-ই আমাদের গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওই যে গেলাম, আর আমরা শহরের বাড়িতে ফিরলাম না। কিছুদিন পরে শহরের বাড়ি ফাঁকা করে ভাড়াটিয়া উঠিয়ে দিলাম।
মার মৃত্যুতে আমরা ছোট দু’ভাই পাথরের মতো জমে গিয়েছিলাম। আছরের পর মার জানাযা হল। গ্রামে জানাযায় এত লোকসমাগম খুব কমই হয়েছে। সবাই ছিল, শুধু ছিল না আমার বড় ভাই আর মেঝো ভাই। মেঝো ভাই তখন সৌদিতে, আর মিয়া ভাই ঢাকা থেকে বাড়ির পথে। শুনেছি, আমার বড় ভাই যখন হয় তখন গ্রামের সমস্ত মানুষকে গরু জবাই করে খাওয়ানো হয়েছিল। তারপর হয় মেঝো ভাই। সাত মেয়ের পর পরপর দুই ছেলে হওয়াতে দাদির অত্যাচার আর বাবার অবহেলার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল মা। মার তখন সাত রাজার ধন তারা। অথচ শেষ জীবনে এসে তাদের সাথেই মার সবচেয়ে বড় দূরত্বটা তৈরি হল। তাদের বউদের সাথেও মার কোনও বনিবনা হল না। একজনের জন্যে মা গ্রামের বাড়ি ছেড়ে শহরের বাড়ি পালিয়ে আসলো, অন্যজন ঘটনাচক্রে মাকে বাসা থেকে বের করে দিল। মানুষে মানুষে বোঝাপড়ায় এত ফারাক! মার খাটিয়া ধরেছিলাম আমি ও আমার ভগ্নীপতিরা। আমরা পরপর এক মুঠ এক মুঠ করে মাটি দিয়ে মাকে আস্তে আস্তে গায়েব করে দিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে মার অস্তিত্ব চিরকালের মতো নেই হয়ে গেল। মা যে একসময় ছিল, তার বড় প্রমাণ এখন আমরাই, এছাড়া আর কোনও প্রমাণ রইল না। অনেক কেঁদেছিলাম সেদিন! আজো ঘরের দরজা বন্ধ করে কেঁদে হাল্কা করি নিজেকে। মা হয়ত টের পান না কিছুই, কিংবা আমার সাথে সাথে মাও কাঁদেন, আমি টের পাই না কিছুই। আমাদের কান্না মা সহ্য করতে পারবেন না, আমাদের বলেছিলেন একদিন। সেই কথা মনে হলে আরও কাঁদতাম, যদি সহ্য করতে না পেরে মা আবার দুম করে চলে আসেন – এই আশায়! তখন মনে হত, মিরাকল তো কখনও কখনও ঘটেও যায়!
বাবা সত্যি সত্যিই পরে আবার বিয়ে করলেন। আমরা কেউই বাধা দিইনি। মার শেষ কথাটা আর ফেলতে পারিনি। আর তাছাড়া, বাবা আর খালিদ তখন গ্রামের বাড়িতে একরকম একাই। আমি চলে এসেছি কুষ্টিয়াই, পড়াশুনা করতে। আজ হোক কাল হোক খালিদও যাবে। তাই বাবাকে বাধা দেওয়াটা যুক্তিহীন ছিল। তবে একথা ঠিক, বাধা না দিলেও আমরা কেউই মানতে পারিনি বিষয়টি। আজও। কিন্তু এডজাস্ট করতে হল, যেমন করে মার চলে যাওয়ার সাথে করলাম, তেমন করে। তবে এখন বুঝতে পারি মা কেনও সেদিন বাবাকে বাধা দিতে বারন করেছিল। বাবার কষ্ট হোক মা সেটা কখন চায়নি। এখন (১৩/৩/১২) বাবার বয়স প্রায় ৮০ ছুঁইছুঁই। বর্তমান স্ত্রীকে নিয়ে আমাদের গ্রামের বাড়িতে থাকেন। মা থাকেন একটু দূরেই। আমরা বছরের দুটো ঈদে একত্রিত হয়। ঈদের নামায শেষে কবরে মার পাশে যাই – আমি, মিয়া ভাই আর খালিদ। ওরা যায় মার জন্যে দোয়া করতে, আর আমি যাই মার গন্ধ শুঁকতে, কবরের স্যাঁতসেঁতে মাটি চেটে চেটে আমি মার গন্ধ শুখি, স্পর্শ নিই। মার জন্যে আমি কি দোয়া করব! আমার সে শক্তি কোথায়? সৃষ্টিকর্তা কি নীরবতার শব্দ বোঝেন না?
মার সাথে আমার অনেক কথা হয়। প্রাণভরে কথা বলি দু’জনে। মা যখন সংসারে ছিলেন, তখন আমার সাথে কথা বলার সময় পেতেন না খুব একটা। বড় একটা সংসারের ঝামেলা বহন করাতেই ব্যস্ত থাকতেন সর্বদা। আমি স্কুল থেকে ফিরে উপরের এক ঘরে বসে থাকতাম, কখনো ছাদের ওপর। কথা বলতাম গাছপালা আর পাখিদের সাথে। কিংবা কারো সাথেই না। বাবা যখন কারণ ছাড়ায় মাকে বকাঝকা করতেন, এটা ওটা এদিক ওদিক ছুড়ে মারতেন, আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম কিংবা ডাল দিয়ে ভাত মাখা প্লেটে এটাসেটা অাঁকাঅাঁকি করতাম। ভাই-বোনেরা যখন বিভিন্ন কারণে মাকে অভিযোগ করত, অকারণে বাবার পক্ষ নিতো, আমি জড়সড় হয়ে বসে থাকতাম বাড়ির পিছনের আমগাছটির মাঝ-ডালে। আজ মার কোন সংসার নেই, অভিযোগ করারও কেউ নেই। আছে শুধু অখন্ড অবসর। আজ আমার সংসার হয়েছে, আছে অভিযোগ করার মতো অনেকেই। এখন আমার একখন্ড অবসর বড় দরকার!
২৩/৪ রাত।
একটা স্মৃতি আমাকে এখনও দুঃস্বপ্নের মতো হানা দেয়। তখন আমি ৭ম শ্রেণিতে পড়ি। সেবার প্রচন্ড আম ধরেছে গাছে। আমাদের পুকুর ধারের দৈত্যকায় গাছটিতে আমের বাজার বসেছে যেন! আম পেকে গাছের চেহারায় বদলে গেছে – মনে হচ্ছে পার্লার থেকে কে বা কারা যেন সাজিয়ে এনেছে ওকে। আমি গাছে উঠে পুকুর ধারের ডালটিতে একটি পাকা আম ছিঁড়তে যাবো, এমন সময় মা বাড়ি থেকে বের হয়ে চেঁচিয়ে বললেন – ‘ওরে পড়ে যাবি। নাম। নাম।’ অমনি ডাল সমেত পুকুরের কিনারে পড়ে গেলাম। সঙ্গে আমটিও। আমার ডান হাত যথারীতি মাঝ খান থেকে ভেঙ্গে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাকে মেহেরপুর নেয়া হল। ডাক্তার এক্সরে দেখে বললেন – এখানে হবে না, কুষ্টিয়াই ডঃ অপূর্ব কুমারের কাছে নিয়ে যান। অপারেশন করা লাগতে পারে। আপাতত তিনি পেইন কিলার দিয়ে হাতটি ব্যান্ডেজ করে দিলেন। পরদিন সেঝো বোনকে সাথে নিয়ে মা আমাকে কুষ্টিয়া নিয়ে গেলেন। ঐ সপ্তাহে ডাক্তার ছিল না। আমাদের ফিরে আসতে হল। মেহেরপুরে পৌঁছালাম রাত আটটার দিকে। মেহেরপুর থেকে আমাদের গ্রাম শালিকা আরও ছয় কিমি পশ্চিমে। আকাশের অবস্থা তখন ভাল না। ঝড়ো হাওয়া বইছে, সাথে ইয়া বড় বড় বিদ্যুৎ চমকানো। যে কোনও সময় বৃষ্টি নামতে পারে। এই আবহাওয়াই রিকশা-ভ্যান কেউ যেতে চাইলো না। আমরা তিনজন হাঁটা শুরু করলাম। মার বয়স হয়েছে, ছয় কিমি আমরা না হয় কোনমতে হাঁটলাম, কিন্তু মা ? বিরূপ আবহাওয়ার সাথে রয়ে গেছে বিরূপ মানুষের ভয়। মা কুরআনের আয়াত পড়তে পড়তে আমাদের আগে আগে হাঁটা শুরু করলো। আমি একবার মার দিকে তাকাই, আর একবার আকাশে দিকে। আমার হাতে তখন প্রচন্ড ব্যথা। হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। মা আমাকে ঘন ঘন জিজ্ঞেস করছিল – ‘তোর কষ্ট হচ্ছে বাবা? যেন কষ্ট হচ্ছে বললেই আমাকে কোলে তুলে নিয়ে হাঁটা দেবে! আমি বললাম – না, ভয় হচ্ছে। মা হাসতে হাসতে বললেন- ‘ভয় কি? আমি আছি না! আর আল্লাহ আমাদের সাথে আছে।’ আমি তখন আল্লাহকে মার মতো করে চিনতাম না। আমি চিনতাম মাকে। আমার আর ভয় করেনি। আল্লাহ ছিলেন বলে ভয় করেনি মারও। হালকা হালকা বৃষ্টি পড়ছিল। আমরা ঝড়ের বেগে সেদিন ঐ ছয় কিমি পথ পাড়ি দিয়েছিলাম। জীবনে আজ অবধি ওতটা পথ আমি আর হাঁটিনি।
২৫/৪ রাত।
মার আরও একটা পরিচয় ছিল। মা ছিলেন বাবার তৃতীয় স্ত্রী। বাবার আগের দুই পক্ষের তিনটি মেয়ে ছিল। বাবার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় ও দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর আমার মাকে বিয়ে করেন। মা প্রায়ই মশকরা করে বলতেন- ‘অভাগার ঘোড়া মরে আর সুভাগার মরে বউ।’ মার কথা সত্যি হলে বাবা সুভাগাই ছিলেন বটে। মার বয়স তখন ১৩। সংসারে এসেই মা হলেন যথাক্রমে ৯,৭ ও ৪ বছরের তিনটা কন্যার জননী। মেয়েরা মাকে মানতে চাইতো না। মা সেই চোদ্দ বছর বয়সেই কিশোরী মনের সখ আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে পরিপূর্ণ মা বনে যান। হাল ধরেন বিরাট একটা সংসারের। আমার দাদি মানে মার শাশুড়ি ছিলেন পৃথিবীর সবথেকে তেজীদের একজন, টিপিক্যাল বাংলার শাশুড়িরা যা হয় আর কি! আর বাবা ছিলেন প্রচন্ড বদরাগী – এই ছিল একটা ১৩ বছরের মেয়ের স্বপ্নের সংসার! এসব নিয়েই মা সুখে থাকতে চেয়েছিলেন এবং জীবনের শেষ সময়টি পর্যন্ত চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেননি – কতটুকু পেরেছিলেন নাই বা বললাম, তবে এটুকু বলব – যদি ‘আত্মহত্যা মহাপাপ’ এই প্রবাদ বাক্যটি (!) মাকে না বলা হত তাহলে হয়ত মা প্রতিদিনই একবার করে আত্মহত্যা করত, কোন কোন দিন দুইবার।
কোনও সন্তান জন্ম দেওয়ার আগেই মা শাশুড়ি হলেন। তারপর নিয়মিত বিরতিতে মা আরো চারটা কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন। বারবার মেয়ে সন্তান জন্ম দেওয়ার অপরাধে বাবা আর দাদী মার ওপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন বহু গুণে। দাদি উঠতে বসতে ‘অপয়া’ ‘মুখপুড়ী’ এসব বলে মাকে খোটা দিতেন। আমার বোনদের জন্ম হয়েছে নানা বাড়ীতে। বাবা গ্রামের কোন মানুষকে পাঠিয়ে খোঁজ নিতেন – ছেলে হয়েছে না মেয়ে হয়েছে। মেয়ে হবার খবর শুনে বাবা নিজে তো দেখতে যেতেনই না পারলে পুরো পরিবার থেকে খোঁজখবর নেয়া বন্ধ করে দিতেন। এদিকে মা সবসময় বাবার পথ চেয়ে থাকতেন, গ্রামের কেউ গেলে বারবার করে বলে দিতেন একটি বারের জন্যে হলেও বাবা যেন মা ও নতুন অথিতিকে দেখে আসে। বাবা আসতেন না, বলে পাঠাতেন- মেয়ে হয়েছে তার আবার খোঁজ…? মা যতবারই কথাগুলো আমাদের বলেছেন ততবারই তাঁর কঠিন হৃদয় ভেদ করে নেমেছে অশ্রুধারা। বাবা দাদির মতো অশিক্ষিত ছিলেন না, তিনি বেশ ভালো করেই জানতেন, মেয়ে হবার জন্যে দায়ী তিনি নিজেই; তারপরও কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার কারণে মার ওপর অত্যাচারের মাত্রা সন্তান জন্মকালীন বেদনাকেও হার মানিয়েছে!
চার কন্যা সন্তানের পর জন্ম হল প্রথম ছেলে সন্তানের – বাড়িতে তখন আনন্দের বন্যা বয়ে গেল, গরু জবাই করে গ্রামশুদ্দ লোক খাওয়ানো হল; মা প্রথম বারের মতন অনুভব করলেন জন্মদানের আনন্দ। তারপর আরও একটি পুত্র সন্তান, মাঝখানে হল একটি মেয়ে তারপর পরপর আরো দুটি পুত্র সন্তান – আমি এবং খালিদ। সবমিলিয়ে আমরা হলাম ৮ বোন ৪ ভাই। মাঝখানে আমার মার আরো দুটি সন্তান ৩ মাস ও ৫ মাস বয়সে মারা গিয়েছিল- বলাবাহুল্য তারাও কন্যা সন্তান ছিল। আমাদের বাড়িতে এক মহিলা টুকটাক কাজ করতো, তার মেয়ে হল। মেয়ে জন্ম দেওয়ার সময় মারা গেল সে। ঐ শিশুটির দায়িত্ব নেয়ার মানুষ পাওয়া যাচ্ছিল না। মা এগিয়ে গেলেন। শিশুটি আমার একটি বোনের সাথে মার বুকের দুধ ভাগাভাগি করে সপ্তাহ খানেক বেঁচে ছিল। ও বেঁচে থাকলে আজ আমরা তের ভাই বোন হতাম। বাড়ির আসে পাশের কিংবা আত্মীয়দের মধ্যে আমার দাদা, নানা সম্পর্কের যারা ছিল তাদের অনেকেই মাকে মা বলে ডাকতো, ফলে মার সন্তান ছিল আরও বেশি।
মা আমাদের তিন পক্ষের ভাইবোনদের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ বুঝতে দেননি। আমি অনেক বড় হয়ে জানতে পেরেছি আমার বড় তিন বোন মার পেটে হননি। আমার ঐ বোনেরাও আমাদেরকে সেইভাবে দেখেনি। মা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন তিনি পুরো পরিবারটার নিউক্লিয়াস হিসেবে কাজ করেছেন। সবার অভিযোগ, আবদার মার কাছে, মাও চেষ্টা করতেন সাধ্য মতো তার একটা বিহিত করার। অনেক সময় গোপনে আমার আগের বোনদের ছেলে মেয়েদের এটা ওটা দিতেন। সবসময় সতর্ক ছিলেন যাতে তারা ফাকিতে না পড়ে। বলতেন – ‘ওদের মা নেই, এজন্যেই তো ওদের আমাকে বেশি দরকার।’ মার মৃত্যুর পরে যাতে করে তারা সম্পত্তিতে ফাকি না পড়ে, সেজন্যে মা আমাদের সকলের জন্যে সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারার কাজটা সম্পন্ন করে রাখেন।
২৭/৬, বিকেল।
সৃষ্টিকর্তার প্রতি ছিল মার অগাধ আস্থা আর বিশ্বাস। প্রচন্ড ভয় পেতেন সৃষ্টিকর্তাকে। আর প্রচন্ড ভালোবাসতেন মানুষকে। একদিকে আল্লাহ আর অন্যদিকে মানুষ- দুইটা দিকই ভালো মতো সামলাতেন। মাকে আমি নামায কাজা দিতে দেখিনি, আবার কোনও মানুষকে বসিয়ে তিনি নামাযেও দাঁড়াতেন না। যেন মানুষ আর সৃষ্টিকর্তা দুটোই তাঁর কাছে সমান গুরুত্বের। মা মানুষের ক্ষেত্রে হিন্দু, মসুলমান, ধনী, গরিব এসব দেখতেন না। সবাই তাঁর কাছে সমান। শুধু গরীবদের ক্ষেত্রে একটু পক্ষপাতমূলক আচরণ তাঁকে করতে দেখেছি। তবে চরিত্রহীন মানুষকে তিনি মোটেও সহ্য করতে পারতেন না। চরিত্রহীন বলতে যারা চুরি করে, বেঁচে থাকার জন্যে টুকটাক অন্যায় করে তাদের কথা বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে যারা অবৈধ সম্পর্ক করে তাদের কথা। আমাদের বাড়ীর আসে পাশে কয়েকজন চাচা-চাচী ছিল এই গোত্রের। মা তাদের সাথে একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন, সুযোগ পেলেই শুনিয়ে দিতেন দু’চার কথা। তারাও বেশ ভয়ে ভয়ে থাকতো মাকে। কাজেই পারিবারিক ভাবে তাদের সাথে আমাদের একটা দূরত্ব ছিল যা এখনো রয়েই গেছে। এমনকি আমার মিয়া ভাই মাকে না জানিয়ে সম্পর্ক করে বিয়ে করলে মা ঠিকভাবে মেনে নিতে পারেননি। প্রেম করাকে তিনি ভালো চোখে দেখতেন না। আমার বোনদের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল বাবা মার পছন্দে, ছেলেদের ক্ষেত্রেও মার একই ইচ্ছা ছিল। মা বেঁচে থাকলে আমি হয়ত নিজের পছন্দে বিয়ে করতাম না, অন্তত চাইতাম না করতে।
মা থাকতে আমাদের বাড়িতে লোকজন আসতেই থাকতো। কারও চাল শেষ, কারো বা তেল। কারও টাকা লাগবে বাজারের। আর সকাল এবং সন্ধ্যায় চুলা থেকে চা-এর হাড়ি নামতই না। মাকে পেয়ে আশে পাশের অনেকেই চা খোর হয়ে উঠেছিল। বাড়িতে চা-এর দোকান বসত যেন! যে কোনদিন চা খায় না তাকেও বলতে শুনেছি – ‘ভাবি/মা গলাটা একটু খুসখুস করচি, এক গ্লাস চা বানি দে তো!’ চায়ের সাথে মুড়ি ছিল ফ্রি। একসাথে কয়েক ড্রাম মুড়ি ভাজা হতো বাড়িতে।
মার কাছ থেকে অনেকেই টাকা নিয়ে ব্যবসা করতো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মা আর সেই টাকা ঠিক মতো ফেরত পেতেন না। বাবার কাছে গোপন রাখা হতো বিষয়টি। একবার এক মিষ্টির ব্যবসায়ীকে দিলেন ২০,০০০ টাকা। ১০ হাজার টাকা মিষ্টি খেয়ে আর একশ’ দুইশ’ করে শোধ হলো। বাকিটা অনাদায়ী পড়ে রইল। কাপড় ও মাছ ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটলো। আমরা কয়দিন আচ্ছা মতো মিষ্টি খেলাম, মাছ খেলাম, কাপড়চোপড় পরলাম, আমাদের লাভ এই যা!
একবার একদিন পশ্চিম পাড়ার এক মহিলা এসে বলল- ‘এ বুন, শুনছি তোর কাছে নাকি ট্যাকার গাছ আছে? কাউকি ঘুরাসনি? মা প্রাচীরের উপরের ডুমুর গাছগুলো দেখিয়ে হাসতে হাসতে বললেন- ‘হ্যাঁ, ওই আমার টাকার গাছ, ছিঁড়ে দেবো, নিবি ? এসব মহিলারা মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে কখনো মুরগী, মুরগীর ডিম বা বানের লাউ, চালের কুমড়া এসব দিয়ে ধার শোধ করত। মার এইসব আচরণের কারণে চাচারা মাকে বলল ‘মনু পাগলি’ বলে ডাকতো। (উল্লেখ্য, মার নাম ছিল মনোয়ারা বেগম।)
মার টাকার রহস্যটা অনেকেরই জানা ছিল। জমিতে ধান, গম যা হতো বাবার অবর্তমানে মা তার থেকে খানিকটা বিক্রি করে দিতেন। দালাল ডেকে আনার জন্যে কিংবা বাবাকে বলে দেবো এই হুমকি দিয়ে আমরাও দু’-পাঁচ টাকা হাতিয়ে নিতাম। আবার রাতে মার পিট চুলকিয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে, সিদ্ধ ধান শুকানোর জন্যে ছাদে উঠিয়ে দিয়ে দু-চার টাকা নিয়েছি। মাঝে মধ্যে দাবি একটু বেশি হয়ে গেলে মা বলত- ‘দুধ দিয়ে দিয়ে সব কাল সাপ পুষছি!’ বাবা যে এ বিষয়ে জানতেন না, তা নয়। বাবা যে জানেন এ কথা মাও জানতেন। সংসারে বাজারের খরচ, আমাদের পড়শুনা, পোশাক-আশাক বাবদ খরচ, হাতখরচ- এসবের বড় একটা অংশ মা-ই দিতেন। আমাদের সমস্ত আবদার ছিল মার কাছে। বাবার পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিলেই দু-চার টাকা পাওয়া যেত, সুতরাং চেয়ে কখনো নিয়েছি বলে মনে পড়ে না। পকেটে হাত দিয়ে যেদিন কিছুই পাইনি, বুঝে নিয়েছি মা আগেই কাজটা সেরে ফেলেছে। দু’ হাতে খরচ করেও মার টাকা বাড়তেই থাকতো। সবাই বলত- ‘তোর মার হাতে বরকত আছে।’ দেখতাম- মা মাঠে জমি কেনাতে বাবাকে সাহায্য করছে। মাসে মাসে কোনও না কোনও মেয়ে জামাইকে এনে পোশাক-আশাক দিয়ে বিদি করছে। আমাদের মেহেরপুর শহরে ছয় কাঠা জমি কেনা হল সম্পূর্ণ মার সঞ্চিত অর্থে। পরে বাবার পেনশনের টাকা দিয়ে শহরে দোতলা বাড়ি করা শুরু হয়ে আটকে গেলে মা সাহায্য করেছে। শুনেছি, গ্রামের দোতলা বাড়িতেও নাকি মার বড় ধরনের অবদান ছিল।
এমনিতেই মা টাকার ব্যাপারে বেশ হিসেবি ছিলেন তবে দান-খয়রাতের ব্যাপারে ছিলেন ঠিক তার উল্টো। মা কখনও ব্যাংকে টাকা রাখতেন না। হয়ত টাকার গোপনীয়তা রক্ষা থাকবে না বলে। মার ড্রয়ার ভর্তি থাকতো টাকায়। এজন্যে ড্রয়ারের চাবিকে কোলের সন্তানের মতো চোখে চোখে রাখতেন। একটুও এদিক ওদিক হবার সাধ্য ছিল না চাবিটার। বাবা মাঝে মধ্যে বলতেন- ‘তোর মা দেখিস কবরেও চাবিটা নিয়ে যাবে।’ সাধারণত ড্রয়ার খুলতেন সবার অলক্ষ্যে। তবে টাকা গুনতে সমস্যা হলে আমাদের কাউকে না কাউকে ডেকে নিতেন। এবং টাকা গোনার বিষয়টি গোপন রাখার জন্যে আবার দু’চার টাকা দিতেন। আমরা মার কাজ কখনও ফ্রি ফ্রি করে দিতাম না। একবার আমি ৭০ হাজার পর্যন্ত গুনে দিয়েছিলাম। তখন আমি ৫ম শ্রেণিতে পড়ি। ওত টাকা একসাথে দেখে আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। গোনার এক ফাকে একটা নোট সরিয়ে ফেলেছিলাম, মা টের পাননি। পরে ঐ টাকা নিয়ে পড়েছিলাম মহা মুশকিলে। ৫০০ টাকার নোট কাউকে দেখাতে সাহস পাচ্ছিলাম না। দোকানদারকেও না। আর তাছাড়া আমার চাহিদা তখন ২ টাকার বাদাম, ২ টাকার দুইটা আইসক্রিম, এক টাকার এক প্যাকেট টিপু সুলতান বুলবুলি, দু’ টাকার নায়ক নায়িকার ভিউকার্ড সমেত আচার, আর বড় জোর চুরি করে দুইটা পটকা ফাটানো। বাকী টাকার কি গতি করব ? পরের সপ্তাহে টাকা গোনার ফাকে জায়গার টাকা জায়গায় রেখে দিয়েছিলাম। মা টের পাননি তখনও। খালি খালি এক সপ্তাহ ঘুম নষ্ট! ঔ এক সপ্তাহে আমি আমার ছোটবোনকে জ্বালিয়ে মেরেছি- এটার দাম কত, ওটার দাম কত? ওহ এত কম! পরে ও সন্দেহ করতে শুরু করলে আমি চুপ মেরে গেলাম। আমার বাড়িতে বরাবরই একটা সুনাম ছিল- টাকার প্রতি লোভ কম। সেই সুনামটা অক্ষত রাখারও একটা ব্যাপার ছিল।
৩/৬ দুপুর।
মা খুব বেশি শিক্ষিত ছিল না। ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত তাঁকে পড়ানো হয়েছিল। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও মা শিক্ষার মর্ম বুঝতো। আমাদের শিক্ষিত হওয়ার পেছনে বাবার থেকে মার অবদানই বেশি ছিল। আমার বোনেরা অনেক মেধাবী ছিল, আমাদের থেকেও বেশি। কিন্তু বাবার কারণে তাদের পড়াশুনা উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত গড়ায়নি। যতটুকু হয়েছে মার কারণে। মা আমাদের প্রাইভেট টিউটর ঠিক করে দিতো। প্রাইমারি স্কুলে থাকতে বাড়ির কাছে হান্নান চাচা, ছিয়ম ভাই, রবি ভাই; মাধ্যমিকে উঠে শহরে আসার আগ পর্যন্ত আকবর চাচা ও আজিজুল ভাই- এদের কাছে পড়েছি। মা-ই ঠিক করে দিতো, মাস গেলে বেতন দিতো। পড়তে ঠিক মতো যাচ্ছি কিনা এসব খোঁজ খবর মা-ই রাখতো। স্কুলেও নিয়োমিত খোঁজখবর নিতো। আমরা একদিন পড়তে না গেলেই মার কাছে খবর চলে আসতো। আর এ ব্যাপারে মার কাছে কোনও প্রশ্রয় মিলতো না। কাজেই আমাদের পড়াশুনায় ফাকি দেবার কোনও উপায় ছিল না। আমি যখন ক্লাস ফোর-এ তখন মিয়া ভাইয়ের উদ্যোগে বাড়িতে টেলিভিশন আনা হল। মা ওটার ঘোর বিরোধী ছিলো। টেলিভিশনের কারণে মার নাইট ডিউটি বেড়ে গেল। রাত ১১-১২টার দিকে আমাদের পড়ার ঘরের দেয়ালে কান দিয়ে টিভি চলছে কিনা বোঝার চেষ্টা করতো। ধরা পড়ে গেলে মহাবিপদ! আমরা টিভির সামনে বসে ভলিউম কমিয়ে দেখতাম। এক কান থাকতো সিড়িতে আর এক কান টিভিতে। মার পায়ের আওয়াজ টের পেলেই টিভি অফ করে গুনগুন শুরু করে দিতাম। আমরা মাকে ততটা গুরুত্ব না দিলেও ভয় করতাম বেশ। কাজেই মার ভয়ে ভয়ে পড়তে হতো অনেক সময়।
তবে মা যে সব সময় আমাদের ওপর রাগ করতো তা কিন্তু নয়। মাঝে মধ্যে বিদ্যুৎ চলে গেলে আমরা উপরের বারান্দায় কিংবা ছাদে মার পাশে শুয়ে পড়তাম। কখনো মার পিঠ চুলকিয়ে দিতাম, কখনো মার চুল মঠ করে দিতাম। মা হাত পাখা ঘুরাতো আর গল্প বলতো। তখন আমি খুব ছোট। মা একই গল্প প্রতিদিন বলতো; ঐ যে সাত বোকার ঐ গল্পটা। এক দেশে সাত বোকা ছিল। তাদেরকে বাগানের আগাছা পরিস্কার করতে বলা হলে সমস্ত বাগানের গাছ কেটে মরুভূমি বানিয়ে দিয়েছিল। তারপর এক বৃদ্ধার দেখাশুনার দায়িত্ব দেওয়া হলে, বৃদ্ধার গায়ে একটি মশা মারতে গিয়ে সাত বোকা পর্যায়ক্রমে এমন করে থাপ্পড় মারল যে মশা তো মরলই সাথে বৃদ্ধাও মরে গেল। তারপর বৃদ্ধার লাশ চাটাই করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় চাটাইয়ের ফাক গলিয়ে পড়ে গেলে, রাস্তায় অন্য এক বৃদ্ধাকে থাপ্পড় মেরে লাশ বানিয়ে ওরা পুড়িয়ে ফেলল। আরও কতো এমন আজব আজব কান্ড করে চলে সেই সাত বোকা! গল্পটির দাঁড়ি, কমাসহ আমাদের মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। তবুও শুনতে চাইতাম, মাও বলতেন এমন করে যেন এই প্রথম বলছেন। গল্প শেষ হওয়ার আগেই আমরা ঘুমিয়ে পড়তাম। মা টের পেলেও হাত পাখা আর গল্প চলতেই থাকতো।
২/৭ রাত।
মা থাকতে বাড়িতে হাঁস, মুরগী, ছাগল সবই পোষা হত। চাষ তুলে দেওয়ার আগে কয়েকটি গরুও ছিল। মা পশু পাখির কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। বাবা ছিলেন গরু পেটানোতে ওস্তাদ। সামান্য কিছু হলে ছাগল মুরগী এদের দিকে তাক করে হাতের কাছে যা পেতেন তাই ছুড়ে মারতেন। এ কারণে মা মাঝে মধ্যে বাবার ওপর খুব রাগ করতেন। আমরা বড় হলে অবশ্য ছাগল, হাস, মুরগী এসব পোষা বন্ধ হয়ে যায়। মা আর এসব ঝামেলা বহন করতে পারতেন না। শুধু কুরবানির আগ দিয়ে ছাগল কেনা হতো বাড়িতে। আমাদের বাড়িতে একসময় একটা কুকুর থাকতো। আমি তখন বেশ ছোট। কুকুরটি ছিল মূলত মার ভক্ত। মার রান্নাঘর পাহারার দায়িত্ব ছিল কুকুরটির। ও থাকা অবস্থায় রান্না ঘরে মুরগী বা অন্য কুকুর ঢুকতে পারতো না। রাত হলে বাড়ির চারিপাশ ঘুরে ঘুরে নাইট গার্ডের কাজ করতো। তারপর এক সময় বয়স জনিত কারণে মারা গেল কুকুরটি। মার আবদারে আমরা বেশ যত্ম করে কবর দিলাম ওকে। একবার মিয়া ভাই কিংবা মেঝো ভাই মাঠ থেকে একটা মেটে ঘুঘু ধরে নিয়ে আসলো। খাঁচায় রাখা হল ওকে। মা এভাবে বন্দি করে পশু পাখি পোষার বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু আমাদের সাথে পেরে উঠতেন না। ঘুঘুটি অনেক দিন ছিল। মা-ই ওর যত্ন-আত্তি করতো। একদিন মধ্য রাতে ঘুঘুটি ঝটপট করে ডানা ঝাপটে উঠলো। মা বাবাকে বললেন- ‘নিশ্চয় কিছু হয়েছে। ও তো কোনদিন এমন করে না?’ বাবা মার কথায় ওতটা গুরুত্ব দিলেন না। মার মন বলে কথা! উঠে আসলেন বিছানা ছেড়ে। তারপর মা চিৎকার করে উঠলেন- ‘এই তোরা ওঠ, সর্বনাশ হয়ে গেছে! চোর ঢুকেছে ঘরে।’ আমরা সবাই উঠে পড়লাম। চোর এক তলার ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পালিয়ে গেল। তেমন কিছু নিতে পারেনি। ঘুঘুটা সেদিন সময় মতো ঐ সংকেতটা না দিলে এবং মা ঐ সংকেতে সাড়া না দিলে সত্যি সত্যি সর্বনাশ হয়ে যেত। মা পরদিন ঘুঘুটিকে ছেড়ে দিতে বলেছিলেন। আমরা ছেড়েছিলাম কি-না মনে পড়ে না। আমি একসময় পায়রা পুষতাম। মেঝো ভাই শুরু করেছিল পায়রা পোষা। মা পায়রা পোষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কারণ, রোজ পায়খানা করে ঘর বাড়ি নোংরা করতো, রান্না ঘরে মাকে খুব জ্বালাতো, ধানের বা চালের বস্তা ফুটো করে ফেলত। আমি মার কথা শুনতাম না। আমার তখন নেশা ধরে গিয়েvাছল। একসময় বেশ কয়টা হারিয়ে গেল। চারটা ছিল তখন। একদিন সকালে উঠে দেখি মার মন খুব খারাপ, কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা। পরে জানতে পারলাম ঐ চারটাও রাতে চোর এসে খাঁচাসহ চুরি করে নিয়ে গেছে। মা কোথায় খুশি হবে তা না আমার থেকে তখন তাঁরই মন খারাপ বেশি। বছর খানেক পর দুটি পায়রা ফিরে এসেছিল। মা একজনকে দিয়ে খাঁচা বানিয়ে ছাদে রেখে দিলেন। আমি ততদিনে মেহেরপুর চলে এসেছি। পরে আর ওদের খোঁজ নেওয়া হয়নি। আর একবার সখ করে বাবা একটা ভেড়া কিনলেন। আমরা প্রায় রোজই ভেড়াটির গোসল করিয়ে দিতাম। মাঝে মধ্যে পশম কেটে দিতেন বাবা। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ও বাড়ির সকলের সাথে ভাব জমিয়ে ফেলল। আমরা যেখানে যেতাম ও পিছন পিছন যেত। সব থেকে বেশি থাকতো মার সাথে। সন্ধ্যার পর আমরা খেয়ে ওপরে চলে যেতাম। মার তখন থালা বাসন ধোয়া, রান্না ঘর গোছানো থেকে শুরু টুকটাক কাজ করতে করতে রাত আট নয়টা বেজে যেত। ভেড়াটি মার সাথে সাথে থাকত। মার কাজ শেষ হলে মার সাথে সাথে ঔ ঘরে যেত। রাতে বেধে রাখলে থাকতে চাইত না। কাজেই ছেড়ে রাখা হতো। রাতে কয়েকবার মার শোবার ঘরে যেত, মা যতক্ষণ না কোনও কথা বলত ততক্ষণ নড়ত না। অসুখ হলে বাবা ওকে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হোন। বিক্রির পরদিনই ওকে জবাই করে কসাইরা। মা শুনে বেশ কষ্ট পেয়েছিল।
শুধু পশু পাখি না, গাছপালার সাথেও মার ছিল মধুর সম্পর্ক। নিজে কিংবা একে ওকে দিয়ে বাড়ির চারপাশে ঔল, মান ও সজিনা, নাজিনা প্রভৃতির গাছ লাগিয়ে নিতেন। আমরা তখন আত্মীয়দের বাড়িতে নিয়ম করে ঔল, মান, ডাটা প্রভৃতি পাঠাতাম। ফুল গাছের প্রতিও মার খুব ঝোঁক ছিল। মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ফুলের চারা কিনে আনতাম, টব কিনতাম। মা গাছগুলো ঘিরে রাখার ব্যবস্থা করে দিতেন। কোনও গাছে প্রথম ফুল ধরলে আমি মাকে ডেকে দেখাতাম, মা খুব খুশি হত।
১০/৭ সন্ধ্যা।
মার সমস্যা একটাই – রেগে গেলে থামানো যেতো না কিছুতেই। সারাদিন বকাবকি করতেন। আমাদের অসহ্য হয়ে পড়তো। তখন বাবা বাড়ির বাইরে কাটাতো বেশির ভাগ সময়। রাতে বাবা উপরে আমাদের সাথে এসে ঘুমাতেন। মা তখন উঠানে দাঁড়িয়ে কিংবা সিঁড়িতে এসে এটা ওটা বলতেন। মার মূল টার্গেট ছিল বাবা। আমরা যখন বাবার পক্ষ নিতাম তখন আমরাও টার্গেটে পরিণত হতাম। বেশির ভাগ সময় ঘটনা চরমে পৌঁছে যেত। বাড়ির আশপাশে মানুষজন জমে যেত। আমরা লজ্জায় দরজা লাগিয়ে দিতাম। আমাদের পরিবারটা যতটা না ছিল বাবার তার থেকে অনেক বেশি ছিল মার। দায়িত্বের দিক থেকে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বলা যেতে পারে। কিন্তু অধিকারের বেলায় বাবাই সব। বাবা মাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চায়লে মার কিছুই বলার ছিল না। সংসার, স্বামী ও সন্তানদের জন্যে একটা কিশোরী তার সমস্তটা জীবন তিল তিল করে নিঃশ্বেস করে দিলেও তাদের কাছে তাঁর শেষ অবধি পরিচয় দাঁড়াল ‘কেউ না’। মা আফসোস করত ছেলে মেয়েরা বাবার পক্ষ নিতো বলে, বিশেষ করে মেয়েরা, যেহেতু তারাই তখন বড়। বাবা যাদের জন্মের সংবাদ শুনে বিন্দুমাত্র খুশি হননি তারাই বড় হয়ে বাবার দলে যোগ দিল, মাকে বোঝার চেষ্টা করলো না কেউ। কিছু হলে সবাই মিলে মার ওপর চড়াও হতো। বাবা আর মেঝো ভাই মাকে শারীরিক নির্যাতনও করেছে। অর্থনৈতিক অভাব বলতে যেটা বোঝায় সেটা আমাদের ছিল না কখনো; বরং গ্রামের আর পাঁচটা মানুষের থেকে অনেক বেশিই ভোগ করেছি আমরা। কিন্তু মানসিক শান্তি ছিল না এতটুকুও। যতক্ষণ বাইরে থাকতাম বেশ ভালোই কাটত সময়, ঘরে ফেরার কথা ভাবতেই কর্পূরের মতো উবে যেত সকল ভাললাগা; ভয় হত- বাড়ি গিয়ে যদি দেখি, মা পাগলের মতো বকে যাচ্ছে, বাবা তাঁর পুরুষত্ত্বের বলে মাতিয়ে রেখেছে চারপাশ, নাট্যমঞ্চের মতো বাড়িটাকে ঘিরে আছে লোকজন। বাবা প্রায়ই মাকে তালাক দেওয়ার কথা বলতেন; দিলে হয়ত মা বেঁচেই যেতেন। মাঝে মধ্যে মা আমাদের নিচের স্টোর রুমটিতে দরজা লাগিয়ে কাঁদতেন। আমি, খালিদ কিংবা মাকছুদা (আমার ছোট বোন) দরজা খোলার জন্যে আকুতি করলে মা বলতেন- ‘ভয় নেই, আমি আত্মহত্যা করব না, তোদের ওপর রাগ করে আমি আমার পরকালটা খোয়াব না।’ আবার মাঝে মধ্যে মা কান্নার মতো সুর করে কুরআন শরীফ পড়ত। আমি কুরআন তেলোয়াত এর শব্দে ভয়ে কুকড়ে যেতাম, যেন মা কোনও মন্ত্র আওড়িয়ে মহাপ্রলয় ডেকে আনবে আজি। কিন্তু পারেননি। মার সেই শক্তি ছিল না। মাকে শেষ পর্যন্ত এডজাস্ট করতে হয়েছে- বাবার সাথে, সন্তানদের সাথে, ক্ষমতার সাথে, সর্বপরি পুরুষতন্ত্রের সাথে। মা প্রায়ই বলতেন- তোরা কেউ আমাকে চিনলি না, আমি যদি লেখক হতাম, আমার সব লিখে শোনাতাম দুনিয়াবাসীকে। আমার গল্প শুনে পাথরেরও মন কেঁদে উঠত। তখন ভাবতাম- লিখলেই পারে। এখন জানি মা কেনও লেখেননি। মার সব ছিল, স্বামী, ঘরভর্তী সন্তান, ভাই-বোন, নিজ হাতে গড়া দু-দুটো দোতলা বাড়ি। সৃষ্টিকর্তা। সবই। কিন্তু কিছুই ছিল না তাঁর। মৃত্যুর সময় তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে এই ভয়াবহ সত্যটার উপস্থিতি আমি টের পেয়েছিলাম। আমি অনেক কেঁদেছিলাম সেদিন- মা মারা গেছে এই জন্যে না যতটা তার থেকে অনেক বেশি ওই সত্যটার জন্যে। এতকিছু থেকেও মানুষ একা হতে পারে!
আমি তখন ছোট, বুঝতাম না কিছুই। মার ওপর আমারও খুব রাগ হতো তখন। ভাবতাম, চুপ থাকলেই পারে। বকাবকি না করলে তো আর কেউ তার ওপর চড়াও হচ্ছে না। মা কেন বকছে, কি জন্যে পাগলের মতো আচরণ করছে বুঝতাম না কিছুই। এখন বুঝি কিছুটা। এখন বুঝতে পারি মা কেন অমন পাগলের মতন আচরণ করতো। মা তো পাগলই ছিল। আমরা সকলে মিলে তাকে পাগল করে ছেড়েছিলাম।
২/৮ দুপুর।
আমি যখন ক্লাশ থ্রিতে- বড় ভাই বাড়িতে না জানিয়ে কুষ্টিয়াতে তার ক্লাশমেটকে বিয়ে করলো। মা ভেঙ্গে পড়লেন প্রচন্ডভাবে। এরই মধ্যে মেঝো ভাই পড়াশুনা বন্ধ করে শহরে ব্যবসা শুরু করলো। ব্যবসায় লসও খেল। ছোটবেলা থেকেই ও ছিল বেশ বদরাগি। শেষের দিকে এসে মেঝোভাইয়ের অত্যাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। কথায় কথায় সে মাকে তেড়ে আসে মারতে; কখন কখন মারেও। মা কখনও বাবাকে সেইভাবে ভয় পাননি যতটা মেজোভাইকে পেতেন। মাঝে মধ্যে মা স্বপ্নে দেখতেন, মেঝোভাই তাঁকে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসছে, ধড়ফড় করে বিছানা থেকে উঠে পড়তেন।
মেঝোভাইয়ের বিয়ে দেয়া হল। কিছুদিন পর সে বাড়ি এবং সম্পত্তির ভাগ চাইল- তাও হল। মা বাবাকে বলে তাকে সম্পত্তি বুঝিয়ে দিলেন। কিছুদিনের মধ্যে মেঝোভাই বাড়ির মাঝখান দিয়ে টিনের প্রাচীর উঠিয়ে দিলো; উদ্দেশ্য- মার চোখে চোখ না দেয়া ও ভাবির বড় উঠান ঝাড়ু দিতে যেন কষ্ট না হয় তার একটা ব্যবস্থা করা (যদিও বেশিরভাগ সময় মা-ই ঝাড়ু দিত উঠানটা)। আমি খালি বাধা দিয়ে বললাম- ভাগ যদি হয় তবে চার ভাগ হবে। ও কেন একা আধাআধি ভোগ করবে? কথাটা শুনে মেঝো ভাই আমাকে চলা হাতে তেড়ে আসলো…। মা দ্রুত ছুটে আসল- ‘ও বাপ, আমার ছেলেকে ছেড়ে দে। তুই যা চাবি আমি তাই দেবো।’
কয়েকটা মাস ভালোই কাটল। মেঝো ভাই কৃষিকাজ ও ব্যবসাতে মনোযোগ দিলো। সেখানে পরপর কয়েকবার লস খেলে তার মেজাজ গেল আরও বিগড়ে; আবার শুরু হল অত্যাচার। মাকে দেখলেই মারতে আসত তেড়ে; মা বাড়িতে প্রচন্ড ভয়ে ভয়ে থাকত। অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যেতে থাকলো। কোন সমাধান করতে না পেরে বাড়ির সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিল মেঝো ভাইকে পুলিশে দেওয়ার কিংবা মানসিক চিকিৎসার জন্যে পাবনা মেন্টালে পাঠানোর- বাধ সাধলো মা। বললেন, ‘আমার ছেলে সেখানে কষ্ট করবে এ আমি সহ্য করতে পারব না; বরং ওর ভালোর জন্যে আমিই বাড়ি ছাড়ছি।’ তিলতিল করে শরীরের রক্ত পানি করে যাদের জন্যে মা এই সংসার দাঁড় করেছিলেন আজ তাদের সুখের জন্যেই সেই সংসার ছেড়ে চলে যেতে চাইছেন! এটুকুই করতে বাকি ছিল তাঁর। পরদিন আমরা মানে আমি মা খালিদ ও বাবা গ্রামের বাড়ি ছেড়ে শহরের বাড়িতে এসে উঠলাম। গ্রামের বাড়িতে আর ফেরা হবে কিনা জানিনা আদৌ। বাবা, খালিদ – কারোরি তেমন একটা অসুবিধে হচ্ছিল না, আর আমার তো বেশ ভালো লাগছিল; শহুরে হওয়ার স্বাধ ও স্বপ্ন আমার বহুদিনের কিন্তু মা মানিয়ে নিতে পারছিলেন না কিছুতেই। যদিও এই শহরেই আমার নানা বাড়ী, বর্তমানে নানা-নানী না থাকলেও মামা আছেন- এই শহরেই কেটেছে তাঁর বাল্যকাল, তবুও এই শহরটাকে আপন করতে পারেননি। গ্রামের মানুষ থেকে শুরু করে প্রতিটি ধূলিকনা, গাছপালা, পশুপাখি সবার সাথে ছিল তাঁর আত্মার আত্মিয়তা। যে বাড়ির প্রতিটি কোষের জীবন বৃত্তান্ত তাঁর জানা, চতুর্দিকের প্রকৃতি সন্তানের মতো মায়ায় লালিত তা ছেড়ে থাকাটাই ছিল তাঁর শেষ জীবনে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। মাঝে মধ্যে মা যখন শত কর্মব্যাস্ততার মাঝেও বারান্দার গ্রীলটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতেন, বিষন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন শূন্যে, তখন খালি মনে হত- সংসারকে সর্বস্ব নিংড়ে দিয়ে কি পেলেন এই মানুষটা? পরবর্তীতে যে কয়েক মাস বেঁচে ছিলেন খুব বেশি একটা যাননি গ্রামের বাড়িতে। যে কয়েকবার গেছেন ফিরে আসবার সময় আর পিছন ফিরে তাকাননি বাড়ির দিকে; মার এই ভয়ংকর-কঠিন রুপটি দেখে আমি অাঁৎকে উঠতাম। মা হনহন করে পুকুরের পাড় ঘেসে উঠে আসতেন রাস্তায়। পথিমধ্যে যতটা সম্ভব নীরব থাকতেন। কি যেন ভাবতেন! কিংবা কিছুই না ভাবার চেষ্টা করতেন।
২/৩/ রাত ১ টা।
আজ খুব করে মনে পড়ে – সেদিন রাতে চন্দ্রগ্রহণ ছিল, আমার জীবনে প্রথম বারের মতো চন্দ্রগ্রহণ দেখা। আমি অনেক রাত পর্যন্ত ছাদে বসে ছিলাম; মা ঐ মধ্যরাতে দেখতে এসেছিলেন আমি ঠিকমত মশারিটা টাঙিয়েছি কিনা। হঠাৎ করে পিছনে তাকিয়ে দেখি মা দাঁড়িয়ে। আমি মাকে চন্দ্রগ্রহণের অপরূপ দৃশ্যটা দেখাতেই মাও আমার পাশে বসে পড়লেন; তারপর আমরা দুজনেই শেষ রাত অবধি বসে ছিলাম। মা আমার কাঁধে হাত রেখে বসে ছিলেন, আমরা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধু হয়ে উঠেছিলাম – আমার জীবনে এই অর্জনের হিসেব কোনদিনই হয়ত আর মেলাতে পারবো না। আমরা বসে ছিলাম অনেকক্ষণ, গ্রহণ লাগা চন্দ্র ততক্ষণে বিদায় নিয়েছে : আমরা টের পাইনি কিছুই – তেমন কথাও হয়নি আমাদের মাঝে।
তারপর আর চন্দ্রগ্রহণ দেখা হয়নি আমাদের – না মার, না আমার। গ্রামের বাড়ী গেলে অনেক রাত অবধি ছাদে উঠে বসে থাকি; মাঝে মাঝে মাও এসে বসেন আমার সাথে; আগের মতই কোন কথা হয়না আমাদের। আমি চাঁদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। মাও থাকেন, তারপর একসময় চাঁদের সাথে মিশে যান – ঘরে ফেরেন মা, ঘরে ফিরি আমি। সবকিছু সেই আগের মতই আছে শুধু দু’জনের বাস এখন দু’ঘরে, এছাড়া খুব একটা পরিবর্তন হয়নি আমাদের – না মার, না আমার। যখন আমি শহরে চলে আসি চাঁদের দিকে তাকাতে ভয় পাই – প্রচন্ড পাপের মধ্যে ডুবে থাকা এই আমি সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে চাই না কিছুতেই।
২৫/৩/ ২০১২ দুপুর।
খুব আফসোস হয় যে কারণে-
মা জানতেন আমাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়া দেখে যেতে পারবেন না। খুব চিন্তা করতেন আমাদের নিয়ে। বিশেষত খালিদকে নিয়ে। আমি স্কুলে বরাবরই প্রথম হতাম। শহরের স্কুলে এসে প্রথম না হতে পারলেও প্রথম সারিতে থাকতাম। সুতরাং আমাকে নিয়ে চিন্তা করার কোনও কারণ ছিল না, অন্তত তখন পর্যন্ত। খালিদ ছিল পড়াশুনাতে কাচা। বয়সেও সবার ছোট। মা যখন চূড়ান্ত শয্যায় আমি তখন এস.এস.সি দেবো, আর খালিদ তখন সিক্সে। কাজেই প্রায়ই বলতেন- ‘আমি চলে গেলে তোদের কি যে হবে ! আমার খালিদকে কে দেখবে! ও একটু কমা, ওকে তোরা ফেলিস না বাবা।’ আমাদের কথা ভাবতেই মার কষ্টটা বেড়ে যেত দ্বিগুণ।
মা চলে গেলেন এপ্রিলের ২৭ তারিখে। সাল ২০০২। পরের মাসেই আমার এস.এস.সি পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশিত হলো। ফোর সাবজেক্ট বাদে ৪.২৫ পেলাম। তখন ওটা খুব একটা খারাপ না ছিল না। রেজাল্ট নিতে আমি যাইনি। তখন আমি গ্রামের বাড়িতে। সন্ধ্যায় কে যেন এসে রেজাল্টটা জানালো। আমি ছুটে গেলাম মার কাছে। মার ধারণা ছিল, তাঁর অসুস্থতার কারণে আমি ফেল করবো। আমি চুপচাপ বসেছিলাম, অনেকক্ষণ। কোনও কথা বলিনি। কাকে বলবো? ঐদিন প্রথম অনুভব করলাম, মা নেই। আমাদের ভালো মন্দ কোনকিছুতেই আর কিছু যায় আসে না তাঁর। বড় খালি খালি লাগছিল সবকিছু। মাকে রেজাল্টটা জানানোর জন্যে বুকের ভেতরটা আনচান করছিল।
খালিদের সময়টা খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না। ও খুব অস্থির হয়ে পড়েছিল। মার মৃত্যুটা নীরব ঘাতক হয়ে সবচেয়ে বড় আঘাতটাই হেনেছিল ওর বুকে। ও তখন বেশ ছোট। বাড়িতে সৎ মা, আর তাছাড়া, মার শেষ সময়টাতে ঐ ছায়াসঙ্গী ছিল। কাজেই ওর জন্যে সময়টা সবচেয়ে কঠিন হয়ে উঠেছিল। ও একবার শিল্পকলায় ভর্তি হল গান আর আবৃতি শেখার জন্যে। পড়াশুনার অবস্থা তখন আরও খারাপের দিকে। মেহেরপুর থেকে গ্রামের স্কুলে ভর্তি করানো হলো। সাহিত্যের বই পড়া শুরু করলো। কয়েকটি কবিতাও লিখলো। বন্ধুদের নিয়ে গ্রামের স্কুল থেকে একটি সাহিত্যের কাগজ বের করলো, নাম দিল ‘অঙ্কুর’। দুটো সংখ্যা বের করে সাহিত্যের পথ থেকে সরে আসলো। এবার শুরু করলো ধর্ম চর্চা। মসজিদেই কেটে যেতে লাগলো তার বেশির ভাগ সময়। মাঝে অবশ্য বাবার ওপর রাগ করে সিগারেটও খেয়েছিল কয়েকটি।
মাধ্যমিকে টেস্ট পরীক্ষায় তিন বিষয়ে ফেল করলো খালিদ। পরে মিয়া ভাইয়ের সান্নিধ্যে ও গভীরভাবে পড়ায় মনোনিবেশ করলো। মাধ্যমিকে ৪.৬০ পেয়ে পাশ করলো। আর্টস থেকে ওই প্রথম। উচ্চ মাধ্যমিকে এসে একটুর জন্যে এ+ পেল না। এ বছর সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে IER এ অনার্স শেষ করেছে। আর আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ শেষ করলাম। আফসোসটা এখানেই। মা এসব দেখে যেতে পারলো না। দেখে যেতে পারলো না, তাঁর সবচেয়ে দুর্বল ছেলেটাই আজ সবার চেয়ে এগিয়ে গেছে। আমাদের এই এগিয়ে যাওয়ার পেছনে বাবার ভূমিকাই প্রধান। তিনি মার অবর্তমানে কোন অভাব বুঝতে দেননি। আমি অর্থনৈতিক অভাবের কথা বলছি। যত টাকাই হোক চাওয়া মাত্রই পেয়েছি। আর সাথে বড় ভাই, ভাবী ও বোনদের সহযোগিতা ও শুভকামনা তো ছিলই। মার ঐ অসুস্থ অবস্থায় একবার যদি কেউ কানে কানে বলে দিত – ‘সময় থেমে থাকবে না, থেমে থাকবে না ওরাও। তোমার দোয়াই ওদের অনেকদূর নিয়ে যাবে।’ তাহলে বোধহয় ওই সময়টা তার জন্যে ততটা কঠিন হয়ে উঠতো না।
প্রতিনিয়ত ছোটখাট যে অর্জন, মাকে যদি জানাতে পারতাম – ইস্, বড় আফসোস হয়! মোবাইল ফোনে অনেকের নাম্বার থাকে, শুধু মার নাম্বারটা থাকে না। মাঝে মধ্যে কল্পনা করি মোবাইলে মার গলার স্বরটা কেমন শোনাত। মা কি প্রতিদিনই ফোন করতো? ফোন ধরতে একটু দেরি হলে বারবার ফোন দিতো? কি জানি!
ডায়রির পাতা থেকে
রচনাকাল ২০০৭-২০১২

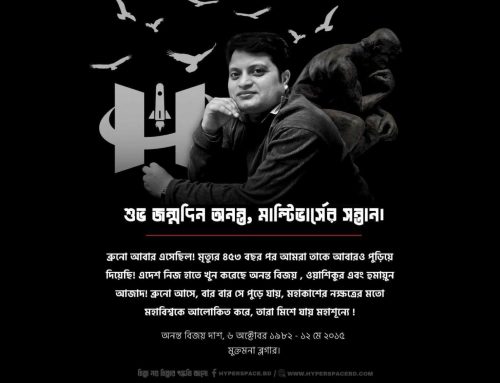
এই প্রথম কোন বিষয়ে ধৈর্য সহকারে পড়লাম। আপনার মাকে আল্লাহ শান্তিতে রাখুন।আমিন।
মাকে নিয়ে লেখাটা গভীরভভাবে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছি ……….শত আঘাতেও এই চোখের পানি পরতে দেইনি……লেখাটা পরে চোখের পানিগুলো আর বাধা মানেনি……আজ অনেক দূরে থেকেও অনেক কাছে মাকে এভাবে গভীরভাবে অনুভব করতে পারব ভাবতেও পারিনি…..আর লেখাটাওযে নিজের মায়ের প্রতিচ্ছবি হয়ে ফুটে উঠবে কল্পনাও করিনি……..লেখার সময়ও চোখের পানি বালিশ ভিজিয়ে দিচ্ছে ……অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে গভীর ধন্যবাদ জানাচ্ছি ……এভাবে কাছ থেকে আমার মাকে অন্যরুপে চিনিয়ে দেয়ার জন্য……….
মোবাইলে পড়েছি আগেই, মন্তব্য করা হয়নি। লেখাটি খুটিয়ে খুটিয়ে পড়ছিলাম আর আমার মাকে খুজছিলাম, পেয়েছিও, সম্ভবত সবাই পায়। বই বেরোলে বাকিটাও পড়ব, আশা রাখি।
ধন্যবাদ।
@হেলাল,ধন্যবাদ ভাইয়া। বই বের হলে জানাব। ভাল থাকবেন।
@মোজাফফর হোসেন,
মনকে দলিত মথিত করা লেখা- একটা প্রিয় কবিতা দিলাম এই লেখাকে কেন্দ্র করে,
আবেগে মথিত হওয়ার মত লেখা। তোমার জীবনের এ অংশটি তো আগে কখনও শোনা হয়নি।
মায়ের জন্য ছেলের অনুভূতি অভিভূত করল। লেখা অব্যাহত রেখো।
@গীতা দাস, দিদি, একটা লেখার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। পরে আরও জানাব। ধন্যবাদ।
মা’কে নিয়ে স্মৃতিকথাটি বেশ লাগলো। আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারের যোনো নিঁখুত একটি নীমগাছ। আপনার মাকে অশেষ শ্রদ্ধা। (Y)
@বিপ্লব রহমান, নীমগাছ । ভাল বলেছেন। ধন্যবাদ।
আমাদের মায়েরা ত এমনই বাঁ এমনই হয়,এখানেই পাশ্চাত্য আর প্রাচ্যের পার্থক্য। যার রক্ত নয় মাস পান করে আমরা এই ভুমিতে আসি তাকে এভাবে স্মরন করবেন না ত কাকে স্মরন করবেন!
আপনাকে ধন্যবাদ অকপট হবার জন্য।
@সপ্তক, ধন্যবাদ। ভাল থাকবেন।
কোন লিখা পড়া শেষ করে আনন্দ বা অন্যান্য অনুভূতি বোধ করার ব্যাপার একরকম, কিন্তু কিছু পড়তে পড়তেই ভীষণ আগ্রহ, অসীম কৌতুহল, এবং গভীর কষ্ট তৎক্ষনাত অনুভব করার ব্যাপারটা হচ্ছে লেখকের বোধ আর অনুভূতির ঠিক সাথে সাথে চলা। আর এ সাথে করে নিয়ে যেতে সবাই কি পারে? আপনি পেরেছেন। খুবই সুন্দর আর আন্তরীক ভাবেই পেরেছেন।
একজন মানুষের জীবনে কত গল্প। আহারে… আপনার মায়ের জীবনের একান্ত গল্পগুলো এ পৃথিবীর কাছে অজানাই থেকে যাবে। আমার মা এককালে কবিতা লিখতেন। সেই কিশোরী বয়েশে তার কলম হতে যে কবিতা বেরিয়েছিল তার বিষয়বস্তু ছিলো মানুষ, মানবতা, প্রেম, চারপাশ ইত্যাদি। ওনার জীবনের গল্পগুলো ধরে রাখবার জন্য দু বছর আগে প্রায় ৩-৪ মাস অনেক খুঁজে একটি ডায়রী উপহার দেই মাকে। দীর্ঘ এক চিঠিতে অনুরোধ জানাই যেন ওই ডায়রীর প্রতিটি পাতায় উনি লেখেন, ওনার যা খুশি তাই…তবু যেন লিখেন। ভেবেছি মা প্রচুর লিখে, ডায়রী ভর্তি করে আমায় চমকে দেবেন। চমকে গেছি সত্যি, যখন দেখলাম শুধুমাত্র ডায়রীর প্রথম পাতায় একটি মাত্র নবজাতক কবিতা, প্রায় ৪০-৪৫ বছর পর।
বিনীত একটি অনুরোধ; কিছু লিখতে গেলে আকারে বড় না ছোট হলো তার উপর মনোনিবেশ না করাটাই বোধ হয় ভালো। হয়ত ভুল একটি সাজেশন, তাও বললাম, কারণ কোন লিখা, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, ডায়রী সে যাই হোক না কেন তার দৈর্ঘত্বে ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু যায় আসেনা, যতক্ষন পর্যন্ত না তার ভেতরগত আবেগ, কাঠামো এবং উপস্থাপন ভঙ্গীর সাথে অসততা না হচ্ছে। হ্যাঁ, আপনার লিখাটা বড়, তাতে কি? এই যে আপনার সুন্দর এই লিখাটির প্রেক্ষিতে আমি এই বিশাল আকারের মন্তব্য করে ফেলছি, তাতেই বা কি? মন থেকে যা বলতে চেয়েছি, বলে গেলাম।
বাহিরের সব কিছু নিয়ে ভেতরগত (সার্বিক অর্থে) এমনতর লিখাকে আমি সাধুবাদ জানাই। ভালো থাকবেন। শুভ কামনা। 🙂
@ছিন্ন পাতা, প্রথমেই ধন্যবাদ এত সুন্দর আর দীর্ঘ মন্তব্য করার জন্য। আসলে লেখাটি আরও বড়। এটা নিয়ে একটি বইয়ের কাজ চলছে। এখানে অংশ বিশেষ দিলাম। এখানে একটু বড় হয়ে গেল বলে আমার মনে হচ্ছিল। মুক্তমনায় স্বাধারণত আমরা এধরনের লেখা পড়তে আসি না। এখানে উপযুক্ত হবে কিনা ভাবছিলাম। এখন মনে হচ্ছে ঠিকই আছে। ভাল থাকবেন আপনি।
চমৎকার লেখা। মা আসলে সবার জন্যই এত বড় সম্পদ, যে অন্যের মাতৃবিয়োগের গল্প শুনতেও কষ্ট হয়। ভালো থাকবেন।
@azizur rahman, ধন্যবাদ। ভাল থাকবেন আপনিও।
মা কে নিয়ে সবচেয়ে সুন্দর লেখা । চোখে পানি এসে গেল। কয়েক বছর আগে চলে যাওয়া আমার মা কে সামনে দেখতে পেলাম। ধন্যবাদ এমন লেখার জন্য।
@হাবিব, হুম। পড়ার জন্য ধন্যবাদ ভাই।
লেখা ভালো লেগেছে, কিন্তু কষ্টই লেগেছে পড়তে, মা আসলে সবার জন্যই এত বড় সম্পদ, যে অন্যের মাতৃবিয়োগের গল্প শুনতেও কষ্ট হয়। যাই হোক, ভালো থাকবেন। 🙂
@রিজওয়ান, ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন।
আপনার মায়ের ছবি আঁকতে গিয়ে আমার মায়ের মুখ বসিয়ে দিলাম। এই একটা বিষয়ে কখনো কারো সাথে এতটা একাত্মতা বোধ করিনি। তাই পড়তে পড়তে আবার উপরে গিয়ে দেখলাম গল্প পড়ছি না ত ? আপনি ছেলে হয়ে মায়ের অনুভুতি উপলব্ধি করতে পেরেছেন..আপনাকে শ্রদ্ধা জানাই।
ছোটবেলায় অনেককিছু বদলে দেবার স্বপ্ন দেখতাম। এখন ভাবি চেষ্টা করেও আমার মায়ের জীবনটাই আমি বদলাতে পারিনি। আর কি …?
@শ্রেয়া, হুম। কষ্টটা ওখানেই – ইচ্ছা থাকলেও আমরা অনেক কিছু পারি না। ধন্যবাদ আপনাকেও। ভাল থাকুন।
চমৎকার লেখা। বাবা-মা ই আমার কাছে ঈশ্বর, তাই আলাদাভাবে কোন কল্পিত সৃষ্টিকরতা বা ঈশ্বর এর প্রয়োজন অনুভব করিনা। লেখককে ধন্যবাদ ।
@ভক্ত, ddddধন্যবাদ আপনাকে। ভাল থাকবেন।
জার্নালটা ভাল লেগেছে। গ্রাম আর শহরের জীবনের ভিতরে পার্থক্যটা প রিস্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। তবে সব কিছুর মধ্যে মায়ের অবস্তানটা বেশ দুঃখের মলিনতায় ভারাক্রান্ত।
@শাখা নির্ভানা, ধন্যবাদ । ভালো থাকবেন।
খুব ভালো হয়েছে। লেখা গতিশীল ও প্রাণবন্ত।
অর্ধেক পড়লাম। বাকীটুকু পর পড়ব।
@আবুল কাশেম, খুব খুশি হলাম শুনে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া। ভালো থাকবেন।
লেখাটা বেশ বড়। কষ্ট করে কেউ পড়লে জানান দেবেন…