“আল্লায় বহুত যত্তন গরি মানুষ বানাইয়ে। আশরাফুল মখলুকাত বানাইয়ে। কদুন নালায়েক নাফরমান শতানেডকদ্দে – মানুষ নাকি আইস্যেদে বান্দরত্তুন। নাউজুবিল্লাহ। আঁই হিয়ান বিশ্বাস ন গরি। কিন্তু তর মিক্কা চাইলে মনে অয় দে হিতারা ঠিক কতা ক-অর পাল্লায়। তরে আল্লায় ন-বানায়, তুই হারামজাদা হুয়ররবাইচ্চা বান্দরত্তুন পয়দা হইয়স দে”
– চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় এরকম বাণী ক্লাস সেভেন থেকে নাইন পর্যন্ত আমাকে প্রায়ই শুনতে হতো আমাদের ইংরেজি স্যার আবু মির্জা’র কাছ থেকে। স্যারের কথাগুলোকে প্রমিত বাংলায় রূপান্তর করলে শোনাবে এরকমঃ “আল্লাহ অনেক যত্ন করে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির সেরা জীব বানিয়েছেন। কিছু নালায়েক নাফরমান শয়তান বলে- মানুষ নাকি বানর থেকে এসেছে। নাউজুবিল্লাহ। আমি তা বিশ্বাস করি না। কিন্তু তোর দিকে তাকালে মনে হয় তারা সম্ভবত ঠিক কথা বলছে। তোকে আল্লাহ সৃষ্টি করেনি। তুই হারামজাদা শূকরের বাচ্চা জন্মেছিস বানর থেকে”। তখনকার দিনে স্কুলে শিক্ষকদের গালিগালাজ, কানমলা, বেত্রাঘাত এগুলোর সাথে আদর স্নেহের একটা পরশও এতই সহজলভ্য ছিল যে আলাদা করে এগুলো নিয়ে ভাবিই নি কখনো।
‘বানরের পেটে জন্ম নেয়া শূকরের বাচ্চা!’ – কী এক অদ্ভুত জন্তুর সাথে তুলনা করতেন আমাকে আবু মির্জা স্যার। শূকর আর বানরের শংকর প্রজাতির কথা স্যার কীভাবে কল্পনা করেছিলেন জানি না। আজ এতগুলো বছর পর কথাগুলো মনে পড়লো বিবর্তন-বিদ্যা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে গিয়ে। আরো নির্দিষ্টভাবে বলা যায় নিসর্গবিদ দ্বিজেন শর্মার একটা মন্তব্য পড়ে। বিবর্তন তত্ত্বের দুটো ক্লাসিক বই বন্যা আহমেদের ‘বিবর্তনের পথ ধরে’ [1] এবং অভিজিৎ রায় ও ফরিদ আহমেদের ‘মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে’ [2]। বই দুটো সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে নিসর্গবিদ দ্বিজেন শর্মা মুক্তবুদ্ধির চর্চার অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন- “বন্যা, অভিজিৎ, ফরিদ কি দেশে থাকলে এসব বই লিখতেন? আমি ৯৯ ভাগ নিশ্চিত যে লিখতেন না” [3]। দ্বিজেন স্যারের সাথে শত ভাগ সহমত প্রকাশ করার কোন কারণ আমার নেই। বাংলাদেশে বসে যদি দ্বিজেন শর্মা “ডারউইনঃ পিতামহ সুহৃদ সহযাত্রী” লিখতে পারেন, আখতারুজ্জামান স্যার ‘বিবর্তন বাদ’ [4] লিখতে পারেন, তবে বন্যা আহমেদ, অভিজিৎ রায় বা ফরিদ আহমেদ পারবেন না কেন? কিন্তু অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির ব্যাপারটা বিবর্তনের একটি প্রয়োজনীয় অনুসঙ্গ। সে রকম একটা পরিবেশ এখন বৈজ্ঞানিক যোগাযোগের উন্নতির সুযোগে ক্রমশ তৈরি হচ্ছে। আজ বাংলাদেশে বসে কাজ করে যাচ্ছেন অসংখ্য যুক্তিবাদী তরুণ-তরুণী। তাই তো দেখতে পাচ্ছি অনন্তের ‘যুক্তি’র ডারউইন সংখ্যা নিয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনে আলোচনা হচ্ছে [5]। তবুও একটা কথা স্বীকার করতেই হবে- ইউরোপ আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় বসে বুদ্ধির মুক্তি ঘটানো বা যুক্তিবোধে শান দেয়া যত সহজ, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে একই কাজ- অনেক বেশি কঠিন। আজ অস্ট্রেলিয়ায় আছি বলেই হয়তো সুযোগ পাচ্ছি পেছন ফিরে দেখার- কোথায় কীভাবে ঘটেছিল বিবর্তনবাদের সাথে আমার পরিচয়।
স্কুলের বইতে ডারউইনের কথা লেখা ছিল না কোথাও। তাই কলেজে ওঠার আগ-পর্যন্ত চার্লস ডারউইনের নামই শুনিনি কারো কাছে। আমার পঁচিশ বছর পরে যারা স্কুলে গেছে- তাদের অবস্থাও দেখছি প্রায় একই রকম। বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কল্যাণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সমস্ত বই এখন অন-লাইনে পাওয়া যাচ্ছে (www.nctb.gov.bd)। প্রথম শ্রেণী থেকে নবম-দশম শ্রেণীর সব বই খুঁজে দেখলাম কোথাও ডারউইন এবং বিবর্তনবাদ সম্পর্কে কিছু পাওয়া যায় কি না। শুধুমাত্র নবম-দশম শ্রেণীর জীববিজ্ঞান [6] বইয়ের তৃতীয় পৃষ্ঠায় চার্লস রবার্ট ডারউইন (১৮০৯ – ১৮৮২) সম্পর্কে লেখা আছে –
“ইংরেজ প্রকৃতি বিজ্ঞানী ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদের (Theory of Natural Selection) প্রবর্তক। গেলাপেগোস দ্বীপপুঞ্জের জীবসম্প্রদায় পর্যবেক্ষণ করে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত গবেষণা পুস্তক ‘Origin of Species by means of Natural Selection’এ তিনি তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেন”।
তারপর চতুর্থ পৃষ্ঠায় চার্লস ডারউইন এর একটা হাতে-আঁকা ছবি ছাপানো হয়েছে। পুরো বইয়ের আর কোথাও ডারউইন বা বিবর্তন তত্ত্ব সম্পর্কে আর কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। আমার মনে হয় না বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক এই ৩-৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ডারউইন সম্পর্কিত লাইন দু’টো ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন মনে করবেন। স্কুলগুলোতে ‘আবু মির্জা’র মত শিক্ষকের অভাব নেই। সুতরাং এটা বুঝা যায় যে বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের কোন শিক্ষার্থীর পক্ষে স্কুলের পড়া থেকে বিবর্তন-বাদ সম্পর্কে কিছুই জানা সম্ভব নয়।
ধরে নিলাম বিবর্তন সম্পর্কে স্কুল-পর্যায়ে না পড়লেও চলে। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণী থেকেই যে ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে! কী লেখা আছে ধর্মীয় শিক্ষার বইগুলোতে? তৃতীয় শ্রেণীর ‘ইসলাম-শিক্ষা’ [7] বইয়ের একেবারে প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম অনুচ্ছেদে একটা ছবির পাশে লেখা আছে-
“ছবিতে আমরা কী দেখি? আমরা দেখি আম গাছ, কাঁঠাল গাছ, নারিকেল গাছ, সুপারি গাছ। আমরা আরও দেখছি নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, চাঁদ-তারা ও ফসলের মাঠ। তোমরা কি বলতে পার, এ সবকিছু কে সৃষ্টি করেছেন? মহান আল্লাহ এসব সৃষ্টি করেছেন। মানুষ, পশু-পাখি, পোকা-মাকড় ইত্যাদিও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তিনি এদের রিয্কদাতা ও পালন-পালনকারী”। (পালন-পালনকারী-ই লেখা আছে, লালন-পালনকারী নয়)।
তৃতীয় শ্রেণীর ‘হিন্দুধর্ম শিক্ষা’ [8] বইয়েরও একেবারে প্রথম পৃষ্ঠায় একটি নিসর্গ দৃশ্য, এবং তার নিচে লেখাঃ
“সুন্দর এই পৃথিবী। এই পৃথিবীর অনেক রূপ। কোথাও উঁচু পাহাড়-পর্বত। কোথাও সমতল ভূমি, কোথাও মরুভূমি। আবার কোথাও নদী, কোথাও সাগর। মাথার উপর নীল আকাশ। ডালে ডালে পাখি। আরও কত যে জীবজন্তু। এসব কিছু কে সৃষ্টি করলেন? এর এক জন স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা আছেন। যেমন কাঠমিস্ত্রি তৈরি করেন চেয়ার-টেবিল। রাজমিস্ত্রি তৈরি করেন দালান। তেমনি সব কিছুর একজন স্রষ্টা আছেন। একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীর। এ সৃষ্টিকর্তার নাম কী? অনেক নাম তাঁর। তাঁকে কেউ বলে ঈশ্বর। কেউ বলে গড। কেউ বলে আল্লাহ। যেমন একই জলকে কেউ বলে ওয়াটার। কেউ বলে পানি। আমরা হিন্দু। হিন্দুরা সৃষ্টিকর্তাকে বলে ঈশ্বর”।
তৃতীয় শ্রেণীর ‘খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা’ [9] বইতেও একই অবস্থা। প্রথম পৃষ্ঠাতেই লেখা আছে
“আমাদের মনে অনেক সময় প্রশ্ন জাগে, আলো কেন সব সময় থাকে না? আলো কে সৃষ্টি করল? কোথা থেকে অন্ধকার আসে? অন্ধকার কেন নেমে আসে? মানুষ কি আলো বা অন্ধকার সৃষ্টি করতে পারে? যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন তিনি কে? ইত্যাদি। যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন তিনিই সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর। তিনি সব কিছু মাত্র ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। প্রথম দিনে তিনি সৃষ্টি করেছেন আলো। দ্বিতীয় দিনে তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ। এসব সৃষ্টি করার জন্য ঈশ্বরের কোন কিছুরই দরকার হয়নি। শুধু কথার দ্বারাই তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন”।
তৃতীয় শ্রেণীর ধর্মশিক্ষার বইগুলোর মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ‘বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা’ [10]। এ বইয়ের কোথাও সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। চতুর্থ থেকে নবম-দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলাম, হিন্দু এবং খ্রিস্ট ধর্মের সবগুলো বইতেও আল্লাহ, ভগবান, আর ঈশ্বরের সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা আলোচনা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো- যে শিক্ষার্থী এরকম বাধ্যতামূলক ধর্মশিক্ষার নামে স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্বে মগজ-ভর্তি করে কলেজে ওঠে- তার পক্ষে হঠাৎ বিবর্তন-তত্ত্বে আস্থাশীল হয়ে ওঠা কতখানি সহজ?
আমাদের সময়ে ধর্ম-শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল না। স্কুলে বিকল্প বিষয়ের ব্যবস্থা থাকলে ধর্মশিক্ষা ছাড়াও এসএসসি পাস করা যেতো। কিন্তু এরশাদ সাহেব ক্ষমতায় এসে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার পাশাপাশি স্কুলে ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছিলেন। উচ্চ মাধ্যমিকের কোন কোন প্রাণিবিজ্ঞান বইয়ের পেছনের দিকে বিবর্তনবিদ্যার ওপর একটা অধ্যায় থাকলেও তা কখনো পড়ানো হয়নি, পড়াও হয়নি। এখনো এ অবস্থার একটুও উন্নতি হয়নি। অধ্যাপক আখতারুজ্জামান ঠিকই উপলব্ধি করেছিলেন-
“বেশ কয়েক বছর থেকে দেশে বিজ্ঞানবিরোধী সাম্প্রদায়িক ও ধর্মান্ধ মৌলবাদের চলছে রমরমা। এক শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তকচ্চ প্রসার ঘটছে মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণার। জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা প্রতিষ্ঠা করার একটি সচেতন ও সংগঠিত প্রচেষ্টা চলছে এসব স্থানকে কেন্দ্র করে। তাই বলা যায় এগুলো হয়ে পড়েছে মধ্যযুগীয় মুর্খতা প্রচার কেন্দ্র” [1]।
১৯৮৬ সালে আমি যখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই- সীমিত পরিসরে বিবর্তনবিদ্যা পড়ানো হতো প্রাণিবিদ্যা বিভাগে। কিন্তু কয়েক মাস পরেই ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র উত্থান ঘটে। তাদের চাপের মুখে বিবর্তনবাদ বাদ পড়ে যায়। ক্রমে ক্রমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসেও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে বিবর্তনতত্ত্ব। ২০০৬ সালে দৈনিক সমকালে ‘বাংলাদেশে কি বিবর্তন পড়ানো হচ্ছে?’ শিরোনামে হুমায়ূন রশীদ রচিত একটি সিরিজ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়[1,11]। সেখানে অনেক শিক্ষার্থী বলেছিলেন পরীক্ষায় পাসের জন্য হয়তো বিবর্তনতত্ত্ব তাদের পড়তে হয়, কিন্তু তারা বিবর্তন তত্ত্বে বিশ্বাস করে না। এখন অবশ্য অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে পরীক্ষা পাসের জন্যও কাউকে বিবর্তনতত্ত্ব পড়তে হয় না। কারণ পরীক্ষাতেও বিবর্তনতত্ত্ব থেকে কোন প্রশ্ন আসে না।
শিবিরের রাজত্বকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যিকারের অন্ধকারের যুগ নেমে এসেছিল। আর সেই আঁধার সময়েই পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হুজ্জোত আলী প্রামাণিক লিখলেন “Religious and Scientific views of the Universe”। সেই সময়ে প্রামাণিক স্যারের সংস্পর্শে এসে বিবর্তনবিদ্যা সহ আরো অনেক আলোকিত দরজা খুলে যায় আমার। তখন স্বাভাবিকভাবেই বইটি প্রকাশ করতে রাজী হয়নি ইউনিভার্সিটি প্রেস কিংবা অন্য কোন প্রকাশক। কিন্তু দুঃসাহসী প্রামাণিক স্যার দমে যাবার পাত্র নন। তিনি তিন-দিন ব্যাপী এখলাস উদ্দিন স্মারক বক্তৃতা’র বিষয় নির্বাচন করলেন “Religious and Scientific views of the Universe”। তখন দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ডীন থেকে শুরু করে আরো অনেক “বিজ্ঞানী”র বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার নামে মারমুখী বিজ্ঞান-ধর্ষণ। বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও উপাত্ত দাখিল করে প্রামাণিক স্যার ব্যাখ্যা করলেন কোরান বা বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব কেন ভুল, ন্যূহের বন্যা কীভাবে অসম্ভব, জীব-জগত ‘সৃষ্টি’ হয়নি- বিবর্তনের ফলে ‘উৎপন্ন’ হয়েছে। বক্তৃতার দ্বিতীয় দিন শিবিরের ছেলেরা স্যারের হাত কেটে নেবে বলে হুমকি দিলো। স্যার হুমকিকে পাত্তা না দিয়ে বক্তৃতা দিলেন। শেষের দিন বক্তৃতা-কক্ষে তালা লাগিয়ে দেয়া হলো। স্যারের বাসার সামনে বোমা পড়লো। প্রক্টর এসে আইনশৃঙ্খলা ঠিক রাখার স্বার্থে বক্তৃতা-মালার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন। সৃষ্টিবাদীদের পেশির দাপট তখনো ছিল- এখনো আছে।
একটা ব্যাপার সবসময় চোখে পড়ে – সেটা হলো ধর্মবাদী সৃষ্টিবাদীদের অসহিষ্ণুতা, গোয়ার্তুমি। তারা যে ধর্মশিক্ষার নামে শিক্ষার্থীদের একেবারে শিশুবয়স থেকেই যতসব গাঁজাখুরি অবৈজ্ঞানিক মিথ্যা-কথা [7-9] শেখাতে শুরু করেন তাতে যুক্তিবাদী বিজ্ঞান-মনস্কদের গাত্রদাহ হলেও তারা কিন্তু কাউকে তেড়ে মারতে আসেন না, ধর্মশিক্ষার বই ছিঁড়েও ফেলেন না বা নিষিদ্ধ করার দাবীও তোলেন না। অথচ সৃষ্টিবাদীদের দেখুন- কার্যকরী বিবর্তনতত্ত্বকে ঠেকানোর জন্য এমন কোন হীন কাজ নেই যা তারা করেন নি বা করার চেষ্টা করেন নি। মধ্যযুগীয় পেশিশক্তির দাপট যেখানে অচল সেখানে ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন নামক অপবিজ্ঞান চালু করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন। সেই অপচেষ্টায় শরিক হয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ থেকে শুরু করে আরো অনেক উচ্চশিক্ষিত অপবিজ্ঞানী। (বিস্তারিত তথ্যের জন্য পড়ুন বিবর্তনের পথ ধরে [1]-র দশম অধ্যায়)।
আমেরিকানদের তুলনায় অস্ট্রেলিয়ানরা অনেক বেশি উদারপন্থী বলে আমার ধারণা। অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী একজন নাস্তিক মহিলা যিনি বিয়ে না করেও তাঁর বয়ফ্রেন্ডের সাথে থাকেন। অস্ট্রেলিয়ান গ্রিন পার্টির প্রধান সিনেটর বব ব্রাউন একজন সমকামী। কিন্তু তাঁদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা কখনোই এ প্রসঙ্গে একটাও কটুবাক্য বলেন না। এমনকি চার্চের কট্টর পাদ্রীদেরও চুপ করে থাকতে হয় রাষ্ট্রের ব্যক্তিস্বাধীনতার নীতির কারণে। দেখা যাক এরকম একটা দেশে ডারউইনের তত্ত্বের কী অবস্থা।
চার্লস ডারউইন তাঁর বিখ্যাত বিগল সমুদ্র-যাত্রার পথে থেমেছিলেন অস্ট্রেলিয়াতেও। ১৮৩৬ সালের জানুয়ারিতে নিউ সাউথ ওয়েল্স এর ব্লু-মাউন্টেনের জীব ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্য দেখেছিলেন ডারউইন। তাঁর সম্মানে অস্ট্রেলিয়ার নর্দান টেরিটরির রাজধানী শহরের নামকরণ করা হয়েছে – ডারউইন। ১৮৬৯ সালে ২৩৩ বর্গ-কিলোমিটারের এই শহরটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত এর নাম ছিল পামারস্টন। ডারউইন শহরের সমুদ্র-বন্দরের নাম ‘পোর্ট ডারউইন’। ক’বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ‘চার্লস ডারউইন ইউনিভার্সিটি’।
ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের হাজারো প্রমাণ ছড়িয়ে আছে অস্ট্রেলিয়ার আনাচে কানাচে। মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন প্রকান্ড একটা দ্বীপ হওয়ার কারণে পুরু দ্বীপটাই হয়ে ওঠেছে বিবর্তনের পরীক্ষাগার। এতবড় দ্বীপটার আবহাওয়া বিচিত্র। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মরুভূমি এখানে। নানারকম আবহাওয়ার সাথে টিকে থাকার জন্য এখানে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিবর্তন ঘটেছে অনেক। মাত্র কয়েক প্রজাতির ইউক্যালিপ্টাস থেকে বিবর্তিত হতে হতে এখন প্রায় আটশ’ প্রজাতির ইউক্যালিপ্টাস বা গাম ট্রি পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়ায়। এদের মধ্যে আছে নিচু এলাকায় নদীর পানিতে টিকে থাকা ‘রেড রিভার গাম’, একদম শুকনো বালিতে টিকে থাকা ‘হোয়াইট গাম’, বরফের মধ্যে টিকে থাকা ‘স্নো গাম’। গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড উত্তাপে প্রায়ই আগুন লেগে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় মাইলের পর মাইল ইউক্যালিপ্টাসের বন। কিছুদিন পর দেখা যায় সেই পোড়া গাছ থেকেই জন্ম নিচ্ছে নতুন গাছ। প্রতিকূল পরিবেশের সাথে টিকে থাকার জন্য জিন-গত পরিবর্তন ঘটে চলেছে এ গাছগুলোর মধ্যে।
অস্ট্রেলিয়ায় বিবর্তন তত্ত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো অস্ট্রেলিয়ান খরগোশের উৎপত্তি। ইউরোপিয়ানরা এসে ঘাঁটি করার আগপর্যন্ত কোন ধরনের খরগোশ ছিল না অস্ট্রেলিয়ায়। মাত্র বারোটি খরগোশ নিয়ে ইংল্যান্ড থেকে ভিক্টোরিয়ায় এসেছিলেন এক ইংরেজ পরিবার ১৮৫৯ সালে। কয়েক বছরের মধ্যেই Oryctolagus cuniculus প্রজাতির এই বারোটি খরগোশ দ্রুত বংশবিস্তার করতে থাকে। বছরে প্রায় একশ’ কিলোমিটার হারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে ১৮৮৬ সালের মধ্যেই ভিক্টোরিয়া থেকে সাউথ অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত পৌঁছে গেলো হাজার হাজার খরগোশ। ১৯০৭ সালের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো কয়েক কোটি খরগোশ। গাছ-পালা ফলমূল শাকসব্জি সব চলে যেতে শুরু করলো খরগোশের পেটে। মেরে, কেটে, বিষ দিয়ে- যত ধরণের পদ্ধতি জানা ছিলো সব প্রয়োগ করেও কিছুতেই কিছু করা গেলো না। খরগোশের সংখ্যা বেড়েই চললো। Rabbit-proof fence এর প্রচলন ঘটে এ সময়। কিন্তু কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছিল না খরগোশের বংশবৃদ্ধি। অস্ট্রেলিয়ার গরু আর ভেড়ার ফার্ম মারাত্মক হুমকির মধ্যে পড়ে গেলো, কারণ গরু-ভেড়ার সব ঘাস চলে যাচ্ছে খরগোশের পেটে [12]।
সব অস্ত্র ব্যর্থ হবার পর বিজ্ঞানীরা জীবাণু অস্ত্র ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিলেন। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর অস্ত্র তৈরি হলো- মশা বাহিত ভাইরাস মাইজোম্যাটোসিস। এই ভাইরাস কেবল ইউরোপিয়ান খরগোশ মেরে ফেলবে, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার অন্য কোন প্রাণীর ক্ষতি করবে না। ১৯৫০ সালে এ ভাইরাস ছাড়া হলো। দু’বছরের মধ্যেই খরগোশের মড়ক লেগে গেল। খরগোশের মৃত্যুর হার দাঁড়ালো প্রায় ৯৯.৯%। কিন্তু জীববৈজ্ঞানিক বিবর্তন শুরু হলো। শতকরা শুন্য দশমিক এক ভাগ খরগোশের জিনের মিউটেশানের ফলে ক্রমশ এক নতুন ধরনের খরগোশের উৎপত্তি হলো যা ইউরোপিয়ান খরগোশ থেকে আলাদা- অস্ট্রেলিয়ান খরগোশ যারা মাইজোম্যাটোসিস ভাইরাসের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে পারে। যে প্রজাতির খরগোশ ইউরোপ থেকে আনা হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায় – সে প্রজাতির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছে। বর্তমান প্রজাতির অস্ট্রেলিয়ান খরগোশের মাইজোম্যাটোসিস ভাইরাসের বিরুদ্ধে টিকে থাকার ক্ষমতা প্রায় ৬০%।
চোখের সামনে ঘটা বিবর্তন দেখেও বাইবেলান্ধ পাদ্রীর অভাব নেই অস্ট্রেলিয়ায়। বিশেষ করে চার্চ থেকে যখন প্রচুর টাকা-পয়সা সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়। তাই তো দেখা যায় ২০০৫-০৬ সালে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের পালে হাওয়া দিয়েছে অনেকগুলো অস্ট্রেলিয়ান চার্চ ও খ্রিস্টান স্কুল [13]। আমেরিকার স্কুলিং সিস্টেম ফেডারেল গভমেন্টের অধীন। সেখানে ধর্মীয় স্কুলে রাষ্ট্রীয় সাহায্য দান আইনের পরিপন্থী। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় স্কুল শিক্ষা রাজ্য সরকারের অধীন। রাজ্য সরকার ইচ্ছে করলে যে কোন ধর্মীয় স্কুলেও সরকারী সাহায্য দিতে পারে। ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনওয়ালারা সে সময় অনেক ক্যাথলিক স্কুলের বিজ্ঞানের সিলেবাসে আই-ডি অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা চালায়। কিন্তু প্রচন্ড সমালোচনা শুরু হয় মিডিয়ায়। এগিয়ে আসে দেশের প্রায় সত্তর হাজার বিজ্ঞানী এবং তাদের প্রতিনিধি ‘অস্ট্রেলিয়ান একাডেমি অব সায়েন্স’। সৃষ্টিবাদ ও ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন সম্পর্কে এক কড়া বিবৃতিতে অস্ট্রেলিয়ান একাডেমি অব সায়েন্স পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেয় যে ‘Intelligent design is not science’ (www.science.org.au/policy/creation.html)। আমেরিকান একাডেমি অব সায়েন্সও যে এরকম বিবৃতি দিয়েছে তা অভিজিৎ রায় ও বন্যা আহমেদ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন ‘বিবর্তনের পথ ধরে’ [1]-র দশম অধ্যায়ে। ন্যাশনাল একাডেমিক প্রেস থেকে প্রকাশিত ‘সায়েন্স এন্ড ক্রিয়েশানিজম’ বইটার [14] কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য।
বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করার সুবাদে অনেক মতবাদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সাথে আলোচনা করার সুযোগ হয় আমার। তাদের মধ্যে বিবর্তন তত্ত্বে বিশ্বাসীর সংখ্যা অনেক বেশি। হতে পারে পদার্থ-বিজ্ঞানের মানুষ বলে এ ধরণের মানুষের সাথেই আমার আলাপ হয় বেশি। তবুও এটা বলা যায় যে এদেশে গায়ের জোরের চেয়েও যুক্তির জোর প্রবল। সুস্থ সমাজে এটাই তো কাম্য। ক্রমশ যুক্তিবাদী হয়ে উঠবে সারা পৃথিবীর মানুষ – ডারউইন দিবসে এটাই আমার কামনা।
তথ্যসূত্রঃ
[1] বন্যা আহমেদ. বিবর্তনের পথ ধরে. ঢাকা: অবসর, ২০০৭.
[2] অভিজিৎ রায়, ফরিদ আহমেদ. মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে. ঢাকা: অবসর, ২০০৭.
[3] দ্বিজেন শর্মা. ডারউইনঃ বিশ্বে ও মহাবিশ্বে. প্রথম আলো ২৯ জুন. ঢাকা, ২০০৭.
[4] ম আখতারুজ্জামান. বিবর্তনবাদ. ঢাকা: হাসান বুক হাউজ, ২০০০.
[5] অনন্ত বিজয় দাশ. যুক্তি https://blog.mukto-mona.com/?p=13155 ২০১১.
[6] ডঃ ইকবাল আজীজ মুত্তাকী, নাসিম বানু, ডঃ মোঃ আবুল হাসান, গুল আনার আহমেদ. মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান নবম-দশম শ্রেণী. ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড,, ২০০৮.
[7] অধ্যাপক আ ন ম আবদুল মান্নান খান, অধ্যাপক মুহাম্মাদ মনসুরুর রহমান, অধ্যাপক মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন, মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান. ইসলাম-শিক্ষা তৃতীয় শ্রেণী. ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড,, ২০০৯.
[8] সুনীত কুমার ভদ্র, নিরঞ্জন অধিকারী, মলয় কুমার সাহা. হিন্দুধর্ম শিক্ষা তৃতীয় শ্রেণী. ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড,, ২০০৯.
[9] ফাদার আদমে এস পেরেরা সিএসসি, সিস্টার ফিলোমিনা কুইয়া সিএসসি, যোসেফ গোমেজ. খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা তৃতীয় শ্রেণী. ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড,, ২০০৯.
[10] ডক্টর সুনন্দা বড়ুয়া, নার্গিস বেগম. বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা তৃতীয় শ্রেণী. ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড,, ২০০৯.
[11] হুমায়ূন রশীদ. পরীক্ষায় পাশের জন্য পড়ি. দৈনিক সমকাল জুলাই ১৫,. ঢাকা, ২০০৬.
[12] Alice Alstone. Book of Australian Facts. Sydney: Reader’s Digest, 1992.
[13] Robyn Willams. Unintelligent Design why god isn’t as smart as she thinks she is,. Sydney: Allen & Unwin, 2006.
[14] National Academy of Sciences. Science and Creationism A view from the National Academy of Sciences,. Washington DC,: National Academy Press, 1999.
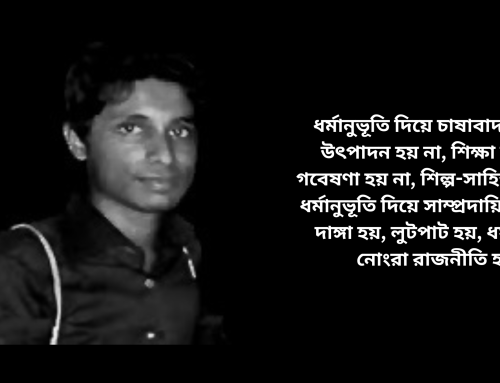
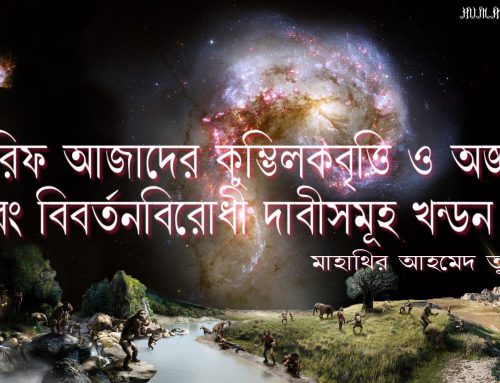
[img]http://www.facebook.com/photo.php?fbid=490323057661223&set=a.395077007185829.111942.100000506002272&type=1&theater[/img]
খরগোস এর ব্যপারে যে বিবর্তনটা হল সেটার সাথে বানর থেকে মানুষ হওয়ার সাদৃশ্য কতখানি ? বিবর্তনের নমুনা আরও দেখতে চান , আরও পাবেন ।
এখন যদি বাংলাদেশের ওপর দিয়ে হেলিকপ্টারে করে বায়ুবাহিত কোন মরণ ভাইরাস ছড়াতে শুরু করেন , দেখবেন ১৬ কোটি [বা ১৮ কোটি ] বাঙ্গালীর মাঝে ১০০-১৫০ জন হলেও সম্পূর্ণ সুস্থদেহে ঘুরে বেড়াচ্ছেন … বেশ কিছু শারীরতাত্ত্বিক এবং সাইকোলজিক্যাল পরিবর্তনও আসবে সেই সাথে – সন্দেহ নেই ।
তবে কখনই বিবর্তনের ফলে তারা আমাদের থেকেও উন্নত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হবে না !
ড্যামেজ হবে , ইম্প্রুভমেন্ট নয় …
মানুষ থেকে বানর হলেও হতে পারে , কিন্তু বানর থেকে মানুষ হওয়ার ব্যাপারটা শুধুই থিয়োরি ।
[আমিও আল্লাহকে বিশ্বাস করি । তবে শুধু বিশ্বাসে অন্ধ হয়েও কিন্তু কমেন্ট করছি না আমি । এ ধরনের মন্তব্য করা হলে সেটা হবে দুঃখজনক একটা ব্যাপার । যুক্তির বাইরে কথা না বলার-ই চেষ্টা করেছি আমি ]
প্রদীপ দেব,
আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এমন একটি সুখপাঠ্য তথ্যবহূল প্রবন্ধের জন্য।
তথ্যবহুল লেখাটা ভালো লাগলো।
দ্বিজেন শর্মার মন্তব্যে আপনার প্রতিক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়া একই। বন্যাপা, অভিদা কিংবা ফরিদ ভাইরা বাংলাদেশে থাকলেও এমন বই লিখতেন। আমাদের বুড়ো প্রজন্মের এটা একটা ভুল ধারণা যে- দেশে থেকে কাজ করা সম্ভব না। অযথাই তারা ভয় টয় দেখান মাঝে মাঝে। এসব নিয়ে চিন্তা না করে কাজ করলেই হয়। বাংলাদেশ মৌলবাদিরা যতো গর্জায় ততো বর্ষায় না। আর এখন দেখছি, এদেশের বেশিরভাগ মানুষই গোঁড়া না। অনন্ত আমি যাদের সাথে চলাফেরা করি।
আজকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডারউইন ডে উপলক্ষে ছোটখাট একটা পাঠচক্র হলো টিএসএসিতে। বিশ পঁচিশজন উপস্থিত ছিলেন। আশা করি, কয়েকমাস পর বন্যাপা, অভিদারা দেশে আসলে বড় সড় একটা সেমিনার করা যাবে।
@রায়হান আবীর, আমরা দেশটাকে যতটা মৌলবাদী বলে জুজুর ভয় দেখাই আসলে দেশটা ততটা মৌলবাদী না। এটা ঠিক যে, আগে আরও অনেক কম ছিল, এখন মৌলবাদ সেই তুলনায় বেড়েছে, কিন্তু সেই সাথে পাল্লা দিয়ে প্রগতিশীলতাও বাড়ছে। কয়েক বছর আগে বিবর্তনের পথ ধরে এবং মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে বইগুলো নিয়ে ডঃ আখতারুজ্জামান, শহিদুল ইসলাম, দ্বিজেন শর্মা, অজয় রায়দের উপস্থিতিতে অডিটেরিয়াম ভর্তি (প্রায় ৫ শ’ লোক হয়েছিল শুনেছিলাম) লোক নিয়ে এক বিশাল সেমিনার করা হয়েছিল। টিকেট কেটে শয়ে শয়ে লোক আসে আসিফের বিজ্ঞান বক্তৃতা শুনতে। অবশ্যই আমরা চাই এই প্রগতিশীলতা আরও ছড়িয়ে পড়ুক, কিন্তু দেশটা হিজাব পড়া মৌলবাদীতে ছেয়ে গেছে কথাগুলোও কিন্তু আসলে ঠিক নয়। দেশে অনেক কিছুই করা সম্ভব, আমার কাছে প্রায়ই মনে হয়, করার লোক নেই বলেই সেগুলো করা হয়ে ওঠে না।
@বন্যাপা, আপনারা দেশে আসলে আমরাও বড়সড় একটা সেমিনার করবো…
@রায়হান আবীর, অনেক ধন্যবাদ।
কবে নাগাদ?
অফ টপিকঃ আপনাদের মেডিকেল ফিজিক্সের জানুয়ারি কনফারেন্স কেমন হলো?
@প্রদীপ দেব,
কবে নাগাদ সেটা নির্ভর করছে বন্যাপাদের আসার ওপর। যথাসময়ের আগেই নিশ্চয়ই আমরা তারিখ ফাইনাল করে, গণসংযোগ শুরু করে দিতে পারব।
আর মেডিক্যাল ফিজিক্সের কনফারেন্সটা পিছিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিলো আঠারোই ফেব্রুয়ারি। এ কারণেই গত কয়েকদিন মারাত্মক ব্যস্ত। স্বাস্থ্যমন্ত্রীরকে একটা এক্সিবিশনও দেখানো হবে, সব মিলিয়ে।
আমাদের মত অজ্ঞদের কথা চিন্তা করেই প্রদীপ দেব খরগোসসহ চমৎকার সব উদাহরণ দিয়েছেন। ইসলাম, হিন্দু ও খৃষ্টান ধর্মের পাঠ্যপুস্তক থেকে উদাহরণও দারুন হয়েছে। বিবর্তানবাদ নিয়ে একটু আলোকিত হলাম।
আর এরশাদ শুধু ধর্ম-শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেই ছাড়েনি, ধর্মকে ব্যাক্তি জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অংশ করে ছেড়েছেন।
ডারউইন দিবস উপলক্ষ্যে ব্যানারগুলো অপূর্ব! সামিয়ার কাজ নিশ্চয়ই।
@গীতা দাস,
না, সামিয়ার নয়। বন্যার করা।
@গীতাসি, ফরিদ ভাই, সামিয়া হচ্ছে ‘প্রো’, আমি হচ্ছি এ্যমেচার ‘ব্যানারক’। সামিয়ার পেশাদার মানের ব্যানারটা খুব অচিরেই লোড করা হবে।
@ব্যানারক বন্যাদি, দারুণ হইসে।
@বন্যা আহমেদ,
অভিনন্দন বন্যা, মুক্ত-মনার সদস্য হিসেবে আপনাকে নিয়ে সত্যিই আমরা গর্বিত।
এত গুণ একজনের মধ্যে! অভিজিৎ ( জহুরী) জহর চিনে।
ধন্যবাদ গীতাদি।
যাক্, অবশেষে ডারউইনের আশীর্বাদে প্রদীপের দেখা মিললো আবার মুক্তমনায়। কডে আছিলা?
তথ্যসমৃদ্ধ লেখা। ধন্যবাদ।
@ইরতিশাদ ভাই,
বারিত গেইলাম দে।
প্রদীপ দেব,
এমন একটি তথ্যবহুল লেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। অস্ট্রেলিয়ার খরগোসদের উদাহরনটা খুব ভাল লাগল। যুক্তি দিয়ে কথা বলেনা এমন কিছু মানুষ বিবর্তনবাদের কথা শুনলেই একটা সবজান্তার হাসি দিয়ে জিজ্ঞেস করে “আচ্ছা ঠিক আছে বুঝলাম বিবর্তনবাদ ঠিক আছে, এখন এমন একটা উদাহরন দাও যেখানে নিজের চোখে দেখছ বান্দরের পেট থাইকা মানুষ জন্মাইছে। পারবা না, সুতরাং বিবর্তন পুরাই ভাওতাবাজী।” জানি এই ঘরনার মানুষদের সাথে তর্ক করা বৃথা, তারপরেও অস্ট্রেলিয়ার খরগোসের উদাহরন দিয়ে কিছুটা বোঝানোর চেষ্টা করা যাবে।
আচ্ছা, আমাদের দেশে ক্ষেতে খামারে পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ করতে কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। শুনেছি যে কীটনাশকে পূর্বে ঠিক মতই পোকামাকড় মারা যেত, এখন আর সেটা কাজ করে না। নতুন আরও শক্তিশালী কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। এটাও কি বিবর্তনের ফল?
@সাদাচোখ,
একেবারেই সত্যি কথা। আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে এই ব্যাপারে। আমি বাসায় নিয়মিত কীট পতঙ্গের উপদ্রব বন্ধ করার জন্যে পেশাদার কীটপতঙ্গ নাশ করার লোক নিয়োগ করতাম প্রায় প্রত্যেক বছর। দুই তিন বছর ভালো গেল। তারপর দেখি আর তেমন ফল হচ্ছে না। ঐ পেশাদার লোক বলল তাদেরকে কয়েক বছর পর পর নতুন ফর্মুলা ব্যবহার করতে হয়। কারণ, মাত্র এক জোড়া পতঙ্গ বাঁচলেই তাদের প্রজন্ম অন্য ধরণের হয়ে যায় যারা পূর্বের ঔষধের বাধা অতিক্রম করে নিয়েছে। এই ভাবেই চলতে থাকে তাদের ক্রম বিকাশ।
এই নিয়ম আগাছার উপরেও চলে।
আমার মনে হয় এই প্রক্রিয়া বিবর্তনের চাক্ষুস প্রমাণ।
@সাদাচোখ,
হ্যাঁ। বন্যা আহমেদের “বিবর্তনের পথ ধরে’র চতুর্থ অধ্যায়ে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
ইন্টার লেভেলে আমাদের অত্যন্ত প্রিয় প্রাণিবিদ্যার এক স্যার বিবর্তন বাদ নিয়ে কয়েকটি কথা বলতে গিয়ে কী পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন তা আজো চোখে ভাসে। তিনি বিবর্তন নিয়ে কিছু বলার আগে বললেন যে, তিনি ব্যক্তিগত জীবনে একজন ধার্মিক মানুষ এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসী!আমি ভাবছিলাম- বিজ্ঞান পড়ানোর সময় ধর্ম বিষয়ক আলোচনা টেনে আনা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত।ওই স্যার হয়তো ভেবেছেন- উনি বিবর্তন নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করলে অনেক স্টুডেন্ট খেপে যাবে।কিন্তু উনি এটা ভাবেননি যে উনি যদি বিবর্তন নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করে বিষয়টি সবার কাছে পরিস্কার করতেন তাহলে হয়তো কিছু ছেলেমেয়ের চোখ খুলে যেতো।তবে তিনি যদি নিজেই বিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে কনফিডেন্ট না হয়ে থাকেন, তাহলে আর কিছু বলার থাকে না।
আমাদের স্কুল-কলেজে বিবর্তন নিয়ে কোন ধারণাই দেয়া হয় না, বরং সবার সামনে বিভ্রান্তিকর চিত্র পেশ করা হয়। তাইতো আজকালের স্কুলের ছেলেমেয়েদের কাছে বিবর্তন মানে ‘বানর থেকে মানুষ হয়েছে’-এই ভুল ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।বিবর্তন তত্ত্ব তাদের কাছে কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নয়- বরং হাসি-ঠাট্টার উপকরণ। এমনকি ভার্সিটি লেভেলের আমার এক ‘বিজ্ঞান পড়ুয়া’ বন্ধুকে বিবর্তন নিয়ে কিছু কথা বলতেই সে চোখমুখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছে- ‘তুই সত্যিই ভাবিস যে তুই বানর থেকে এসেছিস?'(!)
ওর জন্য আমার সত্যিই সেদিন করুণা হয়েছিল।
@নিটোল,
রিচার্ড ডকিন্স যেমন পাদ্রীকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলেন, “আমি এসেছি এইপ থেকে। আপনি?”
১. লেখাটি খুবই ভাল লেগেছে।
২.অস্ট্রেলিয়ার বন্য খরগোস আমার কাছেও ভিন্ন মনে হয়েছে যদিও সাদা খরগোসকেই মানুষের বাসায় পালতে দেখেছি। কয়েকদিন আগে সিডনি হতে রাতের বেলা ড্রাইভ করে মেলবোর্ন এসেছিলাম এবং পথে অনেক ছোট ছোট প্রাণী দুর্ঘটনায় মারা পড়ে আছে দেখে পেট্রোল স্টেশনে বিরতির সময় একজনকে জিজ্ঞেস করায় বলল এগুলো বেশীর ভাগই খরগোস।
৩.অস্ট্রেলিয়ায় মানুষের সাথে মিশে আমার যেটা মনে হল- নতুন প্রজন্ম ধর্ম নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না এমনকি প্রকাশ্যে অনেককেই শুনেছি নাস্তিক পরিচয় দিতে সংকোচ করেনা কিন্তু বয়স্করা ধর্ম নিয়া বাড়াবাড়ি না করলেও রবিবারে চার্চে যাওয়া বাদ দেয় না। তবে মুসলিমদের এখানে বাড়াবাড়ি আমি ঢাকার চেয়েও বেশীই দেখেছি, যদিও সব যায়গায় নয়।
কিছু হাই স্কুলের ছাত্রদের কথা প্রসঙ্গে বিবর্তন নিয়ে প্রশ্ন করায় যা জেনেছি এখানে বিবর্তন নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে কোন সংশয় না থাকারই কথা।
ডঃ প্রদীপ দেবকে ধন্যবাদ এমন একটি সহজ সাবলীল লেখার জন্য।
@হেলাল, অনেক ধন্যবাদ।
লেখা তা অনেক ভালো লাগেছে।
অনেক ধন্যবাদ বিজন।
ডঃ প্রদীপ দেব;
আস্ট্রেলিয়াতে আছি প্রায় ২২ বছর। কিন্তু আপনি যে সব তথ্য দিয়েছেন তা আমি নিজেও জানতাম না। আমি অস্ট্রেলিয়ার ডারউইন শহরে অনেক বার বেড়াতে গিয়েছি–পোর্ট ডারউইনেও। আস্ট্রেলিয়ায় এখন যে খরগোশ দেখা যায় তাদের বেশীরভাগ হচ্ছে হাল্কা কালো অথবা ধুসর বর্ণের এবং এদের মাপ (সাইজ) সাধারণ খরগোশের তুলনায় অনেক বড় বলেই আমার মনে হচ্ছে।
এটা কি বিবর্তনের ফল?
আমার বাসার কাছেই বুশ বা আউটব্যাকে প্রচুর খরগোশ আছে। আমার মনে হ্য় এই খরগোশ সংখ্যা বাড়তির দিকে।
আপনার এই তথ্যবহুল প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ।
আর একটা কথা–আজকাল পশ্চিমে অবস্থানরত ইসলামিস্টরা টের পেয়ে গেছে যে বিবর্তনবাদ তাদের অস্তিতে ঘা দিবে। তাই এখন তারা সুর পাল্টে বলতে শুরু করেছে যে বিবর্তনবাদ কোরানে লিখা আছে। এই ব্যাপারে আমি দুই বছর আগে একটা রচনাও লিখেছিলাম রসিকতার সুরে–এর শিরোনাম ছিল–Darwin was a Muslim.
@আবুল কাশেম,
আপনার লেখার লিংকটা এখানে দিয়ে দিলাম-
Darwin was a Muslim.
@আবুল কাশেম ভাই,
অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার লেখা থেকে আমি ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছুই শিখেছি। “Darwin was a Muslim” পড়ার পর অনেক হেসেছিলাম। কিন্তু মজার বিষয় হলো আমার একজন ইসলামপন্থী ডাক্তার সহপাঠীকে ডাল্টনের কথাটা বলার পরপরই সে সিরিয়াসলি বললো, “এবার দ্যাখ- কোরানেই সবকিছু লেখা আছে, অথচ নাম হয় বিজ্ঞানের”। তাকে মেডিকেল সায়েন্সের বই বাদ দিয়ে কোরান পড়ার উপদেশ দেয়ার সাহস আমার ছিল না।
হ্যাঁ। বন্যা আহমেদের বিবর্তনের পথ ধরে’র চতুর্থ অধ্যায় ‘চোখের সামনেই ঘটছে বিবর্তন’ -এ এরকম আরো অনেক উদাহরণ আছে।
ইন্টারনেটের এই যুগে এখন আর রাষ্ট্রীয় ভাবে মগজধোলাই দিয়ে পার পেয়ে যাওয়া সম্ভব না। উচ্চমাধ্যমিক জীববিগ্গানে শুধু জেনেটিক্স আর ক্লাসিফিকেশনেই ডারউইনের কিছুটা উল্লেখ আসে, এছাড়া পুরো বইয়ের আর কোথাও কোন উল্লেখ নেই। ইন্টারনেটের মাধ্যমেই আমাদের যা করার করতে হবে।
@পৃথিবী, আপনার সাথে একমত।
তথ্যবহুল লেখা, খরগোসের বিষয়টি আমি নতুন জানলাম। তথ্যসূত্র [10] ডক্টর সুনন্দা বড়ুয়া, নার্গিস বেগম. বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা তৃতীয় শ্রেণী. ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড,, ২০০৯. আমি এই বিষয়টি বুঝতে পারছি না যে, বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা শিক্ষায় কি খুবই অনগ্রসর? যাদের একটি তৃতীয় শ্রেনীর ধর্ম বই লিখতে নার্গিস বেগমের হাত ধরতে হয়েছে? নাকি সুনন্দা নামে ডক্টর কিন্ত কাজে শূন্য ! অথবা এটাও কি একটি সুক্ষ বিবর্তনবাদ প্রক্রিয়ার চালুকরন ধর্মাবলম্বীদের উপর? নাকি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের আগামী প্রজন্মকে অতি সরল ভাবে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া, যে, তোমাদের ধর্মের বইটিও আমাদের লিখে দিতে হয়, তোমরা আর কি ধর্ম করবা? তার চেয়ে বরং আমাদের ধর্মে এসে যাও…! এমনকি হতে পারে না? আমি হয়তো আজ ভাবলাম এটি, কিন্ত যে শিশু এই বই পড়ে ও দেখে তার অন্যান্য সহপাঠিদের সাথে বড় হচ্ছে… তার কি অবস্থা হবে?
কেননা, আমার ভাগ্নীর উত্তর আমি এখনো দিতে পারিনি। গত বছর আমার বড় ভাগ্নী মেজ ভাগ্নীর স্কুলের পড়া তৈরী করে দিচ্ছে। উক্ত বইটি আমাকে দেখিয়ে আমার বড় ভাগ্নী বলেছিল, আচ্ছা বড়মামা, বাংলাদেশের বৌদ্ধরা একটি ধর্ম বই ও লিখতে পারে না? আমার বড় ভাগ্নী তখন নবম শ্রেনীর ছাত্রী, তার এই প্রশ্ন ছিল, তা হলে মেজ ভাগ্নীর কি প্রশ্ন থাকবে? সে কি আদৌ কোন দিন আমাকে প্রশ্ন করার মত উপাত্ত পাবে? যেহেতু সে এই ভাবে দেখেই বড় হচ্ছে।
নাকি এটি ও একটি বিবর্তনের শুরু? নাকি ক্ষুদ্র ধর্মীয় জাতিসত্তা গুলোকে বিবর্তনের পথ ধরে বিলীনের একটি নকশা?
আমার ভাগ্নীর প্রশ্নের উত্তরটি আমি জানি না। কেউ জেনে থাকলে আমাকে একটু বলে দেবেন কি?
@সংগ্রামীমানুষ,
আপনার অভিযোগটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। তৃতীয় শ্রেণীর বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা বইতে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কি কোন ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে? যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে ‘নার্গিস বেগম’ কী অপরাধ করলেন? আর বিবর্তনবাদ প্রক্রিয়ার চালুকরণ বলতে ঠিক কী বোঝাচ্ছেন? জৈব বিবর্তন একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। এটা প্রাকৃতিক ভাবেই চালু আছে। এ প্রবন্ধে মূলত ধর্মীয় শিক্ষার অসারতার প্রমাণস্বরূপ তৃতীয় শ্রেণীর ধর্মশিক্ষার বইগুলোর উদাহরণ দেয়া হয়েছে। ধর্ম যে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে আপনার মন্তব্য তারই আরেকটা প্রমাণ।
@প্রদীপ দেব,
যেহেতু আমি বিজ্ঞানের ছাত্র নই, তাই আমি বিজ্ঞান বুঝি কম। তবে বিবর্তন বুঝি এবং মানি। জৈব বির্তন নিয়ে লিখেছেন তাও বুঝতে পেরেছি। আমি হয়তো সামাজিক বিবর্তনের দিকে ঝুকে মন্তব্য করেছিলাম। কেননা ৩য় শ্রেণীর ধর্ম বই এর কথা উল্লেখ করার জন্য, নার্গিস বেগমের কথা কি বলব, আমাদের নিজেদের ধর্মাবলম্বীদের রচিত অনেক বইই তাদের নিজেদের ইচ্ছার প্রতিফলনে ঠাসা। তারপরেও আমরাও একটি ধর্মীয় গোষ্টি, আমরা পরিবারে যা শেখাই তাই আমাদের সন্তানরা স্তম্ভ হিসেবে মেনে নিয়ে বড় হয়।
আমার একটা কথা বিবেচনা করে দেখবেন, যা আমি মানি ও বিশ্বাস করি, ” আপনি না পড়লেও তো পারতেন, বা কেউ স্কুল কলেজে না গেলেও তো পারতো, যার যার মত করে আমরা খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকতাম। আমরা কেন গেলাম শিক্ষায়তনে? কিছু শিখার জন্য (অন্তত আমি মনে করি) স্কুলে গিয়ে ছিলাম। এই খানে যদি চলমান জীবনের কাছে কোন কিছু প্রশ্ন বোধক হয়ে দাড়াঁয় তখন কি উত্তর দেবেন? সামাজিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে? আপনি বিজ্ঞানের বিবর্তন তর তর করে বলে যাবেন, কিন্ত ভুলে যাবেন না আপনি ও এই সমাজের একজন সদস্য, আপনাকে আমাকে দিয়েই এই বিবর্তন। আমি বা আপনিই দেখি এই বিবর্তন। ”
যাক আপনার প্রশ্নে আসি, বেশ কিছু ভুল আছে ঐ বইয়ে। তবে আমি দশম শ্রেনী পর্যন্ত যতগুলো বই আছে সব পড়ে দেখছি। পরে বলবো পড়া শেষ করে।
আপনি যেমন চট্টগ্রামের লোক তেমন আমিও। আপনার গ্রামে কি এখনো মানুষ “হেন্ডইল্লা বা কন্ডইল্লা শব্দ ব্যবহার করে” ? করে না বোধ হয়, এটাই বিবর্তন… প্রাণী বিবর্তন কোন ছার… এটাতো বিজ্ঞানী এবং দূরদর্শীদের ব্যাপার, ……
আপনীতো চাটগাঁর মানুষ, মনে পরে এরশাদের কোন এক আত্নীয় ফটিকছড়িতে মেডিটেশান সেন্টার করতে চেয়েছিল বলে তাকে খুন করে……?
আমি খুজছি… আপনাকে তথ্য দেবার জন্য।
আমি বলতে চেয়েছি, বিবর্তনের ধারে আমরা যেন বিলীন হয়ে না যাই সেই কথা। ধীরে ধীরে হবে বিবর্তন… আপনি তা বুঝেন ও মানেন, আমি ও মানি… কিন্ত সমাজে নিজ ইচ্ছায় বিবর্তন করা শুরু করা কী ঠিক?
আমি নিশ্চিত করে বলছি আমার ভাগ্নী বড় হবে মুসলিম বিদ্বেসী হয়ে। কেন তার ধর্ম বইয়ে অন্য ধর্মাবলম্বীর নাম, শুধু এই নিয়ে, কিন্ত আপনি যদি বিবর্তন বুঝে থাকেন তবে কেন আপনি নিজে গায়ে পরে বিবর্তন করছেন?
আপনার কি উচিত নয়, যে, আমরা নিজে বিবর্তন করব না… পৃথিবীর নিজের নিয়মে বিবর্তন করে নিক, সেই কথাটা বলা???
@প্রদীপ দেব, আপনার সাথে সম্পূর্ণভাবে একমত। দ্বিজেন দার এই মন্তব্যটা দেখে আমি তখনই অভিকে বলেছিলাম যে দেশে থাকলে যে লিখতাম না বা লিখতে পারতাম না এটা ঠিক নয়। হয়তো হাতের কাছে এত বই বা রিসোর্স পেতাম না, কিন্তু লেখার ইচ্ছাটা হয়তো একইভাবে কাজ করতো। আরও অনেকেই তো করেছেন এবং করছেন, বেশী দূর যাওয়ারও তো দরকার নেই, মুক্তমনার অনন্ত, সৈকত, রায়হানদের কাজ দেখলেই তো তার প্রমাণ পাওয়া যায়।
@বন্যাদি, সত্যিই তাই।
মুগ্ধতার আবেশ নিয়ে মুক্তমনায় আমি যাদের লেখা পড়ি, তাদের মধ্যে প্রদীপ দেব অন্যতম। কিন্তু দুঃখ যে, এই ভদ্রলোক অত্যন্ত কম লেখেন। মন্তব্য করেন আরো কম। 😛
স্কুলের পাঠ্য বইতে যে ডারউইন থাকবে না সেটা সহজেই বোধগম্য। বিজ্ঞানের আর কোনো তত্ত্ব সৃষ্টিতত্ত্বের গাঁজাখুরি গালগল্পকে এমনভাবে চ্যালেঞ্জ করে না, যেরকমভাবে চ্যালেঞ্জ করে ডারউইনের মতবাদ। একে পাঠ্য বইতে স্থান দিতে গেলে, ধর্মগ্রন্থগুলোকে উনুনের আগুনে পোড়ানো ছাড়া আর কোনো বিকল্প থাকে না। কল্পিত ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত সরিসৃপ মানবকুলের সেই শক্ত শিড়দাঁড়া নেই। কাজেই, কাপুরুষের মত বিবর্তনবাদকে কর্তন করে মনের আনন্দে নর্তনকুর্দন করে চলেছে তারা দেশে দেশে।
@ফরিদ ভাই,
আমি যে কেমন অলস তা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়। তবুও আপনার কাছ থেকে অসম্ভব সুন্দর উৎসাহ পেয়ে ইচ্ছে করে- যদি আলস্যটা কমাতে পারতাম!
>> এমন দিন কবে আসবে, কবে আসবে এমন দিন?
স্যারের কল্পনাটা বোধ হয় কোরান থেকে এসেছিল- মানুষ থেকে জন্ম নেয়া বানর ও শূকরের কথা কোরানে লেখা আছে।
বিবর্তনের কারণে এদের দৈহিক গঠণের কোন পরিবর্তন হয় বা এরা কি দেখতে ইউরোপিয়ান খরগোশেরই মত?
@আকাশ মালিক,
এটা তো দেখি কোরানিক গালাগালি! চিন্তাও করিনি যে আবু মির্জা স্যারের কোরানে এত দখল ছিল।
জিনগত ভাবে এরা ইউরোপিয়ান খরগোশের চেয়ে অনেক আলাদা। দৈহিক গঠনেও অনেক পরিবর্তন চোখে পড়ে- গায়ের রঙেও অনেক বৈচিত্র্য দেখা যাচ্ছে।
@প্রদীপ দেব,
আর ঐ আগুনে পোড়া নতুন প্রজাতির গাছগুলো? ওরাও কি ভিন্ন আকার, আলাদা আকৃতির?
মাত্র শতকরা শুন্য দশমিক এক ভাগ জিনের মিউটেশানে নতুন ধরনের খরগোশ! দেখেন আল্লাহর কি কুদরত। অবিশ্বাস্য ঘটনা। যে ভাইরাসে তাদের পূর্বপুরুষ বিলুপ্ত হল, এরা সেই ভাইরাসের প্রতিরোধ শক্তি নিয়েই জন্মালো। ঈশ্বর কী না করতে পারে? তাও ঘটলো আমাদের চোখের সামনেই। আচ্ছা দুই সময়ের ছবি পাওয়া যাবে?
সত্যিই তাই, এর পরেও যদি আই,ডি ওয়ালাদের চোখ খুলতো !!!!
দারুন একটি লেখা ডারউইন দিবসে আমাদেরকে দেওয়ার জন্য প্রদীপ দেবকে অনেক ধন্যবাদ।
@মাহবুব সাঈদ মামুন, অনেক ধন্যবাদ। আই-ডি ওয়ালারা তো জেগে ঘুমোচ্ছেন। তাদের জাগানো সহজ নয়।
দুর্দান্ত একটি লেখা প্রদীপ!
অস্ট্রেলিয়ার খরগোশের উদাহরণটি চমৎকার হয়েছে। দিনের উপযোগী লেখা!
@অভিজিৎ,
অনেক ধন্যবাদ। আজকের প্রথম আলোর বিজ্ঞান পাতায় আপনার ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’র ছবি এবং খবর সাথে বন্যাদি’র ‘বিবর্তনের পথ ধরে’র খবর দেখে খুব ভালো লাগলো।
@প্রদীপ দেব,
হাঃ হাঃ, প্রথম আলোতে যে আমাদের বইয়ের কথা লিখেছে, তা আপনি বলার আগে জানতামই না। এখন গিয়ে দেখলাম। তথ্যটির জন্য ধন্যবাদ!