ইয়ারার তীরে মেলবোর্ন [০১] [০২] [০৩] [০৪] [০৫] [০৬] [০৭] [০৮] [০৯] [১০][১১][১২][১৩][১৪][১৫][১৬][১৭][১৮][১৯]
২০
৩০ জুলাই ১৯৯৮ বৃহস্পতিবার
উইলির ফ্ল্যাট
“কোন্ কাজ করিলে কী ফল হয়” নামে একটা চটি বই হাতে এসেছিল ক্লাস এইটে পড়ার সময়। সেখানে বিচিত্র সব প্রশ্নোত্তর ছিল। কিছু কিছু প্রশ্নোত্তর যদিও আমার তখনকার বোধের বাইরে ছিল, তবুও বেশ মজা পেয়েছিলাম বইটা পড়ে। সেখানে হাঁচি প্রসঙ্গে তথ্য ছিলঃ যাত্রাকালে একটা হাঁচি দিলে যাত্রানাস্তি হয়। শুভকাজে একটা হাঁচি অমঙ্গলের লক্ষণ। পরপর দুটো হাঁচি দিলে ফল আবার শুভ হয়। পরপর তিনটা বা চারটা হাঁচি দিলে কী হয় তা বইটাতে লেখা ছিল না। দিদিকে জিজ্ঞেস করলে সে বিজ্ঞের মত উত্তর দিয়েছিল- “এটা হলো অড আর ইভেন নাম্বারের ব্যাপার। বেজোড় সংখ্যক হাঁচি অশুভ, আর জোড় সংখ্যক হাঁচি শুভ”। ‘শুভ-অশুভ’ নামক শব্দগুলোর কোন প্রভাব নেই আমার জীবনে। থাকলে গত ছত্রিশ ঘন্টার হাঁচির হিসেব করার জন্য কাগজ-কলম লাগতো।
ব্যাপারটা শুরু হয়েছে পরশু মধ্যরাত থেকে। চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কার্লটন সেমিট্রির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যাওয়া-আসাটা একটু বেশি হয়ে গেছে। ভেবেছিলাম লম্বা ঘুমেই ঠিক হয়ে যাবো। কিন্তু হয়নি। শরীরের তাপমাত্রা বেড়েছে ইচ্ছেমত। নাক-চোখ দিয়ে পানির সাথে একটু পর-পরই হাঁচি; নাকে-মুখে গামছা চেপেও চাপা যায় না। অনেক দিন পর পুরো একটা দিন দুটো রাত কেটে গেলো বিছানায়।
আজ সকাল ন’টার দিকে অফিসে ঢোকার সময় কেনের সাথে ‘গুড মর্নিং’ বিনিময় হলো। গতকাল যে আসিনি সে ব্যাপারে কিছুই বললেন না। হয়তো খেয়ালও করেন নি। পিটারকে দেখলাম ব্যস্তভাবে কেনের রুমে যাওয়া আসা করছেন। গবেষণার কোন টার্নিং পয়েন্টে আছেন হয়তো।
লেসের ক্লাসটা করার পর ইউনিয়ন হাউজে গেলাম। কাল থেকে খাওয়া হয়নি কিছুই। ফুডকোর্টে মালয়েশিয়ান কাউন্টার থেকে স্টিম রাইস আর হট চিকেন নিয়ে দেয়ালের পাশে একটা খালি টেবিলের দিকে এগোচ্ছি এমন সময় “হাই”। ফিরে তাকাতেই চিনতে পারলাম- কারস্টিন। হাসিমুখে এগিয়ে আসছে।
“রিমেম্বার মি?”
“ইয়েস। হাউ আর ইউ কারস্টিন?”
“গুড। হাউ আর ইউ?”
কারস্টিনের মুখ দেখে বুঝতে পারছি সে আমার নাম মনে করার চেষ্টা করছে। নাম ভুলে যাওয়াটা স্বাভাবিক। আমারও অনেক মানুষের চেহারা মনে থাকে কিন্তু নাম মনে থাকে না। কারস্টিনের নামটা কেন যেন মনে রয়ে গেছে। আজ তার সাথে লুসি নেই। হয়তো স্বামীর কাছে রেখে এসেছে।
“লেট মি গেট সামথিং টু ইট” বলে খাবারের দোকানগুলোর দিকে এগিয়ে গেল কারস্টিন। আমি একটা খালি টেবিলে বসে খেতে শুরু করলাম। লাঞ্চ আওয়ারে ভিড় জমে উঠছে। মালয়েশিয়ান চিকেন খুব মজা হবার কথা। কিন্তু আমার খুব একটা ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে গেছে।
“হোয়াট ইউ ইটিং?”
কারস্টিন ফিরে এসেছে। হাতের প্লেট টেবিলে রেখে চেয়ার টেনে বসলো আমার মুখোমুখি। বললাম “মালয়েশিয়ান রাইস এন্ড চিকেন। তুমি কি খাচ্ছো?”
“ইটালিয়ান পাস্তা”
কারস্টিনের সামনে বসে খেতে আমার অস্বস্তি হচ্ছে। হাঁচি পাচ্ছে। নাকে মুখে দ্রুত রুমাল চাপা দিয়ে হাঁচির শব্দ কমালাম।
“ব্লেস ইউ”
“থ্যাংক ইউ”
কেউ হাঁচি দিলে কী কারণে ‘ব্লেস ইউ’ বলতে হয় জানি না। ব্যুৎপত্তিগত কারণ নিশ্চয় কিছু একটা আছে।
“মেলবোর্নের আবহাওয়া খুব বাজে তাই না?”
“ঠিক তাই”
কারস্টিনের উপস্থিতি ভালো লাগছে, আবার অস্বস্তিও হচ্ছে। বুঝতে পারছি আমার সাথে কথা বলার মতো কোন প্রসঙ্গ তার নেই। তাই আবহাওয়া প্রসঙ্গই ভরসা।
“তোমাদের ইন্ডিয়ায় এখন খুব গরম না?”
“হ্যাঁ ইন্ডিয়ায় এখন খুব গরম, তবে আমি ইন্ডিয়া থেকে আসিনি। আমি বাংলাদেশী”
“হ্যাঁ মনে পড়ছে তুমি বলেছিলে”
মুখে বলছে বটে, কিন্তু আমি জানি আমার চেহারাটা ছাড়া আমার সম্পর্কে তেমন আর কিছুই মনে নেই কারস্টিনের।
“হ্যাল্লো, হিয়ার ইউ আর” বলতে বলতে তিনজন ছেলে এসে ঘিরে ধরলো কারস্টিনকে। দুপুরের এ সময়ে এখানে টেবিল খালি পাওয়া মুশকিল। আমাদের টেবিলে দুটো চেয়ার খালি ছিল। তিনজনের দু’জন বসে গেল চেয়ার দুটোতে। তিনজনই হৈ হৈ করে কারস্টিনের সাথে কথা বলছে। আমার উপস্থিতির কোন প্রভাব নেই এদের কাছে। কারস্টিন হয়তো এদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। নিজেকে কেমন যেন আনফিট মনে হলো। এখান থেকে সরে পড়াটাই উত্তম। বললাম, “আই নিড টু গো, সি ইউ লেইটার”। কারস্টিন হাসিমুখে বললো- “বাই”।
কেন্ তাঁদের থার্সডে লাঞ্চ থেকে ফিরে আসার আগেই আমি বেরিয়ে পড়লাম। সেফওয়েতে গিয়ে দুটো নন্স্টিক পট-প্যান কিনে ফেললাম। দুটো পাত্রের জন্য তিরিশ ডলার খরচ করতে গায়ে লাগলেও করার কিছু নেই। ফিলের জিনিস আর ব্যবহার করবো না।
বাসার সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় দেখলাম সিঁড়ির নিচের একটুকুন জায়গায় গায়ের সাথে গা লেপ্টে মুখে মুখ লাগিয়ে বসে আছে স্কুল ড্রেস পরা একটা মেয়ে আর একটা ছেলে। মেয়েটার মুখের এক পাশ দেখে চেনা চেনা লাগলো। এই শ্যামলা মেয়েটিকে আগে কোথাও দেখেছি। দাঁড়িয়ে ভালো করে দেখার ইচ্ছে থাকলেও দেখা অসম্ভব। কারণ এই সভ্য দেশে তারা যা করছে তা সভ্যতা, কিন্তু তাদের দিকে ভালো করে তাকানোটা নাকি অসভ্যতা।
রুমে এসে সোজা বিছানায়। জানালার কাছে এসে বাইরের দিকে তাকালাম। পার্কিং এরিয়ার পাশ দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে একটু আগের দেখা ছেলে-মেয়ে দুটো। মেয়েটার হাঁটার ভঙ্গি দেখেই মনে পড়লো। বাসা দেখতে আসার দিন বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এই মেয়েটি আমাকে পথ দেখিয়েছিলো। যাকে আমার পথের পাঁচালীর দুর্গা মনে হয়েছিল। বারো-তেরো বছরের একটা কিশোরী। স্থান-কালের সাথে কীভাবে বদলে যায় মানুষের স্বভাব, সংস্কৃতি।
সাতটার পরে রান্নাঘরে ঢুকেছি। বসার ঘর আর রান্নাঘরের দরজা আলাদা করে দিয়ে ফিল একটা ভালো কাজ করেছেন। বসার ঘরে কী হচ্ছে তা আর আমাকে দেখতে হলো না। রান্নাঘরের কাজ এখন আমার আধঘন্টার মধ্যেই হয়ে যায়। সপ্তাহে তিন দিনের বেশি ঢুকতেও হয় না রান্নাঘরে। নতুন ডেক্সিতে ভাতের সাথে ডিম সিদ্ধ করতে দিয়ে সব্জি কাটছি- এমন সময় নাকে সিগারেটের গন্ধ লাগতেই বুঝলাম ফিল বা ডেভিড কেউ আছে আশেপাশে। ডেভিড সেই বিশ ডলার নেবার পর থেকে এড়িয়ে চলছে আমাকে। একটু পরেই রান্নাঘরের দরজা খুলে গেল।
“হাই প্রাডিব, হাউআইয়া মাইট?”
ফিলের মুড খুব ভালো আজ। হাসিমুখ দেখে মনে হচ্ছে দু’দিন আগের উত্তপ্ত বাক্য-বিনিময় ভুলে গেছেন তিনি। মুখে যান্ত্রিক হাসি ফুটিয়ে বললাম, “গুড। হাউ আর ইউ?”
মিনিট দশেক খেজুরে আলাপ করলেন ফিল। জানতে চাইলেন আমার ‘গার্লফ্রেন্ড’ আছে কি না। থাকলে বাসায় নিয়ে আসবো কি না। বললাম, “আপনি তো লিখে রেখেছেন – নো বডি ইজ এলাউড”
“এক্সেপ্ট গার্লফ্রেন্ডস। হাঃ হাঃ হাঃ”
এই হাসিখুশি ফিলের সাথে পরশুদিন সন্ধ্যার কাঠখোট্টা রাগী ফিলের কোন মিল নেই।
ডেক্সি দুটো কেনার সুফল প্রায় সাথে সাথেই পেতে শুরু করেছি। রান্নাঘরের সময় প্রায় অর্ধেক কমে গেছে। ভাত আর তরকারি আধা-সিদ্ধ অবস্থায় রুমে এনে ঢাকনা দিয়ে রেখে দিয়েছি। ঘন্টাখানেক পরে ঢাকনা খুলে দেখি চমৎকার সিদ্ধ হয়ে গেছে। প্রাথমিক সিদ্ধ হবার সময়েই বেশি তাপ লাগে- কারণ তখন পদার্থের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ল্যাটেন্ট হিট বা সুপ্ত-তাপ প্রয়োগ করতে হয়। এরপর একবার সিদ্ধ হতে শুরু করলে আর বেশি তাপের দরকার হয় না। তখন ঢাকনা দিয়ে তাপ সংরক্ষণ করতে পারলে ওই সংরক্ষিত তাপ শোষণ করে ডেকসির ভেতরের বস্তু সিদ্ধ হয়ে যায়। এতে সময় বাঁচলো, শক্তি বাঁচলো। এবার একটা ছুরি আর কাটিং বোর্ড কিনে নিতে হবে। তাতে করে কাটাকুটির কাজটাও রুমে বসে সেরে নেয়া যাবে।
সাড়ে ন’টার দিকে খেয়ে দেয়ে বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখি আমার রুমের দরজা খোলা। অথচ স্পষ্ট মনে আছে আমি দরজা টেনে গিয়েছিলাম। রুমে ঢুকে দেখি জোয়ানা- টেবিলের কাছে ঝুঁকে ছবি দেখছে।
“হাই জোয়ানা”
“হাই প্রাডিব। নাইস ফ্যামিলি ফটোস”
টেবিলে রাখা আমাদের পরিবারের বিভিন্ন জনের ছবির প্রতি নিবিড় আগ্রহ জোয়ানার। মিনিট দশেক ধরে বর্ণনা দিতে হলো তাকে। খেয়াল করে দেখলাম আমার নিজেরও বেশ ভাল লাগছে কাছের মানুষদের কথা জোয়ানাকে বলতে।
কিন্তু একটু পরেই আশঙ্কাটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। জোয়ানা নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আমার রুমে ঢুকেছে। আগের বার গেছে বিশ ডলার। আজ কত যাবে কে জানে। একটু পরেই হয়তো ডেভিড এসে কোন একটা বাহানা তৈরি করবে। সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, “ডেভিড কোথায়?”
“আমি জানি না। আছে কোথাও। আমি যদি কিছুক্ষণ বসি এখানে তুমি কি মাইন্ড করবে?”
“না না, বসো”
বিছানায় বসে পড়লো জোয়ানা। কোন ফাঁদে পা দিচ্ছি না তো? যদি সেদিনের মত শুয়ে পড়ে আমাকে পালাতে হবে রুম ছেড়ে। জোয়ানা পা নাচাচ্ছে। পা নাচানোর অভ্যাস থাকে অনেকের। জোয়ানারও আছে। আমি বিছানা থেকে যথাসম্ভব দূরে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম।
“তুমি ইন্ডিয়া থেকে এসেছো না?”
“না। বাংলাদেশ থেকে”
“স্কুলে আমাদের সাথে একজন ইন্ডিয়ান মেয়ে ছিল”
“তুমি লেখাপড়া করো না জোয়ানা?”
“ইয়ার নাইনের পর ছেড়ে দিয়েছি। ভাল লাগে না লেখাপড়া”
“তবে কী ভাল লাগে?”
“বাচ্চা ভালো লাগে”
“হোয়াট?”
“কিছুদিনের মধ্যেই আমি মা হবো”
চমকে উঠলাম। কত বয়স হবে জোয়ানার? আঠারো উনিশ। স্বাস্থ্য ভালো বলে হয়তো কিছুটা বেশি মনে হচ্ছে। চোখ গেলো তার শরীরের দিকে। এই শীতেও বড় বেশি খোলামেলা। মা হবার স্বাভাবিক চিহ্নগুলো এখনো স্পষ্ট নয় কোথাও। এক ধরণের অস্বস্তি হচ্ছে আমার। আমাকে কেন বলছে এসব? আমাদের দেশের কোন তরুণী কোন অপরিচিত মানুষকে তার মা হবার খবর দেয়ার অর্থ হলো- মাথায় গন্ডগোল। জোয়ানাও কি সেরকম?
কী বলবো কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বাচ্চার বাবা সম্পর্কে প্রশ্ন করা কি উচিত হবে? কিছু না বলে চুপচাপ তো বসে থাকা যায় না।
“ডেভিডের সাথে সম্পর্ক কত দিনের?”
“প্রায় দু’মাস”
সম্পর্কের ব্যাপারে এরা যে বড় দ্রুত-গতি সম্পন্ন তা তো দেখতেই পাচ্ছি। সম্পর্ক গড়া বা ভাঙা কোনটাতেই খুব একটা সময় লাগে না।
বাইরের দরজা খোলার শব্দ হলো। আমার ঘরের দরজা খোলাই আছে। প্যাসেজের আলোতে ডেভিডকে দেখতে পেলাম।
“হাই ডেভিড। জোয়ানা ইজ হিয়ার”
“হাই প্রাডিব। হাই বেবি” বলতে বলতে রুমে এসে জাপটে ধরলো জোয়ানাকে। এলকোহলের তীব্র গন্ধ ডেভিডকে ঘিরে। জোয়ানা উঠে দাঁড়িয়ে ডেভিডকে জড়িয়ে ধরে প্রায় কোলে উঠে গেলো তার। মিনিট খানেক চললো এরকম। ডেভিড বললো-
“হানি, তুমি প্রদীপকে বেশি ডিস্টার্ব করো নি তো?”
ডেভিড ভদ্রতা দেখাচ্ছে। এ ভদ্রতার দাম কত পড়বে জানি না। মনে মনে ভেবে রেখেছি আজ ডলার চাইলে আগের বিশ ডলারের কথা মনে করিয়ে দেবো। বলবো আমার নিজের কোন চাকরি নেই। যাও একটা পাবার সম্ভাবনা ছিল তা তোমার বাবা আমাকে ইন্টারভিউর খবর না জানিয়ে মাটি করে দিয়েছে।
কিন্তু সেরকম কিছু বলতে হলো না। জোয়ানাকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়ার ভঙ্গিতে ফিরে দাঁড়ালো ডেভিড। আমি যা ভেবেছি তাকে ভুল প্রমাণ করে ডেভিড বললো, “আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম। এই নাও তোমার বিশ ডলার। থ্যাংক ইউ সো মাচ”।
বিশ ডলারের নোটটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম। ডেভিডকে অহেতুক দু’নম্বরী মনে করেছিলাম। মানুষকে না জেনে অবিশ্বাস করাটা যে কত বড় অন্যায় তা আমি জানি। আর জেনে শুনে সে অন্যায়টাই আমি করেছি। খুব খারাপ লাগছে। হাঁচি পাচ্ছে খুব। প্রচন্ড শব্দে হাঁচলাম। ওদিক থেকে ভেসে এলো ডেভিডের জড়ানো কন্ঠস্বর- “ব্লেস ইউ”।
৩১ জুলাই ১৯৯৮ শুক্রবার
উইলির ফ্ল্যাট
‘প্লাটিনাম ব্লন্ড’ কথাটা প্রথম শুনেছিলাম ফারুকের কাছে। মাস্টার্সে ‘ইলেকট্রনিক্স ও ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্টেশান’ পড়াতেন ভুঁইয়া স্যার। তিনি ফ্রান্সে পি-এইচ-ডি করতে গিয়েছিলেন কোট-টাই পরে, ফিরেছেন মোল্লাদের মত মানসিকতা আর লম্বা আলখেল্লা নিয়ে। তখন তিনি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান। সুতরাং তাঁর কথার বাইরে আর কোন কথা থাকতে পারে না বলেই তাঁর ধারণা। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের আমেরিকান বই পড়াতে গিয়ে ব্লন্ড আর ব্রুনেটের উদাহরণ পাওয়া গেল। ভুঁইয়া স্যার বললেন ‘ব্লন্ড’ মানে ‘বেঁটে মেয়ে’ আর ‘ব্রুনেট’ মানে ‘লম্বা মেয়ে’। আর যায় কোথায়! ফারুক উঠে দাঁড়িয়ে স্যারের মুখের উপর বলে দিলো- ‘ব্লন্ড মানে সোনালি রঙের চুল। ছেলে বা মেয়ে যে কেউ ব্লন্ড হতে পারে’। ফারুকের এরকম পান্ডিত্যপূর্ণ বোকামীর পরিচয় আমরা আগেও পেয়েছি। কিন্তু এরকম সরাসরি বোমা ফাটানোর নাম আত্মহত্যা। অনেক ভুগতে হয়েছে তাকে এর জন্য। সে অন্য প্রসঙ্গ। আমরা বন্ধুরা ফারুকের কাছ থেকে অনেক ইংরেজি শব্দ শিখেছি, জেনেছি অনেক ধরনের সংস্কৃতির কথা। আজ সকালে ‘প্লাটিনাম ব্লন্ড’ জিনেটের মুখোমুখি হয়েই মনে পড়লো ফারুকের কথা।
সোয়া ন’টার দিকে ডিপার্টমেন্টে গিয়ে দেখি আমার রুমের দরজা হাট করে খোলা। দরজা যেন বন্ধ হয়ে না যায় সে জন্য কাঠের একটা প্রতিবন্ধকও দেয়া হয়েছে। রুমটা কেন যেন একটু অন্যরকম লাগছে। মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে রুমের ভেতর। ম্যান্ডি বা ইমাজিন কেউই এরকম গন্ধ ব্যবহার করে না। তার মানে নতুন কেউ। ফেলুদা হবার চেষ্টা করলাম। ইমাজিনের পাশের ডেস্কের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম- তিনি এসেছেন। ডেস্ক পরিপাটি করে সাজানো। বুক শেল্ফের ধার ঘেঁষে অনেকগুলো খেলনা গাড়ি, ছোট ছোট লাল-নীল-হলুদ। পদার্থবিজ্ঞানীদের এরকম শখও যে থাকে তা জানতাম না।
মিনিট পাঁচেক পরেই খট্ খট্ জুতোর শব্দে ফিরে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। ঘরে ঢুকছে পাঁচ-ফুট আট ইঞ্চি উচ্চতার পারফেক্ট প্লাটিনাম ব্লন্ড। কালো পোশাকের ছিপছিপে মানুষটার সবকিছু এতটাই পরিপাটি যে মনে হচ্ছে সিনেমার পর্দায় কোন হলিউডের নায়িকাকে দেখছি।
“হাই, আই এম জিনেট, জিনেট ফাইফ। ইউ মাস্ট বি প্রাডিব” হ্যান্ডশেক করতে করতে বললো জিনেট। ঝাঁঝালো কন্ঠস্বর জিনেটের। তার কন্ঠ মিষ্টি হলে সব কিছু বড় বেশি নিখুঁত হয়ে যেতো। জিনেটের চোখ ঘন নীল। এরকম চোখের দিকে সরাসরি তাকানো যায় না।
“তুমি এসেছো বাংলাদেশ থেকে, তাই না?”
“হ্যাঁ, তোমাকে কে বললো?”
“ইমাজিন। কেমন লাগছে এখানে?”
জিনেটের ভেতর একটা সহজাত নেতৃত্বের ভাব আছে। কী জানি হয়তো সে স্টুডেন্ট-লিডার টাইপের কিছু। অবশ্য এখানে স্টুডেন্ট পলিটিক্সের ছিঁটেফোঁটাও তো চোখে পড়েনি কোথাও। সে যাই হোক। জিনেট যে স্টুডেন্ট মহলে খুব জনপ্রিয় তা বুঝতে পারলাম একটু পরেই।
এতদিন আছি এখানে- কাউকে দেখিনি ম্যান্ডি বা ইমাজিনকে খুঁজতে এসেছে। অথচ আজ আধঘন্টার মধ্যে পাঁচ-ছ’জন এসে দেখা করে গেলো জিনেটের সাথে। জিনেট তাদের সাথে আমাকেও পরিচয় করিয়ে দিলো। অনার্সের রোল্যান্ড ছাড়া বাকিরা সবাই পি-এইচ-ডি স্টুডেন্ট। পার্টিক্যাল থিওরি গ্রুপের নিকোল আর স্টেফি, এক্স-রে ডিফ্রাকশান গ্রুপের ট্রেসি। ভয়াবহ রকমের মোটা এই ট্রেসিকেই দেখেছি নিচের রিসেপশানে কাজ করতে। তখন তাকে খুব গম্ভীর মনে হয়েছিল। আজ দেখছি জিনেটের সাথে খুব হেসে হেসে কথা বলছে। আমাকেও হাসিমুখে “হাই” বললো। দৈত্যাকৃতি মার্ক যখন ঘরে ঢুকলো- তখন দশটা বাজতে পাঁচ। কোন রকমে হাই- বাই করে চলে গেলাম লেসের ক্লাসে।
লেস একটা এসাইনমেন্ট ধরিয়ে দিলেন সবাইকে। তিনটা প্রোবলেম সল্ভ করে জমা দিতে হবে তিন সপ্তাহের মধ্যে। চোখ বুলিয়ে বুঝতে পারলাম এগুলো সল্ভ করতে হলে কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরির অনেক গভীরে ঢুকতে হবে। শখ করে এই কোর্সে এসে তো দেখছি বিপদে পড়ে গেলাম।
ক্লাস শেষে অফিসে এসে দেখি হলুদ স্টিকারে ঝকঝকে হাতের লেখায় আমার জন্য ম্যাসেজ অপেক্ষা করছে আমার ডেস্কের ওপর- “Ali Called@11:15am 31.08.1998” জিনেটের কাজও বেশ পরিপাটি। অফিসে এখন কেউ নেই। ফোন করলাম আলী সাহেবের অফিসের নম্বরে।
“স্যার, আমি প্রদীপ। আপনি যখন ফোন করেছিলেন আমি তখন ক্লাসে ছিলাম”
“হ্যাঁ, যে জন্য ফোন করেছিলাম। আমি বাংলাদেশে যাচ্ছি সোমবার। তুমি যদি চিঠিপত্র কিছু দাও- আমি নিয়ে যেতে পারি। সানডেতে বাসায় ফোন করো। তখন বলে দেবো ডিটেল্স”
“ও-কে স্যার”
“আরেকটি কথা। তুমি কি বিট্টুর সাথে কথা বলেছো?”
“জ্বি না স্যার”
“তুমি তো আর-এম-আই-টিতে গিয়ে তার সাথে দেখা করতে পারো। তার মোবাইল নাম্বার না থাকলে লিখে নাও”
অফিসের ফোন থেকে মোবাইলে ফোন করা যায় না। নিচে নেমে পাবলিক ফোনে এক ডলার দিয়ে দেড় মিনিটের মত কথা বলতে পারলাম বিট্টুর সাথে। তিনটার দিকে আর-এম-আই-টির কার্ডিগান স্ট্রিটের বিল্ডিং-এ যেতে বললো সে।
কার্লটন এরিয়া ম্যাপ থেকে কার্ডিগান স্ট্রিট খুঁজে বের করলাম। খুব বেশি দূরে নয় এখান থেকে। আড়াইটার দিকে বেরিয়ে পড়লাম। সোয়ান্সটন স্ট্রিটের ওপর আর-এম-আই-টি ইউনিভার্সিটির বিশাল বিল্ডিং-টার কাছে গিয়ে বামে মোড় নিলাম। সোয়ান্সটন স্ট্রিটের সমান্তরাল রাস্তাটিই কার্ডিগান স্ট্রিট। এখানে বেশির ভাগই টাউন-হাউজ। ইউনিভার্সিটির কোন বড় বিল্ডিং-তো চোখে পড়লো না। কার্ডিগান স্ট্রিটের আগাগোড়া হেঁটে একটা ছোট্ট ঘরের সামনে আর-এম-আই-টির একটা সাইনবোর্ড দেখলাম। কোন অফিস বলে মনে হচ্ছে।
কাছে গিয়ে দেখি ঠিক পাশের ঘরের সামনে লাল নিয়ন সাইন জ্বলছে- “ইউটোপিয়া”। নীল রঙের “ওপেন” সাইনটা জ্বলছে আর নিভছে। বন্ধ দরজার ওপর একটা মেয়ের ছবি যে ভঙ্গিতে আঁকা তাতে ভীষণ খটকা লাগছে। দ্রুতগামী একটা ট্যাক্সি এসে থামলো ইউটোপিয়ার সামনে। দু’জন মেয়ে দ্রুত নেমে প্রায় ছুটে ঢুকে গেলো ইউটোপিয়ার বন্ধ দরজা ঠেলে। তাদের পোশাক পরিচ্ছদ সাজ-গোজ দেখে বুঝলাম আমার সন্দেহ ঠিক। একটা ইউনিভার্সিটির অফিসের পাশের রুমেই কিনা চলছে নিষিদ্ধ জগতের আয়োজন!
সভ্যতার নানারকম অসুখও থাকে। ক’দিন আগে লোকাল ফ্রি পেপারে একটা জমকালো বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম। বিজ্ঞাপনের ভাষ্য এরকমঃ একজন স্কুল শিক্ষিকার বেতন ঘন্টায় তেইশ ডলার, একজন নার্সের বেতন ঘন্টায় পঁচিশ ডলার, একজন বিমান-বালার বেতন ঘন্টায় তিরিশ ডলার, একজন ডাক্তারের বেতন ঘন্টায় একশ’ ডলার। কিন্তু তুমি যদি আঠারো থেকে পঁচিশ বছরের মেয়ে হও- ইচ্ছে করলে ঘন্টায় পাঁচশ’ থেকে হাজার ডলার উপার্জন করতে পারো। যোগাযোগের ঠিকানা ইত্যাদি। এরকমই কোন কর্মক্ষেত্র ‘ইউটোপিয়া’ যেখানে কেউ কেউ ঘন্টায় হাজার ডলার উপার্জন করে।
আর-এম-আই-টি’র অফিসে উঁকি দিলাম। বিট্টুর চিহ্নও নেই কোথাও। তবে কি ভুল জায়গায় এসেছি? এখানে অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না। ফিরে এলাম নিজের অফিসে।
রাত আটটায় লেবি থিয়েটারে ফিজিক্স পাবলিক লেকচার। শুক্রবারের সন্ধ্যায় নানারকম বিনোদনের উপাদান উপেক্ষা করে প্রায় শ’তিনেক মানুষ বসে বসে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা শুনলেন। আজকের বিষয় ছিলোঃ New Eyes on Mars: Physics of the Pathfinder Mission. মঙ্গলগ্রহ অভিযানের নানারকম খুঁটিনাটি। বক্তা এসোসিয়েট প্রফেসর ডেভিড জেমাইসন। দাড়িওয়ালা প্রফেসর জেমাইসনকে দেখতে অনেকটা নোবেল বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী আবদুস সালামের মত লাগে। চমৎকার উপস্থাপনা তাঁর। বিজ্ঞানের খটমটে জিনিস যে এত আকর্ষণীয় হতে পারে চোখের সামনে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। দুটো বিরাট বিরাট পর্দায় প্রতিফলিত হলো মঙ্গল গ্রহের ঘূর্ণন, পাথফাইন্ডার মিশনের বৈজ্ঞানিক কাজ-কর্ম। দেড়-ঘন্টার প্রতিটি সেকেন্ড উপভোগ করলাম। ইউনিভার্সিটিগুলোর সাথে জনগণের এরকম সরাসরি যোগাযোগ আমাদের দেশে খুব একটা দেখা যায় না। বক্তৃতা শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বটা আরো আকর্ষণীয়। দারুণ ভালো লাগা নিয়ে বাসায় ফিরলাম রাত দশটার দিকে। ফিলের লাউঞ্জরুমের উইক-এন্ড পার্টি তখন তুঙ্গে।
০১ আগস্ট ১৯৯৮ শনিবার
ফিজিক্স বিল্ডিং
আজ সকাল দশটা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত হেঁটে বেড়িয়েছি মেলবোর্নের ঐতিহাসিক রাস্তায় এবং জেম্স কুকের কুটিরে। এখানে ঐতিহাসিক রাস্তা মাত্র কয়েকটা- যা এই শহরের গোড়াপত্তনের সাক্ষী হয়ে আছে।
মেলবোর্ন শহরের ইতিহাস ইয়ারা নদী থেকে শুরু। অস্ট্রেলিয়ায় শ্বেতাঙ্গদের অভিযানের প্রায় তিরিশ হাজার বছর আগে থেকেই আদিবাসীদের বাস। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অসংখ্য ছোটবড় জলস্রোত মিলেমিশে সৃষ্টি হয়েছে নদী। নদীর তীর ঘেঁষে যে উরুন্ডজেরি (Wurundjeri) সম্প্রদায়ের বাস, তারা নদীকে বলে ‘বিরারুং’ (Birrarrung) যার বাংলা অর্থ- প্রবহমান বা ক্ষেত্রবিশেষে ‘ছায়ায় ঘেরা মায়ায় ঘেরা’। এই ‘বিরারুং’ এসে মিশেছে উপসাগরে- ইংরেজরা যার নাম দেন ‘পোর্ট ফিলিপ বে’।
উরুন্ডজেরি সম্প্রদায়ের জীবন-যাত্রায় বিপর্যয় নেমে আসে যখন তাদের ভুবনে প্রথম শ্বেতাঙ্গ অনুপ্রবেশ ঘটে ১৮০৩ সালে। নিউ সাউথ ওয়েল্স এর সার্ভেয়র জেনারেল চার্লস গ্রাইম্স পোর্ট ফিলিপ ডিস্ট্রিক্ট এর ম্যাপ তৈরি করতে আসেন। গ্রাইম্স নদী আর উপসাগর দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। ফিরে গিয়ে রিপোর্ট করেন যে বসতি গড়ে তোলার জন্য এর চেয়ে ভালো জায়গা আর হয় না।
গ্রাইম্সের জরিপের পর আরো তেইশ বছর কেউ আসেনি এদিকে। ততদিনে তাসমানিয়ার লনচেস্টনে গড়ে উঠেছে ভূমি-আগ্রাসী গোষ্ঠী ‘পোর্ট ফিলিপ এসোসিয়েশান’। ১৮৩৫ সালের ৮ জুন এই গোষ্ঠীর নেতা জন ব্যাটম্যান জাহাজ নিয়ে চলে আসেন পোর্ট ফিলিপ উপসাগরে। ধূর্ত ব্যাটম্যান ভাব জমান উরুন্ডজেরি সম্প্রদায়ের নেতাদের সাথে। জামাকাপড়, ছুরি-কাঁচি, শীতের কাপড়, খাবার দাবার, মদ ইত্যাদির বিনিময়ে তিনি আদিবাসী নেতাদের কাছ থেকে অনেক জমি লিখে নেন। নিজেই দলিল তৈরি করে এনেছিলেন। আদিবাসীরা ব্যাটম্যানের ভাষা বোঝেন না। সরল বিশ্বাসে বন্ধুত্বের নিদর্শন মনে করে হাতের চিহ্ন এঁকে দেন তাতে। জন ব্যাটম্যান এটাকে ব্যবহার করেন চুক্তি-সই এর প্রমাণ হিসেবে। লনচেস্টনে ফিরে গিয়ে জন ব্যাটম্যান ঘোষণা করেন “আমি হলাম পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি জমির মালিক”। তাঁর দাবী মিথ্যে ছিল না। তিনি উরুন্ডজেরিদের কাছ থেকে লিখে নিয়েছিলেন প্রায় ছয় লাখ একর জমি (প্রায় আড়াই হাজার বর্গ কিলোমিটার- সমগ্র ঢাকা জেলার ক্ষেত্রফল মাত্র দেড় হাজার বর্গ কিলোমিটার)।
ব্যাটম্যানের জমি কেনার খবর শুনে লনচেস্টনের আরেকজন নেতা জন প্যাসকো ফকনার দ্রুত একটা জাহাজ কিনে নিজের পরিবার আর লোকজন নিয়ে পোর্ট ফিলিপ বে’তে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। কিন্তু জাহাজ কেনার টাকা না দিয়ে এবং পুরনো ঋণ শোধ না করে পালাবার মতলব করেছিলেন বলে ফকনারকে বন্দী করা হয়। এ সুযোগে লনচেস্টনের আরেক ব্যবসায়ী জর্জ ইভান্স ফকনারের জাহাজ নিয়ে দ্রুত চলে আসেন পোর্ট ফিলিপ ডিস্টিক্টে। ১৮৩৫ সালের আগস্ট মাসে নদীর তীরে পৌঁছেই ইভান্স ইচ্ছেমত জায়গা দখল করে চাষবাস পশুপালন শুরু করে দেন।
জন ব্যাটম্যানের জমি জরিপের দায়িত্ব পড়ে জন হেল্ডার ওয়েজের ওপর। তিনি এসে পৌঁছান ১৮৩৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর। তিনি শুনেছেন আদিবাসীরা নদীকে ‘ইয়ারা ইয়ারা’ বলে উল্লেখ করছে। তিনি ভেবেছিলেন এটাই নদীর নাম। ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি নদীর নাম লিপিবদ্ধ করেন ‘ইয়ারা’। অবশ্য পরে জানা গেছে যে আদিবাসীদের ভাষায় ‘ইয়ারা’ মানে ঝর্ণা।
দ্রুত বসতি গড়ে উঠতে শুরু করলো ইয়ারার তীরে। যদিও নিউ সাউথ ওয়েল্স সরকারের খাতায় এই বসতি ‘বে-আইনী’ তবুও থেমে রইলো না কিছুই। এক বছরের মধ্যেই ইয়ারার তীরে শ’খানেক বসতি গড়ে উঠলো, প্রায় ছাব্বিশ হাজার ভেড়া চড়তে শুরু করলো ইয়ারার তীরে।
বসতি মানেই জীবন-যাপন। আর একে কেন্দ্র করে নানারকম ব্যবসা-বাণিজ্যের শুরু। ধীরে ধীরে একটা শহর দানা বাঁধতে শুরু করলো। ১৮৩৭ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম ল্যাম্ব মেলবোর্নের নামানুসারে এই নতুন শহরের নাম রাখা হলো- মেলবোর্ন। ছয় ব্লক বাই চার ব্লকের ছোট্ট শহর। স্পেন্সার স্ট্রিট, লা-ট্রোব স্ট্রিট, স্প্রিং স্ট্রিট আর ফ্লিন্ডার স্ট্রিট হলো এই শহরের সীমানা। ১৮৩৮ সালের জুন মাসের জরিপে দেখা গেলো- মেলবোর্নের মোট জনসংখ্যা ১৭৭ জন- ১৪২ জন পুরুষ ও ৩৫ জন নারী।
পরবর্তী পনেরো বছর ধরে নগর-পরিকল্পনা, রাস্তা-ঘাট তৈরি এবং ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে স্বাভাবিক নিয়মে। ইয়ারা নদীর সাথে সমান্তরাল করে তৈরি করা হয়েছে ফ্লিন্ডার স্ট্রিট। বাকী সব রাস্তা ও দালানের পরিকল্পনা করা হয়েছে দাবার ছকের মত করে। যতটা সম্ভব জ্যামিতিক নিয়ম মেনে। এখন ম্যাপে দেখা যায়- মেলবোর্নের মূল বাণিজ্যিক এলাকা একটি নিঁখুত আয়তক্ষেত্র।
১৮৫১ সালে মেলবোর্ন শহর হঠাৎ পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী শহরগুলোর তালিকায় নাম লিখিয়ে ফেলে। আক্ষরিক অর্থেই স্বর্ণযুগের সূচনা হয় মেলবোর্নের। সোনার খনি পাওয়া যায় এখানে। শুরুতে ইয়ারার তীরে ওয়ারেন্ডাইট এলাকায় সোনা আবিষ্কৃত হয়। পরে আশেপাশের আরো অনেক জায়গায়। দলে দলে মানুষ আসতে শুরু করে মেলবোর্নে। সবাই লেগে যায় খনি খোড়ার কাজে। প্রতিদিন গড়ে আড়াই শ’ মানুষ এসে বসতি গড়তে শুরু করেছে। তাদের থাকা-খাওয়া ও অন্যান্য চাহিদার যোগান দেবার জন্য দ্রুত বাড়তে থাকে শহরের কলেবর।
সোনার টাকায় গড়ে ওঠে ট্রেজারি বিল্ডিং, পার্লামেন্ট হাউজ, সোয়ান্সটন স্ট্রিটের স্টেট লাইব্রেরি ও মেলবোর্ন টাউন হল, ও এলিজাবেথ স্ট্রিটের জেনারেল পোস্ট অফিস। পরবর্তীতে একই ঘরানার স্থাপত্যে আরো অনেক ভবন তৈরি হয়েছে। ফ্লিন্ডার স্ট্রিট ট্রেন স্টেশন তাদের একটি। আজ ঘুরে ঘুরে সবগুলো বিল্ডিং দেখে এসেছি। ভিক্টোরিয়ান যুগের বিল্ডিং সব। জেনারেল পোস্ট অফিসে এখন নানারকম রেস্টুরেন্ট আর দোকান-পাট। পোস্ট-অফিসগুলো এখন সব প্রাইভেট হয়ে গেছে। কিন্তু জি-পি-ও বিল্ডিংটা রয়ে গেছে আপন বৈশিষ্ট্যে। এটা এখন এলিজাবেথ স্ট্রিট আর বার্ক স্ট্রিট মলের একটি প্রধান আকর্ষণ।
একটা জিনিস স্বীকার করতেই হবে তা হলো সেই সময়ের নেতাদের দূরদর্শিতা। শহরের জনসংখ্যা যখন মাত্র ১৭৭ জন তখনই তাঁরা নগর-পরিকল্পনা করেছিলেন পরবর্তী কয়েকশ’ বছরের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে। এখন এই শহরে প্রতিদিন বিশ লাখ মানুষের আনাগোনা। অথচ সেই ১৮৫০ সালের অবকাঠামো এখনো কার্যকর।
পার্লামেন্ট হাউজের সামনে দিয়ে হেঁটে হেঁটে সরকারি অফিসগুলো বামে রেখে এগোলাম ফিট্জরয় গার্ডেনের ভেতর দিয়ে। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে একটু আগে। পাতাহীন গাছের ডাল থেকে টুপটাপ ঝরে পড়ছে বৃষ্টির রেশ। আরো কিছুদূর গিয়ে ছোট্ট একটা বাগানঘেরা লালচে পোড়া ইটের তৈরি টালির ছাদের ছোট্ট একটা কুটির- কুক্’স কটেজ। ক্যাপ্টেন জেম্স কুকের স্মৃতিজড়িত কুটির। মজার বিষয় হচ্ছে এই পুরো কুটিরটাকে ইংল্যান্ড থেকে তুলে এখানে এনে বসানো হয়েছে।
১৭৫৫ সালে ক্যাপ্টেন জেম্স কুকের বাবা জেম্স কুক ও মা গ্রেস কুক ইংল্যান্ডের নর্থ ইয়র্কশায়ারে এই বাড়িটা কিনে নিজেদের মত সংস্কার করে বসবাস করছিলেন। তাঁদের ছেলে ক্যাপ্টেন জেম্স কুক এই বাড়িতে বসবাস করেছিলেন কি-না তা নিয়ে সন্দেহ আছে অনেকের, কিন্তু তিনি যে তাঁর মা-বাবাকে দেখতে মাঝে মধ্যে আসতেন তাতে কারো সন্দেহ নেই। ক্যাপ্টেন কুকের এটুকু স্মৃতিই বাড়িটার বিখ্যাত হয়ে ওঠার পক্ষে যথেষ্ঠ। তাছাড়া যে বাড়িতে ক্যাপ্টেন কুক জন্মেছিলেন সেই বাড়িটা ১৭৮৬ সালে ভেঙে ফেলার পর ইয়র্ক-শায়ারের এই বাড়িটাই হয়ে ওঠে কুকের একমাত্র স্মৃতি-জড়িত বাড়ি। মালিকানা বদল হতে হতে বাড়িটা মিসেস ডিক্সনের হাতে এসে পড়ে।
১৯৩৩ সালে মিসেস ডিক্সন বাড়িটা বিক্রি করার ঘোষণা দেন। দেশপ্রেম দেখানোর জন্য তিনি একটা শর্ত জুড়ে দেন যে শুধুমাত্র ইংল্যান্ডের ক্রেতাদের কাছেই তিনি বাড়িটা বিক্রি করবেন। এদিকে ১৯৩৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্যের শতবর্ষ পূর্তি হচ্ছে। মেলবোর্নের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রাসেল গ্রিমওয়েড চাইছিলেন এ উপলক্ষে ভিক্টোরিয়ান সরকারকে কিছু একটা উপহার দিতে। ক্যাপ্টেন কুকের কটেজটি নিলামে বিক্রি হচ্ছে জানতে পেরে তিনি লোক লাগালেন। মিসেস ডিক্সনকে রাজী করালেন যেন তিনি তাঁর শর্তটা একটু বদলে নেন। ব্রিটেনের বদলে ব্রিটিশ কলোনির মধ্যে তিনি বাড়িটা বিক্রি করতে রাজী হলেন। অস্ট্রেলিয়া স্বাধীন দেশ হলেও এখনো ব্রিটিশ কলোনির মতোই- ব্রিটেনের রাণীকে নিজেরাও রাণী মানে, পার্লামেন্টে রাণীর একজন প্রতিনিধির জন্য স্থায়ী আসন আছে। নিলাম হলো। ব্রিটিশদের সর্বোচ্চ অফার ছিল তিনশ’ পাউন্ড। আর এক লাফে আটশ’ পাউন্ড দাম হেঁকে বাড়িটা কিনে নিলেন মেলবোর্নের রাসেল গ্রিমওয়েড।
এবার বাড়িটাকে মেলবোর্নে নিয়ে আসার পালা। মেলবোর্ন থেকে একদল স্থপতি গিয়ে সবকিছু দেখেশুনে বাড়ির হুবহু নকশা নিয়ে এলেন। একটা একটা করে ইট-কাঠ-টালি খোলা হলো, প্যাকেট করা হলো। ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে ২৫৩টি বড় বড় বাক্স আর চল্লিশটি ব্যারেল ভর্তি হয়ে মেলবোর্নে এসে পৌঁছালো কুক’স কটেজ। পরের ছ’মাসে এখানে পুনর্গঠিত হলো কুক্’স কটেজ। ১৯৩৪ সালের ১৫ অক্টোবর রাসেল গ্রিমওয়েড কটেজটি আনুষ্ঠানিক ভাবে তুলে দেন মেলবোর্নের মেয়রের হাতে। তখন থেকেই এটা মেলবোর্নের একটা ঐতিহাসিক স্থান।
ভেতরে তেমন দামী কোন আসবাব-পত্র নেই- যা আছে তা সেই সময়ের সাক্ষী। স্কুলের শিক্ষার্থীদের ইতিহাস শেখানোর জন্য নানারকম আয়োজন এখানে সারাবছর ধরে।
কটেজের বাইরে দেখলাম বিয়ের পোশাকে বরকনে ছবি ওঠাচ্ছে। এদেশে বিয়ে মনে হয় শুধু শনিবারেই হয়। ছুটির দিন না হলে সম্ভবত কাউকে ফ্রি পাওয়া যায় না।
ফেরার পথে ফ্লিন্ডার্স স্ট্রিট পার হয়ে ইয়ারার তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে এম-সি-জি’র কাছে চলে গিয়েছিলাম। পৃথিবী বিখ্যাত মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড। এখন ফুটবলের মৌসুম। এ-এফ-এল বা অস্ট্রেলিয়ান ফুটবল লীগ চলছে এখন। প্রতি শনিবার দুপুরে খেলা থাকে এখানে। আমাদের ফুটবলের সাথে এদের ফুটবলের কোন মিল নেই। আমাদের ফুটবল বৃত্তাকার- এদের ফুটবল উপবৃত্তাকার। আমাদের ফুটবলের মাঠ আয়তাকার, এদের মাঠ বৃত্তাকার। আমরা ফুটবল খেলি পা দিয়ে, এরা খেলে হাত-পা সবকিছু দিয়ে। আমাদের ফুটবলের খেলোয়াড় সংখ্যা প্রতি দলে সর্বোচ্চ এগারোজন, এদের ফুটবলের খেলোয়াড় সংখ্যা দল প্রতি আঠারো জন। আরো কত যে পার্থক্য আছে। মেলবোর্নের ঘরে ঘরে ফুটি-ক্রেজ। এম-সি-জি থেকে বেরোনো মানুষের একদলের গায়ে লাল-কালো, অন্যদলের গায়ে হলুদ পোশাকের প্রাধান্য। কোন্ কোন্ টিমের পোশাক জানি না এখনো। এদেশের মানুষ রাজনৈতিক দল নিয়ে একটুও কথা বলে না, বেশির ভাগ কথাই এদের খেলার টিম নিয়ে। তবে এত উত্তেজনার মধ্যেও খেলা নিয়ে কোন মারামারির খবর চোখে পড়েনি এতদিনেও।
বক বক করতে করতে নিশ্চয় তোমার মাথা ধরিয়ে দিলাম। রাখছি এখন। বাসায় যাচ্ছি।
ক্রমশ______

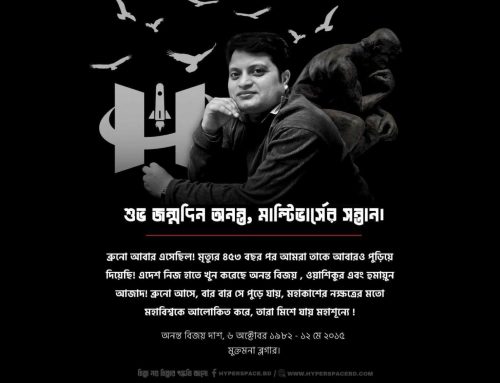
এই সিরিজ আমি সব সময় পড়ি।মাঝে মধ্যে মন্তব্য করে হয়ে ওঠেনা। খুব ভালো লাগে।
দুনিয়ার সব খানেই আদিবাসী বেচারাদের ঘাড়ে কাঁঠাল ভেঙ্গে সভ্য সুশিক্ষিত মানুষেরা খেয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের নিয়ে একটা বিখ্যাত মুভি দেখেছিলাম, র্যাবিট ফেন্স বা তেমন একটা নাম। খুবই করুন।
এই পর্বটিও খুব ভালো লাগলো। চলুক। :rose:
অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ ছিল বরাবরই। আপনার লেখায় তা কিছুটা জানলাম। তবে একই সঙ্গে ‘আদিবাসী’ ও ‘উপজাতি’ কথার ব্যবহার ভালো লাগেনি। :deadrose:
চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়ের মতে, ‘আদিবাসী’ বলতে আদি থেকে কোনো ভূখণ্ডে বাস করে আসছেন এমন ভাষাগত সংখ্যালঘু জনজাতি, যারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত নয়। অন্যদিকে, ‘উপজাতি’ বলতে কোনো নির্দিষ্ট জাতির শাখা জাতিকে বোঝায়; যা একটি নেতিবাচক অভিধা; আদিবাসীরা ‘উপজাতি’ কথাটিকে অনেক আগেই প্রত্যাখান করেছে। …
এ অর্থে, লেখায় শুধুমাত্র ‘আদিবাসী’ কথাটির ব্যবহারই বাঞ্চনীয়। আন্তর্জাতিকভাবেও ‘আদিবাসী’ বা ‘ইন্ডিজিনাস পিপল’ কথাটি স্বীকৃত; ‘উপজাতী’ বা ‘ট্রাইবেল’ ততটা নয়।
অনেক ধন্যবাদ। :yes:
@বিপ্লব রহমান, অনেক ধন্যবাদ। ‘উপজাতি’ শব্দটা নিয়ে এভাবে ভাবিনি। ভুল হয়ে গেছে। আদিবাসীদের একটা সম্প্রদায়ের কথা বলতে চেয়েছিলাম। ‘উপজাতি’ শব্দটা তুলে নিলাম। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।
অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের ওপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার ও আগ্রাসনের কিছু বর্ণনা আমার “অস্ট্রেলিয়ার পথে পথে” বইতে কিছুটা উল্লেখ করেছিলাম।
@প্রদীপ দেব,
আপনার ‘অস্ট্রেলিয়ার পথে পথে’ বইটা পড়তে চাই। কী করে পাবো?
অনেক ধন্যবাদ। :yes: